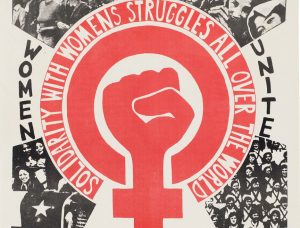দাবিটা হওয়ার কথা ছিল – স্বাস্থ্য নাগরিকের মৌলিক অধিকার। অসুস্থ হলে সুচিকিৎসা পাওয়াটা – জাতি/ধর্ম/সামাজিক অবস্থান/আর্থিক ক্ষমতা-নির্বিশেষে – নাগরিকের মৌলিক অধিকার।
অথচ আমাদের বোঝানো হলো – বুঝিয়ে ফেলা গেল – আর পাঁচটা পণ্যের মতো, আর পাঁচটা পরিষেবার মতো, স্বাস্থ্য-চিকিৎসাও ক্রয়যোগ্য। অর্থাৎ, হতদরিদ্র মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে চিকিৎসা পান সেটুকু সরকার দেখার চেষ্টা করবে – কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে সরকার অত দায়িত্ব নিতে পারবে না, তাঁরা নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, নিজ নিজ ‘চয়েস’ অনুসারে, চিকিৎসা কিনে নেবেন।
সুতরাং, বড় বড় রাস্তার পাশে দেবদারু গাছের মতো করে বেড়ে উঠল একের পর এক পাঁচতারা হাসপাতাল। সেসব হাসপাতালের মস্ত মস্ত হোর্ডিং-এ আকাশ আড়াল হয়ে গেল। আর আমরা জানতে পারলাম, গরীবের জন্য সরকারি হাসপাতাল তো রইলই – যদিও সেই ‘গরীবের হাসপাতাল’ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ কিংবা কর্মী-নিয়োগ বন্ধ করে ব্যবস্থাটিকে রুগ্ন থেকে মুমূর্ষু করে ফেলা হলো – কিন্তু সে যা-ই হোক, সত্যিকারের “আন্তর্জাতিক মানের” চিকিৎসা পেতে হলে যেতে হবে ওই পাঁচতারা হাসপাতালে। সেরা পরিকাঠামো কিংবা সেরা চিকিৎসক – সবই ওইখানে। নেতা-মন্ত্রী গাইয়ে-বাজিয়ে-লেখক -কবি-শিল্পীঅভিনেতা থেকে পেজ-থ্রি সেলিব্রিটি, চিকিৎসার দরকার পড়লে সবাই যান – এবং সবাইকে, সুতরাং আপনাকেও, যেতে হবে – ওই পাঁচতারা হাসপাতালে।
মুশকিল হলো, প্রচার কিংবা বিজ্ঞাপন যা-ই বোঝাক, চিকিৎসা তো সত্যি সত্যি ফেয়ারনেস ক্রিম বা রেস্তোরাঁর খাবারের মতো কোনও বিলাসদ্রব্য নয় – এ হলো একান্তই জরুরি পরিষেবা, প্রয়োজনের মুহূর্তে যে কোনও মূল্যে মানুষ তা পেতে চান। মুমূর্ষু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুচিকিৎসা না পেলে গরীবেরও মনে হয়, হয়তো ওই পাঁচতারা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলেই প্রিয়জন সেরে উঠত। সুতরাং, সরকারি হাসপাতালের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়তে থাকে – বাড়তে থাকে ক্ষোভ – আর পাঁচতারা হাসপাতাল, ক্রমশই, হয়ে উঠতে থাকে একান্ত কাম্য, মৃত্যুর মুখ থেকে সুস্থ করে ফেরাতে পারে এমন স্বপ্নরাজ্যের প্রতীক।
এমতাবস্থায়, সরকারের কাছে অগ্রাধিকার হওয়ার কথা ছিল – সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনিয়োগ, বড় সংখ্যায় কর্মীনিয়োগ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। কিন্তু সে অনেক বড় কাজ – জটিলও বটে, তদুপরি মুনাফামুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থার মালিকদের চটিয়ে ফেলার সম্ভাবনার কারণে বিপজ্জনকও বটে।
সুতরাং সরকার তিনটি কাজ করলেন।
১. সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় কত কমসংখ্যক চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন সেই হিসেবে না গিয়ে প্রচার শুরু করলেন, যে, সরকারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করেন না বলেই মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। এর দ্বারা সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা সহজেই চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বেষে বদলে ফেলা গেল। তদুপরি, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিনির্ধারক কমিটিতেও গুরুত্ব পেতে থাকলেন কর্পোরেট হাসপাতালের ‘বড় ডাক্তার’-রা – সুতরাং স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন পথটি আদতে উন্নততর, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা কোন পথে চলা উচিত সে বিষয়ে কাদের মতামতটা শিরোধার্য, এ বিষয়ে কোনও ধোঁয়াশা রইল না।
২. সরকারি স্বাস্থ্যবীমা-র মাধ্যমে হতদরিদ্র মানুষও যাতে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হলো। গরীব-নিম্নবিত্ত – অর্থাৎ রাজ্যের বড় অংশের মানুষ – এতদিন অব্দি তাঁরা পাঁচতারা হাসপাতালের ‘কাস্টমার’ হতে পারতেন না। সরকারি স্বাস্থ্যবীমা সে ব্যবস্থা করল। অর্থাৎ করদাতাদের অর্থে মুনাফামুখী বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুষ্টি জোগানো গেল। বলাই বাহুল্য, বীমার এই অর্থ সরাসরি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় হলে অনেক বেশি মানুষের উপকার হতো – এবং বীমার টাকা ব্যক্তিমানুষের চিকিৎসায় এককালীন ব্যয় হলেও পরিকাঠামোর উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে লাভ দেয়, সেহেতু পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যয় অনেক বেশি দিন ধরে বেশি মানুষের উপকার করতে পারত।
৩. মুনাফাকামী স্বাস্থ্যব্যবস্থার কর্ণধারদের ডেকে মাঝেমধ্যে সরকার খুব বকে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। সরকারের জনমুখী ইমেজ পুষ্টি পেল তো বটেই, উপরন্তু এর দ্বারা জনসাধারণের কাছে এই বার্তা দেওয়া গেল, যে, আপনার নির্ভয়ে পাঁচতারা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান – খরচা একটু হবে বটে, কিন্তু বেশি খরচা যাতে না হয় সেজন্য সরকার সর্বদাই সজাগ – তবে খরচা হলেও চিকিৎসাটা পাবেন।
হ্যাঁ, কথাগুলো একটু অতিসরলীকরণ করেই বললাম – কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা মোটামুটি এরকমই। এর সঙ্গে আরও কিছু পয়েন্ট যোগ করা-ই যেত – যেমন, যেখানে বিনেপয়সায় চিকিৎসা হওয়ার কথা সেই সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসা করাতে স্বাস্থ্যবীমা-র প্রয়োজনীয়তা, যাতে মানুষ দেখতে পান যে বীমা-কার্ড পাঁচতারা কিংবা সরকারি, দু’জায়গাতেই লাগছে, সুতরাং পাঁচতারার স্বাচ্ছন্দ্যই শ্রেয় – অথবা ন্যূনতম পরিকাঠামো ছাড়াই একগাদা মেডিকেল কলেজ খুলে রাশি রাশি ডাক্তার তৈরি করা হতে থাকল, অথচ তাঁদের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় নিয়োগ করা হলো না, যাতে সেই সদ্য পাশ করা ডাক্তাররা চাকরির জন্য কর্পোরেট হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয় এবং কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ডাক্তার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান সবসময়ই চাহিদার চাইতে ঢের বেশি থাকে – কিন্তু কথা বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন – এককথায় বলতে হলে, সরকারবাহাদুর যেভাবে সুপরিকল্পিত পথে পাঁচতারা স্বাস্থ্যব্যবস্থার মান্যতা-বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটালেন, তা সত্যিই চমকপ্রদ।
এমতাবস্থায়, সর্বশেষ পদক্ষেপটি আর নতুন করে বিস্মিত করার মতো নয়। এবারে সরকারই কর্পোরেট হয়ে উঠতে চলেছেন। সরকারি হাসপাতালেই চালু হচ্ছে নতুন ওয়ার্ড – খরচ পাঁচতারা হাসপাতালের কাছাকাছিই – খবর পেলাম, রাত্রিপিছু বেড-ভাড়া দাঁড়াবে পাঁচ হাজার টাকা থেকে পনের হাজার অব্দি – সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে কর্পোরেট স্বাস্থ্য-ব্যবসার মিলমিশ এবারে দুধ ও জলের সমসত্ত্ব দ্রবণের মতো উপাদেয় হতে চলেছে।
আশা করা চলে, অতঃপর, কোনটি সরকারি আর কোনটি বেসরকারি, কোনটি জনকল্যাণমুখী আর কোনটি মুনাফাকামী – সে ব্যবধান ঘুচে যাবে মানুষের মনেও। সেই চাল ও কাঁকরের ‘সমসত্ত্ব’ মিশ্রণে শেষ অবধি কোন পক্ষ লাভবান হবে, সে বিষয়ে সংশয় থাকার কথা নয়।
এই লেখাটির এক অল্প পরিবর্তিত রূপ আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৪ অক্টোবর ২০২৫ এ প্রকাশিত।