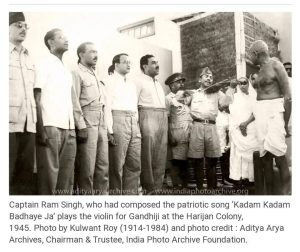সময়কে আমি একটুও ভালবাসি না। আসলে এমন ছটফটে, পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোককে আমার একটুও পছন্দ নয়। ধরে বেঁধে, খোশামোদ করে, ভয় দেখিয়ে কোনওভাবেই যাকে আটকে রাখা সম্ভব হয় না, তেমন ব্যক্তি আমার বন্ধু হতে পারে না কিছুতেই।
বি আর চোপড়ার মহাভারতে গুরুগম্ভীরতম কণ্ঠে সে যতই নিজেকে রাশভারি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুক, আসলে সে একজন তরলমতি, চরিত্রহীন মানুষ সেটা আমার বেশ জানা হয়ে গিয়েছে। আজ একজনের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয়ে কিছুদিন পরেই যে অন্যজনের বসত আবাদ করতে ছোটে, আদতে সে যে শরতের মেঘেদের মতোই নষ্টচরিত্র, এ বিষয়ে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে কি? নেই।
তাই এ হেন নষ্টমতি সময়কে কবজিতে বেঁধে কিংবা ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার নিষ্ঠুর আনন্দে মেতে উঠে আমি সময় মাপার যন্তরটিকে অপ্রয়োজনীয় রকমের ভালবেসে ফেলেছিলাম সেই ছেলেবেলা থেকেই। ঘড়ি।
আমার ঘড়িপ্রেম একটা মিথ বিশেষ। কর্মক্ষেত্রে কারোর বিয়ে, জন্মদিন বা অবসরকালে, বন্ধুস্বজনের বিবাহবার্ষিকী, নতুন চাকরির উদযাপন, পছন্দসই জায়গায় বদলি, সন্তানের পরীক্ষা পাশের উৎসবে — এইরকম অগুন্তি অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে এতকাল যাবত ঘড়ি এবং কেবলমাত্র ঘড়িই আমার প্রথম এবং শেষ পছন্দ।
অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে এখন হাসপাতালের বড়স্যার আমাকে ‘অমুকের বিয়েতে যাচ্ছেন তো? কি গিফট দিচ্ছেন?’ জাতীয় কথা আর জিজ্ঞাসা করেন না — সোজা লং জাম্প দিয়ে প্রশ্ন রাখেন — ‘এবারের নেমন্তন্নে কোন ব্র্যাণ্ড দেবেন?’
উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে যখন পোস্টেড ছিলাম, তখন ঐ গণ্ডগ্রামে বিনোদন বলতে ছিল হাসপাতালের কর্মী স্থানীয় বাসিন্দা কারোর বিয়েশাদির নেমন্তন্ন! তা, সেখানে শৌখিন উপহার কেনার একটিই বিপণি ছিল — রঞ্জন স্টোর্স। সেই মনিহারি দোকানে বিস্কফার্মের নতুন লঞ্চ হওয়া বিস্কুট থেকে ফ্যাশনেবল খেলনা মোটরগাড়ি অবধি কিনতে পাওয়া যেত বলে তার মালিক গর্বে ছাতি দশহাত করে পথ হাঁটতেন।
একবার স্থানীয় এক নব্য চিকিৎসকের বিয়েতে হাসপাতালসুদ্ধু আমন্ত্রিত হলাম। ছেলেটি আবার কালিয়াগঞ্জের তৎকালীন বিধায়কের ভাইপো হয় সম্পর্কে। ওখানে তখন যৌথভাবে উপহার দেওয়ার চল ছিল, মানে সব ডাক্তাররা মিলে একটা গিফট দেবে, আবার সব নার্সিং স্টাফ মিলে অন্যকিছু — এইরকম আর কি! মিসেস কোলে, মানে আমার মঞ্জুদি ঠিক করলেন হরিনারায়ণ বস্ত্রালয় থেকে সাটিনের বেডকভার আর বালিশের খোল দেওয়া হবে, শহরের নতুন আমদানি! আমি পোস্টিং বদলের চক্করে রাইটার্সে ঢুঁ মারার অছিলায় গত ছুটিতে লালবাজারের সামনের ‘টাইম কিং’এ একখানা জম্পেশ দেওয়াল ঘড়ি দেখে এসেছিলাম। সে ভারি মজার জিনিস! পেণ্ডুলামবিহীন ঘড়ি, কিন্তু ঘন্টায় ঘন্টায় মধুর স্বরে সময় জানান দেবে ঠিক। সাটিনের বেডকভার শুনে প্রথমেই নাক কুঁচকেছিলাম শহুরে উন্নাসিকতায় — তার উপর মাসকাবারি বাজার করতে গিয়ে রঞ্জন স্টোর্সে যখন অবিকল ঐ দেওয়াল ঘড়িটিই সাজানো রয়েছে দেখলাম, মরীয়া হয়ে কিনেই ফেললাম সেটা। স্ত্রীর পছন্দ খারিজ হয়ে যাওয়ায় ডঃ কোলে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সম্ভবত — আপত্তি অবশ্য করেননি।
যথাসময়ে বিবাহবাসরে সদলবলে উপস্থিত হয়ে উপহারের বড় সাইজের বাক্সটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কনেকে দিতে ইশারা করলেন স্যার।
আমি ফিসফিস করে বললাম — ‘সবচেয়ে সিনিয়রকেই এই কাজটি করতে হয়’।
আমার স্বল্পবাক বড়কর্তা বললেন — ‘যতজন রয়েছি, তার মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বেশি সেজেছ। আমি তোমার চেয়ে কম সেজেছি। অতএব, যাও — গিয়ে মেয়ের হাতে ওটা ধরিয়ে দাও।’
রঞ্জনের হতভাগা মালিক নাকি সতীর অপমানে ক্ষুব্ধ পতিস্যার, কার কীর্তি জানতে পারিনি — ঘড়ির প্যাকেট কনেবউয়ের হাতে দেওয়া মাত্র রকবাজদের শিসের মতো সুর তুলে হালফ্যাশনের যন্তর যাম ঘোষণা করতে আরম্ভ করল। চকমকে র্যাপার মোড়া প্যাকেট, তাকে খুলে ফচকে আওয়াজি ঘড়িকে থামানো সম্ভব নয়, আমার মুখ লাল, উপস্থিত সকলেই হাসি চাপছে — সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়েছিল বটে!
ষোলো বছর বয়সে প্রথম বাছুরে প্রেমে পড়েছিলাম শ্যামনগর থেকে পার্ক স্ট্রিট লোরেটো যাতায়াতের কালে। সে করুণ কিসসা ইনিয়ে বিনিয়ে ফেসবুকে লিখেওছি এক সময়। তা সেই সুদর্শন সহযাত্রী ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি আমার ষোড়শ জন্মদিনে একখানি গোলাপি রঙের পেন আর গোলাপি স্ট্র্যাপওয়ালা ডিজিট্যাল ঘড়ি (তখন একে ইলেকট্রনিক ঘড়ি বলত — ভারি শস্তা ছিল) উপহার দিয়েছিল। ছ’মাসের মধ্যে ‘সে আমার ছোট বোন’ সম্বোধনে সেই সাধের অকালপক্ক প্রেমের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে — আর আমার সব রাগ এসে পড়ে ঘড়িটার উপর। মায়ের রান্নাঘরের শিলনোড়া দিয়ে তাকে পিটিয়ে ছাতু করে জমাদারের টিনে ফেলে দিয়েছিলাম মনে আছে। আশ্চর্য এটাই, যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও সেই ফাঁসির আসামির সবজেটে স্ক্রিনে সঠিক সময় এবং তারিখ জ্বলজ্বল করছিল। তাই বোধহয় তাকে এখনও ভুলতে পারিনি। (ঘড়িটার কথা বলছি, অন্য কিছু ভাবলে মারাত্মক ক্ষিপ্ত হবো কিন্তু)।
ভাদ্রের বাদরে পুরোনো শাড়িজামা রোদে দেওয়ার সুযোগ হয়নি এবারে। আজ আকাশ একটু চকোসা দেখে আলমারি খুলেছিলাম সেগুলো বের করতে। বাবা মায়ের বিয়ের আলমারি। কি ভেবে লকার হাঁটকাতে আরম্ভ করেছিলাম জানি না — ওদের স্মৃতিতর্পণ করার জন্য আমার কোনও মেমেন্টোর প্রয়োজন তো পড়ে না কখনও।
সেই লকার ঘাঁটতে গিয়ে অনেক মণিমুক্তো বেরোলো। মোটা শিরীষ কাগজে বুড়োদাদুর আলতা রাঙানো পায়ের ছাপ, মায়ের বিয়ের রুপোর সিঁদুরকৌটো, পিঁজে আসা লালচে চেলির ওড়না, আমার ইশকুলের বানান পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার রঙচটা মেডেল আর ১৯৭৩ সালে মাকে লেখা বাবার একখানা চিঠি। ন’জ্যাঠা চাকরি করতেন আসানসোলের কাছে রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেবলস ফ্যাকটরিতে। বছর চারেকের আমাকে নিয়ে শীতের ছুটিতে মা সেখানে ছিল কয়েক সপ্তাহের জন্য — বাবা রয়ে গিয়েছিল উত্তর শহরতলিতে বুড়োদাদুর পৈতৃক বাড়িতে। তখন বাবার নতুন চাকরি হিন্দমোটরে, অধ্যাপনার কাজ ছাড়িয়ে মামা ব্যবস্থা করে দিয়েছে চেষ্টাচরিত্র করে, অফিস থেকে ছুটি পাওয়া কঠিন — অগত্যা চিঠি। দু’জনেই সময়রেখার ওপারে, তাই অনুমতি ছাড়াই পড়ে ফেললাম সেই চিঠি। হলদে হয়ে আসা মোটা প্যাডের কাগজে উইং সাং ঝর্না কলমে ঝরঝরে মুক্তাক্ষরে বাবার লেখা — তাতে বিরহ রয়েছে, কাব্য নেই। নিখাদ গদ্যে মায়ের স্বাস্থ্য, আমার হরলিক্স আর অফিসের চাকরির প্রথম মাইনের টাকায় পাড়ার নরেনের মুদিখানার ধার শোধ করার ফিরিস্তি! তিরিশ বছরের মা বুঝেছিল কিনা জানি না, তবে ছাপ্পান্ন বছরের এই একলা আমি চিঠির প্রতি ছত্রে বাবার আকুলতা, উদ্বেগ আর একাকিত্বের কষ্টটা অনুভব করতে পারল অনায়াসে।
ঐ চিঠির পাশেই আবিষ্কার করলাম আরও একটা জিনিস। একটা স্টিল ব্যাণ্ডের পুরোনো লেডিজ রিস্টওয়াচ। হাতে নিতেই পর্দা সরিয়ে দামাল স্মৃতিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখের পাতায়। ১৯৮৪। আইসিএসই পরীক্ষা। আমার ইশকুলের শেষ পরীক্ষা। বাবা কিনে দিয়েছিল হলদে ডায়ালের এই এইচএমটি-টা। খুব পছন্দ ছিল আমার। কলেজের শেষদিকেও পরেছি। এখন পরতে গেলাম — আঁটল না, কবজি চওড়া হয়ে গিয়েছে। দম দিলাম অন্যমনস্কভাবে। টুকটুক করে চলতে আরম্ভ করল চল্লিশ বছরের পুরোনো সময়রক্ষক। কানের কাছে নিতে শব্দ পেলাম – টিকটিক টিকটিক — আশপাশের নির্জনতা ছাপিয়ে ফিরে পাওয়া একটুকরো হারানো সময়ের স্পন্দন শুনতে পেলাম স্পষ্ট।
নাহ্, আরও ভাল করে খুঁজতে হবে লকারটা। সময় নিয়ে। অনেককাল আগে হারিয়ে যাওয়া একটা গোলগাল হামা টানা হাবলির সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে হঠাৎ।
আমি পছন্দ করি আর না করি, সময় লোকটা খুব শক্তিশালী — খুব।