শুরুর কথা – আয়ুর্বেদীয় দোষ এবং হিপোক্রেটিয় humors
গোড়াতে আমাদের উপলব্ধিতে আসা প্রয়োজন, আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষ তত্ত্ব আমাদের আধুনিক পরিভাষায় মানুষের শরীরের physiology তথা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে সেসময়ের উপযুক্ত জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, অনুমান এবং যৌক্তিক বিচার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চরক-সংহিতা-র সূত্রস্থানে বলা হয়েছে –
“তত্রাহারঃ প্রসাদাখ্যো রসং কিট্টঞ্চ মলাখ্যমভিনির্বর্তয়তে।
কিট্টাদ্ মূত্রস্বেদপুরীষবাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ কর্ণাক্ষিনাসিকাস্যলোমকূপজনন্মলাঃ কেশশ্মশ্রুলোমনখাদরশ্চাবরবাঃ পুষ্যন্তি।” (সূঃ ২৮.৪)
বাংলায় এর অর্থ – এই প্রক্রিয়া থেকে (যেমন আহার) প্রসাদ (the nutrient-rich essence or extract that remains after the body’s metabolic processes) নামক রস এবং কিট্ট[1] নামক মল জন্মে থাকে। কিট্টাংশ থেকে মূত্র, স্বেদ, বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এবং কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ লোমকূপ ও দন্তের মল জন্মে থাকে। কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ইত্যাদি অবয়ব সমূহও কিট্টাংশ থেকে পরিপুষ্ট হয়। (চ।সূঃ ২৮.৪)
পরে বলা হয়েছে – রস ও প্রসাদ নামক ধাতুসকলের গমনপথ স্রোতঃসমূহ। সেই সব স্ব স্ব ধাতুসমূহকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পোষণ (the process of nourishing and supporting the body) করে। এভাবে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় (পানোপযোগী) ইত্যাদি চার রকমের আহার থেকেই শরীর ও শরীরের ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হয়। হিতাহিত আহারের উপযোগ (dietary rules) বশতঃই শরীরের ব্যাধিসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। (চ।সূঃ ২৮.৫)
মীরা রায় বলছেন, সুশ্রুত একটি রোগের ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনার মধ্যে রাখেন – রোগের প্রথম প্রকাশের সময় এবং ঋতু, রোগীর জাত (caste), সেসব উপাদান রোগীকে আরাম দেয়, রোগের কারণ, বেদনা বৃদ্ধির কারণ, রোগীর বল (strenth), হজম এবং ক্ষুধার চরিত্র, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পায়ুদ্বার দিয়ে বায়ুর নির্গমন অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া, সময়ের সাথে রোগের পূর্ণ পরিণতি (maturity)।[2]
দাসগুপ্ত জানিয়েছেন যে, বাগভট (৬ষ্ঠ শতাব্দী) এক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। বাগভট দোষ, ধাতু ও মল-কে পৃথকভাবে দেখেছেন। এবং এদেরকে দেহের মূল হিসেবে বিবেচনা করেন। বাগভটের ধারণানুযায়ী, বায়ু দেহকে ধারণ করে, উৎসাহ (energy), নিঃশ্বাস (inspiration), চেষ্টা (mental and bodily movements), বেগ-প্রবর্তন (ejective forces) প্রদান করে।[3] ১৯৭৪ সালে মিউলেনবেল্ড বলেছিলেন – “চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে (medical point of view) আয়ুর্বেদীয় সংস্কৃত টেক্সটের ব্যাখ্যা অ-ভারতীয় স্কলারেরা দীর্ঘদিন উপেক্ষা করেছেন। বিপরীতদিকে, অনেকসংখ্যক ভারতীয় স্কলার আয়ুর্বেদে বর্ণিত রোগাবস্থাকে (disorders) readily equate … with syndromes and diseases recognized in medicine.”[4]
পরবর্তীতে মিউলেনবেল্ড বলেছেন – “গোড়াতে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলার আছে যে, ভারতীয় মেডিসিনে রোগের গতিপথকে (course of disease) ধরে নেওয়া হয় ক্রমবিকাশের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে। কোন রোগ হল সেরকম কিছু যা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়। পূর্বরূপ (prodromes) বিকশিত হয় পূর্ণাঙ্গ উপসর্গে (রূপ)। পরবর্তী অনুষঙ্গ (secondary affections – উপদ্রব) হল গোড়ার (basic) রোগাক্রান্ত প্রক্রিয়ার (morbid process) পরিণতি। এই প্রক্রিয়ার শেষে আরোগ্য লাভ হয় কিংবা প্রাণনাশক লক্ষণ (অরিষ্ট) প্রকাশ পায়, যা মৃত্যুর পূর্বাভাস। এই বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ আলাদা করে চিহ্নিত করা আছে। বহু ক্ষেত্রে এসমস্ত লক্ষণের বিশেষ বিবরণ পদ্যের আকারে (mnemonic verses) দেওয়া হয় – যেহেতু গদ্যে বিবরণের চাইতে মনে রাখা সহজ।”[5]
বাগভটের (কোথাও কোথাও বাহাট-ও বলা হয়েছে) অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম-এ সূত্রস্থানের ১১শ অধ্যায়ের শিরোনাম “দোষাদিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়”। এই অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটিই হচ্ছে (যা উপরে আলোচনা হয়েছে) –
“দোষধাতুমলা মূলং সদা দেহস্য।” (বা।সূঃ ১.১১.১)[6]
এর ব্যাখ্যা আমরা আগেই দাসগুপ্তকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করেছি। পিত্ত-র ক্ষেত্রে বলা হয়েছে – “পিত্তং পক্তযূষ্মদর্শনৈ।। … শ্লেষ্মা স্থিরত্বস্নিগ্ধত্বসন্ধিববন্ধক্ষমাদিভিঃ।।” (বা।সূঃ ১১.২-৩)[7] বাংলায় এর অর্থ হবে – পিত্ত দেহকে বিপাকক্রিয়ায় (পক্তযূষ্ম – digestive function), শরীরের তাপ (heat), দৃষ্টিশক্তির কাজ (দর্শনৈ), ক্ষুধা, গাত্রবর্ণ (প্রভা), মেধা (retentive faculty, retentiveness (of memory)[8], ধী (power of understanding), শৌর্য্য (courage), এবং “তনু মার্দবৈঃ” অর্থাৎ দেহের নরম ভাব রক্ষা করতে সাহয্য করে।
শ্লেষ্মা দেহের দৃঢ়তা (স্থিরত্ব), স্নিগ্ধত্ব (unctuousness), “সন্ধিবন্ধ” (serving to unite the joints), “ক্ষমাদিভিঃ” (power of tolerance, endurance, forgiving nature) প্রদান করে।
সামগ্রিক পর্যালোচনার পরে দাসগুপ্ত জানাচ্ছেন – “A disease, on this view, is the disturbance of doṣas, and as doṣas are entities independent of the dhātus, the disturbance of doṣas may not necessarily mean the disturbance of dhātus.”[9]
মিউলেনবেল্ড অষ্টাঙ্গ হৃদয়-এ যে বিষয়গুলোর অবতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক কী সে বিষয়ে তাঁর অভিমত মিত বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন – “therapeutic procedures indicated in cases of increase or decrease of a bodily element or waste product (11.30-33)…”[10]
এবার আমরা ভিন্নতর বিষয়ের অবতারণা করি। রাহুল পিটার দাস তাঁর ম্যাগনাম ওপাস বিপুলাকায় গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন “The Problems”।[11] কেন শুরুতেই সমস্যার কথা তুলে ধরলেন দাস? এর উত্তরও তিনিই দিয়েছেন – আর্তব (সুশ্রুত সংহিতা-য় ব্যবহৃত শব্দ – মেয়েদের procreational fluid or menstrual discharge অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, যেমন শস্য, বৃষ্টিভরা মেঘ ইত্যাদি। এরকম আরও কিছু প্রাচীন শব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণের সমস্যা নিয়ে তাঁর মতামত হচ্ছে – “this small example shows how necessary a critical edition of this text remains, and it is a crying need even after over a hundred and fifty years of what purports to be critical scholarship on the subject of Indian medicine no such editions(s) exist, except for SIDDHI (সিদ্ধিস্থান)।”[12]
আমি text-এর critical edition নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। তবে এখানে আয়ুর্বেদের মূল ভিত্তি ত্রিদোষ তত্ত্ব এবং হিপোক্রেটিয় মেডিসিনের ভিত্তি humours নিয়ে কিছু কথা বলে নিই।
বরেণ্য নৃতাত্ত্বিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ Francis Zimmermann তাঁর ব্যাখায় দোষ-কে ব্যাখ্যা করেছেন humuor বলে। তাঁর কথায় – “A major problem facing Western translators of Ayurvedic texts is that of the specialized usage of a common Sanskrit word to designate strange physiological processes or products, such as coctions, spirits, humors. These words are literally untranslatable, because they are embedded in a culture-bound set of specifIc images. No Indian pundit will ever accept to say “humors” for the doṣa-s, or “wind” for vāta (wind defined as a body fluid, one of the three humors). They will argue that, in such translations, wrong metaphors are mistakenly substituted for right conceptions … Due to their metaphorical nature, all translations are treasons – all the more so when the matter under consideration is not based on facts but on speculation.”[13]
Dominik Wujastyk-ও জিমারম্যানকে অনুসরণ করে দোষ-এর প্রতিশব্দ হিসেবে হিপোক্রেটিয় “হিউমার”-কে ব্যবহার করেছেন।[14] কেনেথ যিস্কও দোষ-কে “humours” বলেছেন।[15] যিস্ক-এর ধারণানুযায়ী, ত্রিদোষ তত্ত্বের ধারণা বৌদ্ধ চিকিৎসা থেকে আহরিত হয়েছে। তিনি উদাহরণ হিসেবে সুশ্রুত-সংহিতা-র উল্লেখ করেছেন – “The discussion of doṣas in the Suśruta Saṃhitā is presented in same style as that found in early Buddhist literature. Not only are there four pathogenic agents, arranged in a similar three-plus-one construction, but the literary style used to introduce them is also the same, a prose passage followed by a summary verse.”[16]
যিস্ক আরেকটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন – আলেকজান্ডার যে সময়ে তৎকালীন ভারতীয় ভূখন্ডে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিলেন, সেসময়ে গ্রিক মেডিসিনের প্রভাব আয়ুর্বেদের ওপরে পড়ে থাকতে পারে – “The examination of the Greek theories of disease-causation revealed a plurality of ideas, some of which harmonised with the developing Ayurvedic nosology, where different theories and numerical configurations of the basic elements were being discussed and tried out. A fixed number of doṣas, therefore, evolved over time.”[17] অধিকন্তু “The parallels and similarities between ancient Indian and Greek nosological theories further testifies to an intellectual environment in ancient (northwest) India, where medical concepts were discussed and eventually adopted.”[18]
এতক্ষণের আলোচনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের গভীরতর ভাবনার জন্য সামনে এল – (১) দোষ-এর অনির্ধারিত চরিত্র এবং উপাদান, (২) আয়ুর্বেদের প্রাচীন স্তরের ওপরে তাত্ত্বিকভাবে বৌদ্ধ মেডিসিন ও চিকিৎসাপদ্ধতির সম্ভাব্য গভীর প্রভাব, এবং (৩) গ্রিক মেডিসিনের “humour” তত্ত্বের প্রভাব আয়ুর্বেদের ওপরে পড়ে থাকতে পারে – দীর্ঘ সময়ের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।
কিন্তু এসব সত্ত্বেও জিমারম্যান যেভাবে দোষ-কে “body fluid”-এর গোত্রে ফেলেছেন, বিষয়টি সম্ভবত এতটা সরল নয়। দোষ-এর চরিত্র কী?
দোষ-এর চরিত্র নির্ধারণ করা একটি প্রায় দুঃসাধ্য একটি কাজ। তাবড় স্কলারেরাও এর সঠিক চরিত্র ব্যখ্যা করতে পারেন নি। চরক সংহিতা-র সূত্রস্থানের ১৮শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে –
“বাতে পিত্তে কফে চৈব ক্ষীণে লক্ষণমুচ্যতে।
কর্মণঃ প্রকৃতাদ্ধানির্বৃদ্ধির্বাপি বিরোধিনাম্।। (সূ.১.১৮.৫২)”
বাংলায় অর্থ – “বায়ু পিত্ত কফহীন হলে এদের স্বাভাবিক অবস্থার যে যে কাজ হয়ে থাকে তাদের হানি হয় অথবা এদের বিরুদ্ধ কাজের বৃদ্ধি হয়ে থাকে।”
পরবর্তী শ্লোকটি হচ্ছে –
“দোষপ্রকৃতিবৈশেষ্যং নিয়তং বৃদ্ধিলক্ষণম্।
দোষাণাং প্রকৃতির্হানির্বৃদ্ধির্বাপি পরীক্ষ্যতে।। (সূ.১.১৮.৫৩)”
বাংলায় অর্থান্তর করলে – “বায়ু পিত্ত ও কফের স্বাভাবিক কাজের আধিক্য হলে তার দ্বারা দোষের বৃদ্ধি বুঝতে হবে হবে। এইভাবে দোষের প্রকৃতিস্থ অবস্থা, হানি ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করা যায়।”
২১শ শতকে তথা ইউরোপীয় আধুনিকতার ধারণায় সিক্ত আমাদের বৌদ্ধিক যুক্তিক্রম দিয়ে আমরা এর মূলানুগ নির্যাস কী নিষ্কাশন করতে পারব?
আয়ুর্বেদের একজন আধুনিক তন্নিষ্ঠ পাঠকও যেমন এরকম দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হন, তেমনি যে সব স্কলারেরা আয়ুর্বেদের গভীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন টীকাকারের ব্যাখ্যার তুল্যমূল্য সুগভীর বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাও এর লাগসই উপযুক্ত ইংরেজি প্রতিশব্দ (যে প্রতিশব্দ আধুনিক পাঠকের বোধগম্য হতে পারে) তৈরি করতে পারেন নি।
এক্ষেত্রে আমরা তিনজন ভারতীয় স্কলারের পর্যবেক্ষণ দেখে নিতে পারি – “Suśruta admits that the anomaly in terminology of the three types of body-channels: śirā, srota and dhamanī. Any rigid rendering of these terms into their modern equivalents veins, ducts, and arteries will prove erroneous and confusing. This confusion is due to the fact that all the three are found at the same location, have similar shapes and branching ramifications. But their actual functions are quite different from one another. They are said to remain full and distended even after death (Ṥā. 9, 1-2)[19]
রাহুল পিটার দাস দোষ-এর ইংরেজি করেছেন “morbific entitities”। তিনি এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – “Though in medical texts also used in the meaning “fault; deficiency; defect’ disorder” or the like, doṣa is a technical term in general the commonest name for the three morbific entities wind, bile (pitta) and phlegm (śleṣman-, kapha).”[20] শুধু তাই নয়, দাস আরও অগ্রসর হয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন – “doṣa is a technical termin general the commonest name for the three morbific entities wind, bile (pitta-) and phlegm (śleṣman-, kapha-). According to Vogel, the correct translation of the term should be “source of faults” (“Fehlerquelle”), since doṣa- is derived not from the simple verb √duṣ, but from the causative.”[21]
স্বয়ং মিউলেনবেল্ড-ও বলছেন “doṣa – morbific entity”[22] এবং দোষ-এর বিস্তৃত আলোচনা এবং এর উৎস সন্ধানে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-র A History of Indian philosophy (volume 2) দেখতে বলেছেন। প্রকৃতিগত দোষ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দাসগুপ্ত বলছেন –
“The only sense (as Cakrapāṇi says) in which a doṣa is that a doṣa grows strong in a system in which a corresponding doṣa is constitutionally predominant, and it grows weaker when the opposite is the case … though the doṣas are mutually opposed to one another, they do not always neutralize one another, and it is possible for them to grow simultaneously violent in a system.”[23]
দাসগুপ্ত আরও বলছেন – “The attribution of certain number of specific qualities to the doṣas is due to a belief that the qualities of effects are due to the qualities of causes.”[24]
চরক-সংহিতা-য় বলা হয়েছে –
“তদযথা – অশীতির্বাতবিকারঃ চত্ত্বারিংশ পিত্তবিকারঃ, বিংশতি শ্লেষ্মবিকারশ্চ।” (চ।সূ.২০.১১)
বাংলায় এর অর্থ – নানা ধরনের রোগের মধ্যে বায়ুজনিত রোগ আশিপ্রকার, পিত্তজনিত রোগ চল্লিশপ্রকার এবং কফজনিত রোগ বিংশতিপ্রকার।
এটুকু আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্কলাররা একে একটি entity তথা অস্তিত্ব বা সত্তা হিসেবে দেখেছেন – তরল বা বায়বীয় বা কঠিন, কোন বর্গেই একে ফেলতে পারেন নি।
Hartmurt Scharfe তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রতে ত্রিদোষ-এর অর্থ করেছেন “three faults (doṣa)” হিসেবে – “According to the standard doctrine of Indian traditional medicine (Ayurveda) a person’s health depends on the balance of the three “faults”।[25]
আমরা আবার চরকে ফিরে আসি। সূত্রস্থানে বলা হয়েছে –
“রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষশ্চলোহথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সম্প্রশাম্যতি।।” (সূ.১.৫৯)
“রুক্ষ, (dry), শীত (cold), লঘু (light), সুক্ষ্ম (subtle), চল (moving), বিশদ (scattering everything else in different directions) এবং খর (rough) – এই কয়েকটি বায়ুর গুণ। এদের বিপরীত গুণবিশিষ্টদ্রব্যের সাহায্যে বায়ু প্রশমিত হয়ে থাকে।”[26]
পরের দুটি শ্লোকে পিত্ত এবং শ্লেষ্মা-র চরিত্র ও গুণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সমগ্র আলোচনা থেকে বায়ু, পিত্ত ও কফ তথা শ্লেষ্মার নির্দিষ্ট রূপ কী, এর যথাযথ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব একটি কাজ।
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বিচার অনুযায়ী, অথর্ববেদ-এও বিভিন্ন ধরনের বায়ু-র উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও আগে ছান্দোগ্য উপনিষদ-এ পৃথ্বী, জল এবং অগ্নিকে “world-principles of construction” হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণে – “It seems fairly certain that the theory of vāta, piita and kapha is a later development of the view which regarded air (পবন), fire (দহন) and water (তোয়) as the fundamental constitutive principles of the body.”[27]
দাসগুপ্তের এ ধারণার সমর্থন মেলে সুশ্রুত সংহিতা-র শারীরস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোকে – “as acknowledged by some authorities, those in which vāyu, agni (fire) and jala (water) predominate are the same as those dominated by vāta, pitta and kapha; the constituents with a predominance of earth (the pārthiva constitution) and ākāśa (the nābhasa constitution) possess their own distinctive characteristics (4.80).”[28]
এখান থেকে বোঝা সম্ভব যে, চরক– ও সুশ্রুত-সংহিতা-র আদি স্তরের মাঝে অথর্ববেদ এবং উপনিষদের কিছু ধারণা (যা শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে) অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে।
যাহোক, দাসগুপ্ত দোষ-কে “morbid elements” বলেছেন।[29] পরে বলেছেন – অনেক শ্লোক আছে যেখানে বায়ু, পিত্ত ও কফ-কে নির্দিষ্ট রঙ এবং “material consistency”-সম্পন্ন সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং একথাও বলা হয়েছে যে, দেহের বিভিন্ন স্থানে এরা সঞ্চিত হয়। দাসগুপ্ত আরও বলেছেন – “this would be impossible upon the interpretation that they are not real entities, but hypothetical, having only a methodological value as being no more than convenient symbols for a collective grasp of different symptoms.”[30]
অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন দাসগুপ্ত। তিনি বলছেন, সংস্কৃতে একই শব্দের স্থান বিশেষে অর্থান্তর ঘটে। তাঁর কথায় – “I could only give one sense of a word, which in the original Sanskrit has been used in a variety of senses which the word has.”[31] উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, রুক্ষ শব্দটিকে তিনি “rough” হিসেবে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এই রুক্ষ শব্দটিই “slim”, “lean”, “having insomnia”, “or (of a voice) broken” ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে সঠিক প্রতিশব্দ দেওয়া যথেষ্ট দুঃসাধ্য একটি কাজ।
এতসবের পরেও দোষ-এর চরিত্র কী এবং এর উপযুক্ত ব্যাখ্যার সমস্যাটি রয়েই গেল।
মিউলেনবেল্ড তাঁর ঋদ্ধ গবেষনাপত্রে মন্তব্য করছেন – “The classical treatises on āyurvéda are in large measure dominated by the doctrine of the doṣas, but nevertheless they do not specify which characteristics determine that a particular constituent of the body belongs to that group. Systematic expositions on this subject are not found in the commentaries on the classical Saṃhitäs either. It may therefore be useful to collect material which sheds light on those properties which are decisive in making a constitutive element of the body a doṣa.”[32]
তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী, ক্লাসিকাল সংহিতাসমূহের টীকাকারেরা দোষ-কে চিহ্নিত করেছেন এভাবে – “a set of ear-marks which they regard as distinctive for a doṣa.”[33]
তিনি এর মধ্যে ৩টির আলোচনা করেছেন – “(1) the ability to corrupt all those constituents of the body which belong to the category düṣya, (2) the ability to initiate processes leading to the manifestation of a disease, and (3) the ability to dominate a constitution.”[34] এর অতিরিক্ত কিছু মিউলেনবেল্ড বলেন নি। বিভিন্নভাবে এর স্তরায়িত ব্যাখ্যা করেছেন।
গ্রিক হিউমোরাল তত্ত্ব
Vicki Pitman তাঁর গ্রন্থে আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষ তত্ত্ব এবং গ্রিক “হিউমোরাল থিওরি” নিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে – “In spite of some differences, the model of three humours, tridoṣa, is in several aspects strikingly similar to those of the Corpus (Corpus Hippocraticum: a collection of around 60 early Ancient Greek medical works strongly associated with the physician Hippocrates and his teachings).”[35] তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী – “Although different parts of the body are made up of combinations of doṣa, one doṣa, is responsible for a particular body function, organ or tissue.”[36]
গ্রিক মেডিসিনের প্রাজ্ঞ গবেষক এডেলস্টাইন humours-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – শরীরে গোলযোগ ঘটে যখন যে কোন একটি humour প্রাধান্যকারী অবস্থানে থাকে এবং প্রতিটি ঋতুতে এরকম ঘটনা ঘটে আবার অন্য ঋতুতে “automatically cancelled out again by the opposite season.”[37]
তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল, যেহেতু humours দিয়ে দেহের সমস্ত রোগের ব্যাখ্যা করা যায় সেজন্য “Such a theory makes it unnecessary to take internal organs or their form and character into account.”[38]
এডেলস্টাইনের দুটি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষ তত্ত্বের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে রোগের সৃষ্টি এবং শরীরের অঙ্গসংস্থান-সংক্রান্ত ধারণার কিছু সাযুজ্য পাওয়া যায়। হিপক্রেটিসের মান্য অনুবাদক humours-কে juice বা রসালো পদার্থ হিসেবে গণ্য করেছেন।[39] আরেক গবেষক বলছেন – “The coction, change, attenuation, and thickening into the form of humours, take place through many and various forms”[40] এগুলো সবই সম্ভবত juice-এর ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
আমাদের ত্রিদোষ-এর উপাদান শ্লেষ্মা-র সচরাচর অনুবাদ করা হয় phlegm হিসেবে। কিন্তু হিপোক্রেটিয় phlegm চরিত্রগতভাবে সম্পুর্ণ পৃথক – “A proof that phlegm is very cold is that when you touch phlegm, bile and blood you will find phlegm coldest.”[41] “Black bile” বা কৃষ্ণ পিত্ত নিয়ে হিপোক্রেটিস বলছেন – “black bile is the most viscous of the humours in the body, and that which sticks fast the longest.”[42]
এরকম এক বস্তুর (entity?) অস্তিত্ব কল্পনা করলে তা তরল, চটচটে এবং মাঝারি ঘন চরিত্রের বোঝায়, যার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষ-এর properties-এর বিচারে কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।
খানিকটা ভিন্ন প্রসঙ্গে গিয়ে উল্লেখ করতে হয়, বাংলাতে সুশ্রুত-সংহিতা-র বাংলায় প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকদের একজন যশোদানন্দ সরকার তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রারম্ভিক “বিজ্ঞাপন”-এ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন –
(১) “নাড়ীজ্ঞান – চরক ও সুশ্রুতে নাড়ীপরীক্ষার উল্লেখে নাই।”
(২) “অণুবীক্ষণ যন্ত্র – সুশ্রুতে উল্লেখ নাই বটে … সুশ্রুতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কীটের উল্লেখ আছে, তাহাদের সংখ্যাদিও বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে যে উহাদের বিষ সহস্র সহস্র মানবদেহে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্ময় হয়।”[43] পরে বলেছেন – “চরক বা সুশ্রুতের অনুবাদ ভ্রমশূণ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা অভিমান করি না।”[44] তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি “ডল্লনাচার্য্য সংগৃহীত সুশ্রুত টীকাই অনুবাদ করেছেন”। এবং ডল্লনাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন বলে তাঁর ধারণা। উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন, গোধা = গোসাপ, তরক্ষু = নেকড়ে ইতি ভাষা, ক্রৌঞ্চ = কোঁচবক ইতি ভাষা, কেশপ্রসাধনী = ভিরুণী বা কাঁকুই ইতি লোকে… ইত্যাদি।”[45]
ভিন্ন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। যেহেতু আজ থেকে ২০০০ বছরেরও বেশি আগে যখন কোন উন্নত পরিমাপ পদ্ধতি শাস্ত্রকারেরা জানতেন না তখন স্বাভাবিক পরিমাপ পদ্ধতি (normalized measurement) ব্যবহার করেছিলেন – যেমন চরক ও সুশ্রুতের দুটি টেক্সটেই আছে মানুষের দেহের পরিমাপ স্ব স্ব অঙ্গুলিতে ১২০ আঙ্গুল।
আবার ১৩-১৪শ শতাব্দীতে রচিত শার্ঙ্গধর সংহিতা-য় আরেক ধরনের পরিমাপের বর্ণনা আছে। “মাগধ পরিভাষা –গবাক্ষের অভ্যন্তরে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিলে সেই কিরণে যে সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দৃষ্ট হয়, সেই রেণুর ত্রিশভাগের একভাগকে পরমাণু কহা যায়। ত্রিশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়। ত্রসরেণুর অপর নাম বংশী। ছয়টি বংশীতে এক মরীচি, ছয় মরীচিতে এক রাজিক, তিন রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা বা রক্তিকা (কুঁচ বা রতি), ছয় রক্তিকায় এক মাষা হয়। চারি মাষায় এক শান হয়। শানের অপর নাম ধরণ ও টঙ্ক। দুই শানে এক কোল (এক তোলা) হয়…” ইত্যাদি।[46]এখানেও দেখতে পাচ্ছি প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
শারীরস্থান – নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ
এই অধ্যায়ের নাম থেকে বোঝা যায়, এই অধ্যায়গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেহ-সংস্থান তথা anatomy নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ধাপে ধাপে সংক্ষেপে অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা করব। যদিও এই আলোচনায় physiology-র কথাও আলোচনায় আসবে।
আমি শারীরস্থানের ১০টি অধ্যায়ের মধ্যে কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। এবং এই আলোচনায় বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে যেসমস্ত চিকিৎসার কথা এবং তার বিস্তৃত বিবরণ আমি পরিহার করেছি। যেটুকু অংশ সাধারণভাবে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষিতে বোঝার জন্য কাজে লাগবে, আমার আলোচনাকে আমি সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। আশা করি এতে মূল টেক্সটের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বুঝতে আদৌ কোন সমস্যা হবেনা।
শারীরস্থানের ১ম অধায়ের শিরোনাম “সর্বভূতচিন্তাশারীরং”। মিউলেনবেল্ডের ভাষ্যে এই অধ্যায়টি “is devoted to an exposition of Sāṃkhya and its relevance to medicine. The subjects dealt with are: the avyakta and its charateritics (লক্ষ্মণ); the avyakta is the seat (অধিষ্ঠান) of many kṣetrajňas (ক্ষেত্রজ্ঞ – Spirituality, knowledge of the soul[47]) (1.3) … in medical science, however, the farsighted (পৃথুদর্শিন) regard swabhāva (স্বভাব – inherent nature), kāla (কাল – time), yadṛccha (যদৃচ্ছা – chance), niyati (নিয়তি – fate) and pariṇāma (পরিণাম – transformation) as prakṛti (প্রকৃতি – The natural condition or state of anything) (1.11)”[48]
অন্য একটি শ্লোকে সেসময়ের সামাজিক-রাজনৈতি-সাংস্কৃতিক পরিবেশে-স্থিত আয়ুর্বেদে স্বাভাবিক নিয়মেই ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে – “দেবতাদের আধিপত্যকে অধিদৈবত বলা যায়। তার মধ্যে ব্রহ্মা বুদ্ধির, রুদ্র অহঙ্কারের, চন্দ্রমা মনের, দিক্ সকল শ্রোত্রের (auditory organ), বায়ু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়ের, জল রসনার, পৃথিবী ঘ্রাণের (olfactory organs), অগ্নি বাক্যের, ইন্দ্র হস্তদ্বয়ের, বিষ্ণু পাদদ্বয়ের, মিত্র (অপর নাম সূর্য্য) পায়ুর (anus) এবং প্রজাপতি উপস্থের (external genital organs of both males and females)।” (শাঃ ১.৭)
অন্যত্র বলা হচ্ছে – “The unmanifest (অব্যক্ত), mahat (মহৎ), ahaṅkara (অহঙ্কার) and five tanmātrās – these are prakṛti (প্রকৃতি – causative source) while the remaining sixteen are vikāra (বিকার – products).”[49]
পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে –
“তস্যোপযোগোহভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্বদা।
ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে।। (শা.১.১৩)
বাংলায় – “চিকিৎসাস্থলে ঔষধাদিরূপে ভূতগ্রামের (ভুতসমূহ – আকাশ ইত্যাদি ভূত অর্থাৎ “an element; they are five – পৃথ্বী, অপ (জল), তেজস (অগ্নি), বায়ু এবং আকাশ[50]) প্রয়োগকেই সর্বদা উল্লেখ করা হয়। কেননা চিকিৎসায় পঞ্চমহাভূত থেকে জন্ম নেওয়া অস্তিত্ত ছাড়া অন্য বিষয়ের চিন্তা চিকিৎসকের নেই।”
নজর করার মতো বিষয় হল, এই অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের প্রভাব এবং সেখান থেকে সরাসরি আহরণ করা হলেও আয়ুর্বেদে এসে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর একটি প্রতিসরণ তথা refraction ঘটল। হুবহু সাংখ্যদর্শনের প্রয়োগ হলনা।
উপরোক্ত উদাহরণ ছাড়াও আরেকটি উদাহরণ হল – “আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পুরুষকে সর্বব্যাপী না বলে অসর্বব্যাপী বা প্রদেশবর্তী বলে। সাংখ্য ইত্যাদি শাস্ত্রে পুরুষকে (The soul (opp. প্রকৃতি); according to the Sānkhyas it is neither a production nor productive; it is passive and a looker-on of the Prakṛiti) সর্বব্যাপী বলে। আয়ুর্বেদোক্ত পুরুষ সর্বব্যাপী না হলেও তাঁর মধ্যে নিত্য পুরুষব্যাপক হেতুসমূহের উদাহরণ আছে।” (১.১৬)
ভিন্ন একটি বিষয়ও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে – যশোদানন্দন সরকার এবং পি ভি শর্মা দুজনেই পতঞ্জলির উল্লেখ করেছেন (১.৬)।
তাহলে কী এটা অনুমান করা যায় যে, সুশ্রুত-সংহিতা-র আগে পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়েছিল?
শেষের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে – “এই শল্যতন্ত্রে ও শালাক্যতন্ত্রে প্রকৃতি ও ষোল রকমের বিকার (products) বলা হয়েছে এবং সংক্ষেপে পুরুষও বর্ণিত হয়েছে।”[51] (১.২২)
শারীরস্থানের ২য় অধ্যায়ের শিরোনাম “শুক্রশোণিতশুদ্ধিশারীর” অধ্যায়।
মিউলেনবেল্ড তাঁর নিজস্ব ধরনে সংক্ষেপে মূল অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় জানিয়েছেন – “devoted to the purity (শুদ্ধি) of the male and female procreational fluids (শুক্র এবং শোণিত) and a number of related issues (conception, the development of foetus etc.).”[52]
অধ্যায়ের শুরুতেই বিভিন্ন ধরনের রেত তথা শুক্রের বর্ণনা করা হয়েছে –
“বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-কুণপ গ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবতি” (২.৩)
বাংলায় – “বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং কুণপ (মৃতদেহের গন্ধ), গ্রন্থি (a knot, bunch, protuberance in general[53]), পূতি-পূষবর্ণ, ক্ষীণতা ও মূত্র-পুরীষগন্ধ, এই সমস্ত দোষে শুক্র দূষিত হলে পুরুষ পুত্র উৎপাদনে সমর্থ হয় না (প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবতি)।”
আবার মিউলেনবেল্ডের শরণ নিই অল্প কথায় সমগ্র বিষয় প্রকাশ করার জন্য – “when corrupted by blood, the semen smells like a decomposing corpse (কুণিপগন্ধিন) and is profuse in quantity; semen corrupted by vāta shows clots (গ্রন্থিভূত); corrupted by pitta and kapha, it resembles foul-smelling pus (পূতিপূয়নিভ); corrupted by pitta and vāta, it is small in quantity (ক্ষীণ) and shows the features described… (2.4)”[54]
শুক্রের এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কুণপ-শুক্র, গ্রন্থি-শুক্র, পূতিপূয়-শুক্র ও ক্ষীণশুক্র কষ্টসাধ্য (curable with difficulty)। মূত্র-পুরীষ-গন্ধি শুক্র অসাধ্য (incurable). অন্যপ্রকার দূষিত শুক্র সাধ্য (curable)।
নারীদের আর্তব-এর (menstrual discharge) শুক্রের মতো একইরকম দোষযুক্ত হয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধ্য, কষ্টসাধ্য এবং অসাধ্য এই ৩ ভাগে বিভক্ত। (২.৫)
এখানে লক্ষ্য করলে দেখব, আর্তব শব্দটির ইংরেজি অর্থ কখনো menstrual discharge, কখনো mentstrual blood, আবার কখনো procrational substance করা হচ্ছে। প্রেক্ষিত-সাপেক্ষে এর অর্থান্তর ঘটছে।
আমাদের নজরে থাকবে এই শ্লোকগুলো –
“ঋতুকালে স্ত্রী দিবানিদ্রা-রত হলে তার সন্তান নিদ্রাশীল হয়। অঞ্জন (চোখের কাজল) ধারণ করলে সন্তান অন্ধ হয়। রোদন করলে বিকৃতদৃষ্টি (ophthalmic disorders) হয়। স্নান ও অনুলেপন (the application of scented pastes or herbal formulations to the body) দুঃশীল হয়, তৈলাভ্যঙ্গ (oily massage) করলে কুষ্ঠ হয়। নখ কাটলে কুনখী হয়। ধাবন করলে (দৌড়লে) চঞ্চল হয়। হাসলে সন্তানের দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়। বেশি কথা বললে সন্তান বহুভাষী (talkative) হয়। অতিশব্দ শ্রবণ করলে সন্তান বধির হয়। অবলেখন (চুল আঁচড়ানো) করলে সন্তানের মাথায় টাক হয় এবং বায়ুসেবন ও কষ্টকর পরিশ্রম করলে সন্তান উন্মত্ত হয়। এজন্য এসব পরিহার করতে হয়।” (২.২৪)
ঋতুমতী নারী তিন রাত্রি ভর্তৃসমাগম (coitus) করবে না। “ঋতুস্নানের পরে নারী যাকেই প্রথম দর্শন করবে, সন্তান তার মতো হবে। এজন্য ভর্তার মুখই প্রথম দর্শন করতে হয় … পুরুষ পুত্র লাভ করতে হলে একমাস ব্রহ্মচারী থেকে রাত্রিতে ঋতুস্নাতা নারীতে গমন করবে। গমন করার আগে সর্পিঃ (ঘি) পান করে স্নিগ্ধ হবে এবং সর্পি দুধের সাথে শাল্যান্ন ভোজন করবে।” (২.২৫-২৬)
গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ না নারী হবে সে বিষয়ে সুশ্রুত জোড় এবং বিজোড় সংখ্যক দিনের কথা উল্লেখ করেছেন – “পুত্র ইচ্ছা করলে ঋতুস্নানের চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিনে স্ত্রীগমন করবে। সেসময়ে স্ত্রীগমন করলে আয়ু, আরোগ্য এবং পুত্রের সৌভাগ্য, ঐশর্য্য ও বল হয়ে থাকে।” (২.২৮-২৯)
“স্ত্রীকামী ব্যক্তি পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিবসেও স্ত্রীগমন করতে পারে। ত্রয়োদশ প্রভৃতি দিনে স্ত্রীগমন সঠিক নয়, নিন্দনীয়।” (২.৩০)
কীভাবে বর্তমান পরিভাষায় শুক্রাণু ও ডিম্বানু পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায়, সে বিষয়টি সুশ্রুত এভাবে বলছেন – “যেমন ঘৃতপিণ্ড অগ্নিকে আশ্রয় করলে গলে যায়, সেভাবে নারীর আর্ত্তব (procrational substance[55]) পুরুষসমাগমে গলে গিয়ে বিসর্পিত হয় (dislodged) হয় এবং শুক্রের সাথে মিলিত হয়ে থাকে।” (২.৩৬) আবার “সেই শুক্র বায়ুকর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হলে, মাতৃজঠরে অবতীর্ণ দুই জীব তাতে আশ্রয় করে থাকে। এতেই যমজ সন্তান হয়। যমজেরা অধর্মকে সম্মুখীন করেই অবতীর্ণ হয়।” (২.৩৭)
“মাতা পিতার অল্পশুক্রতার কারণে আসেক্য[56] (শিথিলশিশ্ন – A kind of eunuch or neuter man[57]) নামক পুরুষ তৈরি হয়। সেই পুরুষ শুক্র পান করলে ধ্বজোচ্ছ্রায় প্রাপ্ত হয় (gets an erection)।” (২.৩৮)
এরপরে বলা হয়েছে – “যে সন্তান পূতিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাকে সৌগন্ধিক বলে। সে যোনি ও শেফের (male genitals, especially penis) গন্ধ পেলে বল লাভ করে অর্থাৎ শিথিলশিশ্ন দৃঢ় হয়, এ ধরনের নপুংসককে নাসাযোণি বলে।” (২.৩৯)
পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে – “আসেক্য, সৌগন্ধিক, কুম্ভীক ও ঈর্ষক, এই চারটি বিভাগের পুরুষ স-রেতাঃ (do have semen) হয়ে থাকে। আর ষণ্ড নামক পুরুষ অশুক্র হয়।” (২.৪৪)
এরপরে যৌন সংসর্গের বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে – একজন চিকিৎসকের চোখ দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহভাবে। “যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি স্ত্রীদের পায়ুতে পুরুষভাবে প্রবৃত্ত হয় (a man who first accepts to be the passive partner in anal intercourse and then proceeds to anal penetration of a woman) তাকে কুম্ভীক বলে। যে ব্যক্তি অন্যদের ব্যবায় (sexual intercourse) দেখে ব্যবায়ে প্রবৃত্ত হয় তাকে ঈর্ষ্যক বলে (a man who is potent only after looking at the intercourse of another couple is called īrṣyaka)।
ঋতু হবার পরে যে পুরুষ ভার্য্যাতে মোহবশতঃ উত্তানভাবে শয়নপূর্বক গমন করে, তার সেই কর্ম থেকে স্ত্রীলোকের মতো আকারপ্রকারবিশিষ্ট ষণ্ড নামক সন্তান উৎপন্ন হয় – “when a man, in a female fashion, has intercourse with his wife (during the menstrual period), a ṣaṇḍhaka may be born, who looks and behaves like a woman” যে অঙ্গনা পুরুষকে উত্তানভাবে স্থিত করে ব্যবায় (sexual intercourse) করে, তার সেই ব্যবায়ে কন্যা জন্ম নিলে সে কন্যার কার্যকলাপসমূহ (চেষ্টিত) পুরুষের মতো হয় – “when a woman, still menstruating, assumes the male position during intercourse, and a daughter is conceived, she will show male behavioural traits (2.38-43).”[58]
এখানে একটি উলেখযোগ্য শ্লোক আছে lesbian নারীদের বিষয়ে – “নারীদ্বয় রমণে ইচ্ছুক হয়ে যদি পরস্পর গমন করে এবং পরস্পর যদি শুক্রমোচন করে, তাহলে অস্থিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়।” (২.৪৭)পরের শ্লোকে বলা হয়েছে – “যে ঋতুস্নাতা নারী স্বপ্নে মৈথুন করে বায়ু তার আর্তব গ্রহণ করে কুক্ষিতে (womb) গর্ভ উৎপাদন করে। সেই গর্ভিণীর গর্ভলক্ষণ মাসে মাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলল (jelly-like or semisolid mass like sputum) পৈতৃকগুণ বিবর্জিত হয় (কললং জায়তে তস্যা বর্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈ)।” (২.৪৮)[59] এরপরে বলা হয়েছে – “the birth of deformed children, looking like a serpent, scorpion or gourd should be regarded as the result of bad acts (2.50)”[60]।
এই অধ্যায়ের শেষে কর্মফল এবং পূর্বজন্মের কথা বলা হয়েছে – “জীব যে কর্ম দ্বারা পৃথিবীতে আসে, পুনর্জন্মে তারই ফলাফল পায়। পুর্বজন্মে যেসব গুণ তাহার অভ্যস্ত থাকে, এ জন্মেও সেসব গুণ প্রাপ্ত হয়।” (২.৫৮)
সুশ্রুত সংহিতা-র শারীরস্থানে ৩য় অধ্যায়ের শিরোনাম “গর্ভাবক্রান্তি” – “devoted to conception, development of the child within the womb, and some related topics.”[61]
বলা হয়েছে – “শুক্রের আধিক্য থাকলে পুরুষ এবং আর্তবের আধিক্য থাকলে কন্যাসন্তান উৎপন্ন হয়। আর শুক্র এবং আর্তবের সমতা থাকলে নপুংসক সন্তান হয়।” (৩.৫)
মিউলেনবেল্ড বলছেন – “the period suitable to impregnation (ঋতু) consists of twelve days after (the cessation of) the menses; some are of the opinion that the same rule holds good when the woman has not menstruated visibly (অদৃষ্টাশ্রবা) (3.6).”[62]
“স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়সে আর্তব (menstruation) শুরু হয়, পঞ্চাশ বছরে বন্ধ হয়।” (৩.১১)
এখানেও আগের অধ্যায়ের মতো বলা হয়েছে – “intercourse on even days leads to to the conception of a male, and on odd days to the conception of a female child (3.12).”[63]
এরপরে গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে – “প্রথম মাসে কলল (তরল গর্ভ) উৎপন্ন হয়। ২য় মাসে মহাভূতের (শীত উষ্মা ও অনিলের সংযোগে) প্রভাবে সংহত ও ঘনীভূত (solid mass) হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিণ্ডাকৃতি (globular) হলে পুরুষসন্তান হয়, দীর্ঘাকৃতি (পেশী) হলে কন্যাসন্তান এবং অর্বুদাকৃতি (শাল্মলী কুঁড়ির মতো) হলে নপুংসক সন্তান হয়। ৩য় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তকের ৫টি পিণ্ড উৎপন্ন হয় এবং বুক্ক-পিঠের মতো অঙ্গ ও নাক চিবুক ইত্যাদি প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মভাবে উৎপত্তি হয়। ৪র্থ মাসে “the major and minor body parts become visible, and the cetanādhātu (চেতনাধাতু – the principle of consciousness) begins to manifest itself because the heart of the foetus has been formed” – হৃদয় চেতনাধাতুর স্থান। এজন্য চতুর্থ মাসে বিষয়ে অভিলাষ করে (long for objects) এবং এই সময় থেকে গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী বলে – “the defets of children, resulting from neglect of the pregnant woman’s longings; the importance of their satisfaction (3.18-21)”[64]
“৫ম মাসে মনের বোধশক্তি (মানস) অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ৬ষ্ঠ মাসে বুদ্ধি হয়। ৭ম মাসে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ স্ফুটতর হয়। ৮ম মাসে “the ojas becomes unstable; a child born in this month will not survive, because of the deficiency of its ojas (নির্জোস্তব), and also because it belongs to Nirṛti (নির্ঋতি)[65] to whom propitiatory offerings (বলি) of মাংসৌদন (rice boiled in meat broth) should be given in this period…”[66]
“নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের অন্যতম মাসই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হবার সময়। এর অন্যথা হলে জন্মের পরে বিকার ঘটে (abnormal)।” (৩.৩০)
“গর্ভস্থ নাভীনাড়ী (umbilical cord) মা-র রসবহা নাড়ীতে সংযুক্ত থাকে। সেই গর্ভনাড়ী মাতার আহারের রসবীর্য গর্ভশরীরে বহন করে। মাতার সেই উপস্নেহ (nutrients) দিয়ে গর্ভের অভিবৃদ্ধি হয়। মাতার সর্বশরীরাবয়ব-গামিনী (which run through the whole body) রসবহা ধমনী সমূহ গর্ভশরীরে গর্ভকে জীবিত রাখে।” (৩.৩১)
এর আগে একাধিক শ্লোকে গর্ভিণীর আকাঙ্খার (longings) ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – “the effects on the child of particular longings (3.22-28).
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – “যে গর্ভিণীর গোমাংসে দৌহৃদ (two hearts – one of the mother and the other of the embryo) হয়, সে বলবান সর্বক্লেশসহ সন্তান প্রসব করে। মহিষমাংসে যার দৌহৃদ হয়, সে শূর (সাহসী), রক্তচক্ষু ও লোমশ সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংসে যার দৌহৃদ হয়, তার নিদ্রালু এবং সাহসী সন্তান প্রসব করে। মৃগমাংসে যার দৌহৃদ হয়, সে লম্বা পা-বিশিষ্ট সাহসী, দ্রুত পদচারুণায় সক্ষম এবং বনচর পুত্র (জঙ্ঘালং সদা বনচরং সুতম্) প্রসব করে।”
এটুকু অংশ পাঠ করার পরে বোঝা যায়, আয়ুর্বেদের মাঝে নিবিষ্টভাবে স্তরায়িত হয়ে রয়েছে একদিকে যেমন পুনর্জন্ম, কর্মফল এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাসের মতো উপাদান, আরেকদিকে তেমন গর্ভিণীর গোমাংস, মহিষমাংস, বরাহমাংস, মৃগমাংস ইত্যাদি কোন ধর্মীয় বিধান না-মানা খাদ্যবিধির উপাদান। আয়ুর্বেদের মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, উন্মুক্ত চিন্তার পূজারি রচয়িতাদের সেসময়ের উচ্চকিত এবং প্রবল শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে পদে পদে আপস করেও নিজেদের মুক্তচিন্তাকে প্রবাহিত করেছেন তাঁদের রচিত শাস্ত্রে – বিভিন্ন শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংস্কারের পরেও অন্তর্ভুক্ত এই অংশগুলো রয়ে গেছে অদ্যাবধি।
যাহোক, শৌনক, মার্কণ্ডেয়, পরাশরের পুত্র (পারাশর্য্য), কৃতবীর্য, সুভূতি গৌতম প্রভৃতি ঋষিদের মধ্যে (এখানে সুশ্রুতের নাম অনুল্লেখিত) গর্ভে (foetus) কী ক্রমানুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয় এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার-নিষ্পত্তি আসে ধন্বন্তরির কাছ থেকে – “the final verdict came from Dnvantari who, declaring all these opinions to be false, exponded that all major and minor parts of the body develop simultaneously, although they cannot be distinguished clearly in early stages (3.32)”[67].
মিউলেলেনবেল্ড ধন্বন্তরির যুক্তিকে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করছেন – “the constituents of the foetus derive from father, mother, rasa, ātman, and sātmya; of paternal origin are all the firm (স্থির) parts; hair of the head (কেশ), face (শ্মশ্রু), and body (লোমন), bones, nails and teeth, sirās (সিরা – বানানটি নজর করুন), snāyus (স্নায়ু) and dhamanīs (ধমনী), semen (রেতস), etc.; derived from the mother are all the soft (মৃদু) parts; muscles, blood, fat (মেদস), bone marrow, heart, umbilical region, liver, spleen, intestines, ano-rectal region, etc.; derived from the rasa are: bodily solidity (উপচয়), strength (বল), complexion (বর্ণ), maintenance (স্থিতি) and decay (হানি); derived from the ātman (আত্মন) are: the senses, spiritual and worldly knowledge (জ্ঞান এবং বিজ্ঞান), span of life (আয়ুস), happiness (সুখ), grief (দুঃখ), etc.; derived from the sātmya (সাত্ম্য) are: বীর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, বর্ণ (complexion) and intelligence (মেধা) (৩.৩৩)”[68]।
এরপরে বলছেন “signs indicating that the child is male, female, or a নপুংসক, the sign indicationg that a twin-birth is expected (3.34).”
এই লক্ষণগুলো কী কী? “যে গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে প্রথম দুগ্ধদর্শন হয়, দক্ষিণ কুক্ষি আকারে বৃহত্তর হয় (দক্ষিণকুক্ষিমহত্বং চ), দক্ষিণ পদ (পা) আগে চলে (হাঁটার সময়), স্বপ্নে পুরুষ-নামের দ্রব্যে প্রধানত দৌহৃদ হয় – যেমন, পদ্ম, জলপদ্ম (water lily), উৎপল (নীল পদ্ম), কুমুদ (লাল পদ্ম), আম্রাতক (hog-plum তথা আমের ঘন রস) ইত্যাদি দর্শন হলে মুখের বর্ণ প্রসন্ন হয়, সে পুরুষ সন্তান প্রসব করবে একথা বলা যায়। এর বিপরীত হলে কন্যা প্রসব করবে… ইত্যাদি। যে গর্ভিণীর পার্শ্বদ্বয় উন্নত, উদর সামনে উন্নত ও পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন হয়, সে নপুংসক সন্তান প্রসব করে।”
শেষ শ্লোকটি হল – “অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ইত্যাদি স্বভাব থেকে হয়। কিন্তু “good or bad features of these parts are due to (the balance of) ধর্ম and অধর্ম (in previous life) (3.36).”[69]
আধুনিক embryology-র সাথে সুশ্রুত-বর্ণিত গর্ভাবস্থা এবং এর বিশদ বিবরণ যদি আমরা এক করে না দেখে ভালো করে খেয়াল করি, তাহলে আধুনিক পরিভাষায় anatomy এবং physiology উভয় ধরনের বর্ণনাই রয়েছে – একথা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।
শারীরস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের শিরোনাম “গর্ভব্যাকরণ” – “devoted to a more detailed exposition on the foetus.”
“The subjects dealt with are: the prāṇas (প্রাণ), which consist of agni, soma, vāyu, sattva, rajas, tamas, the sense organs, and the bhūtaman (4.3) – অগ্নিঃ সোমো বায়ুঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মেতি প্রাণাঃ।”
এরপরে ভ্রূনের মধ্যে দুধের ওপরে সরের মতো (ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ) ৭টি ত্বকের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে – প্রথম ত্বকের নাম অবভসিনী যার স্থুলতা একটি ব্রীহির সমান (সম্ভবত একটি ব্রীহি ধান্য যার উল্লেখ বেদের সময় থেকে পাওয়া যায়) ১৮ ভাগের ১ ভাগ, এর নীচের ২য় ত্বককে লোহিতা বলে (ব্রীহির ১৬ ভাগের ১ ভাগ), ৩য় ত্বকের নাম শ্বেতা (ব্রীহির ১২ ভাগের ১ ভাগ), ৪র্থ ত্বকের নাম তাম্রা (ব্রীহির ৮ ভাগের ১ ভাগ), ৫ম ত্বকের নাম বেদিনী (ব্রীহির ৫ ভাগের ১ ভাগ), ৬ষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিণী (১টি ব্রীহির সমান) এবং ৭ম ত্বকের নাম মাংসধরা (২টি ব্রীহির সমান)। এরপরে এদের যেসমস্ত “disorders” হয় তার কথা বলা হয়েছে (এত বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়)। (৪.৪)[70]
পরের শ্লোকে বলা হয়েছে – “কলাও (tissue) সাতটি – “a kalā is the tissue forming boundary between dhātu and aśraya (receptacle) (4.5); a dhātu becomes visible on cutting through the fleshy parts; the structure called kalā are covered by snāyus (স্নায়ু), encased in a membrane (জরায়ু), and surrounded by phlegm (শ্লেষ্মন) (4.6);”[71] descritions of the seven kalās, called successively মাংসধরা,[72] রক্তধরা, মেদোধরা, শ্লেশ্মধরা, পুরীষধরা, পিত্তধরা, এবং শুক্রধরা (4.8-20).”[73]
এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। কেন আমি বারংবার মিউলেনবেল্ডের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি? তার একাধিক কারণ আছে – (১) মিউলেনবেল্ড শিক্ষার জগতে একজন চিকিৎসক এবং psychiatrist (Utrecht Univerversity, Neherlands) এবং একই সঙ্গে Jan Gonda-র অধীনে indology নিয়ে নিবিড়তা এবং যতদূর সম্ভব গভীরতা নিয়ে সংস্কৃত চর্চা করা যায় ততদূর করেছেন। তাঁর পিএইচডি থিসিস হল বিখ্যাত The Madhavanidāna। (২) যে কোন সংস্কৃত, বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে যে কথাগুলো অনেক বিস্তারে বলা আছে, মিউলেনবেল্ড সে কথাগুলোর সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য নির্যাস খুব অল্প কথায় তাঁর মিত বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে বলেছেন; (৩) মিউলেনবেল্ডের ম্যাগনাম ওপাস A History of Indian Medical Literature (HIML) ১৯৯৯-২০০২ সালের মধ্যে ৫টি বিপুলাকৃতির খণ্ডে (1A, 1B, IIA, IIB, III) রচিত আয়ুর্বেদের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাস। এজন্য তাঁকে আন্তর্জাতিক জগতে স্কলারেরা “এনসিক্লোপিডিয়া অফ আয়ুর্বেদ” বলে থাকেন; (৪) ২০০২ সাল পর্যন্ত যত সংখ্যক ম্যানাসক্রিপ্ট, মুদ্রিত পুস্তক কিংবা অন্য যেকোন সম্ভার পেয়েছেন (ইংরেজি, ডাচ, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতি, হিন্দি, তামিল, বাংলা, শারদা লিপিতে রচিত গ্রন্থ ইত্যাকার সমস্তকিছু) তাঁর ৫ খণ্ডের রচনাসম্ভারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; (৫) ২০০২ সালের পরে যে ম্যানাসক্রিপ্টগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো নিয়ে এখন স্কলারেরা কাজ করছেন। কিন্তু সবারই “reference point” হলেন মিউলেনবেল্ড। (৬) তিনি যেসব শব্দের উপযুক্ত ইংরেজি প্রতিশব্দ পেয়েছেন বলে নিশ্চিত হয়েছেন সেগুলো ব্যবহার করেছেন। যেক্ষেত্রে পান নি সেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দটিই রেখে দিয়েছেন, কোন অবান্তর এবং ভুল ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি; এবং, সর্বোপরি, (৬) তিনি “মেডিক্যাল লিটারেচার” (“মেডিক্যাল সায়ান্স” নয়) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তরভাবে একে বিজ্ঞানের replica হিসেবে দেখেন নি।
মিউলেনবেল্ডের কথায় – “semen is present throught the whole body, just as ghee in milk and juice in the sugarcane (4.21); the place where the śukra enters the; it flows out through the urethra (4.22); the process of ejaculation (4.23); pregnant women do not menstruate because the channels (স্রোত) tarsporting আর্তব are obstructed by the foetus; part of the আর্তব is the material out of which the placenta (অপরা) is formed, the remaining part makes the breasts swell (4.24); liver (যকৃৎ) and spleen (প্লীহা) of the foetus are formed from blood, the phuppusa (ফুপ্পুস – ফুসুফুস নয়)[74] from the foam (ফেনা) of blood, the উণ্ডুক (এর সঠিক প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পাইনি। যশোদানন্দন এবং পি ভি শর্মা একে caecum বলেছেন, মিউলেনবেল্ড কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ দেননি[75]) from the waste products (কিট্ট) of blood (4.25); the intestines, ano-rectal region and bladder are formed from the pure parts (প্রসাদ) of blood and kapha (কফ), acted upon by vāta and pitta (4.26-27ab); the tongue is formed from from the pure parts of kapha (কফ), blood and muscular tissue (4.27cd-28ab); the channels (স্রোত) arise from from combined action of kapha (কফ), blood and muscular tissue (4.27cd-28ab); the peśis (পেশি) arise in the same way; the channels (স্রোত) arise from the combined action of vāta and uṣman…”[76]
মিউলেনবেল্ড জানাচ্ছেন – “বাত এবং পিত্ত ও মেদ-এর স্নেহ-র সাহায্যে সিরা এবং স্নায়ু তৈরি করার ক্ষেত্রে পেশি অংশত রূপান্তরের “agents”; মৃদু পাক (heating) থেকে সিরার উৎপত্তি সুগম হয়, খর (strong) পাক থেকে স্নায়ু-র উৎপত্তি হয় (4.29-30ab)”। এভাবে একে একে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গর্ভাবস্থায় উৎপত্তির বর্ণনা দেওয়া আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হৃদয় তথা heart-এর উৎপত্তি – “the heart is the basis of প্রাণবহ ধমনীসমূহের ভিত্তি।” (৪.৩১)
লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গর্ভাবস্থায় উৎপত্তির ক্ষেত্রে দোষ-এর উপাদান রয়েছে। তার সাথে অন্য উপাদানের permutations-combinations হয়েছে।
যশোদানন্দন এক্ষেত্রে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন (উৎস অজানা) – “উণ্ডুক স্থুলান্ত্রের প্রথম সীমা। এরপরে স্থুলান্ত্র উর্ধমুখে উঠে যকৃৎ ও আমাশয়কে বেষ্টন করে ফুসফুসের (ফুপ্পুস নয়?) নীচ দিয়ে গিয়েছে। পরে প্লীহার কাছে গিয়ে নীচের দিকে মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়েছে। স্থুলান্ত্রের শেষভাগকে ইংরাজিতে রেক্টম ও সংস্কৃতে গুদ বলে অন্ত্র সকল যকৃৎ ও কোষ্ঠকে (আমাশয়কে) বেষ্টন করে গিয়েছে।”[77]
আবার মিউলেনবেল্ডের বয়ানে – “the heart is basis of (আশ্রয়) of the prāṇa (প্রাণ)-transporting dhamanīs (ধমনীসমূহ); below the heart, on the left side, are spleen and phuppusa (ফুপ্পুস – বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাদটীকা দ্রষ্টব্য)[78] located, on the right side liver and kloman (ক্লোম); the heart is in particular the seat of consciousness (চেতনা – লক্ষ্যণীয় হল, আধুনিক মেডিসিন anatomical এবং physiological দৃষ্টিকোন থেকে heart-কে আমরা যেভাবে বুঝতে অভ্যস্ত, আয়ুর্বেদে সে অর্থ ও ব্যঞ্জনা একেবারেই ভিন্ন), which explains that all living beings sleep when it is covered by tamas (তমস) (4.31)”[79]। যশোদানন্দন বলেছেন – “হৃদয়ের আকার পদ্মমুকুলের ন্যায় (পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্)। উহা অধোমুখে (inverted) থাকে। উহা জাগ্রত অবস্থায় বিকশিত (open) এবং নিদ্রিত অবস্থায় নিমীলিত (closed) থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবী মায়া।”[80] মিউলেনবেল্ড বলছেন – “the foetus grows thanks to rasa (রস) (of the mother) and the blowing (আধ্মান – blowing inflation[81]) of vāta (4.57)”[82]।
এই অধ্যায়ে এরপরে সত্ত্ব, রজ ও তম বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের চরিত্র বিস্তারিতভাবে বিচার করে সেগুলোর সুবিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে, যা আমাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় নয়।
এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি হল – “ভিন্ন ভিন্ন শরীরের প্রকৃতি স্থির করে সেভাবে চিকিৎসা করতে হবে। সত্ত্বরজস্তমঃকৃত এইসব মহপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসমূহ বলা হল। ভিষক্ এগুলি সম্যকভাবে ভেবে দেখবেন।”[83] (৪.৯৭-৯৮)
শেষ কথা
আমরা সুশ্রুত-সংহিতা-র প্রথম ৩টি অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রধানত anatomy ও physiology বোঝার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দেহকে ত্রিদোষ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যাত বিভিন্ন চরিত্র এবং প্রকৃতির কথা, গর্ভধারণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এবং গর্ভধারণের পরে মাতৃদেহে ভ্রূণের বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ বুঝতে পারলাম। এর মধ্যে দ্বৌহ্রৃদিনী বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। আমরা পরের অধ্যায়ে প্রধানত দেহের অঙ্গসংস্থান (anaotomy) এবং আধুনিক পরিভাষায় “ডিসেকশন” বলতে যা বোঝায় আদৌ সেরকম ঘটনা সুশ্রুতের সময়ে ঘটেছিল কিনা সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।
___________________________________________
[1] সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কিট্ট-র ইংরেজি প্রতিভাষা হিসেবে secretion ব্যবহার করেছেন – দাসগুপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭।
[2] Mira Roy, “Āyurveda”, in The Cultural Heritage of India, ed. Priyadaranjan Ray and S. N. Sen, vol. IV, p. 152-176. Quotation on p. 167.
[3] S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy (hereafter HIP), in 5 volumes, vol. 2, 1998, p. 327.
[4] Meulenbeld, The Mādhavaniāna: With ‘Madhukośa’, the Commentary by Vijayarakṣita and Ṥrīkaṇṭhadatta (Chapters 1-10), 2008, p. 612.
[5] Ibid, p. 612.
[6] Aṣṭāňga Hṛdayam, trans. K. R. Srikantha Murthy, 2009, vo. 1, p. 154.
[7] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫।
[8] Apte, ibid, p. 879. যদিও দাসগুপ্ত মেধা-র ইংরেজি প্রতিভাষা imagination ব্যবহার করেছেন – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮।
[9] Dasgupta, HIP, vol. 2, p. 328.
[10] Meulenbeld, HIML, IA, p. 399.
[11] Rahul Peter Das, The Origin of the Life of a Human Being: Conception and the Female According to Ancient Indian Medical Science and Sexological Literature, Motilal Banarsidass, 2003.
[12] Ibid, p. 15, fn. 26.
[13] Zimmerman, “Terminological Problems in the Process of Editing and Traslating Sanskrit Medical Texts”, in Approaches to Traditional Chinese Medical Literature: Proceedings of an International Symposium on Translation Methodologies and Terminologies, ed. Paul U. Unschuld, 1989, pp. 141-155. Quotation on p. 144.
[14] Wujastyk, The Roots of Ayurveda: Selections from Sanskrit Medical Writings, 1998.
[15] Kenneth Zysk, “Doṣas by Numbers: Buddhist Contributions to the Origin of the Tridoṣa-theory in Early Indian Medical Literature with Comparisons to Early Greek Theories of the Humours”, History of Science in South Asia 2021, 9: 1–29.
[16] Ibid, p. 5.
[17] Ibid, p. 23.
[18] Ibid, p. 24.
[19] Suśruta Saṃhitā (A Scientific Synopsis), Priyadaranjan Ray, Hirendranath Gupta and Mira Roy, 1993, p. 26.
[20] Das, The Origin of Life, p. 548.
[21] Ibid, p. 548.
[22] Meulenbeld, The Mādhavanidāna, p. 469.
[23] Dasgupta, HIP, vol. 2, p. 335.
[24] Ibid, p. 337.
[25] Scharfe, “The Doctrine of Three Humors in Indian Medicine and the Alleged Antiquity of Tamil Siddha Medicine”, Journal of the American Oriental Society 1999, 119 (4): 609-629.
[26] সতীশচন্দ্র শর্মা (সরকার), চরক-সংহিতা, ১৯০৪, পৃঃ ৮।
[27] S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy (পরবর্তীতে HIP), in 5 volumes, vol. 2, 1991, p. 333.
[28] Meulenbeld, HIML. IA, p. 249.
[29] দাসগপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৯।
[30] Ibid, p. 337.
[31] Ibid, p. 337, fn. 1.
[32] Meulenbeld, The Characteristics of Doṣa”, JEAS 1992, volume 2, pp. 1-5.
[33] Ibid, p. 2.
[34] Ibid.
[35] Vicki Pitman, The Nature of the Whole: Holism in Ancient Greek and Indian Medicine, 2006, p. 157.
[36] Ibid, p. 161.
[37] Ludwig Edelstein, Ancient Medicine, p. 72.
[38] Ibid, p. 266.
[39] W. H. S. Jones, Hippocrates, vol. I, p. 346. “The health of the body depends upon the combination of its various juices.” – p. 346, fn. xi. “Diseases, local or general, depend upon the humours.” – ibid, fn. xiv.
[40] Francis Adams, The Genuine Works of Hippocrates, in 2 volumes, vol. 1, p. 174.
[41] Jones, ibid, vol. IV, p. 19.
[42] Ibid, p. 41.
[43] সুশ্রুত-সংহিতা, অনুঃ যশোদানন্দন সরকার, ১৯০৪।
[44] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৵৹ (২/১৬)
[45] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৵৹ (২/১৬)
[46] শার্ঙ্গধর চিকিৎসাসংগ্রহঃ ভিষগ্বর মহামতি শ্রী শার্ঙ্গধর বিরচিত, সম্পাঃ কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন সংস্করন, মাঘ ১৪০৫, পৃঃ ৪।
[47] আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪০।
[48] Meulenbeld, HIML, IA, p. 243.
[49] P. V. Sharma, Suśruta Saṃhitā, vol. II, p. 119. এখানে তন্মাত্র-র ব্যাখ্যা হল – “পঞ্চতন্মাত্র [পঞ্চ সূক্ষ্মভূত – শুল ভাষায় বলিলে প্রত্যেক ভূতের (1. Become, being, existing. 2. Produced, formed – আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২১) অমিশ্র পরমাণুকে সেই ভূতের তন্মাত্র বলা যায়” – সরকার, সুশ্রুত সংহিতা, পৃঃ ২০২।
[50] আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২১।
[51] যশোদানন্দন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪।
[52] Meulenbeld, ibid, p. 244.
[53] আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭১।
[54] Meulenbeld, ibid, p. 244.
[55] Meulenbeld, HIML, 1A, p. 245.
[56] রাহুল পিটার দাস বিষয়টিকে এভাবে দেখেছেন – “’perverted male’ called āsekya-, who attains the erection by drnking semen … by means of fellatio of someone else with his mouth, though Indu in his commentary on As,Ṥā 2,p.293 says that he drinks his own or someone else’s semen.” – The Origin of the Life, p. 527.
[57] আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৯।
[58] Meulenbeld, HIML, 1A, p. 245.
[59] এখানে দুটি ব্যাখ্যা আছে। যশোদানন্দন বলছেন – “অর্থাৎ তার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দাঁত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি হয় না।” – পৃ ২০৮। মিউলেনবেল্ড বলছেন – “Ḍalhaṇa remarks that Jejjaṭa did not accept these verses.” – ibid, IB, p. 371.
[60] Meulenbeld, HIML, IA, p. 245.
[61] Meulenbeld, ibid, p. 246.
[62] Ibid, p. 246.
[63] Ibid, p. 246.
[64] Ibid, pp. 246-247.
[65] এখানে মিউলেনবেল্ড ব্যবহৃত নির্ঋতি শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যশোদানন্দন এর কোন কথাই উল্লেখ করেন নি, শর্মা একে demon বলেছেন। নির্ঋতি শব্দটির বাংলায় অর্থ অলক্ষ্মী বা উপদ্রব। এসমসস্ত বিভিন্ন কারণে text critical edition-এর প্রয়োজনীয়তা এত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি তথ্যও আগ্রহী পাঠকের কাজে লাগতে পারে – নির্ঋতির উপযুক্ত ইংরেজি প্রতিশব্দ আপ্তে বা মনিয়ের-উইলিয়ামস-এর অভিধানে পাওয়া যায়নি। বাংলা অভিধানগুলোর মধ্যে সুবল মিত্রের, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা বাংলাদেশ বাংলা অ্যাকাডেমি থেকে ৩ খন্ডের অভিধানেও এর উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র জ্ঞানেদ্রমোহন দাসের (১৯১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত) বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এর ২য় খণ্ডে শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মিউলেনবেল্ড এই শব্দটির বহুল ব্যবহারের অনেকসংখ্যক উদাহরণ দিয়েছেন – প্রাগুক্ত, IB, পৃঃ ৩৭১।
[66] Meulenbeld, IA, p. 247, IB, p. 371.
[67] Meulenbeld, ibid, p. 247. মিউলেনবেল্ডন তাঁর টীকায় যোগ করেছেন, চরক-সংহিতা-র শারীরস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের ২০-২১ নম্বর শ্লোকে সমধর্মী বক্তব্য পাওয়া যায় – IB, p. 371।
[68] মিউলেনবেল্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭। টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন – চরক-সংহিতা-র শারীরস্থানের ৩য় অধ্যায়ের ৩-১৪ নম্বর শ্লোকে সমধর্মী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় – IB, পৃঃ ৩৭১।
[69] Meuleenbeld, ibid, IA, p. 247.
[70] এখানে মিউলেনবেল্ড তাঁর টীকায় যোগ করেছেন – “Compare Ca.Ṥā.7.4, IB, p. 372.
[71] মিউলেনবেল্ড টীকায় বলছেন – “Compare Saṃgitaranākara 1.2.76-78” – IB, p. 372.
[72] মিউলেনবেল্ড দেখিয়েছেন, সিঙ্ঘাল একে endo-, peri- and epimysium বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন একে facsia বলেহেন – IB, p. 372। আবার সেই শব্দার্থের সমস্যা
[73] Meulenbeld, ibid, p. 248.
[74] এখানে মিউলেনবেল্ড তাঁর টীকায় মন্তব্য করছেন – “সিঙ্ঘাল এবং ভিষগরত্ন একে lungs বলেছেন।” – পৃঃ IIB, 372. এই প্রেক্ষিতে রাহুল পিটার দাসের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য – “This organ has not been identified properly, though many scholars hold it to refer to the lungs, a lung, or part of a lung, in keeping with the meaning of its relatives in New Indo-Aryan today … Some texts say (e.g. Ādhamalla’s commentary ṤAR 1.5, 43 or Ḍalhaṇa’s commentary on SU, Ṥā 4,25) that is joined to the hṛdayanāḍikā (হৃদয়নাড়িকা)-, i.e. the tubule of the heart (hṛdaya-) or the like.” – Das, The Origin of ife of a Human Being, pp. 566-567.
[75] তাঁর টীকায় মিউলেনবেল্ড বলেছেন – “The maladhrā kalā bounds the uṇḍuka, which contains waste products derived from from the food. Ḍalhaṇa regards it as identical with Caraka’s purīṣādharā and mentions poṭṭalaka as its vernacular name …” – HIML, IB, p.372.
[76] Meulenbeld, HIML, IA, p. 248.
[77] সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।
[78] সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেছেন – “Suśruta speaks of phuppusa as being on the left side of and kloma as being on the right. Sine the two lungs vary in size, it is quite possible that Suśruta called the left lung phuppusa and the right one kloma. Vāgbhaṭa I follows Suśruta. The Atharve-Veda, Caraka, Suśruta, Vāgbhaṭa and other authorities used the word in singular, but in Bṛhad-araṇyaka, I, the word kloma is used in the plural number…” – HIP, vol. 2, p. 288, fn. 1.
[79] Meulenbeld, HIML, IA, p. 248.
[80] যশোদানন্দন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪-২১৫।
[81] আপ্তে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।
[82] Meulenbeld, HIML, IA, p. 248.
[83] যশোদানন্দন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।





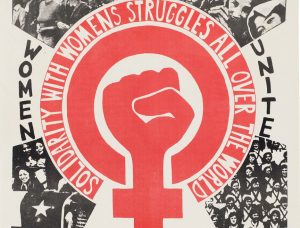








I hope current students are exposed to the history of medicine. This extraordinary piece quietly highlights that need.