“আয়ুষ্মান ভারত” ভারত সরকারের তরফে ভারতীয় জনতার কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য একটি “ফ্ল্যাগশিপ স্কিম” (যেমনটা সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে)।
২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রী এই “স্কিম”-এর সূচনা করেন। মন্ত্র ছিল “কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবেনা”। সরকারি বিজ্ঞপ্তি থেকেই জানা যায় – (১) দেশের সবচেয়ে দুর্বল ও আর্থিক অবস্থানে সবচেয়ে নিচে থাকা প্রায় ৫০ কোটি মানুষ “সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি” পরিষেবার জন্য বছরে ৫,০০,০০০ টাকার সরকারি “ইন্সিউরেন্স”-এর সুবিধে পাবে (চিকিৎসা পাবার মুহূর্তে যেকোন রোগই থাকতে পারে, সেটা বিবেচ্য নয়), (২) হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে ৩ দিন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে ১৫ দিন পর্যন্ত সমস্ত খরচ এই ইন্সিউরেন্স-এ বহন করা হবে, (৩) কেন এই স্কিম নেওয়া হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি বছর ৬ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য “বিপর্যয়কর খরচ” মেটাতে গিয়ে দারিদ্র সীমার নিচে তলিয়ে যায়, সেটা যাতে প্রশমিত করা যায়, (৪) ২০১১ সালে শেষবারের জন্য হওয়া “সোশিও-ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস (জাত গণনা)”-এর ওপরে ভিত্তি করে দুর্বল শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে – যেমন, নমুনা হিসেবে, ভিখিরি, রাস্তার হকার, বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমের সঙে যুক্ত বিভন্ন পেশার দরিদ্র মানুষ, ঝাড়ুদার, যারা ময়লা পরিষ্কার করে, ধোপা ইতাদি এবং (৫) এটা পৃথিবীর “বৃহত্তম ইন্সিউরেন্স স্কিম”। এছাড়াও আরেকটি কারণ ছিল আন্তর্জাতিক জগতের স্বাস্থ্যের অধিকার সংক্রান্ত যেসমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে (যেমন, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ৩) তার তুল্য হয়ে ওঠা।
এতসবের পরেও ৬ মাস আগে যখন সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে ৯ জানুয়ারি, ২০২৫-এ খবর হয় যে, বাঙ্গালোরে ৭২ বছরের এক ক্যান্সার রোগীর আয়ুষ্মান ভারত-এ নাম নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার “বিপর্যয়কর খরচ” না মেটতে পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন, তখন এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে সামগ্রিকভাবে কিছুটা গভীরে দেখাই বোধহয় সমীচীন। প্রসঙ্গত, ভারতের ৫টি রাজ্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গ্রহণ করেনি।
এখানে উল্লেখ করা দরকার, ৬৪,০০০ কোটি টাকা (স্বাস্থ্য বাজেট) আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে বিপুল পরিমাণ মনে হলেও প্রতিটি পরিবারের জন্য এর প্রিমিয়ামের বরাদ্দ দাঁড়াবে ৬৪০ টাকায়, যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম বললেও কম বলা হয়। উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, ছত্তিসগড়ে চিফ মিনিস্টার হেলথ ইন্সিউরেন্স স্কিম-এ আয়ুষ্মান ভারত-এর ৫,০০,০০০ টাকার এক-দশমাংশ অর্থাৎ ৫,০০০ টাকা “কভার” করা হয় (বীমার ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা)। কিন্তু প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১,১০০ টাকা।
অন্য আরেকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে – ইন্সিউরেন্স স্কিম এবং স্বাস্থ্যখাতে বিপর্যয়কর খরচ-এর মধ্যে সরাসরি কোন সংযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চিনে ৯০% নাগরিকের ইন্সিউরেন্স কভারেজ থাকলেও ১৮% জনসংখ্যা বিপর্যয়কর খরচ-এর মখোমুখি হয়। ভারতে ইন্সিউরেন্সের আওতায় থাকা মানুষের সংখ্যা চিনের তুলনায় মাত্র ২০%, কিন্তু বিপর্যয়কর খরচ-এর মখোমুখি হয় ১৭% মানুষ। ফলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প স্বাস্থ্যখাতে বিপর্যয়কর খরচ কমাবে এমন কোন পরিসংখ্যান অনুপস্থিত।
বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রাক্তন মহাসচিব (১৯৯৮-২০০৩) গ্রো হারলেম ব্রুন্টল্যান্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮-এ ল্যান্সেট জার্নালে প্রকাশিত “ইন্ডিয়া’জ হেলথ রিফর্মসঃ দ্য নিড ফর ব্যালান্স” প্রবন্ধে লিখেছিলেন – “একটি ঝুঁকি এই স্কিমে রয়েছে। সেটা হল ভারতের স্বাস্থ্যসংস্কার মানুষের কাছে পৌঁছুনো আর্থিক সাহায্যকে বিকৃত করে টারশিয়ারি কেয়ারের জন্য বেশি খরচ খরচ করতে পারে। এর ফলে ভারত সরকারের ঘোষিত স্ট্র্যাটেজি প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুষ্ট করার লক্ষ্যটিই, যেখানে জনস্বাস্থ্যের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ করা হবে, বিনষ্ট হবে।” বাস্তবেও সেটাই ঘটেছে – প্রান্তিক অঞ্চলে, দুর্গম জায়গায় খন্ডহরের মতো পড়ে রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো। কেউ ফিরেও তাকায় না চিকিৎসার জন্য। এই খাতে প্রায় কোন ব্যয় বরাদ্দ নেই।
২০০৮ সালে “দ্য এলডারস” বলে একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন নেলসন ম্যান্ডেলা, গ্রো হারলেম ব্রুন্টল্যান্ড, কোফি আন্নান, বান-কি মুন, ডেসমন্ড টুটু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা। ২০১৬-১৭ সালে তাঁরা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন “ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (ইউএইচসি) ইন ইন্ডিয়াঃ এ কল ফর গ্রেটার পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ফিনান্সিং”। এঁরা ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতগুলো বিপদ চিহ্নিত করেছিলেন – (১) “পৃথিবীর ফার্মেসি” বলে পরিচিত দেশে মানুষ ওষুধ পায় না, (২) জনস্বাস্থ্যখাতে খরচের চেহারা করুণ, (৩) স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ অন্তত ২.৫% করতে হবে, (৩) সামাজিক সুরক্ষা জাল-কে (সোশ্যাল সেফটি নেট) সর্বব্যাপী করতে হবে, (৪) প্রতিটি নাগরিকের কাছে অত্যাবশ্যক মেডিসিন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ বিনা মূল্যে পৌঁছে দিতে হবে, এবং, (৫) সর্বোপরি, স্বাস্থ্য কখনো আয়ের নিরিখে বিচার করা চলবে না, এটা হল মৌলিক মানবাধিকার। অনুমান করা যায়, এ সবকিছুর সম্মিলিত চাপ ছিল ভারত সরকারের নীতি প্রণেতা সুবিশাল আমলাবাহিনী এবং স্বয়ং ভারত সরকারের ওপরে।
প্লস মেডিসিন-এর মতো জার্নালে (মার্চ ৭, ২১৯) আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ঘোষিত হবার পরে প্রকাশিত হয় “দ্য আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা অ্যান্ড দ্য পাথ টু ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ইন ইন্ডিয়াঃ ওভারকামিং দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ স্টুয়ার্ডশিপ অ্যান্ড গভর্নেন্স”। এ প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো নজরে আনা হল – প্রথম, ভারতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বিশ্বের দেশগুলোর নিম্নতমর একটি; দ্বিতীয়, এক বহুবিস্তৃত সংস্কারের প্রয়োজন আছে এ প্রোগ্রাম সফল করার জন্য অর্থাৎ ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে – পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরকে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদশালী হতে হবে প্রোগ্রামকে কার্যকরী করা, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সামগ্রিক দেখভালের জন্য।
নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডসিন-এ প্রকাশিত “গেটিং কভারেজ ফর ৫০০ মিলিয়ন ইন্ডিয়ানস” (জুন ১৩, ২০১৯) প্রবন্ধেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে – এই সংস্কার কেবলমাত্র তখন সফল হতে পারে যখন (১) প্রকৃত অর্থে, বাস্তবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেওয়া হবে, (২) স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য সহকারী শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা যাবে, (৩) স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে যুক্ত করা যাবে, এবং (৪) স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়ার মানকে গুণগতভাবে বাড়ানো যাবে। প্রবন্ধের শেষে অবশ্য সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করা হয়েছে – “উচ্চপর্যায়ের ব্যর্থতা সমগ্র গতিশীলতাকে বিপরীতদিকে ঘুরিয়ে দেবে। ভারতের কাছে সাফল্যের সূত্র আছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি এখানে যেসব জায়গায় জোর দেবার কথা বলা হয়েছে সেগুলো পৃথিবীকে দেখাতে পারে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা বাস্তবে সম্ভব, এমনকি সবচেয়ে জটিল অবস্থাতেও।”
নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল-এই একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে – “Primary Care – From Common Good to Free-Market Economy” (মে ২৯, ২০২৫, পৃঃ ১৯৭৭-১৯৭৯) – পরিষ্কার বলা হয়েছে – “More than 30% of U.S. adults lack a usual source of primary care. As the population ages, the gap between primary care demand and supply is poised to widen.” অর্থাৎ আমেরিকায় ৩০%-এর বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রাইমারি কেয়ারের সংস্থান নেই এবং মানুষেরা যত বৃদ্ধ হয় তত বেশি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যের জন্য চাহিদা এবং তার জোগানের মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বেড়ে যায়।
বলা হয়েছে – প্রাইমারি কেয়ারে খোলা বাজার ঢুকে পড়ার ফলে “exit ramps (বড়ো রাস্তার বাইরে সরু রাস্তা) toward the free market are widening.” (পৃঃ ১৯৭৯)
এর ফলাফল? প্রবন্ধটির উদ্বেগ হচ্ছে – “For individual patients and physicians, this shift also provokes deeper questions about what it means to have a primary care doctor — and to be one.” (পৃঃ ১৯৭৯)
ভারতের অবস্থা কি আমেরিকার থেকে খুব বেশি পৃথক? উত্তর হবে নেতিবাচক।
এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালোরের ৭২ বছরের ক্যান্সার রোগী বৃদ্ধর চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে আত্মহত্যা করার বিষয়টি দেখতে হবে। সবক্ষেত্রে গর্জন বেশি হলেই আকাঙ্খিত বর্ষণ হবে, এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।








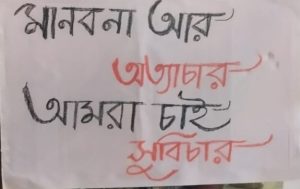







এখানে সমাজতত্ত্ব আর ইকোনমিক্স মিলে মিশে মিথোজীবিতায় ঋদ্ধ। শারীরবিদের অধীত জ্ঞ্যান জৈবিক বাঁচার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যর যত্ন নিতে গেলে লেখা পড়তেই হয়।