ড: ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রি.)
[সংবিধান ও গণতন্ত্র যখন বিপন্ন, দলিত জনজাতির মানুষ যখন আক্রান্ত তখন তঁার স্মরণ নেওয়া হয়। আবার জীবদ্দশায় যে মহামানব উচ্চবর্ণ ও হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস ও আর.এস.এস. হিন্দু মহাসভার যাবতীয় বাধা, অবহেলা ও চক্রান্তের শিকার আজ ভোটের আগে সেই বিজেপি ও কংগ্রেস তঁার শরণাপন্ন। যে বামেরা তঁাকে গুরুত্ব দেননি তঁারাও আজ তঁার পুজো শুরু করেছেন। এমনকি নকশাল সহ অন্যরাও। যাকে নিয়ে এত টানাটানি তঁাকে একটু বোঝার চেষ্টা।]
বাবাসাহেব বি আর আম্বেদকর মস্ত বড়ো দেশনেতা ও ব্যক্তিত্ব, পশ্চাদপদ দলিত সমাজের ত্রাতা, সংবিধানের জনক, অগ্রগণ্য সমাজসংস্কারক, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, অর্থনীতিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, মহাপণ্ডিত, লেখক, পত্রিকা সম্পাদক, স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার অকংগ্রেসী সদস্য এবং ইদানীং কোণঠাসা রাজনৈতিক দলগুলির ও বামপন্থীদের টিকে থাকার আশ্রয়স্থল। তিনি ১৯২৬ থেকে ১৯৩৭ অবধি বম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ১৯৩৭-৪২ বম্বে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ও বিরোধী নেতা, ১৯৪২-৪৬ অবধি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শ্রমমন্ত্রী, ১৯৪৬-৪৭ বাংলা থেকে ও ১৯৪৭-৫০ বম্বে থেকে কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইন্ডিয়ার নির্বাচিত সদস্য এবং ১৯৪৭-৫১ ভারতের আইন ও বিচারমন্ত্রী ছিলেন।
ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনে জাতপাতদীর্ণ পশ্চাদপদ ভারতীয় সমাজে অচ্ছ্যুৎ মারাঠি মাহার সম্প্রদায়ের এক ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা সুবেদারের পরিবারে মধ্যপ্রদেশের মৌ (বর্তমানে আম্বেদকরনগর) ফৌজি ক্যান্টনমেন্টে আম্বেদকরের জন্ম। প্রথমে সেখানেই অন্যান্য ভাইবোনের সাথে বেড়ে ওঠা, পরবর্তীকালে সাতারা, রত্নগিরি, মুম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস। শিক্ষার অতটা চলও ছিল না সেইসময় নিম্নবর্ণের মাহার পরিবারে। অন্যান্য ভাইবোনেরা পড়াশুনায় বিশেষ এগোতে না পারলেও, অত্যন্ত মেধাবী আম্বেদকর প্রথম থেকেই পড়াশোনায় ব্যুৎপত্তি দেখান। পরে আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রমুখ বিষয়ে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় (বি এ, এম এ), মার্কিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (এম এ, পি এইচ ডি), ব্রিটেনের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্ (এম এস সি, ডি এস সি) থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনের গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। সেইসময়ের নিরিখে এক অতিনিম্ন দলিত পরিবারের সন্তানের পক্ষে এই আরোহণ ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং এক বিরল বৈপ্লবিক ঘটনা। এর জন্য তাঁকে প্রবল সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল।
শিক্ষা থেকে চাকরি জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে দারিদ্রের পাশপাশি মোকাবিলা করতে হয়েছিল তীব্র জাতিভেদ, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, এবং বর্ণহিন্দুদের লাগাতার বিদ্রুপ, উৎপীড়ন, ষড়যন্ত্র, বয়কট ও অত্যাচার। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্যদের মত হার না মেনে তিনি জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সারাটি জীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ জারি রাখেন। শিক্ষকতা, আইনচর্চা, বরোদা রাজের চাকরি সব ছেড়ে তিনি জাতি বৈষম্যের অবসান ও সমাজসংস্কারকে পাখির চোখ রেখে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ভারতীয় দলিত সমাজকে সংগঠিত করেন। ১৯২০ ও ‘৩০-র দশকে দলিতদের মন্দিরে প্রবেশ ও জলাশয় ব্যবহার নিয়ে আম্বেদকর বড়ো বড়ো আন্দোলন সংগঠিত করেন যার মধ্যে মাহাদ, পার্ব্বতী মন্দির ও কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জমিদারি, তালুকদারি, জেনমি, খোটি, মালগুজারি, রায়োতরি ব্যবস্থায় ও মহাজনী ঋণে দলিত কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। শিল্পাঞ্চলে দলিত অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং তাঁদের পরিবারের সঠিক বাসস্থান, তাঁদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে মনযোগী ছিলেন। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে দলিতদের জন্য নির্বাচনী আসন সংরক্ষণের জন্য সওয়াল করেন। তিনি ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিকে নিয়ে বিশাল অভিযান সংগঠিত করেন। সি পি আই-এর শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসিকে সঙ্গে নিয়ে এক লক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত করেন। তিনি সার্বজনীন শিক্ষা, শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার, প্রতিরক্ষা বাজেট কমানো, কাশ্মীরে গণভোট প্রভৃতি দাবিগুলি তুলে ধরেন।
তাঁর সংগ্রাম ও আন্দোলনের চরিত্র ছিল মূলত গণতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী। ধর্ম ও জাতকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজের জাতিভেদের অবসান তাঁর মূল লক্ষ্য থাকলেও আশু লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন এবং ‘স্বাধীনোত্তর’ নবীন কংগ্রেসী শাসকদের সাথে দরকষাকষি করে দলিতদের জন্য যতটা সম্ভব অর্থনৈতিক সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা। আইনসভায় সংরক্ষণ থেকে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর লাগাতার প্রয়াস ও কৌশল ব্যাপকভাবে সফল হয়। অন্যদিকে উদীয়মান জাতীয়তাবাদী ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন প্রতিহত করতে ব্রিটিশদের অনেকগুলি কৌশলের একটি ছিল বর্ণহিন্দু, মুসলমান, দলিতদের ধর্মীয় ও জাতপাতগতভাবে আরও পৃথক ও বৈরী করে তোলা এবং কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা সৃষ্টি করে এদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে প্রতিস্থাপিত করে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে অপ্রতিহত রাখা। আর ১৯৪৭-এর পর বৃহৎ শিল্পপতি, বৃহৎ সামন্তপ্রভু এবং ব্রিটিশ লগ্নীপুঁজির প্রতিনিধি ভারতীয় শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ছাড় দিয়ে ব্যাপক দলিত সমাজকে নিষ্ক্রিয় এবং অনুকূলে রাখা। স্বাভাবিকভাবে আম্বেদকরও ভারতীয় রাজনীতিতে ওই পরিস্থিতিতে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত দলিতদের স্বার্থরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে আম্বেদকর দলিত ভোট ও সমাবেশকে ব্রিটিশ ও কংগ্রেসকে চাপে রাখতে কাজে লাগান। কিন্তু সেগুলিকে সামন্ত, পুজিঁ ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামকে ক্ষুরধার করতে কাজে লাগানোর কথা ভাবেননি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্র অন্ত্যজ ভূমিহীন পরাধীন দলিতদের আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে সামন্ত ও পুজিঁ বিরোধী এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। আম্বেদকর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকৌশল হিসাবে প্রধানত আলাপ-আলোচনাকেই বেছে নেন এবং পুণে চুক্তি সহ বহু ক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য পান। জাতিবৈষম্যের অবসান, শ্রম ও নারীর মুক্তি নিয়ে তাঁর ধ্যানধারণা অনেকটাই ছিল আদর্শবাদী। স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসাবে ভারতীয় সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই সর্বমঙ্গলবাদী চিন্তা প্রতিফলিত হয়। ক্রমে গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ বর্ণহিন্দু কংগ্রেসী নেতৃত্বের কৌশলী চাল ও ষড়যন্ত্রে তিনি রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে মানবতাবাদী বৌদ্ধধর্ম চর্চার দিকে ঝোঁকেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে পাঁচ লক্ষ দলিত সমর্থককে নিয়ে নাগপুরে প্রকাশ্য সভায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।
মাহার সম্প্রদায় হিন্দুত্ববাদী জাতিভেদ ব্যবস্থায় মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত নিম্নবর্ণীয় জল অচল অস্পৃশ্য সম্প্রদায় যারা সুদূর অতীত থেকে জাত ও শ্রেণিগত শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার। মহারাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ এই দক্ষ কৃষক-যোদ্ধা-কারুশিল্পী সম্প্রদায় অনেকটা পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মত। মাহারদের গ্রামের মধ্যে থাকতে দেওয়া হত না। তাঁরা গ্রামের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে থাকতেন। তাঁদের মূল কাজ ছিল গ্রামের পাহারা, নিরাপত্তা ও যোগাযোগ রক্ষা। এছাড়া চাষবাস করে সামন্তপ্রভুদের খাদ্য যোগানো, বস্ত্র বয়ন ও নানারকম কারুশিল্প রচনার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের চাহিদা মেটানো। এছাড়াও ময়লা সাফ করা থেকে যাবতীয় শ্রম ও পরিষেবার তারাই ছিলেন মূল কারিগর। অথচ তাদের স্পর্শ বা ছায়া মাড়ালে কিংবা গ্রামের পুষ্করিণী বা কুয়োর জল ভুল করে বা বিপদে পড়ে শিশু বা নারীরা ছুঁলে বিপদ ও প্রায়শ্চিত্তের শেষ ছিল না। প্রথমত সেই মাহার পরিবারের কঠিন শাস্তি হত এবং যাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের খরচও তাঁদের বহন করতে হত।
অনেকসময়েই লোলুপ সামন্তপ্রভুরা মাহার সহ নিম্নবর্গীয় নারীদের ভোগ করতেন। এতে অবশ্য তাদের জাত ধর্মের কোন ক্ষতি হত না, উল্টে অভাগী অত্যাচারিতা দলিত নারীরা সমাজে পতিতা হতেন। মধ্যযুগে কৃষি অর্থনীতির ব্যাপক বিকাশ এবং সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার বাতাবরণে সমাজ ভিতর থেকেই কিছুটা পরিবর্তনকামী হয়ে ওঠে। সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে ভক্তি আন্দোলন এবং ইসলামের ভুবনে সুফি উদারতাবাদ ছড়িয়ে পড়ে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেইসময় মাহারদের মধ্যে চোখামেলা, কর্মমেলা, বাকা, নির্মলা, সোয়ারবাঈ, ভাগু প্রমুখ সংস্কারবাদী নেতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্মাচারণ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটালেও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ব্যবস্থায় তাঁরা দাঁত ফোটাতে অক্ষম হন। পশ্চাদপদ কুনবি সম্প্রদায়ের শক্তিশালী মারাঠা নৃপতি ছত্রপতি শিবাজী মাহার এবং অন্যান্য দলিতদের অনেকটা গুরুত্ব দিয়ে এক দুর্ধর্ষ সেনাদল গঠন করেন। এই মাহার বাহিনী অতর্কিত হানা, গেরিলা যুদ্ধ, দুর্গ দখল ও রক্ষা প্রভৃতিতে খুবই কুশলী ছিল। কিন্তু শিবাজীর রাজত্বের শেষ দিকে রণক্লান্ত বয়স্ক অসুস্থ শিবাজী যখন অনেকটাই পুরোহিত ও পেশোয়াদের ঘেরাটোপে পড়ে যান তখন থেকে মাহারদের আবার অধোগমন। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত্যাভিমানী অত্যাচারী পেশোয়াদের রাজত্বকালে মাহারদের উপর অত্যাচার ও শোষণ বহুগুণ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ব্রিটিশের আগমনে ও শাসনকালে মাহাররা কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ব্রিটিশরা মাহার রেজিমেন্ট গঠন করেন। মাহাররাও ভীমা-কোড়েগাঁও সহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে নিজেদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৮১৭-১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্ণায়ক তৃতীয় ইং-মারাঠা যুদ্ধে মাহার যোদ্ধাদের সাহায্যেই কম সৈন্য নিয়ে ইংরেজরা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের বিশাল মারাঠা বাহিনীকে পরাস্ত করে মহারাষ্ট্রের দখল নেয়।
মাহারসহ দলিতদের মধ্যে প্রথম কার্যকারিভাবে শিক্ষা, চেতনা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সংস্কার সাধন করেন মালি সপ্রদায়ের জ্যোতিরাও ও সাবিত্রী ফুলে এবং তাঁদের ‘সত্যশোধক সমাজ’ ১৯ শতকের শেষার্ধে। মাহারদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষিত হতে সচেষ্ট হন। ব্রিটিশ শাসনে তাদের সামরিক মিত্র হিসাবে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। কিন্তু মনুবাদী হিন্দু জাত কাঠামোয় মাহারদের জাতি বৈষম্যের দুর্দশা ঘোচে না, আজও ঘোচেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে আম্বেদকর যখন মৌ ক্যান্টনমেন্টের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত তখনও তিনি শ্রেণিকক্ষে অন্য সহপাঠীদের সাথে বসতে পারতেন না। তাঁকে ক্লাসের বাইরে গানি ব্যাগের স্তূপের উপর বসে শিক্ষকের পড়ানো শুনতে হত। তিনি স্কুলে পানীয় জলের কলসি ছুঁতে পারতেন না, অন্য কেউও তাঁকে পানীয় জল দিত না। একমাত্র নিম্নবর্গীয় এক পিয়ন তাঁকে জল সরবরাহ করতেন। কোনো কারণে তিনি না এলে শত তৃষ্ণা পেলেও বালক আম্বেদকরের পানীয় জল জুটত না। দলিত হয়ে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের তীব্র যন্ত্রণা যে না মোকাবিলা করেছে সে যতই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হোক তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ওই জায়গা থেকে আম্বেদকর স্বীয় প্রতিভাবলে এবং পরে গায়কোয়াড়ের মহারাজার আর্থিক সহায়তায় এতখানি আত্মোন্নতি ঘটিয়েছিলেন, অবহেলিত দলিত সমাজের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন এবং দলিত সমাজের উন্নয়নে লাগাতার কাজ করে গিয়েছেন যা এককথায় অনন্য নজির।
দুঃখের বিষয় তাঁর কঠিন পথচলায় বর্ণহিন্দু জাতীয়তাবাদী অথবা বিশ্বমুক্তিকামী কমিউনিস্টরা তাঁকে সহযোগিতা করেন নি। বরং যতটা সম্ভব বাধা দিয়েছেন। মাহার সহ মহারাষ্ট্র ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত দলিত সমাজের কিছুটা সংগঠিত হিসাবে উঠে আসা এবং সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তিতে মহামতি ফুলে ও বাবাসাহেব আম্বেদকরের বিশিষ্ট অবদান অনস্বীকার্য। তাই দলিত পরিবারে তাঁদের ঈশ্বরের মতো পূজনের বিষয়টি এলিট ও বাবু বিপ্লবীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য হিসাবে আম্বেদকরের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মাহার রেজিমেন্টের গুরুত্ব বাড়ে এবং দরিদ্র ভূমিহীন মাহার সম্প্রদায় থেকে ব্যাপকহারে সেনাদলে যোগদান করা হয়। আম্বেদকরের প্রচেষ্টাতেই স্বাধীন ভারতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মাহার রেজিমেন্ট স্বীয় অস্তিত্ব ও গুরুত্ব বজায় রাখে এবং কাশ্মীর সীমান্ত সংঘর্ষ সহ প্রতিটি পাক-ভারত যুদ্ধে প্রবল বীরত্ব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। পরে ধুরন্ধর ভারতীয় শাসকরা অভ্যুত্থানের ভয়ে অন্যান্য এলাকা ও জাতিভিত্তিক রেজিমেন্টগুলির মতো মাহার রেজিমেন্টেও অন্যান্য জাতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মাহারদের সংখ্যালঘু করে দেয়। ১৯৫৬-এ এবং তার পরেও আম্বেদকরের পথে মাহারদের একটি অংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ-দলিত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
আম্বেদকরকে প্রকৃতপক্ষে বুঝতে হলে স্থান-কাল-পাত্র সহ এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকৃতি দিতে হবে ও বুঝতে হবে। এছাড়াও তিনি নিজে প্রচুর লেখালেখি করেছেন, আর তাঁকে নিয়ে আছে অজস্র লেখা, রিপোর্ট, দলিল, বই, স্মৃতি বহু কিছু। ‘কাস্টস ইন ইন্ডিয়াঃ দ্য মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’, ‘দ্য এনহিলিশন অফ কাস্ট’, ‘রিডলস ইন হিন্দুইজম’, ‘হু ওয়ার দ্য শূদ্রজ?’ ‘দ্য বুদ্ধ অ্যান্ড হিজ ধম্ম’, ‘ওয়েটিং ফর আ ভিসা’, ‘দ্য প্রব্লেম অব দ্য রুপিঃ ইটস অরিজিন অ্যান্ড ইটস সলিউশন’ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর ছিল নিজস্ব এক বিশাল গ্রন্থাগার। অনেকেই তাঁর কাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। এদের মধ্যে গেইল ওমবেত এবং ইলিয়েনর জেলিয়ট অগ্রগণ্য। আম্বেদকরের মৃত্যুর পর দলিত আন্দোলন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে দলিত গোষ্ঠীর প্রভাবের ক্ষেত্রে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকরের পুত্র ভাইসাহেব আম্বেদকর এবং অন্যান্য দলিত নেতৃত্ব চেষ্টা করেও ওই শূন্যতা পূরণে সফল হন না। অন্যদিকে কংগ্রেসের কূটকুশলী বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব কাউকে সুযোগ ও বেশিরভাগকে প্রতারিত করে এবং দমনপীড়ন চালিয়ে এই উদীয়মান দলিত ব্লককে ছত্রাখান করে দেন। বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দলিত গোষ্ঠী, নেতৃত্ব এবং আম্বেদকরের পরম্পরা গড়ে ওঠে। এক শাসক সহযোগী সুবিধাভোগী অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ক্ষমতার আস্বাদন পেয়ে চলেন, নিজেদের গুছিয়ে নেন, আদবকায়দা- জীবনযাত্রা পাল্টে ফেলেন। পাশাপাশি ভোট রাজনীতিতে পোক্ত হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রিত দলিত সমাজকে নিছক ভোটব্যাঙ্ক পুতুলে পরিণত করেন এবং সামগ্রিকভাবে দলিত আন্দোলনের অভিমুখকে ঘুলিয়ে দেন। অন্য একটি অংশ তার তীব্র জ্বালা ও আবেগকে সম্বল করে উগ্র দলিতবাদে ঝোঁকেন এবং জাতিসংঘর্ষে জড়িয়ে যান। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একই তিমিরে থাকা ব্যাপক দলিত সমাজ আর এক মসিহার সন্ধানে প্রতীক্ষা করেন। গান্ধীবাদী কংগ্রেসের পর মনুবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদী আর.এস.এস.-বি.জে.পি কেন্দ্র ও রাজ্যে নির্বাচনী সাফল্যের উদ্দেশ্যে উপরি উপরি আম্বেদকর বন্দনা শুরু করে দেয়।
আম্বেদকর ১৯৩৬-এ ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ গঠন করে কোঙ্কন সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে খোটি, ভেট্টি, মাহারকি নামে আজন্ম ও বংশপরম্পরায় উচ্চবর্ণের জন্য দলিতদের যে বেগার শ্রমের প্রথা ছিল তা তুলে দিতে জোরালো আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দলিত শ্রমজীবী ও সংস্কারবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। বরং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণকে ঘিরে আরও দাবি দাওয়া নিয়ে গণবিছিন্ন সুবিধাভোগী দলিত চাকরিজীবী ও আধিকারিকদের সুবিধাবাদী আন্দোলন। কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলিতে শয়ে শয়ে গজিয়ে ওঠে তফশিলি জাতি উপজাতি কর্মীদের সংগঠন। ১৯৪২-এ আম্বেদকর যে ‘অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন’ তৈরি করেছিলেন ১৯৫৭-তে তা কলেবর বাড়িয়ে ‘রিপাবলিকান পার্টি’ নামক রাজনৈতিক দলে পরিণতি পায়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এন. শিবরাজের কার্যকাল ছিল ১৯৬৪ পর্যন্ত। ১৯৫৪-তে তারা ভূমিহীন দলিত কৃষকদের জমি বণ্টন নিয়ে বড়ো সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৬৪-তে বি.কে. গায়কোয়াডের নেতৃত্বে আরেকটি বড়ো সত্যাগ্রহ হয়। তাঁর প্রধান দাবিগুলি ছিল: (১) আইনসভার কেন্দ্রীয় কক্ষে আম্বেদকরের চিত্র স্থাপন; (২) কৃষকদের হাতে জমি; (৩) পতিত জমি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন; (৪) পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য সরবরাহ; (৫) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ; (৬) বস্তিবাসী ও দলিতদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন; (৭) ন্যূনতম মজুরি আইন ‘৪৮ লাগু করা; (৮) দলিত বৌদ্ধদের তফশিলি সংরক্ষণের সুযোগ দান; (৯) অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইনে সুবিচার; (১০) চাকরিতে সংরক্ষণ ১৯৭০ অবধি বজায় রাখা।
দলিতদের উপর অত্যাচারের বিরোধিতা এবং সমতা সৈনিকদের মাধ্যমে পার্টি শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে রিপাবলিকান দল তার অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। বি.কে. গায়কোয়াড ছাড়াও উঠে আসেন বি.সি.কাম্বলি, দীঘে, জি.কে.মানে, এইচ.আর.শোনুলে, দত্তকাট্টির মতো জনপ্রিয় নেতা। গণসমর্থনে তারা প্রত্যেকেই সাংসদ হন। কিন্তু ১৯৬৭ তে জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী হওয়ার পর থেকে তাদের ভিত আলগা হতে শুরু করে। পার্টি দ্বিবিভাজিত হয়ে গায়কোয়াড ও খাবারগাদির নেতৃত্বে দুটি অংশ হয়ে যায়। ১৯৭৪-এ সাময়িক সংযুক্তি হলেও ‘৭৫-এ আবার দু’দুবার বিভাজন হয়ে খাবারগাদি, গাভাই ও কাম্বলির নেতৃত্বে তিনটি ভাগ হয়ে গুরুত্ব হারায়। নেতারাও অন্যান্য সাবেকি ভারতীয় দলগুলির নেতৃত্বের মতো নিজ ও নিজ পরিবারের সুযোগ সুবিধা, অর্থ ও ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে অধঃপতিত হন। বাবাসাহেবের নাতি প্রকাশ আম্বেদকর ৮০-র দশক থেকে এই আন্দোলন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও তেমন সফল হননি।
পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আম্বেদকরের মূর্তি ও বাণীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলিত শ্রমিক, কর্মচারী, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল ‘দলিত সাহিত্য আন্দোলন’, ‘দলিত রঙ্গভূমি’, ‘অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড এস.সি. ওবিসি অ্যান্ড মাইনরিটিজ এমপ্লয়িজ ফেডারেশন’ প্রমুখ। ওম প্রকাশ বাল্মীকিদের লেখনীতে সৃষ্টি হতে থাকে ‘জোথানে’র মতো সাড়া জাগানো উপন্যাস। বম্বে ততদিনে হয়ে উঠছে দেশের প্রধান শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক রাজধানী। সেখানে যাবতীয় শিল্প কারখানা। কেরল, বিহার ছাড়াও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে হাজির হতে থাকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক যাদের প্রধান অংশটিই মাহার সহ দলিত সম্প্রদায়। তাদের অঢেল সস্তা শ্রমে উপচে ওঠে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের পুঁজি। কর্মস্থলে মালিকের শোষণ ও নিম্নমানের চাউলগুলিতে (বাসস্থান) অবর্ণনীয় জীবনযাপনের পাশাপাশি তারা অতিষ্ট হয়ে ওঠে মালিক-শাসক-মাফিয়া নিয়োজিত শিবসৈনিক গুণ্ডাদের অত্যাচারে। ইতিমধ্যে শিবসেনা ও অপরাধীদের সহায়তায় মালিকপক্ষ শিল্পগুলিতে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের শ্রমিক সংগঠনকে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে শিবসেনা গুণ্ডা ও বর্ণহিন্দু বৈষম্যকে হিম্মতের সাথে মোকাবিলা করে দলিত শ্রমিকদের নওজোয়ান সন্তানরা মার্কিন কালো মানুষের প্রতিবাদী দল ব্ল্যাক প্যান্থারস্ পার্টির অনুকরণে ১৯৭২-এ তৈরি করেন জঙ্গী ‘দলিত প্যান্থার’ দল। অচিরেই লড়াইয়ের ময়দানে পাঙ্গা কষে এরা বম্বের রাজপথ থেকে পিছনে হটিয়ে দিল শিবসেনাকে। সারাদেশে সাড়া জাগিয়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল পুনে, নাসিক, আওরঙ্গাবাদ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশে। সমসাময়িক বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তেও পৌঁছে যায়। দলিত আন্দোলন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুঙ চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত হয়। কসাইয়ের ট্যাক্সিচালক সন্তান নামদেব দাসালের লেখনী থেকে বেরোয় ‘গোলপিথা’র মতো অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। মহাত্মা ফুলের শোষিত ‘দলিত’ সংজ্ঞা প্যান্থারদের কাছে হয়ে ওঠে তফশিলি, আদিবাসী, নব বৌদ্ধ, শ্রমিক, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, নারী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত সমস্ত শোষিত শ্রেণি ও সম্প্রদায়। ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও যাবতীয় অত্যাচারের প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে দলিতদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন হয়ে ওঠে তাদের প্রধান কর্মসূচী। অচিরেই শাসকশ্রেণি ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ওপর। দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ লাগিয়ে দেয়। র্যডিকাল মার্কসবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে রাজ ধালেরা দাসালদের বহিষ্কার করেন। ১৯৭৪-এর মধ্যেই দলে ভাঙন ধরে। পরে কংগ্রেস ও শিবসেনা দাসালদের গ্রাস করে। অধ্যাপক অরুণ কাম্বলের নেতৃত্বে এক মধ্যপন্থী ধারা চেষ্টা চালালেও দলিত প্যান্থার আন্দোলন তার গুরুত্ব হারায়।
১৯৭১-এ ডিআরডিও-র চাকরি ছেড়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম-শহর চষে ফেলে আম্বেদকরের বার্তা ছড়িয়ে পাঞ্জাবের নিম্নবর্ণ পরিবার থেকে আসা কাঁশীরাম ভাল সংখ্যক দলিতদের সংগঠিত করেন। ১৯৭৩-এ তৈরি করেন ‘বামসেফ’। পরে মুসলমানদের একটি অংশকে দলে টেনে ১৯৮১-তে তৈরি করেন ‘ডি.এস.ফোর’। তার জ্বালাময়ী ভাষণে দলিতদের এক বড়ো অংশ নতুন অবতারের সন্ধান পান। ১৯৮৪ থেকে তাঁর দল ‘বহুজন সমাজ পার্টি’ বা বিএসপি-র উত্থান এবং পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে নাটকীয় অগ্রগতি। ২০০৬-এ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রশিষ্যা মায়াবতীর ২০০৭-এ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা জিতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। অচিরেই পদস্খলন, দুর্নীতি, ক্ষমতালিপ্সা ও স্বৈরাচারের পাকে জড়ানো। কিন্তু দলিত ভোটব্যাঙ্ক এবং মুসলমান ও ব্রাহ্মণদের একাংশকে দলে টেনে শিল্পপতি, আমলা ও মাফিয়াদের সাথে বোঝাপড়া করে এবং বিজেপি/কংগ্রেস/সপার সাথে সমঝোতা করে বহিনজী আরও তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান। একদা ঝুপড়িবাসী দলিত কন্যা এখন বৈভবে বিভোর এবং ক্ষমতার অলিন্দে টিকে থাকায় যথেষ্ট দক্ষ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সহ কিছু জায়গায় কিছুটা গণভিত্তি ধরে রাখলেও অতীতের কাঁশীরাম-মায়াবতীর সেই লড়াকু বিএসপি আজ সম্পূর্ণ অস্তমিত। দুর্নীতিবিদ্ধ মায়াবতী আজ বি.জে.পি.-র হাতের পুতুল। এর অনেক আগে বরিশালের দলিত নেতা যোগেন্দ্র মন্ডল ফজলুল হকের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলায় যে শক্তিশালী মুসলিম-দলিত রাজনৈতিক জোট গড়ে মন্ত্রীসভা তৈরি করেছিলেন তা ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কুশল চালে দুর্বল হয়ে যায়।
সত্তরের দশকে বিহারের মুচি সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা ‘ডিপ্রেসড ক্লাস লিগ’ ও ‘ক্ষেত মজুর সভা’র নেতা বাবু জগজীবন রামকে ইন্দিরা কংগ্রেস কৃষি, রেল, প্রতিরক্ষা প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদে বসায়। পরে তিনি জনতা মন্ত্রীসভার উপপ্রধানমন্ত্রী হন। কেরলের নিম্নবর্ণীয় পারাভান সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা কে.আর, নারায়নকে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। বিহারের হাজিপুর থেকে বিশ্বরেকর্ড করে জিতে আসা পাসোয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাম বিলাসকে কংগ্রেস একাধিক মন্ত্রীত্ব দিয়ে বাগে আনে। এভাবে দেখা যায় যখনই কোন দলিত নেতা নজর কেড়েছে তখনই তাঁকে গণবিচ্ছিন্ন করে ক্ষমতার ভাগ দিয়ে আত্মস্থ করা হয়েছে। অন্যদিকে এটি তাদেরও মতাদর্শগত সমস্যা ও চারিত্রিক দুর্বলতা। মহারাষ্ট্রের মত উত্তরপ্রদেশে অনেক দলিত বৌদ্ধ ধর্ম নেন। পরে দুই জায়গাতেই অনেকে হিন্দুত্বে ফিরে আসেন। কেরলে অনেক দলিত খ্রিষ্টান হয়ে যান। পাঞ্জাবে শিখ। তাদের বলা হয় মাঝাবি, রামদাসিয়া, রবিদাসিয়া, রাংরিতা, রাই, মানসি প্রমুখ। মধ্যপ্রদেশে ঘাসিদাসের শিষ্যরা হন সৎনামী, বাংলায় গুরুচাঁদের শিষ্যরা মতুয়া, পাঞ্জাবে মঙ্গুরামের শিষ্যরা আদি ধরম এবং কেরলে আয়ান কালির শিষ্যরা ‘সাদনো জানা পারপালান জোগান’। মায়াবতী যেমন ক্ষমতা তার একার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত করেন, উদিত রাজ-রামদাস আতায়ালে প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ দলিত নেতৃত্ব আবার জাতিভেদকে চ্যালেঞ্জ না ছুড়ে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের দিকেই মনোনিবেশ করেন। এভাবেই আম্বেদকরপন্থী দলিত আন্দোলনগুলি শ্রেণি ও জাত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে ও তার সাথে বোঝাপড়া করে নিছকই সঙ্কীর্ণ ও সুবিধাবাদী দাবি দাওয়ার আন্দোলনে অধঃপতিত হয় এবং শেষমেষ অতীতে ক্ষমতাসীন জাতীয় কংগ্রেস এবং বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে যায়।
যখন শাসক শ্রেণি দলিতদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী এলিট অংশ তৈরি করে দলিত প্রশ্ন ও দলিত ঐক্যের নামে এক দলিতবাদী সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার নরমপন্থী আন্দোলন, দলিত বিভাজন এবং শ্রমিক- কৃষক সহ দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তখন বিস্তীর্ণ গ্রামীণ ভারত এবং শহর-শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র দলিতদের উপর শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য বেড়েই চলেছে যার বিরুদ্ধে সেভাবে কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না। মাওবাদী তাত্ত্বিক অনুরাধা গান্ধী প্রমুখের এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। দলিত নারীধর্ষণ ও খুন, দলিত ছাত্রকে হত্যা বা জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রতিবাদী দলিত কৃষকের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটেই চলেছে। এই রকম জাত্যাভিমানী আবহের মধ্যে আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজি ও দেশীয় ক্রনি পুঁজির মদতে আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদীরা ২০১৪-তে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে। তারপর থেকেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে খ্রিষ্টান, মুসলমান আর দলিত সম্প্রদায়। তীব্র অত্যাচার যেমন প্রতিবাদের জন্ম দেয়, তেমনই হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবৈষম্যের শিকার রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা, গুজরাটের উন্নায় মুদ্দাফরাসদের উপর গোরক্ষকদের তাণ্ডব প্রমুখ ঘটনাবলী নতুন দলিত জঙ্গী প্রতিবাদের জন্ম দেয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে বিশাল বিশাল দলিত প্রতিবাদী সমাবেশ সংগঠিত হয় যার মধ্যে থেকে উঠে আসে নতুন ভাষা স্লোগান আঙ্গিক সংস্কৃতি ও কর্মসূচি। মহারাষ্ট্রের ‘কবীর কলা কেন্দ্রে’র শীতল শাঠের উদাত্ত গণসঙ্গীত, মধ্যপ্রদেশের মাওলার দলিত মহিলা নাগরি ব্যাণ্ডের রণবাদ্য গড়ে তোলে নতুন চেতনা, নতুন উদ্দীপনা। আবার এর প্রতিক্রিয়ায় বর্ণহিন্দুরা মারাঠা মূক অভিযান সংগঠিত করেন। উনার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ঢোলকা তালুকের ভূমিহীনরা জমি পান, আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সাফাই কর্মীরা স্থায়ী হন। কর্ণাটকের উদিপিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল দলিত সম্মেলন। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে উজ্জীবিত হয় দলিত ছাত্র আন্দোলন। এই নতুন দলিত জাগরণের পক্ষে বামপন্থীরা স্বাভাবিক মিত্র হিসাবে সহযোগী ভূমিকা থেকে অংশীদার বিভিন্ন ভূমিকা নেন। লাল ও নীল পতাকার সহাবস্থান শুরু হয়, ‘জয় ভীম, লাল সেলাম’ নতুন স্লোগান তৈরি হয় কানাইয়া কুমারদের ভাষায়। জাতীয় রাজনীতিতে প্রেক্ষিত হারানো সিপিআই, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল আশ্রয় খোঁজেন দলিত আন্দোলনের র্যডিকাল মর্মবস্তুতে।
ব্রিটিশের সহযোগিতায় তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত চিরস্থায়ী সহযোগী সামন্ত-মুৎসুদ্দি-অত্যাচারী অনুপস্থিত জমিদার পরিবারের আলোকপ্রাপ্ত অংশের একাংশ যেমন উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইওরোপ আমেরিকার স্বাধীনতা ও জাতীয়তা আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন করেছেন সেরকমই ফরাসি বিপ্লব, জার্মান সমাজতান্ত্রিকদের কার্যকলাপ, আরও নির্দিষ্টভাবে সফল রুশ বিপ্লবের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী অংশটিও বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে ঝোঁকেন। ভারতীয় সভ্যতার প্রাকবৈদিক সাম্যবাদ এবং ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ধারাগুলির সংমিশ্রণে উত্তরভারতে আর্যবাদীদের বিপরীতে সমাজতন্ত্রী বা সোশ্যালিস্ট ধারাটিও শক্তিশালী হয় যা কিনা রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের লালনে তাত্ত্বিক ভিত্তি পায়।
কিন্তু দেশ জুড়ে উদীয়মান বিবিধ আন্দোলনকারী বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী ধারা মূলত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরেই বিকশিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টিরও আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো মতে আন্দামানের সেলুলার জেলে, কারো মতে বিবেকানন্দ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা, সিপিআইয়ের মতে ১৯২৫-র কানপুর সম্মেলনে, সিপিআইএমের মতে কলকাতায় মুজফফর আহমেদরা এবং অন্য মতে ১৯২০ তে রাশিয়ার তাসখন্দে তদানীন্তন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নেতা মানবেন্দ্র রায় (বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)-র তদারকিতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (ICP) তৈরি করেন। ঐতিহাসিকভাবে তৃতীয় মতটিই গ্রহণযোগ্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ধারার নেতৃত্বে একের পর এক শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষ করে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে দেশজুড়ে বিগত একশ বছরে, যার মধ্যে তেভাগা১ ও তেভাগা২, তেলেঙ্গানা, পুন্নাপ্পা ভায়লার, শ্রীকাকুলাম, নকশালবাড়ি, ভোজপুর ও দণ্ডকারণ্য অগ্রগণ্য।
স্বভাবতই এই আন্দোলনগুলিতে স্থানীয় শোষিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনজাতির মত দলিতরাও অংশ নেন, কিন্তু বাম ও মার্কসবাদী, মার্কসবাদী- লেনিনবাদী এবং মাওবাদীদের নেতৃত্বে আদিবাসীদের একাংশ যেমন ভ্যানগারড হিসাবে গড়ে ওঠেন দলিত এবং মুসলমানদের সেরকম দেখা যায় না কিছু ব্যতিক্রম এবং ভোজপুর সহ একদা মধ্যবিহারের লেলিহান ক্ষেতখামারে কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি ছাড়া। এক সময় গোদাবরী পারুলেকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে, অজিতাদের নেতৃত্বে কেরলে, জয়ন্ত রংপি, হোলিরাম তেরাংদের নেতৃত্বে অসমে কিংবা বর্তমান ছত্তিশগড়ের, ওড়িশার ও মহারাষ্ট্রের দণ্ডকারণ্যে আদিবাসী সমাবেশের ক্ষেত্রে বামেরা যেখানে সফল, সম্প্রদায় হিসাবে দলিতদের সংগঠিত ও সমাবেশিত করার ক্ষেত্রে অসফল। বিপরীতে ১৯৪৬-‘৪৭-র তেভাগার কৃষক সংগ্রাম থেকে ২০১৫-‘১৬-র দিল্লির ছাত্র আন্দোলন সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের মেরুকরণ ঘটিয়ে দুর্বল করার ক্ষেত্রে এবং বলাই বাহুল্য প্রতিটি নির্বাচনে এক একটি স্পর্শকাতর জাত্যাভিমানী ইস্যু বা অর্থনৈতিক সুবিধা সামনে এনে শাসকশ্রেণিই বরং সফল বাম আন্দোলনকে নির্বিষ করে দিতে। উত্তর ও পশ্চিমভারত জুড়ে নব্য দলিত আন্দোলনের দিশা ও শক্তিকে তারা অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারলেন দলিতদের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রভাবশালী মহারাষ্ট্রের মারাঠা, গুজরাটের পতিদার প্যাটেল, রাজস্থানের গুজ্জর এবং হরিয়ানার জাঠদের সংগঠিত ও সমাবেশিত করে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনেও দেখা গেল আর.এস.এস-বি.জে.পি. খুব দক্ষতার সাথে জাটভ বাদে বাকি দলিতদের, যাদব বাদে বাকি পশ্চাদপদ ভোটকে একত্রিত করে, তাদের পক্ষে নিয়ে এসে, তার সাথে সমগ্র উচ্চবর্ণ হিন্দু ভোট ও একাংশ শিয়া ও পসমন্দা মুসলমান ভোট যুক্ত করে বাজিমাত করে দিল। বাম নেতৃত্বের ভাঁড়ারে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন অস্ত্র নেই। তারা জে.এন.ইউ.-তে ঐক্যবদ্ধ হলেন যত না হিন্দুত্ববাদীদের রুখতে, তার চাইতেও ব্যাপক ভাবে আগুয়ান দলিত ছাত্র সংগঠন ‘বাপসপা’কে প্রতিরোধ করতে। সত্যি কথা বলতে বামেদের কাছে এখনও কোন উত্তর নেই জাতসমস্যা সমাধানের ও জাতপাতের রাজনীতির মোকাবিলার, যেমন নেই বৃহত্তর হিন্দি ও গোবলয়ের এবং দ্রাবিড় দাক্ষিণাত্যের মননকে ছুঁতে পারার। ফলে গ্রামীণ সামন্ত অবশেষ এবং বৃহৎ মুৎসুদ্দি পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণি সংগ্রামের পরিসরে ব্রাহ্মণ্যবাদ, মনুবাদ ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংঘর্ষের পরিবর্তে সম্মুখসারিতে আসছে দলিত-পশ্চাদপদ, দলিত-মুসলমান, পশ্চাদপদ-মুসলমান জাত-সম্প্রদায়গত মেরুকরণ ও সংঘর্ষ কিংবা সঙ্কীর্ণ সুবিধাবাদী দলিতবাদ অথবা মুসলমান মৌলবাদের জয়গান।
লুক্সেমবার্গ, দিমিত্রভ, গ্রামসি, কাফকা, কামু, সাঁত্র, পল সুজি, বেটলেহাইম, ফুকো, ফুকিয়ামা, এডওয়ার্ড সঈদ প্রমুখকে নিয়ে ভারতীয় বাম ও বুদ্ধিজীবীরা যত চর্চা করেন, ততখানি অজ্ঞ ভারতীয় সমাজে রামানন্দ, কবীর, নামদেব, শ্রীচৈতন্য, একনাথ, গুরুনানক, সত্যপীর, বামনদেব, মীরাবাঈ, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ্জালান, মইনুদ্দীন চিস্তি, ধনেশ্বর, জনাবাঈ, তুকারাম, শঙ্করদেব, মাধবাচার্য, লালন ফকির, আরজ আলি মাতব্বর, দুদু মিঞা, কুমারম ভীমা প্রমুখের অবদান সম্পর্কে। আজও তারা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নারায়ণ গুরু, জ্যোতিরাও ফুলে, পেরিয়ার, লোহিয়া, দয়ানন্দ সরস্বতী, সৈয়দ আহমেদ, আম্বেদকরদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেননি। তুলে ধরেননি ডিরোজিও, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, সাবিত্রী ফুলে, রামাবাঈ রাণাডে, আয়াধা দাস, ভাল্লালার, আয়ন কলি, মাকথি থাঙ্গল, বীর শৈলম, প্রেমচাঁদ, শরৎচন্দ্র, যশপাল, মন্টো, জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়াল প্রমুখদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা। রাহুল সংকৃত্যায়ন, এম জি মোরে, এম জি মুরুগাইয়ান, ডি.ডি.কোশাম্বি, বিনয় ঘোষ, গোবিন্দ পানেশর, আনন্দ তেলতুম্বলে প্রমুখের ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা ব্যতীত কোনো সার্বিক সংগঠিত প্রয়াসের অভাব। এই পরিস্থিতিতে ভূয়োদর্শী সমাজদ্রষ্টা দার্শনিক আম্বেদকরের পথনির্দেশ গ্রহণ করে গণ আন্দোলনের দাবিতে অন্তর্ভুক্ত করে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে ভারতীয় সমাজের প্রধান অন্তরায় ধর্ম ও জাতিভেদকে অতিক্রম করে আধুনিকতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে।





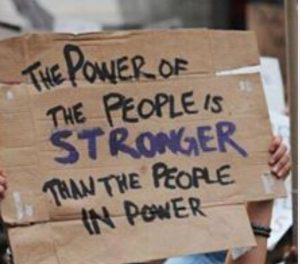








খুব ভালো লেখা। লেখকের পরিচয় আরও বিশদে দিলে মনে শান্তি পাওয়া যেত।