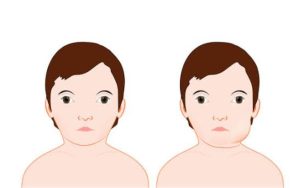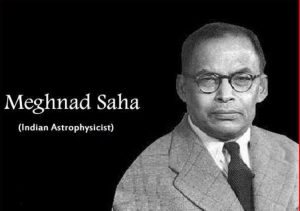সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-ভাবনার বদল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি মাস্টারপিস ইতোপূর্বে লিখিত। আরোগ্য নিকেতন। কিন্তু সে মূলত ক্ষয়িষ্ণু এক চিকিৎসাপদ্ধতির বিপরীতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জয়ের কাহিনি। সময়ের বদলের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হারিয়ে-যাওয়া হেরে-যাওয়া প্রাক্তন ক্ষমতাশালীর প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ বা সহানুভূতি নিয়ে বলার কিছু নেই – জলসাঘর এক চমৎকার উদাহরণ – কিন্তু আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশাই আধুনিক বিজ্ঞানের আগমনকে শুধুই নিজের পরাজয় হিসেবে দেখেন না। কিন্তু আপাতত আমরা সেই আলোচনায় ঢুকতে চাইছি না।
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘গণমিত্র’-ও চিকিৎসা-ভাবনার বদলের প্রেক্ষিতে রচিত। কিন্তু এখানে বদলটা যতখানি প্রাচীন বনাম নবীন গবেষণার, তার চাইতে ঢের বেশি চিকিৎসকের মূল্যবোধের। চিকিৎসা যেখানে জনমুখী সেবা, বা পরিষেবা, ও অর্থোপার্জন যেখানে প্রাথমিক লক্ষ্য নয় – সেখান থেকে অর্থোপার্জন-মুখী চিকিৎসা, এমনকি মুনাফাকেন্দ্রিক চিকিৎসা, যেখানে অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি চুরিচামারি চিটিংবাজি কিছুই আর, খাতায়কলমে যা-ই হোক, বাস্তব প্রয়োগে তেমন দোষের নয় – এই বদলটা ধরতে চেয়েছেন লেখক।
উপন্যাসের স্টোরিলাইন খুব জটিল নয়। কয়েক পুরুষের চিকিৎসক পরিবার – পূর্বে তাঁরা কবিরাজ ছিলেন – বংশের প্রথম আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত ডাক্তার দেবকিঙ্কর। মেডিকেল কলেজ থেকে পাস। তাঁর ছেলে জীবক – সে ডাক্তার হোক, এমনটাই সবাই চেয়েছিলেন, চেয়েছিল সেও – জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স না পাওয়ায় সে মেডিকেল পড়তে যায় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে। ছেলে পয়সা দিয়ে ডাক্তারি পড়ুক, এমনটা দেবকিঙ্কর চাননি – কিন্তু পরিবারের চাপে মেনে নেন। দেবকিঙ্কর ও জীবক – দু’রকম মেডিকেল স্কুলের প্রোডাক্ট, দুরকম সময়ের, দুরকম জীবনদর্শনেরও। এই সঙ্ঘাতই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। পৌরাণিক গল্প প্রসঙ্গে দেবকিঙ্কর ছেলেকে যেকথা বলেন, সেই কথা মূল উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। “ইয়েস। ওইসব গল্পই। সত্যি নয়, কিন্তু ওগুলোর মধ্যে একটা সত্য আছে। মানুষকে শিক্ষা দেয়…।”
মূল কাহিনির মধ্যেই কখনও এসেছে সনাতন – এইডস-আক্রান্ত বাবা-মায়ের উজ্জ্বল ছাত্র, নিচু জাতের মানুষ। কখনও চপলা, অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচেও গ্রামে হাসপাতাল বানানোর স্বপ্ন দেখে, বানিয়ে ফেলেও – যার ছেলে শ্রীমন্ত সেই অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েও মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়ে আসতে পারে। এসেছে আরও অনেকের গল্প। যাঁরা স্বপ্নময়বাবুর লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন তাঁর মায়াবী গদ্যের কথা, তাঁর আপাত অগোছালো সুরে ছাড়া-ছাড়া গল্প বলার মাধ্যমে তুখোড় কাহিনি নির্মাণের দক্ষতা – সেসবের বিশদে ঢুকছি না। উপন্যাসটি কাহিনি হিসেবে অতিমাত্রায় সার্থক মেনে নিয়েও আমরা কথা বলব – উপন্যাসের ভালোমন্দ নিয়ে নয় – কথা বলব এ বইয়ের মূল উপজীব্য বিষয় নিয়ে। অর্থাৎ কখন ডাক্তার গণমিত্র হিসেবে গণ্য হবেন আর কখন নয়, এ নিয়ে। এবং ভাবতে বসব, গণমিত্র হতে পারা বা না পারা, এমনকি হতে চাওয়া বা না চাওয়া – তা কি সবসময় ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভরশীল?
উপন্যাসের কেন্দ্রে যে পরিবারের চরিত্ররা, তাঁরা বংশানুক্রমে ডাক্তার। অতএব, চিকিৎসা পেশার যে dignity ও honour, যে ‘অতীত গৌরব’, যে কথা ‘কোড অফ এথিক্স’ বারবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে – এবং যে কথাগুলো আমি পরিষ্কার করে বুঝতে পারিনি – সে বিষয়ে দেবকিঙ্কর বা জীবকদের মনে অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। তারপরও দেবকিঙ্কর মানবসেবার ভাবনায় সুস্থিত, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী জীবকের চোখে এই পেশা বড়লোক হওয়ার এক কার্যকরী রাস্তা মাত্র। বাণিজ্যিক সিনেমা হলে দেবকিঙ্কর হিরো ও জীবক ভিলেন হয়ে যেতে পারতেন অনায়াসেই, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি অত সাদা-কালো?
দেবকিঙ্কর, বা ডাক্তার দেবকিঙ্কররা, একটা সময়ের প্রতিনিধি। একটা চিকিৎসা-দর্শনেরও। যখন চিকিৎসার সঙ্গে মিশে থাকত আরও অনেক কিছু, যার মধ্যে অভিভাবকত্বও। সনাতনের বাবার এইচআইভি টেস্ট করানোর অংশে সেই অভিভাবকত্বের পরিচয় রয়েছে। বর্তমান সময়ে ডাক্তারের পক্ষে যেটা উচিত মনে হয় তেমনই করে ফেলার কাজটা সহজ নেই আর। গ্রামীণ অঞ্চলে হয়ত পরিস্থিতিটা খুব বদলে যায়নি, কিন্তু শহরাঞ্চলে? বিশেষত তথাকথিত ‘বড়’ হাসপাতালে? দেবকিঙ্করের তুলনায় জীবক যে আলাদা, তার একটা বড় কারণ, জীবকদের সময়টা আলাদা। পাস করে বেরিয়ে জীবক যে যে চাকরি করে ‘অভিজ্ঞ’ বা ঝানু হয়ে ওঠে, দেবকিঙ্করদের সময়ে সেসবের অস্তিত্বই ছিল না। অর্থাৎ জীবকও একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার ফসল, ব্যক্তিমানুষের ভূমিকায় গুরুত্ব দিতে দিতে সেই ব্যবস্থাটা ভুলে গেলে মুশকিল। স্বপ্নময়বাবু হয়ত ব্যক্তিমানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে এঁকেছেন – কিন্তু পাঠক যদি পড়ার সময় জীবকের জীবনদর্শনকে (বা স্খলনকে) শুধুই ব্যক্তিমানুষের লোভ-উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণতি হিসেবে দেখেন, তাহলে সেটা ভুল হয়ে যাবে।
বাবা-ছেলে দুই প্রজন্ম ডাক্তার – এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-দর্শনের বদল – এই বিষয় নিয়ে একখানা চমৎকার বই পড়েছিলাম। ‘দ্য গুড ডক্টর’ (The Good Doctor), লেখক ব্যারন লার্নার (Barron H. Lerner)। লেখক তাঁর বাবার সময়কার চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তদসংলগ্ন মূল্যবোধ এবং তাঁর নিজের চিকিৎসাভাবনা – এই দুইয়ের তুলনা করেছেন। একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে মৃতপ্রায় রোগীকে যেকোনও মূল্যে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াসকে আটকাতে লেখকের বাবা রোগীর বিছানা আটকে রেখেছিলেন, যাতে হাসপাতালের মেডিকেল টিম ‘শেষ চেষ্টা’ না করতে পারে। অথচ, সেই ক্ষেত্রে, মরিয়া ‘শেষ চেষ্টা’ যাতে না করা হয়, তেমন সম্মতিপত্র (হাসপাতালের ভাষায় Do Not Resuscitate, সংক্ষেপে DNR) রোগী বা পরিজনের তরফে ছিল না। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে লেখকের বাবা বিশ্বাস করতেন, যে, এতদিন ধরে দেখে আসা রোগীর ভালো-লাগা খারাপ-লাগা চাওয়া না-চাওয়া তিনি পরিজনের চাইতে কম বোঝেন না। বরং তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, এমন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে দিশেহারা পরিজনের তুলনায় ডাক্তারবাবু ঢের বেশি উপযুক্ত। অথচ সেই ডাক্তারবাবুর পুত্র, অর্থাৎ ‘দ্য গুড ডক্টর’ বইয়ের লেখক, তিনিই বাবার এমন কাজ মন থেকে সমর্থন করতে পারেন না। কেননা, বর্তমান চিকিৎসা-দর্শনে রোগীর ইচ্ছে-অনিচ্ছেই শেষ কথা। সেই ইচ্ছে অনুমান করে, বা স্পষ্ট করে সে বিষয়ে মত না নিয়ে, ডাক্তার স্বয়ং নিজের মত অনুসারে চিকিৎসা করবেন (বা চিকিৎসা বন্ধ করবেন), এটা অবাঞ্ছিত তো বটেই, অনুচিত ও অন্যায়ও। আবার সেই লেখকই পরে ভাবতে গিয়ে দোটানায় পড়ে যান, বাবাদের সময়কার চিকিৎসাব্যবস্থাটাই কি এখনকার চাইতে ভালো ছিল না? ডাক্তার এবং রোগী, উভয়ের পক্ষেই?
তবে ‘দ্য গুড ডক্টর’ বইয়ে বদলটা চিকিৎসা-বিষয়ক ভাবনায়। আর আগেই বললাম, ‘গণমিত্র’ বইয়ে বদলটা যতখানি চিকিৎসা-বিষয়ক ভাবনায়, তার চাইতেও বেশি মূল্যবোধে। সেক্ষেত্রে স্বপ্নময়বাবুর পক্ষে – এবং পাঠকের পক্ষেও – সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা সহজ। সকলেই, সম্ভবত, নিশ্চিত যে আগের ব্যবস্থাটিই ভালো ছিল। অর্থগৃধ্নু মানসিকতা বা দুর্নীতি দেখতে দেখতে চোখ বা মন অভ্যস্ত হয়ে গেলেও ব্যাপারটা যে সম্মানার্হ নয়, এটুকু সকলেই বোঝেন। আগেকার সেই সুন্দর দিন, যেখানে চিকিৎসক নিছক চিকিৎসক নন, অভিভাবকও। যেখানে চিকিৎসকের দায় শুধুমাত্র চেম্বারে রোগী দেখে দুকলম প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়াতে শেষ হয়ে যায় না।
(শেষাংশ আগামী পর্বে)