১৯৬৩ সাল। মার্চ মাস। পাঁচ বছরের মেয়ে এসে বাবাকে বলল, “বাবা, দেখো দেখো, গলাটা দেখো!”
বাবা জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যথা?”
“হুম… খুব…”
চোয়ালের দু-পাশও ফুলেছে খানিক। বাবা বুঝলেন, মাম্পসই হয়েছে হয়তো। রাত তখন একটা। কী করবেন? মেয়েকে নিয়ে গেলেন ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।
তাঁর নিজের একটা ছোট গবেষণাগার ছিল। তিনি সেখান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসে মেয়ের গলার একটা সোয়াব নিয়ে নিলেন। ওঁর ল্যাবেরেটরিতেই হিমায়িত করে রাখলেন সেই স্যাম্পেল। তখনকার দিনে, বা এখনও মাম্পস যে খুব ভয়াবহ তা নয়। কিন্তু, কখনও কখনও এর আনুষঙ্গিক জটিলতা হিসেবে আসত বধিরতা; মাথা, শুক্রাশয় কিংবা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ (প্যাঙ্ক্রিয়াইটিস) ইত্যাদি হত। শিশুরাই মূলত শিকার হত এই ভাইরাসের। বোঝাই যাচ্ছে, মেয়েটির বাবা যে সে মানুষ ছিলেন না। রীতিমতো গবেষক, আবিষ্কারক, প্রোফেসর! না, এদেশের নন, তবে বিদেশের শঙ্কু হতেই পারতেন।
তো তিনি তখন কন্যার গলায় বাসা বাঁধা ভাইরাসটিকে নিজের ল্যাবে বড় করে তুললেন। মানে, মুরগির ভ্রূণের সারি সারি কোষে এই ভাইরাসের ঘর বেঁধে দিলেন। ভাইরাসটি মনের সুখে বড় হল সেই কোষের ঘরে। তারপর বংশবৃদ্ধিও করল। এক প্রজন্ম থেকে আরেক… আরেক থেকে অনেক…। ফলে একসময় সেই ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করতে ভুলেই গেল। সে তখন শুধু মুরগিতে মত্ত! মানুষের জন্য কমজোরি (অ্যাটেনুয়েটেড) হয়ে ওঠা এই ভাইরাসটিকে এবার যদি মানুষের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কী হবে?
সংক্রমণের ক্ষমতা তো সে কবেই হারিয়েছে, কাজেই মাম্পস হবে না! কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়া ভাইরাস অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করবে। আর এই অ্যান্টিবডিই মানুষকে সত্যিকারের ক্ষমতাবান মাম্পস ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দেবে ভবিষ্যতে।
এমন চমকে দেওয়া আবিষ্কারকে তাহলে কী নামে ডাকা যায়?
আজ্ঞে, এইই তো ভ্যাকসিন! টিকা!
কিন্তু এ সবই মুখের কথা মাত্র। বৈজ্ঞানিক ধারণাকে কাজে লাগাতে হলে হাতেনাতে প্রমাণ চাই। চাই এমন মানুষ যার দেহে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হবে। দেখা হবে ফলাফল।
জেরিল লিন, সেই ছোট্ট মেয়ে যার গলার ভাইরাসটি গবেষক বাবা তুলে এনেছিলেন ভ্যাকসিন তৈরির জন্য, তার বোনের নাম ক্রিস্টেন। ১৯৬৬ সালে ক্রিস্টেনের বয়েস ছিল একবছর। প্রথম যাদের দেহে এই ভ্যাকসিন পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হল ক্রিস্টেন তাদের মধ্যে একজন। দিদি বা দাদার থেকে সংক্রমণ বাড়ির ছোটটির দেহে ছড়িয়েছে এমন উদাহরণ তো মেডিসিনের ইতিহাসে হরবখ্ত পাওয়া যায়। কিন্তু দিদির গলার সংক্রমণ থেকে তৈরি হওয়া ভ্যাকসিনের বোনকে সুরক্ষা দেওয়ার নজির এই প্রথম। ১৯৬৭ সালে এই মাম্পস ভ্যাকসিন লাইসেন্স করলেন দুই মেয়ের বাবা মরিস হিলম্যান।
এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে বাচ্চাদের যে চোদ্দ রকমের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তার আটটাই (মিজলস, মাম্পস, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, চিকেন পক্স ইত্যাদি) হিলম্যানের তৈরি করে দেওয়া। অথচ তিনি বলতেন, “আমার নাম যদি খবরের কাগজে বেরোয় কিংবা টেলিভিশনে ক্যামেরার সামনে দেখায় অথবা রেডিওতে শোনা যায়, লোকে হয়তো ভাবতে পারে, আমি কিছু একটা বিক্রি করছি!” এই মনোভাব থেকেই কি না কে জানে, হিলম্যান তাঁর তৈরি করা কোনও ভ্যাকসিনের নামের সঙ্গেই নিজের নাম জুড়ে দেননি। মানুষ এবং পশুদের জন্য প্রায় চল্লিশ রকমের ভ্যাকসিন তৈরি করে দিয়ে গেছেন, হিলম্যান এবং তাঁর টিম।
আজও যে মাম্পস ভ্যাকসিনের স্ট্রেন ব্যবহৃত হয় তার বেস কিন্তু, হিলম্যান-কন্যা জেরিল লিনের গলা থেকে মাঝরাত্তিরে ছেঁকে নেওয়া সেই ভাইরাস! তাই এই ভ্যাকসিন ভাইরাস স্ট্রেনটির নাম আজও, জেরিল লিন স্ট্রেন।
মেডিসিনের ইতিহাসে কোন গবেষকের একক প্রচেষ্টায় যদি সবচেয়ে বেশি মৃত্যু রোখা যায়, তিনি মরিস হিলম্যান। শুধু মিজলস ভ্যাকসিনই ২০.৩ মিলিয়ন মৃত্যুকে রুখে দিয়েছে ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে। এছাড়া, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের দৌলতে এই রোগের প্রকোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ প্রায় ৯৫% কমে গেছে!
এই হিলম্যানই প্রথম বলেছিলেন ক্ল্যামাইডিয়া কোন ভাইরাস নয়, ব্যাকটেরিয়া। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জিনের গঠন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় (Antigenic drift and shift), এও তাঁর দেখানো। ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বললেই মহামারীর কথা মনে আসে। তাই আরেকটি ঘটনার কথা বলি।
সাল ১৯৫৭, এপ্রিল মাস। হংকং-এ এক নতুন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হল। হিলম্যান ততদিনে জিনের মিউটেশনের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জার নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারটা বুঝে গেছিলেন এবং এই নবাগত ইনফ্লুয়েঞ্জা যে অচিরেই অতিমারীর রূপ নেবে, সেটা ১৭ই এপ্রিলের নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এ হংকং এর অবস্থা পড়ে আন্দাজ করে ফেলেছিলেন হিলম্যান।
তখনও বিশ্বের কোনও বিজ্ঞানী কিংবা WHO, কেউই বুঝতে পারেনি এই আসন্ন মহামারীকে।
পরদিনই হিলম্যান মার্কিন সেনাবাহিনীকে আবেদন করেন ওখানকার ভাইরাসের নমুনা কোনভাবে সংগ্রহ করার জন্য। প্রায় একমাস বাদে হংকং-এ কর্মরত একজন অসুস্থ নৌসেনার গার্গল করা জল স্যাম্পেল হিসেবে হাতে পেলেন হিলম্যান। একাধিক সিভিলিয়ান, মিলিটারির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখলেন, সকলেই সেই নতুন ভাইরাসে ‘Susceptible’ অর্থাৎ কারো দেহেই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডিটি নেই!
তিনি যোগাযোগ করলেন একাধিক ওষুধবিক্রেতা কোম্পানির সঙ্গে। চাইলেন, এমন নমুনা থেকে ভ্যাকসিন তৈরির একটি সুযোগ। সময়টা ১৯৫৭ বলেই, ইউ এস ভ্যাকসিন রেগুলেটরি এজেন্সির অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানিগুলো হিলম্যানকে সুযোগ দিল। মুরগির ডিমের কুসুমে সেই ভাইরাসকে বড় করে, তার সংক্রমণ ক্ষমতা কমিয়ে হিলম্যান তৈরি করলেন নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ভ্যাকসিন! চল্লিশ মিলিয়ন ডোজ তৈরি হয়ে গেছিল, যখন এই প্যানডেমিক আছড়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে। সেবছর শীতেই, এতকিছুর পরেও, সেই মারণ ব্যাধিতে মৃত্যু হয় প্রায় এক লক্ষ মানুষের। কিন্তু হিলম্যানের তৈরি ভ্যাকসিনের দৌলতে বেঁচে যান আরও বহু লক্ষাধিক মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন ভাইরাসের দ্বারা তৈরি হওয়া কোনও মহামারীকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভ্যাকসিন দিয়ে রুখে দেওয়ার উদাহরণ সেই একটিই! সেখানেও, পথপ্রদর্শক এই হিলম্যান।
আজও আমরা বসে রয়েছি এক প্যানডেমিকের গর্ভে। আজও চেষ্টা চলেছে ভ্যাকসিন দিয়ে এই মহামারীকে হারিয়ে দেওয়ার। আজও আমরা অপেক্ষা করছি করোনামুক্ত পৃথিবীর। ততদিন পর্যন্ত ইতিহাসের এই রঙিন পাতারাই আমাদের স্বপ্ন দেখাক।
“silly পয়েন্ট-এ পূর্ব প্রকাশিত”।






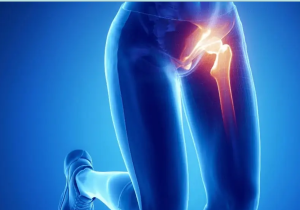







অসাধারণ তথ্য। না বললে হয়ত এই গবেষকের কথা জানতেই পারতাম না।
ভালো লেখা।