লকডাউনের মধ্যে ভুলে গেলেন নাকি যে সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ শুরু হচ্ছে এই মে মাসের দু’ তারিখে? ১৯২১এর ২ মে তাঁর জন্ম। তাঁর মৃত্যুর আঠাশ বছর পার হচ্ছে এবছর, এপ্রিলেই । আর তা মনে রেখেই এই দুই হাজরার গপ্পো!
নির্ঘাৎ ভাবছেন, কিছু ভুল হচ্ছে! ‘দুই হুজুরের গপ্পো’ নামে একটা বাংলা নাটকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছি ভাবছেন? ভাবছেন সে তো এক রুশ নাটকের অনুসরণে সায়কের নাটক। সেখানে আবার সত্যজিত রায় আসছেন কি করে? না, দুই হুজুর নয় । দুই হাজরা। একজন আসল। আর একজন নকল। ডা হাজরা।
লেটার হেডে নাম ছাপা রয়েছে, তাতে J দিয়ে হাজরা লেখা। আর চিঠির নিচে নাম সই করা হয়েছে যে হাজরা লিখে তার হাজরায় হাজির Z। ফেলুদা এই J আর Z দেখেই নকল হাজরা আর আসল হাজরাকে চিনে নিয়েছিলেন। অন্তত সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার কেল্লা’ বইতে সে কথাই লেখা আছে। তবে ‘সোনার কেল্লা’ সিনেমার দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে J আর Z ভেদে আসল আর নকল হাজরার তফাৎ বোঝা গিয়েছিল ডা. হাজরার ভিজিটিং কার্ড আর সার্কিট হাউসে রাখা রেজিস্টারে নকল হাজরার সই দেখে! গোয়েন্দা ফেলুদা তো J আর Z দেখে আসল আর নকল হাজরা ধরে ফেললেন। কিন্তু বাস্তবে কী আসল নকল ধরা অত সহজ নাকি!
জাল আর আসল মানুষ নিয়ে অনেক কাহিনী আমাদের ইতিহাসে রয়ে গেছে। সন্ন্যাসী, ভাওয়ালের রাজা কিনা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের জাল ছবির প্রদর্শনী পর্যন্ত! আমাদের জীবনে এইসব চমকপ্রদ ‘জাল’-এর জালিয়াতির কাহিনী নিয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন অদ্রীশ বিশ্বাস। সে-বই প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই আত্মঘাতী হন লেখক।
যাই হোক, এ লেখা শুধু জালের গল্প নয়। একই নামের দাবিদার ‘লক্ষ্মীবাবুর আসলি সোনা চাঁদি কা দোকান’ বা দুলাল চন্দ্র ভড়ের ‘আসল’ তালমিছরির কথাও এই লেখায় বলছি না। এ লেখার বিষয় জাল ডাক্তার আর আসল ডাক্তার, যার জন্য উপক্রমনিকায় সত্যজিতের ডাক্তার হাজরাকে স্মরণ করা!
বছর কয়েক আগে আমাদের রাজ্যে একের পর এক ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়ছিলেন। কেউ কেউ আদৌ ডাক্তারি পড়েন নি, কেউ আবার কোনও হাতুড়ে পাঠক্রমের ছাত্র ছিলেন; সেই পড়াকে পাথেয় করে চেম্বার সাজিয়ে বসে পড়েছিলেন। কেউ তাঁদের সেই সব মন গড়া নকল ডিগ্রিটাই ইংরেজি নানান বর্ণে সাজিয়ে হাজির করেছিলেন। নামের আগে ডা. আর নামের পেছনে ইংরেজি বর্ণমালার বহুবিচিত্র বিন্যাস রোগীকে আকৃষ্ট করত। ডাক্তারের পসার যেত জমে। কোনও কোনও নকল ডাক্তার মিথ্যে করে এম. বি. বি. এস. বা এম. ডি., এম. এস. ডিগ্রি ব্যবহার করতেন। একই সঙ্গে ব্যবহার করতেন অন্য কারুর মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর। আশার কথা, আমাদের পুলিশ আর গোয়েন্দার সাহায্যে সেই সব ভুয়ো ডাক্তাররা একের পর এক ধরা পড়েছিলেন।
এখন না হয় ডাক্তারি পড়ানো হয়। সেই পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নেয়। সেই পরীক্ষা হয় লিখিত এবং ব্যবহারিক, যাতে কৃতকার্য হলে ডাক্তারি পাশের ছাড়পত্র মেলে। তবে তারপরেও ডাক্তারি করার ছাড়পত্র পেতে অপেক্ষা করতে হয়। ইন্টার্ন বা শিক্ষানবীশী পর্বের পর মেডিকেল কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করার পর মেলে ডাক্তারি করার ছাড়পত্র।
এখন প্রশ্ন হল, যখন এরকম ডাক্তারি প্রথামাফিক প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হত না তখন কি করে আসল ডাক্তার বিচার করা হত?
ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যায় ডাক্তারির পেশা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আবুল ফজল, নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং লাহোরি ওই সময়কার উলেমা (গবেষক) এবং কবিদের তালিকা তৈরি করার সময় ডাক্তারদেরও সেই তালিকায় যুক্ত করেছিলেন। এই ডাক্তাররা যুক্ত ছিলেন মুঘল বাদশাহদের সভায়। আকবরের আমল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়।
কিন্তু এই রাজকীয় কাজে যোগ দেওয়া সহজ ছিল না। ডাক্তারদের এই কাজে যোগ দেওয়ার আগে নিয়োগকর্তার করা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। রাজা-মহারাজা সন্তুষ্ট হলে তবেই না চাকরি! সবচেয়ে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বেছে নেওয়ার জন্য কড়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত। মাসিরুল-উমারা থেকে জানা যায়, হাকিম আলি গিলানির নিযুক্তির সময় আকবর বেশ কিছু বোতলে নানারকম তরল ভরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সব বোতলের কোনটায় ছিল সুস্থ মানুষের প্রস্রাব, কোনটায় অসুস্থ মানুষের প্রস্রাব। আবার কোনটায় গরু বা গাধার প্রস্রাব। হাকিম নাকি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং সসম্মানে শাসকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই গিলানির নামডাক বাড়তে থাকে। তিনি আকবরের খুবই ঘনিষ্ঠ হন। এ থেকেই বোঝা যায় সেই সময়ে বিকারতত্ত্ব বা প্যাথোলজি কতটা উন্নত ছিল। একই রকম ঘটনা শাহ আলমের আমলেও ঘটেছিল বলে মানুচি জানিয়েছেন।
মানুচির মন্তব্য থেকে জানা যায়, ডাক্তারদের ‘সাম্রাজ্যিক কৃত্যক’ –এ এক ধরনের ক্রমোচ্চশীল ব্যবস্থা ছিল। সবচেয়ে ওপরে থাকতেন মুখ্য ডাক্তার, যাঁর অধীনে থাকতেন বেশ কয়েকজন ডাক্তার, যাঁরা তাঁর আদেশ পালন করতেন। মুঘল যুগে এই মুখ্য ডাক্তারের নাম ছিল সারমদ-ই-অভিব্বা বা সরমদ-ই-হুকুম। আর রাজপরিবারের মুখ্য ডাক্তার ছিলেন ‘হাকিমুল মুলক’, যাঁরা একরকম স্বাধীনভাবে মনসব ভোগ করতেন। আকবরের আমলে সবচেয়ে পরিচিত চিকিৎসক, যিনি সবচেয়ে বড় মনসবদারি ভোগ করতেন তিনি হলেন হাকিম আবুল ফাথ। আর ‘হাকিমুল মুলক’ ছিলেন হাকিম শামসুদ্দিন গিলানি। ১৬২৯-এ শাহজাহান শাসক হওয়ার পর এই শামসুদ্দিন গিলানির ছেলে হাকিম আবুল কাশিম হন ‘হাকিমুল মুলক’। এরপরে এই পদে অভিষিক্ত হন হাকিম মির মুহাম্মদ মাহদি আরদিস্তানি, পরে হাকিম সাদিক খান।
মুঘল চিত্রশিল্পেও চিকিৎসকদের এই ক্রমোচ্চশীলতার ছাপ মেলে। সেখানে ভাগ ছিল এরকম – রাজার ডাক্তার, যুবরাজের ডাক্তার, অভিজাতদের ডাক্তার। দু-তিনটে ছবিতে দেখা যায় মুখ্য ডাক্তার তাঁর অধীনস্থ চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করছেন। ডাক্তারদের ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশের বৃত্তান্ত মেলে নানান উপাদানে। অনেকেই বড় বড় মনসবের ভাগ পেতেন। আর যাঁরা এই মনসবদার হতেন না, তাঁদের দেওয়া হত দৈনিক বা বার্ষিক বেতন। আবার মনসব দেওয়ার পরও তাঁদের ‘জার-ই-জেব’ বা ‘পকেটমানি’ দেওয়া হত জরুরি ওষুধপত্র সঙ্গে রাখার জন্য। সেই ষোড়শ শতকে বেতন ছিল বছরে ৩৬০০টাকা থেকে ১০০০০টাকা। মানুচি জানিয়েছেন শল্য চিকিৎসকরা দিনে পেতেন ২ থেকে ৭০০ টাকা। এই টাকার পরিমাণ কম-বেশি হত দক্ষতা আর যোগ্যতার জন্য। যোগ্য ডাক্তারই তো আসল ডাক্তার!
খাস শাসকের ডাক্তার হলেও খাস অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার সহজ ছিল না। মানুচি লিখেছেন, রাজকীয় ‘হারেম’ বা আমীরদের ‘হারেম’-এ প্রবেশের আগে চিকিৎসকের গা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হত আর তাঁকে হারেমে সঙ্গে করে নিয়ে যেত হিজড়ারা। হারেমের মধ্যে রাজপরিবারের অসুস্থ নারীর চিকিৎসার জন্য একটা ‘বিমারখানা’ থাকত। রাজ পরিবারের কারুর চিকিৎসা শুরু করার আগে শাসকের অনুমতি লাগত। শাসক সব সময়ই ভয়ে থাকতেন। চিকিৎসককেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। ভয় ছিল ষড়যন্ত্রের। অসুস্থ চিকিৎসকের চিকিৎসার অনুমতি মেলে নি, এমন উদাহরণও আছে। ১৬৮৩তে চিকিৎসক দিলের খান অসুস্থ হয়ে পড়লে সম্রাট শাহ আলম তাঁর চিকিৎসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। কাজেই মুঘল যুগে সম্রাটরা শুধু আসল বা নকল ডাক্তার নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। যোগ্যতার পাশাপাশি বিবেচ্য ছিল বিশ্বস্ততা।
আর বিশ্বস্ত, যোগ্য চিকিৎসকের ওপর শাসক ও আমীর ওমরাহরা খুব নির্ভরও করতেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসকের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। তবে সেখানেও যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকদের কাজ এবং দক্ষ চিকিৎসার প্রতি তাঁর প্রত্যাশা ছিল খুবই বেশি। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলে আবার তিনি চিকিৎসকদের ভর্ৎসনা-অপমান করতেন। তাঁর রোগ সারাতে না পারায় তিনি এক চিকিৎসককে কোনও না কোনও অজুহাতে পদচ্যুত করেন। অর্থাৎ রাজার অসুখ সারানোটাই চিকিৎসকের যোগ্যতার নির্ধারক ছিল। তবে সবটাই তো বিশ্বাস আর নির্ভরতার ব্যাপার। কোনও অসৎ চিকিৎসককে পদচ্যুত করার পরও শাসক নিজের প্রয়োজনে আবার তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন, এমন উদাহরণও আছে। আবার মুখল যুগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি-ষড়যন্ত্রের প্রভাবও পড়ত চিকিৎসকদের ওপর। হাকিম তাকাররুব খানের অবসরের পর বন্দী শাহজাহানকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার ‘অপরাধ’-এ তাঁর ছেলেকে আওরঙ্গজেব হাকিম পদ থেকে অপসারিত করেন। পরে আওরঙ্গজেব নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সেই হাকিমেরই শরণাপন্ন হন, উঠে যায় পদচ্যুতির আদেশ!
উল্টো গল্পও রয়েছে বৈকি!
এক চিকিৎসক রাজা বা অভিজাতের চিকিৎসক হিসাবে কাজে যোগ দিলেও তিনি সারাজীবন তাদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন না। সত্যিকারের পেশাদারের মত তিনি তাঁর ইচ্ছেমত নিয়োগকর্তা বদল করতে পারতেন। তবে শাসকের সন্দেহ আর ষড়যন্ত্রের ভয় কিন্তু সবসময়ই সঙ্গী ছিল। শাসকরাও চিকিৎসকের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে নানান পুরস্কার দিতেন। ১৬১৮তে হাকিম রুহুল্লাহ, নূরজাহান বেগমের অসুখ নিরাময় করার পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন তাঁর দেশের বাড়ির একটি গ্রাম যা চিহ্নিত হয় ‘মাদাদ-ই-মাস’ নামে যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত। চিকিৎসকের এই স্বীকৃতি লাভে তাদের চিকিৎসার দক্ষতাই একমাত্র বিবেচ্য ছিল। কোনও ধর্মগত বা ভাষা ও গোষ্ঠীগত পরিচয় নয়।
রাজকীয় বা আমীর ওমরাহদের চিকিৎসা করা ছাড়া কাজের জন্য অন্য ক্ষেত্রও ছিল মুঘল আমলে।
‘দারুশ-শিফা’ বা ‘শিফাখানা’ অর্থাৎ হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল মুঘল আমলে। মূলত জাহাঙ্গীরের শাসনকাল থেকে গড়ে ওঠা এই হাসপাতালে চিকিৎসকদের দৈনিক ভাতা দেওয়া হত সরকারি তহবিল থেকে। আওরঙ্গজেবের সময়কালের কাগজপত্র থেকে জানা যায় ঔরঙ্গাবাদের এক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের কাজের জন্য পেতেন দৈনিক ছ’টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৮০ টাকা। তবে শাসককে প্রদেয় অর্থ কেটে নেওয়ার পর চিকিৎসক হাতে পেতেন মোট ১৩৬ টাকা। এই অল্প পারিশ্রমিকে কী আর যোগ্য চিকিৎসক মিলত যেখানে সম্রাট বা অভিজাতর চিকিৎসক হলে পাওয়া যেত এর কয়েকগুণ বেশি অর্থ!
চিকিৎসকদের কাজের কিন্তু অন্ত ছিল না। শুধু রোগ নির্ণয় এবং তা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করা নয় তাঁকে ওষুধও তৈরি করতে হত। মনে করা হত যে ওষুধ তিনি রুগীকে খেতে দিচ্ছেন তা তৈরি করে দেওয়াটাও তাঁরই কাজ। ফলে ‘ফার্মাসিস্ট’-এর কাজও করতে হত ডাক্তারকে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হত ওষধি গুঁড়ো, তরল (শরবত, আরক) ইত্যাদি। মুঘল আমলে ডাক্তারির নানান শাখার অগ্রগতি ঘটেছিল। মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু চিকিৎসা ইত্যাদি। লেখা হয়েছিল এইসব বিষয়ে বইপত্রও। ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যার বইয়ের অনুবাদও হয়েছিল। উইলিয়াম হারভের রক্তসংবহনতন্ত্রর তত্ত্বও এ দেশের চিকিৎসকদের অজানা ছিল না।
এইসব যোগ্য চিকিৎসকরা সবাই যে শাসকবর্গর চিকিৎসা বা শাসক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে চিকিৎসা করেই জীবন কাটিয়ে দিতেন তা নয়। অর্থ-নিরাপত্তা আর পদপ্রাপ্তিই তো সব নয়। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থেকে এঁরা শুরু করতেন ‘প্রাইভেট প্র্যাকটিস’। এঁ
দের বলা হত ‘মুতাতাবিব-সিরহিন্দি’ বা বাজার-ডাক্তার। শাসক বা আমীর ওমরাহদের চিকিৎসা করলে অর্থ মিলত বটে কিন্তু চিকিৎসা করার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে যেত। ডাক্তার যদি ডাক্তারিই না করতে পারেন তবে আর ‘কাজ’ করে লাভ কী! এই ভাবনা থেকে যোগ্য ডাক্তাররা ‘প্রাইভেট প্র্যাকটিস’ করতেন।
আর এখানেই শুরু হত আসল ডাক্তার আর নকল ডাক্তারের দ্বন্দ্ব। রাজার ডাক্তার হওয়ার সময় না হয় ভালরকম ‘পরীক্ষা’ দিয়ে চাকরি পেতে হ’ত কিন্তু ‘বাজার-চিকিৎসক’ যোগ্য না অযোগ্য, আসল না নকল – সে বিচার কে করবে? স্বভাবতই জাল ডাক্তারও ছেয়ে গিয়েছিল বাজারে। বাদাউনি জানিয়েছেন এমন বহু চিকিৎসক বাজারে মিলত যারা হাতুড়ে বা কোয়াক ডাক্তার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুচিও লিখেছেন অসংখ্য জালিয়াত ডাক্তারের কথা, যাঁরা বিভিন্ন সরাইতে ডাক্তারির নামে পর্যটকদের ঠকাতেন। এই বাজার-চিকিৎসকদের মধ্যে যোগ্য লোককে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না!
যোগ্য ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের নিজস্ব ক্লিনিক ছিল। তাঁরা ‘প্রাইভেট প্র্যাকটিস’ করতেন। তাঁদের চাহিদা বেড়েই চলত। ফলে চিকিৎসা পেশাকে কেন্দ্র করে একটা পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীই গড়ে উঠেছিল। আর তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকতেন অসংখ্য ‘নকল হাজরা’। ফেলুদা ‘জে’ (J) আর ‘জেড’ (Z) দিয়ে ‘নকল হাজরা’কে ধরে ফেলেছিলেন। এখনকার দিনে ডিগ্রি আর রেজিস্ট্রেশন যাচাই করে ‘নকল হাজরা’ ধরা যায় কিন্তু সেই সময় আসল-নকল ধরা মোটেই সহজ ছিল না। ডাক্তারির জগতে আসল-নকলের সমস্যা ভারতের মুঘল আমলের ইতিহাসে ভাল রকমই ছিল। সাধে কী আর বলে, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়!
কৃতজ্ঞতাঃ S. Ali Nadine Reach, ‘Physicians as Professionals in Medieval India’, Deepak Kumar edited, Disease and Medicine in India, New Delhi: Tulika, 2001.

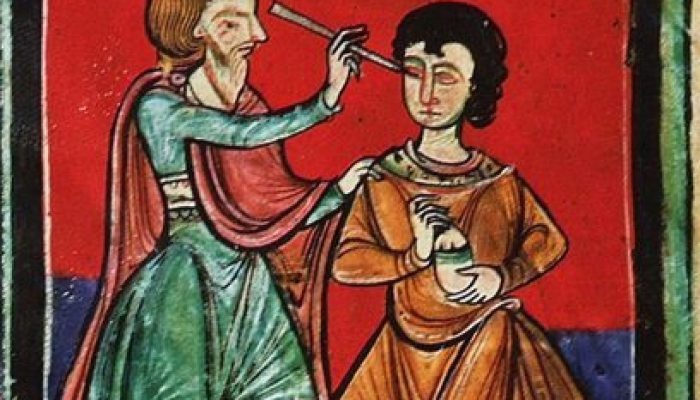

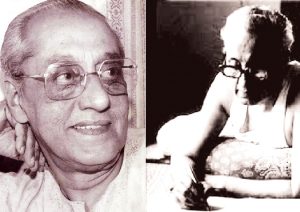
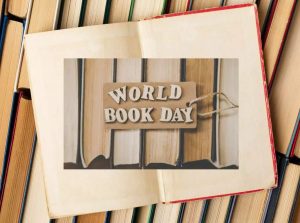
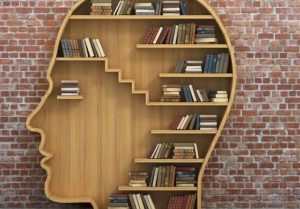








অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম স্যার।