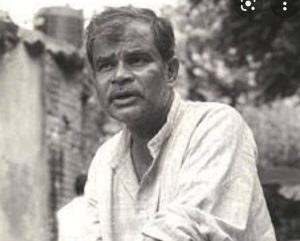দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি বিশেষ ১
বছর শেষ হতে চলল। অনেক মনীষীর জন্মশতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ পালন হয়েছে। এই একজনের কথা অনেকদিন ধরে লিখব ভাবছি। আজ লিখেই ফেলি। রোজ আই সি ইউ-তে ঢোকার আগে আমি এঁকে একবার স্মরণ করি। সুইডেনের ডা. স্বেন আইভার সেলডিঙ্গার। ১৯২১ সালে যাঁর জন্ম হয়েছিল। এ বছর ছিল যাঁর জন্ম শতবার্ষিকী।
ডা.সেলডিঙ্গার ছিলেন একজন রেডিওলজিস্ট। আজকের ইন্টারভেনশনিস্ট (রেডিওলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট)-দের জগতে তাঁর নাম অহরহ স্মরণ হয়, তাঁর আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতির জন্য। তার নাম “সেলডিঙ্গার টেকনিক”। আধুনিক চিকিৎসায় যখন প্রতিদিনই এঞ্জিওগ্রাফি বা এঞ্জিওপ্লাস্টির কথা ওঠে, মাত্র বছর সত্তর আশি আগেও ধমনী বা শিরার মধ্যে একটি ক্যাথিটার ঢোকাতে গেলে শল্যবিদদের চোখে জল আসত। এক্স রে-তে দেখা যায় না, চামড়ার ওপর থেকে গভীরে থাকা শাখা প্রশাখা বোঝা যায় না, তার মধ্যে একখানা টিউব ঢুকিয়ে দেওয়া তো শিবের অসাধ্য। শিরাতে সুঁচ বা ক্যাথিটার ঢোকানোর কথা ভাবা হত, কিন্তু ধমনী? যাতে ফুটো হলে হৃদপিণ্ডের তালে তালে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে?
বাইরে থেকে চোখে দেখা যায় না, তাই ধমনী বা শিরা পেতে হলে আগে ডিসেকশন করে, চামড়া কেটে, তার নীচের চর্বি আর মাংস কেটে, চোখের সামনে বের করে এনে তবে তাতে ক্যাথিটার টিউব ঢোকাতে হত। মড়া কাটতে তো অসুবিধে নেই রে বাবা, কিন্তু এ তো জিয়ন্ত মানুষ! রক্তারক্তি আর কাটাকুটির পরের ব্যথার বহরের জন্য নানা ধরণের টিউব, ক্যাথিটার, নল যাই তৈরি করতেন আর পরাতেন বিজ্ঞানীরা, সেসব কিছুদিন চলার পর বাতিল হয়ে যেত। কেউ কেউ অল্পস্বল্প কেটে কাজ করতে পারতেন, কেউ গলার, কেউ বা পায়ের ধমনী বা শিরা কাটতে দক্ষ, কিন্তু সবার দক্ষতা তো সমান নয়!
শুধু সেলডিঙ্গার নয়, বহুদিন ধরে আরো অনেক চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী এই আসুরিক পদ্ধতির একটা সহজ সরল প্রতিস্থাপক খুঁজছিলেন। এমন কোন পদ্ধতি, যাতে শিরা/ধমনীর ভেতর একটা ক্যাথিটার ঢুকিয়ে দেওয়াটা ছোট থেকে বড় সব ডাক্তারের আয়ত্তের মধ্যে থাকবে।
ততদিনে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে হৃদপিন্ডের ধমনীতে জমে থাকা ক্লট পরিষ্কার করে দিলে বা বন্ধ হয়ে যাওয়া ধমনীকে চওড়া করে দিলে, হার্ট অ্যাটাকের রোগীদের বাঁচানো সম্ভব। আরও কত অসুখ আছে। জন্মগত হৃদপিন্ডের অসুখ, হার্টের ভালভের অসুখ সব ই সারানো যায়! কিন্তু মানুষের হৃদয়- সে অবধি পৌঁছতেই তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে গেল! কত কবির কবিতা, চিত্রকরের মহান শিল্প, সঙ্গীতজ্ঞের স্বর্গীয় প্রতিভা বৃথা গেল! সেই ১৯৪০ সাল থেকে এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন কুরন্যান্ড আর রিচার্ড নামে দুজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। শিরার মধ্যে দিয়ে হৃদপিন্ডের ডানদিকের অলিন্দ নিলয়ে পৌঁছনো যেতে পারে,এই নিয়ে এক বেপরোয়া পরীক্ষা চালালেন কুরন্যান্ড। হিটলারের ভক্ত ছিলেন জানা যায়, নাহলে অমন দুঃসাহস হয়? নিজেরই হাতের শিরা ডিসেকশন করে কেটে তার মধ্যে ক্যাথিটার ঢুকিয়ে, তার পরে এক্স রে নিয়ে প্রমাণ করে দিলেন। দেখা গেল, ক্যাথিটার তাঁর বুকের ডানদিকের অলিন্দে ঢুকে রয়েছে!
এদিকে ১৯৫১ সালে, সুইডেনের ক্যারোলিন্সকায় মেডিকেল কলেজের রেডিওলজির দ্বিতীয় বর্ষের মুখচোরা ছাত্র ডা.সেলডিঙ্গারের জীবনে এল একটি “ইউরেকা” মুহুর্ত। বেশ কিছুদিন ধরেই সেলডিঙ্গার বুঝতে পারছিলেন, মোটা পলিইউরিথিনের ক্যাথিটার গুলোকে ডিসেকশন করে, ধমনী কেটে ঢোকালেও ঢুকতে চায় না, এক তো ধমনীর দেওয়াল কুঁচকে যেতে থাকে, আর পলিইউরিথিন ধমনীর গহবরে আটকে আটকে যায়, এগোতে চায় না। কাজেই ক্যাথিটারটাকে ভগীরথের মত পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটা লম্বা তার ঢুকিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তারটা ঢোকাতেই হচ্ছে যত গন্ডগোল। একটা ফুটো করলেই তো আর তার সোজা ধমনীতে চলে যাবে না!
তখনই মাথায় এল, ফুটো করার ফাঁপা সুঁচ বা পাংচার নিডলের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে তার, ধমনীর ভেতর অনেকটা। তারপর সুঁচকে তারের ওপর দিয়ে বের করে নাও। পাজামা খোলার মত। তার থেকে যাবে ভেতরে। এবার ঐ তারের ওপর দিয়ে পায়ে পাজামা গলানোর মত পরিয়ে দাও ক্যাথিটার। তারপর ভগীরথ তারকে বের করে নাও। গোটা ব্যাপারটায় ব্যথা লাগবে শুধু ধমনীর চারদিকটা অবশ করার সময় যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তাতে। তারপর আর কোন ব্যথা নেই। রক্তারক্তি কমে গেল অনেক। ব্যথা কমে গেল অনেক। হাতের কব্জির ধমনী দিয়েই হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার পাঠিয়ে দেবার মত উপায় তৈরি হয়ে গেল। খুলে গেল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়।
তিন দশক পরে একবার এই কিংবদন্তীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কি করে আবিষ্কার করলেন, ব্যাপারটা? উনি বললেন, এক সেকেন্ডের জন্য মাথায় উদয় হয়েছিল এক অতি সাধারণ বুদ্ধি!
“Now! After an unsuccessful attempt to use this technique I found myself disappointed and sad, with three objects in my hand – a needle, a wire and a catheter – and… in a split second I realized in what sequence I should use them: Needle in – wire in – needle off – catheter on wire – catheter in – catheter advance – wire off.
I have been asked how this idea turned up and I quote Phokion, the Greek. “I had a severe attack of common sense”.”
১৯৫২ সালে নিজের আবিষ্কৃত এই টেকনিককে সবার সামনে তুলে ধরলেন হেলসিঙ্কিতে আয়োজিত মেডিকেল রেডিওলজির একটি সমাবেশে। তখনও তিনি ছাত্র। তারপর একে একটা প্রামাণ্য পেপার হিসেবে জমা দিলেন ১৯৫৩ সালে। সারা বিশ্বে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দের মধ্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠল এই পদ্ধতি। শুধু চিকিৎসক নয়, প্রয়োগ করে ভালো ফল দেখার পর, রোগীদের মধ্যেও এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ল।
সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় সেলডিঙ্গার নিজের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিটি নিয়ে গবেষণাপত্র জমা দিতে চাইলে সেটি থিসিস হিসেবে স্বীকৃতই হয়নি সে সময়। পরে, ১৯৬৬ সালে, পারকিউটেনিয়াস হেপাটিক কোলাঞ্জিওগ্রাফির ওপর নিজের থিসিস সম্পূর্ণ করেন, নিজেরই আবিষ্কৃত পদ্ধতিকে প্রামাণ্য ধরে।
সেলডিঙ্গারের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে এখন এঞ্জিওগ্রাফি, এঞ্জিওপ্লাস্টি, পেসমেকার প্রতিস্থাপন, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথিটার, ডায়ালিসিস ক্যাথিটার, ত্বকে স্বল্প পরিসরে ছিদ্র করে শরীরের গভীরে গিয়ে পুঁজ,জমাট রক্ত বা অন্যান্য তরল বের করে নেওয়া, চেস্ট ড্রেন, পেরিটোনিয়াল ড্রেন, গ্যাস্ট্রোস্টমি টিউব, ট্রাকিওস্টোমি… সব কিছুই করা হয়। এতটাই সর্বজনবিদিত প্রক্রিয়া, যে ইন্টারভেনশনিস্ট দের কাছে এটা এখন চোখের পলক ফেলা বা শ্বাস নেবার মতই হয়ে গেছে।
অবাক করা ব্যাপার ১৯৫৬ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল দেওয়া হয়েছিল সেই কুরন্যান্ড, রিচার্ড আর ফর্সম্যানকে।সোজাসুজি হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার প্রবেশ করানো এবং রোগগ্রস্ত শিরা ও ধমনীর অবস্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।
কিন্তু ইন্টেন্সিভ থেরাপিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দেওয়া এই চিকিৎসককে নোবেল কমিটি মনে রাখেনি, কার্ডিওলজিস্টরাও কতটা মনে রেখেছেন জানি না।
তবে ডা. স্বেন আইভার সেলডিঙ্গার চিরকাল হয়ে থাকবেন আমাদের মত বেডসাইডের শ্রমিক ও নিশাচর ডাক্তারদের সুপারহিরো।