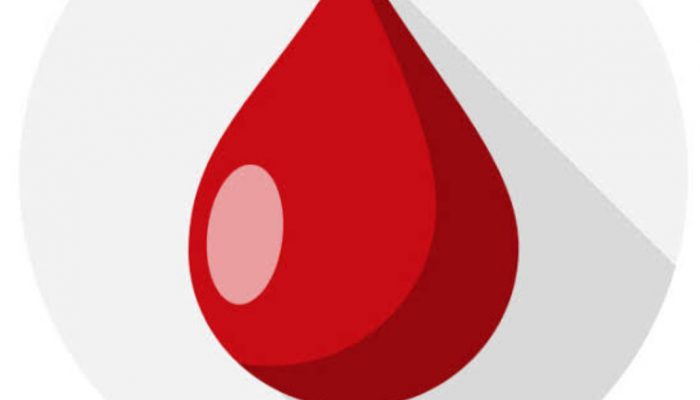রক্তদানের পর, সেটিকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং কোনো রোগের লক্ষণ আছে কি না সেটা প্রথমে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পর কোনো রোগের লক্ষণ পাওয়া না গেলে সেটিকে গ্রুপ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়।
দান করা রক্তের যে পরীক্ষাগুলো করা হয় সেগুলি হলো –
ক) ABO গ্রুপের শনাক্তকরণের পরীক্ষা –
এটি দুটো ভাগে করা হয় –
১) রক্তের RBC নিয়ে তাতে Anti A, Anti B ও Anti AB বিকারক (reagent) দিয়ে agglutination (অর্থাৎ বিক্রিয়া হয়ে আর.বি.সি.র জমাট বাঁধা) -র উপর ভিত্তি করে Antigen A ও B উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। এটিকে forward/ front type test বলা হয়।
২) রক্তরস (plasma/serum) নিয়ে তাতে আগে থেকে জানা A, B এবং O গ্রুপের RBC দিয়ে অ্যাগ্লুটিনেশনের উপর ভিত্তি করে Antibody A ও B এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি নমুনার জন্য ৩ টি পৃথক প্যানেল বা পুল (pool) cell ব্যবহার করা হয়। এটিকে reverse / back type test বলা হয়।
উপরের পরীক্ষাগুলি আবার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হয় –
1) Conventional Tube Testing (CTT),
2) Column Agglutination Technology/ Gel Card Method,
3) Solid phase test systems/ microplate test.
এবারে –
Blood Group A হলে – RBC তে Antigen A থাকে, রক্তরসে Anti B Antibody থাকে।
Blood Group B হলে – RBC তে Antigen B থাকে, রক্তরসে Anti A Antibody থাকে।
Blood Group AB হলে – RBC তে Antigen A ও B দুটোই থাকে, রক্তরসে Anti A বা Anti B, কোনো অ্যান্টিবডিইথাকে না।
Blood Group O হলে – RBC তে Antigen A বা Antigen B কোনোটাই থাকে না, রক্তরসে Anti A ও Anti B – এই দুটো অ্যান্টিবডিই থাকে।
খ) Rh (D) আছে কি নেই তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য পরীক্ষা –
রক্তের নমুনায় RBC তে Rh-D Antigen আছে কিনা তা দেখার জন্য দুটো আলাদা উৎস থেকে Anti-D বিকারক ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি বিকারক Immunoglobulin M (IgM) নামক অ্যান্টিবডি ও অপরটি Immunoglobulin M ও Immunoglobulin G (IgG) নামক দুটি অ্যান্টিবডির মিশ্রণ হলেই ভালো। একটিতেও বিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে সেটিকে Rh (D) Positive হিসেবে ধরা হয়। দুটির কোনটিতেই বিক্রিয়া না হলে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নমুনার RBC এর সাথে IgG থাকা একটি বিকারক মিশিয়ে Centrifugation করে বিক্রিয়া হয়েছে কি না দেখা হয়। এটি পদ্ধতিটিকে Indirect anti-globulin testing (IAT) method বলা হয়। এরপরে বিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে সেটিকে Rh (D) Positive -Weak (D) রক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, আর বিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া না গেলে সেটিকে Rh (D) Negative হিসেবে গণ্য করা হয়।
এছাড়াও Partial D নামক একটি প্রকারভেদ আছে।
এই পরীক্ষাগুলি আগের মতোই Tube Testing, Column Agglutination Technology, microplate test পদ্ধতিতে করা হয়।
গ) রক্তরস (Plasma/Serum) এ কোনো অপ্রত্যাশিত অ্যান্টিবডি (Unexpected Antibodies) আছে কি না তা শনাক্তকরণের পরীক্ষা – রক্তরসের সাথে Anti-Human Globulin phase – এ Pooled O Rh (D) positive RBC দিয়ে অথবা 3 Cell panel ব্যবহার করে IAT পদ্ধতিতে Unexpected antibodies নির্ণয় করা হয়।
রক্তরসের নমুনায় ঐরূপ অ্যান্টিবডি পাওয়া গেলে মূল রক্তের শুধুমাত্র RBC গুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। এরপরে RBC গুলির Direct Antiglobulin Test (DAT) করে দেখতে হবে। বিক্রিয়া না হলে তবেই সেটি সঞ্চালনের (Transfusion) কাজে ব্যবহার করা যাবে।
? Phenotyping Test কী?
ইতোমধ্যেই ABO গ্রুপএবং RhD গ্রুপের ব্যাপারে জানা গেছে যে গ্রুপগুলো রক্তে থাকা বিভিন্ন অ্যান্টিজেন (এবংঅ্যান্টিবডির) উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তিতে তৈরী। একইভাবে রক্তের থাকা সাড়ে তিনশতর বেশি অ্যান্টিজেনের উপর ভিত্তি করে মোট ঊনচল্লিশটি Blood Group System (একটি গ্রুপ সিস্টেমের অস্তিত্ব শর্তসাপেক্ষ) বানানো হয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলিতে দেহে Clinically Significant Antibody তৈরী হয়, রক্ত সঞ্চালনের সময়ে সেই ব্লাডগ্রুপের পদ্ধতির গ্রুপের মিল-অমিলের ব্যাপারে খেয়াল রাখা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইসব অ্যান্টিজেন দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত বা বেশী পরিমাণে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে যার ফলে এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরী হলে hemolytic reactions তাড়াতাড়ি বা বেশী পরিমাণে হয় যেটা অন্য অ্যান্টিজেনের থেকে শরীরের অধিক ক্ষতি করতে পারে।
এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ABO system এবং Rh system এর D অ্যান্টিজেন, সঞ্চালনের সময় এগুলোর অমিল হলে Acute hemolytic reactions হয়। এরপরেআসে Rh system এর Rh-c, Rh-C, Rh-e, Rh-E, (চারটি), Kell এর K (একটি), Duffy এর Fya, Fyb (দুইটি) , Kidd এর Jka and Jkb (দুইটি), MNS এর S, s (দুইটি) অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট এগারোটি অ্যান্টিজেন। এই পরের গুলি প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এক বা দুইবার রক্ত সঞ্চালনের সময় তেমন দেখা যায় না, তাই সাধারণত রক্ত পরীক্ষার সময়ে ABO এবং RH-D অ্যান্টিজেনেরউপস্থিতির/অনুপস্থিতির পরীক্ষা করে রক্ত সঞ্চালন করা হয় (কারণ এই ক্ষেত্রে এদের অমিল হলে অ্যান্টিজেন – অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়ার প্রভাবে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে)। কিন্তু কোনো মানুষের বারবার রক্তের প্রয়োজন হলে আগের অ্যান্টিজেনগুলির উপস্থিতি/অনুপস্থিতি জানার সাথে সাথেই পরের অ্যান্টিজেনগুলির উপস্থিতি/অনুপস্থিতি জেনে নিয়ে তবে রক্ত সঞ্চালন করা উচিৎ।
বিশেষত যে সকল রোগে আগে থেকেই যদি জানা যায় যে পরবর্তীকালে রোগীর বারংবার রক্তের প্রয়োজন (যেমন – থ্যালাসেমিয়া, ব্লাডক্যান্সার, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ডায়ালিসিস ইত্যাদি), সেই ক্ষেত্রে প্রথমবার রক্তসঞ্চালনের আগেই এই Phenotyping Test এর মাধ্যমে রোগীর রক্তের Extended Phenotype জেনে নেওয়াই ভালো। কারণ কোন রক্তদাতার রক্ত শরীরে ঢোকার পরে রোগীর শরীরে তার নিজের ও রক্তদাতার – দুই রকমের অ্যান্টিবডিগুলোই উপস্থিত থাকবে, যেখানে কোনটা কার সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে আবার Rh system এর Rh-c, Rh-C, Rh-e, Rh-E, (চারটি), Kell এর K (একটি)- এ পাঁচটি অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বিচার করে রক্ত সঞ্চালন করলেই নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে রক্তসঞ্চালন জনিত প্রতিক্রিয়া আটকানো যায় তাই Phenotyping এর জন্য এগুলি আবশ্যক।
যাদের বারবার রক্তের প্রয়োজন হয় তাদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা না করে রক্তসঞ্চালন করলে তার শরীরে নানারকম অ্যালোঅ্যান্টিজেন আসবে। যার প্রতিক্রিয়ায় দেহে অ্যালো অ্যান্টিবডি তৈরী করবে।কাজেই পরবর্তীকালে রক্ত নিলে অ্যান্টিজেন – অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়ার জন্য সেই গৃহীত রক্তের লোহিতকণিকা ভেঙে রক্তের আয়ু কমতে থাকবে। ফলে শরীরের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে পরপর রক্ত নেওয়ার সময়ের ব্যবধান কমতে থাকবে এবং চিকিৎসার খরচ বাড়তে থাকবে। এবং একটা সময়ে এমন অবস্থা হতেই পারে যেখানে যেকোনো রক্ত দিলেই এই Alloimmunization-এর ফলে তার লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যাবে।
ঘ) রক্তের মাধ্যমে যেসব রোগ সংক্রামিত হতে পারে তার কোনো রোগ দান করা রক্তের মধ্যে আছে কিনা তা পরীক্ষা করা (Screeing Test for Transfusion Transmitted infection) ।
Transfusion Transmissible Infections (TTI) পরীক্ষার বোঝার আগে সহজভাবে তার মূলনীতিটি বুঝে নিই চলুন। আবার সেই একই রকম গল্পে আসছি।
ধরুন, আপনি একটি বিশাল বাড়িতে থাকেন আর তাতে একদল চোর হানা দিলো। এবার তাঁরা এসে দেখলো যে তাদের সংখ্যা কম। তখন তারা কিছু সময় ধরে নিজেদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকলো। এরপরে তারা আরো কিছু সময় ধরে তাঁরা যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে শুরু করলো। এবার যদি আপনার রক্ষী বাহিনী তাদের খুঁজে পেলো, তখন যুদ্ধ হয়ে দুই দলের থেকেই লোকজন মারা গেলো। আর যদি তারা আপনার রক্ষীবাহিনীদের মতই রূপ নিয়ে ফেলে, তখন তাদের খুঁজে না পেলে তারা তাদের সংখ্যা উপযুক্ত ভাবে বাড়ানোর পরে আপনার ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে বা গর্ত খুঁড়ে আপনার ঘরে ঢুকল। আর এই খোঁড়ার ফলে মাটি বা দেওয়ালের অংশ কিন্তু ঘরের মধ্যেই পাওয়া যেতে শুরু করল। আর আরো কিছু সময় ধরে এইভাবে চুরি চলার পরে সবশেষে আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনার সম্পত্তি কমছে।
অতএব এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে গেলে চোর ধরতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এটি এইভাবে হতে পারে –
১) সবচেয়ে ভালো হয়, যখন প্রথমে চোরের দল এসেছিলো তখন চোরকেই শনাক্ত করে চুরি হওয়ার আগেই আটকানো।
২) তারপরে, চোরেরা যখন যন্ত্রপাতি জড়ো করছিলো তখন সেই যন্ত্রপাতি দেখে চুরির ব্যাপারে বুঝলেও চলে যায়।
কারণ, এই পর্যন্ত আপনার তেমন ক্ষতি কিন্তু হয় নি।
৩) এরপরে উপায় হলো, চোরদের অথবা আপনার রক্ষীদলের মৃতদেহ দেখে চুরির ব্যাপারে বোঝা। আর মৃতদেহ দেখতে না পেলে আপনার ঘরের পড়ে থাকা অংশ দেখে চুরির ব্যাপারে বোঝা।
৪) আর সবচেয়ে শেষ উপায় হলো, আপনার সম্পত্তি কমে যাচ্ছে দেখে চুরির ব্যাপারে বোঝা। এই ক্ষেত্রে আপনার ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।
একই ভাবে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দেহে আক্রমণ করলে তার DNA বা RNA প্রথমে দেহে পাওয়া যায়, তার পরে সে দেহে নিজের সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং নিজের কাজের জন্য প্রোটিন তৈরী করতে থাকে (Antigen) এবং এরপরে দেহ তার বিরুদ্ধে প্রোটিন (Antibody) তৈরী করতে থাকে। শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে লড়াই হলে এই পরজীবীগুলির সাথে শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকার মৃত্যু ঘটে। আর তার সাথেই সাথেই আস্তে আস্তে রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়।
এছাড়া যে রক্ষীবাহিনী যত কম সংখ্যক চোরদের উপস্থিতিতে দেখেই চুরির ব্যাপারে বুঝতে পারে, সেই রক্ষীবাহিনী তত ভালো।
Window Period – সংক্রমণ হওয়া এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ার মধ্যবর্তী সময়কে সেই রোগের সেই পরীক্ষার উইন্ডো পিরিয়ড বলে। অর্থাৎ এই উইন্ডো পিরিয়ডে থাকার সময়ে ঐ পরীক্ষাটি করলেও ঐ রোগটি ধরা যায় না, ঐ সময়সীমা পার করার পরেই রোগটি ধরা যায়।
কাজেই এই সময়সীমা যত কম হবে, সেই পরীক্ষাপদ্ধতিটি তত ভালো।
Sensitivity – কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করা হলে সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়া নমুনার মধ্যে ইতিবাচক অনুপাতের পরিমাণ হলো তার সেন্সিটিভিটি। অর্থাৎ, ধরা যাক ১০০০০ জন মানুষের মধ্যে ৮০০০ জনের বাস্তবে একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ হয়েছে। এবার ঐ ৮০০০ জনের উপর একটি পরীক্ষায় দেখা গেলো ৭৯৯২ জনের ক্ষেত্রে ঐ রোগটি ধরা পড়ছে। অতএব ঐ পরীক্ষার সেন্সিটিভিটি = ৭৯৯২/৮০০০ =০.৯৯৯ বা ৯৯.৯%।
কাজেই কোনো পরীক্ষার সেন্সিটিভিটি যত বেশী হবে, সেই পরীক্ষাপদ্ধতিটি তত ভালো।
Specificity – কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করা হলে রোগের অনুপস্থিতি সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়া নমুনার মধ্যে ইতিবাচক অনুপাতের পরিমাণ হলো তার স্পেসিফিসিটি। অর্থাৎ, ধরা যাক ১০০০০ জন মানুষের মধ্যে ১০০০ জনের বাস্তবে একটি ভাইরাসঘটিত রোগ হয়েছে এবং ৯০০০ জনের ঐ রোগটি হয়নি। এবার ঐ ৯০০০ জনের উপর একটি পরীক্ষায় দেখা গেলো ৮৯৯১ জনের ক্ষেত্রে ঐ রোগের অনুপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ঐ পরীক্ষার স্পেসিফিসিটি = ৮৯৯১/৯০০০ =০.৯৯৯বা৯৯.৯%।
কাজেই কোনো পরীক্ষার স্পেসিফিসিটি যত বেশী হবে, সেই পরীক্ষা পদ্ধতিটি তত ভালো।
TTI পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পরীক্ষা আবিষ্কার করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে আমরা আরো দ্রুত এবং আরো নিশ্চিতভাবে রোগ ধরতে শুরু করেছি। কিছু পদ্ধতিতে অণুজীবের নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতির প্রমাণ খোঁজা হয়, কিছু পদ্ধতিতে অনুজীবের দ্বারা তৈরী করা অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির প্রমাণ খোঁজা হয়, কিছু পদ্ধতিতে অ্যান্টিজেনের জন্য দেহে যে অ্যান্টিবডি তৈরী হয় তার প্রমাণ খোঁজা হয় ইত্যাদি।
যেসব রোগ বা তার ভাইরাস / ব্যাকটেরিয়া আছে কি নেই তা দেখতে যেসব পরীক্ষাগুলো ভারতবর্ষে করা হয় সেগুলো হলো –
১) এইচ আই ভি (র্যাপিড/ ই এল আই এস এ/ কেমিলুমিনেসেন্স পদ্ধতিতে) ,
২) হেপাটাইটিস বি (র্যাপিড / ই এল আই এস এ / কেমিলুমিনেসেন্স পদ্ধতিতে),
৩) হেপাটাইটিস সি (র্যাপিড / ই এল আই এস এ / কেমিলুমিনেসেন্স পদ্ধতিতে),
৪) সিফিলিস (ভি ডি আর এল / আর পি আর / টি পি এইচ এ / কেমিলুমিনেসেন্স প্রক্রিয়ায়) এবং
৫) ম্যালেরিয়া (অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে)।
এছাড়া Nucleic AcidTest (NAT) নামক পরীক্ষা আছে যেটি সবচেয়ে আধুনিক এবং ভালো পরীক্ষা। এক্ষেত্রে নমুনার নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) নিয়ে, যন্ত্রের মাধ্যমে সেই নিউক্লিয় অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং তারপরে সেটায় নির্দিষ্ট কোনো অণুজীবের নিউক্লিয় অ্যাসিড উপস্থিত আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা হয়।
এই পরীক্ষাগুলি Screening Test অর্থাৎ এই পরীক্ষাগুলোয় কোনো নমুনায় কোনো রোগের লক্ষণ পাওয়া গেলে সেই নমুনাটিকে নিয়ম মেনে নষ্ট করা হয়। কিন্তু সেই নমুনাটি যে মানুষের দেহ থেকে এসেছে তাকে নিশ্চিতভাবে রোগী হিসেবে ধরা হয় না। বরং তার সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ করে Confirmatory Test করে সত্যিই তার মধ্যে সেই রোগটি আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। ফলে এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্পেশিফিসিটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই পরীক্ষার সেন্সিটিভিটি। এমন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ দরকার যার সেন্সিটিভিটি অত্যন্ত উচ্চমানের।
বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির গড় (Median) উইন্ডো পিরিয়ড
| ভাইরাসের নাম | উইন্ডো পিরিয়ড | |||
| র্যাপিড | ই এল আই এস এ (চতুর্থ প্রজন্ম) | কেমিলুমিনেসেন্স | ন্যাট | |
| এইচ আই ভি | ৯০ দিন | ১৬ থেকে ২৮ দিন | ১১ থেকে ১৫ দিন | ৫ থেকে ৭ দিন |
| হেপাটাইটিস বি (HBV) | ৬০ থেকে ৯০ দিন | ২৪ থেকে ২৮ দিন | ২০ থেকে ২৫ দিন | ১০ থেকে ১৫ দিন |
| হেপাটাইটিস সি (HCV) | ৬০ থেকে ৯০ দিন | ৩০ থেকে ৪০ দিন | ১০ থেকে ১৮ দিন | ৫ থেকে ৭ দিন |
এইসব পরীক্ষার সেন্সিটিভিটি ও স্পেসিফিসিটি খুবই উচ্চমানের হয়ে থাকে। আর যে পরীক্ষার সেন্সিটিভিটি যত বেশী এবং উইন্ডো পিরিয়ড যত কম, সেই পরীক্ষাব্যবস্থা তত ভালো। কিন্তু একবারে ১০০.০০% সেন্সিটিভিটির এবং ১ সেকেন্ড উইন্ডো পিরিয়ডে থাকা পরীক্ষাব্যবস্থা এখনও পাওয়া যায় নি। তাই প্রতিবার রক্ত সঞ্চালনের সাথে লক্ষভাগের একভাগ হলেও একটা ঝুঁকি থেকেই যায়।
এই রচনায় ডা ঋতম চক্রবর্তীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
(চলবে)