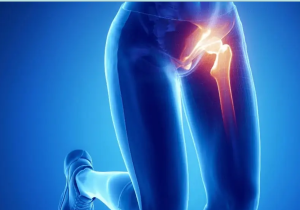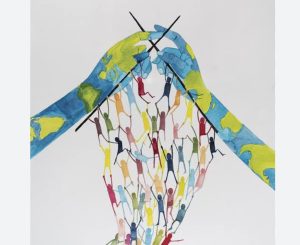চিকিৎসাব্যবস্থার ভালোমন্দ নিয়ে স্বপ্নময়বাবু এই প্রথম ভাবতে বসলেন, এমনও নয়। এর আগে তাঁর একখানা চমৎকার বই রয়েছে – ‘চার ডাক্তার’ – চারখানা নাতিদীর্ঘ আখ্যান জুড়ে সেই বই। আখ্যানগুলো আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত হলেও দুই মলাটের মধ্যে বইটিকে একখানা উপন্যাস হিসেবেও পড়া যেতে পারে। এবং পড়া জরুরিও। তিনটি আখ্যানের কেন্দ্রে তিনজন মানুষ। প্রথমজন হাতুড়ে। দ্বিতীয় আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক হোমিওপ্যাথ। যিনি কিনা নিজের বিষয় – হোমিওপ্যাথি – তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে যারপরনাই সন্দিহান – তবু রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা ও যত্নের কারণে যিনি স্থানীয় মানুষের কাছে ভগবান। প্রথম গল্পের হাতুড়েও কম কিছু সম্মান পান না স্থানীয় মানুষের কাছে। ডাক্তারির কতটুকু অংশ যে ওষুধ আর কতটুকু জুড়ে সহমর্মিতা নির্ভরযোগ্যতা, তার অঙ্ক কে-ই বা কষে উঠতে পারে! তৃতীয় আখ্যানের উপজীব্য আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা মডার্ন মেডিসিনের ডাক্তার, লেখক যাঁকে অ্যালোপ্যাথ বলেছেন। সেখানে ব্যস্ত ডাক্তারবাবু ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় মাসচটক, শহরে যাঁর রমরমা প্র্যাক্টিস, শহরের উপকণ্ঠে বনেদি পারিবারিক ভিটেয় এসে তিনিও মুখোমুখি হন চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা বিষয়ক জরুরি কিছু প্রশ্নের। যে দায় বা দায়িত্বর কথা, সম্ভবত, ভুলেই ছিলেন তিনি। বয়সে অনেক ছোট সরকারি হেলথ সেন্টারের ডাক্তার ডা ইন্দ্রাণী রায়, তাঁকে দেখেই ডা মাসচটকের চিকিৎসকের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ, ‘গণমিত্র’ বইতে নতুন প্রজন্ম, জীবক, চিকিৎসকের দায়বদ্ধতার পরিবর্তে যেনতেনপ্রকারেণ অর্থোপার্জনে প্রয়াসী – কিন্তু ‘চার ডাক্তার’ বইয়ের ইন্দ্রাণী, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি, তিনি গল্পে পুরোনো প্রজন্মের প্রতিনিধির তুলনায় দায়বদ্ধ চিকিৎসক। সেই বইয়ের চতুর্থ তথা শেষ আখ্যানের নাম – ডাক্তার, বিশেষণহীন। কলকাতার অনতিদূরে এক গ্রাম্য এলাকায় জনৈক গৃহবধূকে সাপে কাটে। বধূ তখন গর্ভবতীও বটেন। শুরুতে মসজিদে ইমামের দোয়া পড়া, তারপর স্থানীয় হাসপাতাল – সেখান থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজ। আখ্যানের পরতে পরতে মিশে আছে সমকালীন বাস্তবতা। রাজনৈতিক দাদাদের নাম করে চোখরাঙানি। হাসপাতালে পরিজন হিসেবে এসে পাড়ার মাতব্বরদের তড়পানি। ধর্মীয় সংস্কার। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতা। যাবতীয় তড়পানি-হুমকি অগ্রাহ্য করে প্রায় নির্বিকল্প দশা প্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসকদের নিরলস প্রয়াস। হিপোক্রেটিক ওথ-এর প্রসঙ্গ।
কিন্তু শেষ আখ্যান প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, মেডিকেলে ভর্তি আজকাল কেন্দ্রীয় স্তরের পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। বাংলা মিডিয়াম, শুনতে পাই, সেখানে দুয়োরাণী। সরকারি স্কুলগুলোর অবস্থা তো ক্রমশ নিম্নগামী। এমতাবস্থায়, আকাশ-বাতাস মুখরিত কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে, যেখানে পড়ার খরচ হাজারের অঙ্কে নয়, লাখে। সেক্ষেত্রে ডাক্তারি পড়তে আসছে যারা, তাদের আর্থসামাজিক বিন্যাসে কি বদল ঘটে যাবে না? পাস করার পর তাঁরা যা হবেন, ‘গণমিত্র’-র দেবকিঙ্করদের থেকে দূরত্ব তো কিয়দংশে অনিবার্য। হ্যাঁ, অবশ্যই, এর মধ্যেও এক-আধজন শ্রীমন্ত রয়ে যাবে – দুস্থ চপলার মেধাবী পুত্র শ্রীমন্ত – শ্রীমন্ত হতে গেলে দুঃস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা বাদে উপায় নেই, এমনও নয় – কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় শ্রীমন্তদের যাত্রা কি ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠবে না?
আবারও এথিক্সের প্রসঙ্গে আসি। চিকিৎসা পেশার dignity যাতে রক্ষিত হয়, এথিক্সের নির্দেশিকা মানলে এমন আচরণই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই dignity ব্যাপারটা কী? কয়েকখানা অভিধান খুলে দেখতে চাইলাম। একটিতে বলা হয়েছে, the quality of a person that makes him or her deserving of respect আরেকটিতে the quality or state of being worthy, honored, or esteemed অক্সফোর্ডের অভিধানে, the fact of being given honor and respect by people. এককথায়, ব্যাপারটা মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত। যে সমাজব্যবস্থায় আর্থিক সাফল্য ও বহিরঙ্গের ঠাটবাটই মানুষের মনে সমীহ জাগায়, এমনকি নির্বিকল্প সম্মানও জুটিয়ে দেয়, সেখানে dignity শব্দটার দ্যোতনা কি বদলে যায় না? কাজেই, আরও ধনী হওয়া, আরও বড় গাড়ি করে আরও বড় হাসপাতালে ডাক্তারি করতে যাওয়া – এককথায় পাব্লিকের লব্জে ‘বড় ডাক্তার’ হয়ে ওঠা – সেটাই কি চিকিৎসকের dignity-র নতুন সংজ্ঞা নয়? তাহলে সেই dignity অর্জনের রাস্তাটাও কি বদলে যাবে না?
‘দ্য গুড ডক্টর’ বইয়ে লেখকের বাবা, অর্থাৎ পুরোনো-পন্থী চিকিৎসক – গণমিত্র-র দেবকিঙ্কর থেকে যিনি মানুষ হিসেবে খুব দূরে নন – তিনি হতাশ হয়ে বলেন, এই সময়ে যারা ডাক্তার হয়ে উঠছে, তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যারা প্রায় রোবটের মতো। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু প্রটোকল নির্ভর চিকিৎসার বাইরে ভাবতে পারে না। দুই, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বড়লোক হওয়া, আরও বেশি বড়লোক হয়ে ওঠা। আর তিন, যাদের ডাক্তার না বলে ঠগবাজ জোচ্চর বলা উচিত। এরা টাকার জন্য সবই করতে পারে।
এই কথার মধ্যে নিঃসন্দেহে অতিকথন রয়েছে – ‘আমাদের সময় সবই ভালো ছিল’ গোত্রের অতিকথন – কিন্তু কিছু সত্যও তো রয়েছে। পড়তে পড়তেই মনে হচ্ছিল, পুরোনো দিনের ডাক্তারবাবুর করা শ্রেণীবিভাগে, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে সীমারেখাটি ঝাপসা। আর খুব তিক্ত সত্যিটা হলো, পুরো ব্যবস্থাটাই টিকে থাকতে পারে ওই প্রথম দলভুক্তদের জন্য, যাঁরা বুদ্ধিমান ও মেধাবী – একেবারেই অসৎ নন, যথেষ্ট সহমর্মী ও নিষ্ঠাবান – কিন্তু নির্বিবাদে প্রটোকল মেনে চলার মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখেন।
গণমিত্র-র জীবক ওই দ্বিতীয় আর তৃতীয় দলের কোনও একটিতে, বা দুইয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। আমাদের চারপাশে এক আশ্চর্য চিকিৎসাব্যবস্থা, যা যতখানি টিকে আছে রোগীদের হাইটেক চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার কারণে – তার চাইতেও বেশি, সুস্থ মানুষকেও রোগের ভয় দেখিয়ে সম্ভাব্য রোগীতে পরিণত করতে পারার সুবাদে, অন্তত তাঁদের হাসপাতাল-মুখী করতে পারার সাফল্যের সুবাদে। যে কাজটিকে জীবকের গুরু – অভিযান, কর্পোরেট হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টের হর্তাকর্তা – বলেন, ‘পেশেন্ট জেনারেট’ করা। হ্যাঁ, ‘পেশেন্ট ট্রিট’ করা বা সারিয়ে তোলা নয়, ‘পেশেন্ট জেনারেট’ করা বা পেশেন্ট তৈরি করা। এই শব্দবন্ধ স্বপ্নময়বাবুর কষ্টকল্পনা নয়, এটি কর্পোরেট হাসপাতালের বহুপ্রচলিত লব্জ। এমনধারা বিভিন্ন ‘শিক্ষক’-এর উজ্জ্বল উদাহরণ দেখতে দেখতে জীবকও দক্ষ হয়ে ওঠে, অনৈতিক আর বেআইনি, এই দুইয়ের মধ্যেকার সূক্ষ্ম সীমারেখা ধরে দিব্যি এগোতে থাকে। ঘটনাচক্রে জীবক যেদিন মার খায়, সেদিন তার তেমন দোষ ছিল না – মূল দায় যাঁর, তিনি গর্ভপাত করিয়ে চটজলদি দিল্লি চলে গিয়েছেন, ওষুধকোম্পানির আপ্যায়ন গ্রহণ করতে। ঠিক যেমন অসাধু সার্জেন প্রতাপও মার খেয়ে যান যেদিন, সেদিন তাঁরও বিশেষ দোষ ছিল না।
তো কথাটা হলো, প্রতাপ কিংবা জীবক মার খান, কিন্তু এমন অনেক প্রতাপ অনেক জীবক দিব্যি করেকম্মে খান কোনওরকম সমস্যায় না পড়েই। কালক্রমে তাঁদের ‘সাফল্য’ দেখে আরও অনেক নব্য চিকিৎসক সেই পথে এগোতে ‘অনুপ্রাণিত’-ও হন। ভাঙচুর হোক বা না হোক, কেয়ার নার্সিং হোম-রা বহাল তবিয়তে টিকে থাকে। দ্য পারফেক্ট মেডিক্যাল হল-এ ডাক্তারদের চেম্বারও। এদের পাশে গজিয়ে উঠতে থাকে ঝাঁ-চকচকে ম্যাডোনা হসপিটাল, মাইলস্টোন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। সেখানে অভিযানের মতো দক্ষ ম্যানেজাররা থাকেন, যাঁরা ‘পেশেন্ট জেনারেট’ করার কাজে বাকিদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যাঁরা অনেক জীবককে ‘তৈরি’ করে ফেলেন। আর ডা সুকৃতি বর্ধনের মতো ‘বড় ডাক্তার’-রা তো থাকেনই। ক্ষোভ আর নিষ্ফলা আক্রোশ আছড়ে পড়ে পাব্লিকের মার জীবকরা খায়, জীবকের সিনিয়র হিসেবে অভিযানের চাকরি যায় – মালিকের গায়ে আঁচটুকু পড়ে না। সিস্টেম চলতে থাকে নিজের ছন্দে। এই বিপুল শক্তিশালী সিস্টেমের বিপ্রতীপে চপলা-শ্রীমন্তর – দেবকিঙ্করেরও – বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, তার ক্ষমতা কতটুকুই বা!
পড়তে পড়তেই মনে হচ্ছিল…
“হাততালির শব্দ শুনতে পাচ্ছি হাওয়ায় হাওয়ায় মুচিঘরের ছেলে সনাতন হাততালি দিচ্ছে, ক্যাওটা ঘরের, ঘরামি ঘরের, ডোম ঘরের ডাক্তার হয়ে ওঠা এই প্রজন্ম, দমিয়ে রাখা, দাবিয়ে রাখা ঘরগুলোর উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা ইঁটের পাঁজা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা হিলহিলে পাতাদের মতো…”
কথাটা পড়তে শুনতে বিশ্বাস করতে ভালো লাগলেও প্রশ্ন রয়ে যায়, বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রর মতো ব্যক্তিগত উদ্যোগ – খুবই প্রশংসনীয় ও আশাপ্রদ উদ্যোগ হলেও – তা দিয়ে কি সিস্টেম বদলাবে? শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তরা, কেন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় থাকবে না? দেবকিঙ্করদের মতো মানুষরা কি পারতেন না মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হয়ে আরও অনেক দেবকিঙ্কর তৈরি করার কাজে ব্রতী হতে? একদিকে যখন ম্যাডোনা বা মাইলস্টোন, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রর পক্ষে কি সামান্য প্রতিরোধটুকুও গড়ে তোলা সম্ভব?
আর তার চাইতেও বড় প্রশ্ন, যে সমাজব্যবস্থায় দেবকিঙ্করের মতো প্রকৃত-অর্থে চিকিৎসককে দেখে তাঁর সন্তান জীবক গর্ববোধ করার পাশাপাশি বিরক্তও হয় – যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় বৃহত্তর ডাক্তারসমাজে দেবকিঙ্কর পুরোনো হিসেবে বাতিল হয়ে যান – সেই ব্যবস্থাটায় মূলগত পরিবর্তন না এলে আলাদা করে চিকিৎসাব্যবস্থা বদলাবে কী করে?
জীবক-প্রতাপরা মার খাবেন, একদিন হয়ত শ্রীমন্তও মার খাবে। কেয়ার বা মাইলস্টোনে ভাঙচুর হচ্ছে, হতেও থাকবে – কিন্তু সেখান থেকে বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে ভাঙচুর হয়ে যাওয়াটাও কি খুবই অসম্ভব? জীবক-প্রতাপদের ছাড়িয়ে বেশিদূর ভাবতে চাইলে আমরা হয়ত অভিযান বা ওইরকম কোনও ম্যানেজমেন্টের মুখ অবধি দেখতে পাই। কিন্তু তার পরে যে গাঢ় অন্ধকার, যে অন্ধকারে বসে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালকরা পানাহার করেন, তার চেহারা না চিনলে তো…
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গণমিত্র বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার পচা-গলা চেহারাটা স্পষ্ট করেছেন। অতীতের প্রেক্ষিতে বর্তমান ব্যবস্থাকে রেখে আমাদের ভাবাতে চেয়েছেন। তারপরও বলি, এটুকু মেনে নেওয়া জরুরি – দেবকিঙ্কররা অতীত, দেবকিঙ্করদের মতো করে চিকিৎসাও অতীত। ভেবে দেখুন, মূলত ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টের উপর ভরসা করে থাকা দেবকিঙ্কর নিজের স্ত্রী অতি গুরুতর অসুস্থ হওয়া অবধি সেই অসুস্থতার আঁচ পাননি, যদিও অসুখটা ক্রনিক ধরনের। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা ঘটলে আপনি কী করতেন? তবে দেবকিঙ্করদের ধাঁচে চিকিৎসা অতীত হলেও তাঁদের মূল্যবোধকে কি বাতিল ভাবব? চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি কি কেবলমাত্র মূল্যবোধের বিনিময়েই ঘটতে পারবে? আধুনিক চিকিৎসা বলতে কি অনিবার্যভাবে জীবক-প্রতাপ-অভিযান বা সুকৃতি বর্ধনদের প্রতিপত্তি?
উত্তরটা যদি ‘না’ হয়, তাহলে বিকল্প কী?
দেবকিঙ্করদের যদি অতীত ভাবি, তাহলে বর্তমানে – এমনকি ভবিষ্যতে – গণমিত্র হয়ে ওঠার রাস্তাটাই বা কী?
স্বপ্নময়বাবু ভাবিয়েছেন। স্পষ্ট উত্তর দেননি। স্বাভাবিক। এই বহুমাত্রিক সমস্যা থেকে চটজলদি উত্তরণের কোনও স্পষ্ট দিশা দেখিয়ে দেওয়াটা কঠিন – কঠিন নয়, অসম্ভব। তাছাড়া সহায়িকা প্রকাশ করার জন্য অন্য প্রকাশনী রয়েছে। সে কাজ বা দায় ঔপন্যাসিকের নয়।
(শেষ)