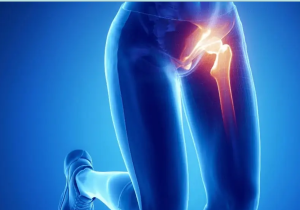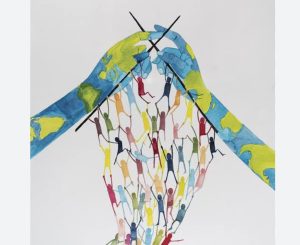১৯৭১ সালে দাঁড়িয়ে লিনাস পলিং দাবী করলেন, স্রেফ ভিটামিন সি বেশী বেশী করে খেলেই বিশ্বের ক্যানসারের সংখ্যা দশ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব। আর ১৯৭৭ সালে বলে বসলেন, হ্যাঁ, ভিটামিন সি মেগাডোজ দিয়ে ক্যানসারের সংখ্যা পঁচাত্তর শতাংশ কমিয়ে ফেলা তো সম্ভব বটেই, এমনকি যাঁদের ক্যানসার বেশ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে, তাঁদেরও সারিয়ে তোলা সম্ভব। আর এতো শুধু ভিটামিন সি- আরো বিভিন্নরকমের নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট দিয়ে ক্যানসার আরো কমিয়ে আনা সম্ভব, বিভিন্ন রোগব্যাধি ভ্যানিশ করে দেওয়া সম্ভব। স্রেফ এই পথেই মানুষের আয়ু বেড়ে যাবে চড়চড় করে – গড় মার্কিনী বেঁচে থাকতে পারেন একশ দশ কি একশ কুড়ি বছর, আরামসে – আর সবকিছু ঠিকঠাক চললে সেদেশে মানুষের গড় আয়ু ভবিষ্যতে দেড়শ বছর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।
না, আপনার শুনতে তাজ্জব লাগলেও, জিনিয়াস বিজ্ঞানীর এমন ভবিষ্যৎ-বাণীর পেছনে কোনো তথ্যপ্রমাণ ছিল না। ক্যানসার-হ্রাসের অঙ্কটা দশ শতাংশ থেকে পঁচাত্তর শতাংশে ফাঁপিয়ে তোলা বা গড় আয়ুর বৃদ্ধি – কোনো সংখ্যার পেছনেই কোনো রকম গবেষণালব্ধ প্রমাণ ছিল না – ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭, এর মধ্যে নতুন গবেষণা থেকে সপক্ষে নতুন কিছু প্রমাণ মেলেনি, বরং, বিপরীতে তথ্যপ্রমাণ ছিল প্রচুর, পলিং মানতে চাননি কিছুই – বিপরীত যুক্তি ও প্রমাণকে অস্বীকার করে নিজের মতবাদের উপর উত্তরোত্তর নিজের বিশ্বাস বেড়ে চলাকে আর যা-ই হোক, বিজ্ঞান বলা চলে না।
কিন্তু, বিজ্ঞান থাকুক আর না-ই থাকুক, পলিং-এর কথার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল ঈর্ষণীয়- বক্তা হিসেবে পলিং ছিলেন অসামান্য, আশ্চর্য ক্যারিশমা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। আর দুর্ভাগ্য এটাই, পলিং-এর উপর আমজনতার এই অগাধ আস্থার পিছনে ছিল বিজ্ঞানের উপর মানুষের ভক্তি- অর্থাৎ, এত বড় বিজ্ঞানী যখন একথা বলছেন, সে কি মিথ্যে হতে পারে!! যদিও বিজ্ঞান শেখায় সত্যকে যাচাই করে চিনে নিতে, আমরা অত খতিয়ে ভাবি না – স্রেফ বিজ্ঞানীর মুখের কথাকেই বেদবাক্য বলে মেনে নিই – বিজ্ঞানের যে মূল স্পিরিট, সেই প্রশ্ন করার অভ্যেসকেই ভুলে গিয়ে অন্ধ বিশ্বাসকেই পাথেয় করি – আর, এজন্যেই বিজ্ঞানের জগতের মানুষেরা যখন অবৈজ্ঞানিক কথা বলেন, আমরা সেটাকেই বিজ্ঞান বলে ধরে নিয়ে বিভ্রান্ত হই। এই ঘোলা জলে মাছ কারা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, সে নিয়ে বেশী ভাবতে চাই না।
এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। অসুখটা নিয়ে তার আগে নাড়াঘাঁটা হলেও, গতশতকের আশির দশকের শুরুর দিকে প্রথম জানা যায়, মারণব্যধি এইডস-এর কারণ – এইচআইভি ভাইরাস। সেসময়ে সেল বায়োলজি ও মলিকিউলার বায়োলজির অন্যতম খ্যাতনামা গবেষক ছিলেন পিটার ডুয়েসবার্গ – লিনাস পলিং-এর মতো তিনিও খুব অল্পবয়সে বিশ্বের এক প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হন – ভাইরাল জিন আর ক্যানসারের যোগসাজশের খোঁজ দিয়ে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সদস্য নির্বাচিত হল, সে-ও কম বয়সেই।
এহেন পিটার ডুয়েসবার্গ, তিনি কিছুতেই মানতে রাজি ছিলেন না, যে, এইডস একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এইচআইভি একটি নিরীহ ভাইরাস – এবং এইডস অসুখের কারণ দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, নেশার ইঞ্জেকশন, সমকাম ইত্যাদি ইত্যাদি। না, সমকামী বাদ দিয়েও অনেকেই এউডসে আক্রান্ত হতে পারেন – সংক্রামিত রক্তের মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে হিমোফিলিয়া বা থ্যালাসেমিয়ায় ভোগা বাচ্চারাও – ডুয়েশবার্গের তত্ত্বে এঁদের অসুখের কারণ নিয়ে বিশেষ কথা ছিল না – কিন্তু, সে নিয়ে ডুয়েশবার্গ বিচলিত হননি।
নব্বইয়ের দশক থেকে একের পর এক গবেষণায় এইডস ব্যাধি বা তার চিকিৎসার নতুন নতুন পরিসর উন্মোচিত হয় – কিন্তু, পিটার ডুয়েশবার্গ নিজের মত বদলান নি, শুধু তত্ত্বে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন মাত্র। যেমন, আফ্রিকায় এইডস-এর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তাঁর তত্ত্ব ছিল খুব সরল – গরীব আফ্রিকানদের মধ্যে এইডসের কারণ অপুষ্টি, আর ধনী আফ্রিকানদের মধ্যে এইডস হওয়ার কারণ – হ্যাঁ, ওই এইচআইভি সংক্রমণের বিরুদ্ধে যে চিকিৎসা করা হচ্ছে, সেই ওষুধগুলোই। আর হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে এইডস-এর কারণ, রক্তের মধ্যে কিছু বিশেষ ফ্যাক্টর, যেটা ধরা যায়নি এখনও, কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই ধরা যাবে – মোট কথা, এইচআইভি নামক ভাইরাস বাদ দিয়ে অন্য কিছু একটা এইডস-এর কারণ। অবশ্য, ডুয়েশবার্গ একা নন, পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন, অর্থাৎ পিসিআর আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন যিনি, সেই রসায়নবিদ ক্যারি মুলিস তো সোচ্চার ছিলেন, এইচআইভি থেকেই যে এইডস হয়, তার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কই!! আর লিনাস পলিং, সত্তরের দশকে আমেরিকায় এইডস নিয়ে হইচইয়ের বাজারে স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, এইডস থেকে বাঁচাতে পারে, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, বেশী বেশী ডোজে ভিটামিন সি।
আফ্রিকায় এইডস মহামারীর আকার নেওয়ার ব্যাপারে, সেখানকার প্রথমসারির অনেক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন আশ্চর্য তত্ত্বে আস্থা রাখতেন। যেমন, কেনিয়ার নোবেলবিজয়ী ইকোলজিস্ট ওয়াঙ্গারি মাথাই বিশ্বাস করতেন, এইচআইভি মনুষ্যসৃষ্ট এবং জীবাণুযুদ্ধের স্বার্থে ল্যাবে তৈরী। ঠিক এরকম সময়েই, নেলসন ম্যাণ্ডেলার পরে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হলেন থবো এমবেকি। এমবেকি-মশাইও বিশ্বাস করতেন, এইচআইভি-এইডস নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে, সেসবই আজগুবি আর ভ্রান্ত। এটুকু বিশ্বাস থাকলে অতখানি ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সাথে সাথে তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, এইডস-এর ওষুধ বলে যেগুলো বাজারে চলছে, সেগুলো সাক্ষাৎ প্রাণঘাতী বিষ – এবং, যেসব ডাক্তারেরা ওসব ওষুধ ব্যবহার করছেন, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রোগীর ক্ষতি চেয়েই ওষুধ প্রয়োগ করছেন।
এমবেকি যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, ১৯৯৯-এর শেষের দিকে, পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে এইডস মহামারীর আকার নিয়েছে – বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক এইডস রোগীর বাস সেদেশে – প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক দক্ষিণ আফ্রিকীয়র মধ্যে একজন এইডস আক্রান্ত – পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো পরিকাঠামো বা আর্থিক সামর্থ্য, দুইয়ের কোনোটাই সরকারের হাতে নেই। আর, এমিবেকি তো জানতেনই, এইডস-এর ওষুধ বলে যেগুলো বাজারে চলছে, সেগুলো ভালো তো করে-ই না, উল্টে প্রাণঘাতী। জনান্তিকে বলা যাক, এমন বিশ্বাসের মাধ্যমে চিকিৎসাটাই বাদ দেওয়া গেলে, রোগীদের যা-ই হোক, সরকারের অনেকটা খরচা বিলক্ষণ বেঁচে যায়।
অতএব, প্রেসিডেন্ট হয়েই এমবেকি তড়িঘড়ি এইডস মোকাবিলার জন্যে তৈরী করলেন বিশেষ ক্ষমতাশালী কমিটি। আর সেই কমিটির মাথায় বসানো হল – হ্যাঁ, আবারও আপনার অনুমান অভ্রান্ত, পিটার ডুয়েসবার্গকে। অনুমান করা হয়, এমবেকি-ডুয়েসবার্গ যুগলবন্দীর ফলে চিকিৎসাহীন অবস্থায় বেঘোরে প্রাণ হারান তিন লক্ষেরও বেশী মানুষ।
কিন্তু, কথায় কথায় বড্ডো দূরে চলে এসেছি। যেকথা বলছিলাম, লিনাস পলিং অথবা পিটার ডুয়েসবার্গ, দুজনের কারোর দাবীর মধ্যেই বিজ্ঞান ছিল না, ছিল স্রেফ ভ্রান্ত বিশ্বাস। কিন্তু, আমরা, অর্থাৎ আম-আদমি সেসব কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি, কেননা আমাদের বিজ্ঞানের উপর ভরসা অগাধ – এবং, আমাদের কাছে বড় বিজ্ঞানী যা-ই বলেন, তা-ই বিজ্ঞান। একের পর এক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় তাঁদের দাবীদাওয়া ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও, আমরা সেসব তথ্যের খোঁজ না নিয়ে, ধর্মগুরুদের বাণীর মতো করেই, বিজ্ঞানীর দাবীর উপর বেশী ভরসা রাখি।
এমবেকি ডুয়েসবার্গকে সামনে রেখে ব্যবহার করেছিলেন – বা, বলা ভালো, বিজ্ঞানী হিসেবে ডুয়েশবার্গ-এর খ্যাতিকে সামনে রেখে ব্যবহার করেছিলে , এবং বৃহত্তর অর্থে বলা যায়, বিজ্ঞানীর বক্তব্যমাত্রেই বিজ্ঞান, সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুল-প্রচলিত এই বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছিলেন – দক্ষিণ আফ্রিকার গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ প্রতিবাদ করেন নি – ডুয়েশবার্গের বক্তব্যে আস্থা রেখেছিলেন, আস্থা রেখেছিলেন, এমনকি সেদেশের একটা বড় সংখ্যার চিকিৎসকও। প্রাণ গেছিল কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষের। ভিটামিনের গল্প শোনাতে গিয়ে একটু অপ্রাসঙ্গিক চর্চা হয়ে গেল, সম্ভবত। কিন্তু, যেকথা বলতে চাইছি, বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের মতো চোখ বুঁজে বিশ্বাস করে বসলে বা বিজ্ঞানী যা-ই বলছেন, যাচাই না করেই সেটাকে শাশ্বত সত্য ভেবে বসলে, আখেরে লাভের গুড় খেয়ে যায় অন্তরালের খেলোয়াড়েরা। ঠিক একারণেই আমাদের আরো, আরো বেশী করে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া জরুরী – বিজ্ঞানের যে মূল নির্যাস, সেই খতিয়ে দেখা, খুঁটিয়ে দেখা – দুটো লাইনের মাঝে কোন সত্য চাপা পড়ে থাকছে, নিরন্তর প্রশ্নের মাধ্যমে সেই সত্যিটাকে যাচাই করে দেখা – বিজ্ঞানের এই মূল স্পিরিটটুকু যতদিন না আমরা, অর্থাৎ আমজনতা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক, আত্মস্থ করতে পারছি, ততদিনই বিজ্ঞান ব্যবহৃত হতে থাকবে ক্ষমতার কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে – সে ক্ষমতা কখনও রাষ্ট্রযন্ত্র, উদাহরণ ডুয়েশবার্গ – আবার কখনও বা কর্পোরেট বহুজাতিক, উদাহরণ লিনাস পলিং।
যে কথা দিয়ে আগের পর্ব শেষ করেছিলাম, পলিং-এর দাবীকে ব্যবহার করে মুনাফা বাড়িয়ে নিয়েছিল ভিটামিন-প্রস্তুতকারক বড় কর্পোরেট কোম্পানি – ব্যবসা বেড়ে যায় দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, দশগুণ – প্রতি চারজন মার্কিনীর একজন ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করেন – পরবর্তীকালে ফুড সাপ্লিমেন্টের বড় ব্যবসার পরিসরটা খুলে যায় এভাবেই, পলিং-এর লাগাতার প্রচার গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক নিঃসন্দেহে।
আর ক্ষতি? ক্ষতিও কি হয়নি? মেগাডোজ ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট যে ভালোর চেয়ে খারাপই করে বেশী, ক্যানসার ঠেকানোর চাইতে ক্যানসারের কারণ হয়ে উঠতে পারে – একথা তখন থেকেই জানা যাচ্ছিল একটু একটু করে, পলিং কানে তোলেন নি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু জন্যেও কি তাঁকেই, মানে তাঁর অপরিণামদর্শী ভিটামিন-প্রীতিকে দায়ী করা চলে??
কিন্তু, সেসব প্রসঙ্গে পরে আসছি – আপাতত, লিনাস পলিং-এর ভিটামিন সি খাইয়ে ক্যানসার সারানোর দিনগুলোতে ফিরে আসি। আর দেখা যাক, তাঁর এই লাগাতার প্রচারের চোটে সবচেয়ে বিপাকে পড়লেন ঠিক কারা??
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, কোম্পানিদের লাভের খাতাটি ফুলেফেঁপে উঠলেও চূড়ান্ত বিপাকে পড়লেন – ডাক্তাররা – বিশেষ করে সেই ডাক্তারবাবুরা, যাঁরা ক্যানসারের চিকিৎসা করেন।
(চলবে)