দ্বারকানাথের জীবনকাহিনী নিয়ে কিছু বলতে গেলে সচরাচর শিল্পোদ্যোগ এবং মহানুভবতার এক খণ্ডচিত্র নির্মাণ হয় – ইতিহাসের চালিকাশক্তি অধিকাংশক্ষেত্রেই পেছনে চলে যায়। যে কারণে এধরনের চিত্রায়ণ খানিকটা অনৈতিহাসিকও বটে। বিভিন্ন সময়ে বহুল পঠিত এবং প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রেও এরকম একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিতও হয়েছে। একইসাথে জমিদার, ব্যবসায়ী এবং ইংরেজেদের আনুকূল্য নিয়ে ভারতের প্রথমসারির একজন শিল্পোৎপাদক – এ সমাহার সহজলভ্য নয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে সময়ে দ্বারকানাথের উত্তুঙ্গ পরিক্রমণ সে সময়ে এক অর্থে ইতিহাসের নায়ক সময়, মানুষ সময়ের সন্তান, সাথী এবং ব্যবহারকারী।
১৮শ শতাব্দির শেষ থেকে ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ভারতকে একটি অতি বৃহৎ সামাজিক পরীক্ষাগার করে তুলেছিল। বিভিন্ন ‘ট্রায়াল অ্যান্ড এরর’-এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় শাসন আর ভূমি-রাজস্বের নতুন সব পথ ও পন্থা তৈরি করেছিল। একইসাথে ১৯শ শতকের অভিঘাতে জন্ম নেওয়া ওদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এদেশের পরিবেশে রোপণ করার ফলাফল বুঝে নিতে চেয়েছে। দ্বারকানাথের বাণিজ্য-বৃহস্পতি যখন তুঙ্গে (১৮৩০-১৮৪৪) সেসময়ে ইংল্যান্ডে বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পীয় পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছুচ্ছে। পরিণতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবাধ বাণিজ্য, স্বাধীন প্রেস, নিজেদের দাবীদাওয়া পেশের জন্য বিভিন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা, নানা রকমের সামাজিক সংস্কার, “ইন্টাররেশিয়াল পার্টনারশিপ”, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি গড়ে উঠছে – এ দেশের অতি ক্ষুদ্র এবং ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকারী অংশের মাঝে।
স্মরণে রাখবো, ১৮১৩ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা ছাঁটা শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণ কৃপালনি দ্বারকানাথ নিয়ে তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করছেন “The age of laissez faire had arrived.” কৃপালনির গ্রন্থ থেকে জানতে পারছি – তাঁর জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে তিনি ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতেন এবং তাঁর এ কাজের সহযোগীরা ছিলেন রামমোহন রায় এবং পাথুরিয়াঘাটার আত্মীয়রা। (Dwarakanath Tagore: A Forgotten Pioneer, A Life, National Book Trust, 1981, পৃঃ ৭৪)
এর কিছু নমুনা দেখা যাক। ১৮২১ সালে কলকাতার এক ব্রিটিশ এজেন্টের সাথে পার্টনারশিপে সুদূর আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে এক জাহাজ রাম (মদ), মৌরি এবং জায়ফল পাঠিয়েছিলেন। Resolution নামে এই জাহাজটির বহন ক্ষমতা ছিল ২৬ টন। ফেরার পথে জাহাজটি তামা ভরে নিয়ে এসেছিল, যা ভারতে বিক্রির জন্য আদর্শ ছিল। (Dwarakanath Tagore: A Forgotten Pioneer, পৃঃ ৭৫) এর সাথে ছিল আফিমের ব্যবসা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কুলি তথা “দাস’ সরবরাহ করার ঠিকেদারি, নীল চাষ ইত্যাদির মাধমে বিপুল অর্থোপার্জন। ছিল রাণীগঞ্জের কয়লার ব্যবসা।
(আফিমের ব্যবসার একটি নমুনা)
একইসঙ্গে আরও দুটি নতুন ব্যবসায়ে তিনি হাত দিলেন ব্রিটিশ পার্টনারদের সঙ্গী করে – (১) সে সময়ে শৈশব অবস্থায় থাকা ব্যাংকের ব্যবসা, এবং (২) ইন্সিউরেন্স ব্যবসা। তৎকলীন কলকাতায় কোন জয়েন্ট-স্টক ব্যাংক ছিল না। ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন দ্বারকানাথ ১৮২৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিয়ন ব্যাংক খুললেন ১২ লক্ষ ৫০০ টাকা পুঁজি নিয়ে। কিন্তু তিনি রইলেন পশ্চাদপটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ কাস্টমস-এর কর্মচারী হিসেবে লবণ, সোরা এবং আফিম রপ্তানির কাজ চালাতেন। এরপরে তাঁর তুতো ভাই রামনাথকে ব্যাংকের ট্রেজারার করে এবং ব্যবসায়িক বন্ধু উইলিয়াম কার-কে সঙ্গী করে প্রতিষ্ঠা করলেন ইউনিয়ন ব্যাংক। এবং পরবর্তীতে কার টেগোর অ্যান্ড কোং। ১৮২২ সালে খুললেন ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্সিউরেন্স – “owned jointly by himself and the partners of the three commercial houses – Ferguson & Co., Crutenden & Co., and the Mackintosh & Co.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬)
এখানে আরেকটি উল্লেখযোগয় তথ্য দিয়েছেন ব্লেয়ার কিং তাঁর Partner in Empire: Dwaranath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India (University of California Press, 2020) গ্রন্থে – “Only three months elapsed between the opening of the Union Bank and the closing of John Palmer and Company, whose bankruptcy inaugurated the devastating commercial crisis of 1830-33. The atmosphere of confidence and expansiveness evaporated overnight. Alexander and Company closed its doors in December 1832 and Mackintosh in January 1833. By January 1834 no major house had survived and the entire system had to be rebuilt. During this period, Dwarkanath stood firm as a rock. He was the only solvent partner in the now diminished Commercial Bank, and as soon as Mackintosh failed he issued a notice that he would pay all outstanding claims against the Commercial Bank and receive sums due to it. He did the same with the Oriental Life Assurance Society, owned by himself and the partners of three fallen houses — Fergusson and Company, Cruttenden and Company, and Mackintosh and Company. The society had been founded in 1822 to insure the lives of agency-house partners and debtors whose liabilities could then be met in case of death. Its assets had been used as additional trading capital by the proprietors, and when their houses failed, Dwarkanath Tagore, the only solvent partner, assumed the assets and agreed to meet demands on the company. In 1834 he formed the. New
Oriental Life Assurance Company with a new set of partners to carry out the engagements of the old company.” (পৃঃ ৪৩-৪৪)
এরিক স্টোকস তাঁর “দ্য ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যান্ড ইন্ডিয়া” গ্রন্থে কলকাতার উদীয়মান বাণিজ্যিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলছেন – “substantially it swelled the great tide of liberalism engulfing the English mind in the eighteen-thirties.”। (পৃঃ ৪৩) শুধু তাই নয়, স্টোকস আরও বলছেন – “Utilitarian hopes of inaugurating a competitive society based on individual rights in the soil, depended as much upon the revenue assessment, and the registration of landholdings which accompanied it, as upon the superstructure of judicial codes and establishments.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১)
এসবের সামগ্রিক অভিঘাত তখন প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে ব্রিটিশ মহা সাম্রাজ্যের “দ্বিতীয় নগরী” (লন্ডনের পরেই) কলকাতার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মানচিত্রে। সমাজের অতি ক্ষুদ্র ওপরতলার বাসিন্দারা এর পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করছে। পূর্বতন মোগল সাম্রাজ্যের রাজা-প্রজার সম্পর্ক ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাচ্ছে। জায়মান নাগরিক সত্তা তৈরি হচ্ছে। ফলে প্রেসের স্বাধীনতা, বাণিজ্যের বিধিনিষেধ কমে যাওয়া, সতীদাহ প্রথা রদ করা, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদির মতো আরও বেশ কিছু বিষয়ে দেশীয় মানুষদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। এবং যেহেতু সমধর্মী পরিবর্তন খোদ ইংল্যান্ডেও হচ্ছে এজন্য এখানকার ভাঙ্গাচোরা সংস্কারের চেষ্টা পালে বাতাসও পাচ্ছে।
“সমাচার চন্দ্রিকা” পত্রিকায় ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩-এ লেখা হচ্ছে – “এতদ্দেশে উন্নত হওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকর্ম … আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগ্ দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস এবং জমীদার হইবেক”। (বানান এবং যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত)
শিল্পীয় উদ্যোগের সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন “ল্যান্ডহোলডার্স সোসাইটি” তৈরি করার ক্ষেত্রে মূল ভুমিকা নিচ্ছেন দ্বারকানাথ। ব্রিটিশের কাম্য একটি “loyal opposition” তথা “অনুগত বিরোধিতা” গড়ে উঠছে। লর্ড বেন্টিঙ্কের সাথে নিয়মিত পত্র বিনিময় হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার ঘটাবার লক্ষ্যে (যা বাণিজ্যের মুনাফা সুগম করবে এবং এখনও যা আমরা হামেশাই দেখে থাকি) “funds for Afghan War, widows or victims of famine in Ireland or of cholera in France”-এর জন্য চাঁদা তুলছেন, নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছেন। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ব্লেয়ার ক্লিং-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)
তথ্যের ক্ষেত্রে কিছু গরমিল থাকলেও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পাচ্ছি – “১৮৩৭ খৃস্টাব্দে মফস্বলের পুলিশ-ব্যবস্থার জন্যে গভর্নমেন্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় দ্বারকানাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব আনেন। (হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র এরই ফললাভ করেছিলেন!) তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন এই কমিশনের সদস্য। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকরণে দ্বারকানাথের দান অসীম। কোনো হিন্দু তখন শবচ্ছেদ করতেন না। দ্বারকানাথ নিজে শবচ্ছেদগৃহে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের উৎসাহ দেন শবচ্ছেদ করতে। চারটি চাহত্রকে তিনি ইংলন্ডে পাঠান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য। (এ তথ্যটি ভুল। তিনি দু’জন ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন)।” (ভারতের শিল্প-বিপ্লব – রামমোহন ও দ্বারকানাথ, কলিকাতাঃ বৈতানিক, ১৯৬৪, পৃঃ ৯)
আমার বিচারে এরকম পটভূমিতে দ্বারকানাথকে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত। কিশোরীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থ (Memoir of Dwarakanath Tagore, কলিকাতা, ১৮৭০) থেকে জানতে পারি ইংল্যান্ডের উঁচুতলার সমাজে দীর্ঘসময় কাটিয়ে ফেরার পরে অক্টোবর ৯, ১৮৪২-এ বেন্টিঙ্ক (তখন ভারতের ভাইসরয় নয়) একটি চিঠিতে দ্বারকানাথকে লিখছেন যে ওদেশের সংসর্গ “will enable you to impress upon your countrymen the happy consequences”। বেন্টিঙ্ক তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন ইউরোপীয় মডেলে কলকাতায় “business house” গড়ে তোলার জন্য। (পৃঃ ১২)
কিশোরীচাঁদ আরও জানাচ্ছেন – “Dwarakanath was one of the first to estimate rightly the influence of the landed aristocracy and the importance of utilizing that influence , and bringing it to bear on the good government of the country.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯)
ক্লিং মন্তব্য করছেন, “Dwarakanath, the representative zamindar, might criticize the government, but he did so as an insider, a confidant of governors-general, a man whose social position and fortune depended on the British.”
আমার নিজের গবেষণায় পেয়েছি ১৮৩৬ সালের ১লা জানুয়ারি দ্বারকানাথ সাহারানপুরের কলেক্টর জে এন ব্যাটেনকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিখছেন – “I have converted at least 200 young good Hindu College boys by giving them the holy water that comes from Corbonell & Co., so that by and by they will sing a chorus with me at some of the chapels.” (রবীন্দ্রভবন আর্কাইভস, দ্বারকানাথ ঠাকুর ফাইল, DTF (GF) 01/38) ভারতের এরকম বিশ্বস্ত “পার্টনার ইন এম্পায়ার” আর ক’জনই বা হতে পারে?
ইংল্যান্ডে পৌঁছুনোর মুহূর্ত থেকে পরবর্তী চার মাস তাঁর কর্মব্যস্ত জীবন কেটেছে। পার্লামেন্টে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিটিং এবং, সর্বোপরি, রাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড পামারস্টোন ও অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (কিশোরীচাঁদ মিত্রের “মেমোয়ার অব দ্বারকানাথ টেগোর” পুস্তকে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। দ্বারকানাথ কিরকমভাবে কয়েক লক্ষ টাকার উপঢৌকন ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে বিতরণ করেছিলেন। এমনকি নাইটহুডের জন্যও তাঁর নাম দু-একবার আলোচনায় এসেছিল।)। তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছিলেন “a slave in the land of liberty” বলে। বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর History of Indian Social and Political Ideas (From Rammohan to Dayananda), Calcutta, 1996) গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে রামমোহন এবং দ্বারকানাথ দুজনেই “supported the scheme of colonization”।
ব্রিটিশ-নির্ভর উপনিবেশিক অর্থনীতির মধ্যে থেকে “loyal opposition” যতটুকু বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধে এবং রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেটুকুর পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। চীনে যখন ১৮৩৯ সালে “অহিফেন যুদ্ধ” শুরু হয়েছে সেসময়টি ওদেশে এখান থেকে আফিম রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সবচেয়ে সুন্দর সময়। আফিম পরিবহনের জন্য তাঁর তিনটি দ্রুতগামী জাহাজও ছিলো – ৩৭১ টন, ৩৬৩ টন এবং ১১২ টন আফিম বহন করতে পারতো। কৃষ্ণ কৃপালনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে কৌতুকছলে এই আফিমব্যবসার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বলছেন – “Did he know that his grandfather was an enthusiatic party to the ‘crime’ from which he and other merchnats of Calcutta reaped a good harvest?” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭) প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথের কর্মকাণ্ডের মধ্যে নৈতিকতার স্থান কমই ছিল।
১৮ জুন, ১৮৩৬ সালে টাউন হলের এক মিটিং-এ (ব্রিটিশদের কিছু আইনী সুযোগ হ্রাসের পরে হলে যে মিটিং হয়েছিল) সে মিটিং-এর একজন প্রস্তাবক হিসেবে তিনি বলেছিলেন – “ভারতীয়রা এখন অব্দি ক্রীতদাস হিসেবে আছে; এজন্য কি ইংরেজদেরও ক্রীতদাস করে তুলতে হবে?” তাঁর হুবহু বক্তব্য ছিলো, “They have taken all which Natives possessed; their lives, lives, liberty, property and all were held at the mercy of the Government, and now they wish bring the English inhabitatnts of the country to the same state! They will not raise the Natives to the condition of the Europeans, but they degrade the Europeans by lowering them to the status of the Natives. (প্রচণ্ড হাততালি)” (কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪) “ইংরেজদের ভারতীয়দের স্তরে অবনমিত করতে চাইছে” – এটা তাঁর কাছে একেবারে অসহনীয় ছিলো, কারণ ইংরেজরা তাঁর অন্ন ও সমৃদ্ধি দাতা। এখানে ব্লেয়ার ক্লিং-এর (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) মন্তব্য প্রাসঙ্গিক – “Bengal, led by its loyal, reliable zamindars, was, in this period, the pillar of the Raj.” (ব্লেয়ার কিং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭)
আরও কিছু কথা
বিমান বিহারী মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি দ্বারকানাথের ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দোলাচলচিত্ততা/দ্বিচারিতার বিষয়ে দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কোন এক বিশেষ মুহুর্তে (১৮ জুন, ১৮৩৬-এ একটি মিটিয়ে) দ্বারকানাথ বলেছিলেন – “ওরা (ব্রিটিশেরা) আমাদের অধিকারে যা যা ছিল সবকিছু নিয়ে নিয়েছে; দেশীয়দের জীবন, ধন-সম্পদ, এবং আর যা কিছু আছে সরকারের দয়ার ওপরে নির্ভরশীল।” (পৃঃ ১২৭) আবার, বিপরীত সুরে একই মানুষ টাউন হলে ১৫ ডিসেম্বর, ১৮২৯-এর মিটিংয়ে বলেন – “আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি নীলের চাষ এবং ইউরোপীয়ানদের বসতি তথা উপনিবেশ স্থাপন রায়তদের (সাধারণ কৃষক) জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করেছে এবং জমিদারদের ধনী এবং সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এর ফলে সমাজ এবং দেশের প্রভূত লাভ হয়েছে।” (পৃঃ ১২৭)
এই দোলাচলচিত্ততা বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁর একটি প্রাধান্যকারী উপাদান।
ব্লেয়ার কিং তাঁর পুস্তকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন – “দ্বারকানাথের প্রথম বৃহৎ উদ্যোগ ছিল কয়লা কোম্পানি। তথাপি তিনি নিজের হাতে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবে ‘বেঙ্গল কোল কোম্পানি’ তৈরি হবার পরে এ ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। একটি কারণ হল বিনিয়োগের পরিবর্তে নিজের জীবনধারার ধরনকে রাজকীয়ভাবে রক্ষা করা এবং চালিয়ে যাবার জন্য নগদ অর্থ চাইছিলেন। নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি নিজেই দ্বিচারিতায় ভুগতেন। তিনি কি ব্যবসায়ী নাকি ‘প্রিন্স’ ছিলেন? … he was always on the search for new directions and new opportunities.” (পৃঃ ১২১)
এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন কিং – কিভাবে লাভজনক একটি বিনিয়োগ ছেড়ে দ্রুত অন্য একটিতে চলে যাওয়া যায়।
আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে, পুঁজির ভিন্নতর চরিত্র সত্ত্বেও একথাগুলো সমান প্রযোজ্য। পুঁজির বিশ্বস্ত পাহারাদার চাই – কি তখন, কি এখন। আবার একই সঙ্গে পলাতক পুঁজিরও রাষ্ট্রিক পাহারাদার চাই বর্তমান ভারতে।

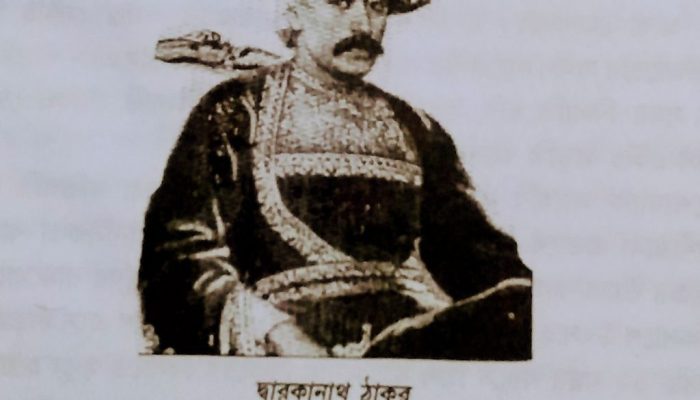



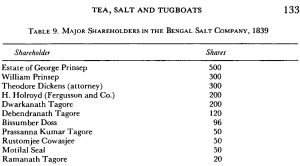











সমৃদ্ধ হলাম
Khub bhalo ebong jathesto tathyo samridhyo lekha.Dwarokanath er patitalayer byabsao chhilo,jatodur jani,setar ullekh korle bhalo hoto.
Aapnar ei asadharon lekhanir jonno bohu ajana jinis jante parlam. Asesh Dhonnobad Doctor babu. 🙏🙏
সার্থক শিরোনামে অসাধারণ লেখা। দ্বারকানাথকে দারুণ ধরার চেষ্টা করেছেন ডঃ জয়ন্ত। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার থেকে ভারতীয় শিক্ষা ও ব্যবসার আধুনিকীকরণের ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছেন দ্বারকানাথ। ধন্যবাদ লেখককে।