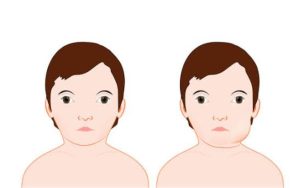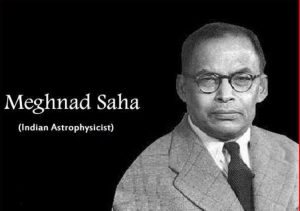খবরের কাগজে কত খবরই তো আসে। বড় একটা অবাক হই না। কিন্তু একখানা খবর পড়ে একেবারে চমকে গেলাম।
কলকাতার একটি নামকরা কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে এসে এক রোগিণী অভিযোগ জানিয়েছেন, সেখানে তাঁর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেন এক পুরুষ টেকনিশিয়ান। হ্যাঁ, কক্ষে ডাক্তারবাবু উপস্থিত ছিলেন, রোগিণীর বুকের উপর ইকোকার্ডিওগ্রাফির ‘ট্রান্সডিউসার প্রোব’ বুলিয়ে হৃদযন্ত্রের নড়াচড়া বা তার গোলযোগের যে ছবি ফুটে উঠছিল কম্পিউটার মনিটরে, ডাক্তারবাবুর নজর ছিল সেদিকেই। মহিলাদের শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার মুহূর্তে কক্ষে আরেকজন মহিলার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, ছিলেন তেমন ‘ফিমেল অ্যাটেন্ড্যান্ট’-ও। পুরুষ টেকনিশিয়ান অভব্য আচরণ কিছু করেছেন, এমন অভিযোগ কিছু ওঠেনি। রোগিণী শুধু জানিয়েছেন, পুরুষ টেকনিশিয়ান তাঁর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেছেন, এতেই তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। এবং সেই মর্মে অভিযোগ দাখিল করেছেন “ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন”-এ।
চমকের শেষ এখানেই নয়।
খবরে এও প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কমিশন অভিযোগটি রীতিমতো গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখেছেন। এবং অবিলম্বে যাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারিণীর কাছে লিখিতভাবে দু:খপ্রকাশ করে নেয়, সেই মর্মে কমিশন নির্দেশিকা জারি করেছেন। কমিশনের প্রধান বিচারপতি অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এও জানিয়েছেন, মহিলাদের উপর শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা বা বিভিন্নধরনের টেস্ট যাতে কেবলমাত্র মহিলা টেকনিশিয়ানরাই করতে পারেন, এ বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা যায় কিনা, সেটা তাঁরা আলোচনা করে দেখছেন।
এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা খুবই দু:খিত, কিন্তু পর্যাপ্ত মহিলা টেকনিশিয়ান না থাকার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে – তবে ভবিষ্যতে যেন এমনটা না হয়, তাঁরা সেদিকে নজর রাখবেন। তাঁদের বক্তব্য পড়ে মনে হল, যেন মহিলাদের জন্য মহিলা টেকনিশিয়ান, এমনটাই দস্তুর। যদিও নিয়মানুসারে মহিলা অ্যাটেন্ডেন্ট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এও জানিয়েছেন, কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁরা তা মাথা পেতে গ্রহণ করবেন।
মনে করিয়ে দেওয়া যাক, এই ঘটনা ঘটছে একবিংশ শতকের পশ্চিমবঙ্গে, ‘আলোকপ্রাপ্ত’ কলকাতা শহরে।
তাহলে এরপর থেকে মেয়েদের শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারবেন শুধুই মেয়ে টেকনিশিয়ানরা?
কমিশনের “আলোচনা”-য় কি আরেকটু প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া যেতে পারে না, যে, মেয়েরা অসুস্থ হলে তাঁর চিকিৎসা করতে পারবেন শুধুই মেয়ে চিকিৎসকরাই?
কমিশনে যেসব বাঘা বাঘা ডাক্তাররা রয়েছেন, তাঁরা – দুর্ভাগ্যবশত – সকলেই পুরুষ। কমিশনের মাথা যিনি, বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও মহিলা নন। দুশ্চিন্তা একটাই, এঁরা সবাই মিলে মেয়েদের ‘উপকার’-এর জন্য এমন বড় সিদ্ধান্তটা নিয়ে উঠতে পারবেন কি?
সরকার-নিয়োজিত কমিশন। সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, আশা করা যাক, অনুরূপ সিদ্ধান্ত লাগু হবে সরকারি হাসপাতালেও। নইলে যা-ই সিদ্ধান্ত হোক, তা বড্ডো দ্বিচারিতার মতো শোনাবে। বেসরকারি হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসা করাতে পারবেন, শুধু সেই মেয়েদেরই আব্রু-হায়া থাকবে, আর সরকারি হাসপাতালে আসা মেয়েদের কথা ভাববেন না! তাঁরা তো বানের জলে ভেসে আসেননি। কমিশন যেভাবে ব্যাপারটা দেখছেন, তাতে, জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক নারী ধরলে মেয়েদের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত হওয়া উচিত মোট চিকিৎসক-টেকনিশিয়ান সংখ্যার অর্ধেক – এবং তাঁরা সকলেই হবেন নারী, এমন হওয়াটাই অভীষ্ট, অবশ্যপালনীয় কর্তব্যও বটে। সরকার যদি ভাবেন, সে বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। যদি এখুনি না হয়, লেডিজ মেডিকেল কলেজ চালু করে ঘাটতি পূরণ আর কতটুকুই বা সমস্যা! সারা দেশ জুড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য এমনিতেই অবহেলিত, যে ক’দিন এই ঘাটতি পূরণ না হচ্ছে, মেয়েরা না হয় বিলকুল চিকিৎসাহীনই থাকবেন। তা থাক, চিকিৎসার মতো তুচ্ছ কারণে আব্রু-হায়া রক্ষার মতো বড় বড় ভাবনাগুলো অবহেলা করা যায় না। যা-ই বলুন, বৃহৎ আদর্শের দিকে চলার পথে কিছু ছোট ছোট ক্ষতি ঘটতেই পারে, সে নিয়ে বিচলিত হওয়াটা অনুচিত।
তবে চিকিৎসার যে দর্শন বা চিকিৎসার যে এথিক্স, যেখানে মেয়েদের বা ছেলেদের নিছক মেয়ে বা ছেলে হিসেবে দেখার শিক্ষা কখনোই দেওয়া হয় না (আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবশ্য মস্ত অভিযোগ, ছেলে বা মেয়ে তো বাদই দিন, মানুষটাকে মানুষ হিসেবে দেখার অভ্যেসই ভুলিয়ে দেওয়া হয়) – কমিশনের সিদ্ধান্ত-আলোচনা সেই বুনিয়াদী ভাবনাচিন্তার একেবারে বিপ্রতীপ। কিন্তু, সে হোক গে। নতুন ইতিহাস গড়ার পথে এসব টুকটাক এথিক্স ঐতিহ্য অভ্যেস শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবারও মানে হয় না।
কমিশনকে অনুরোধ, ঢিলেঢালা করবেন না, সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলুন। কাজটা করে ফেলা গেলে ব্যাপারটা দারুণ হবে কিন্তু। হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো। চিকিৎসার মতো ব্যাপারে এতখানি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ – এতখানি রিগ্রেসিভ ভাবনা – গোবলয় বলে যাদের হ্যাটা করে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি, সেসব রাজ্যগুলোও এখনও ভেবে উঠতে পারেনি। এগিয়ে বাংলা, সত্যিই।
তবে যে রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়াররা প্রাইমারি ইশকুলে পড়ানোর দায়িত্ব পান (সিভিক ভলান্টিয়ার পদে যোগদানের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, সে প্রশ্ন না-ই বা তুললাম) – অনবদ্য যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়, ‘প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইংরেজি ও অঙ্ক শেখানোর ব্যাপারে অনেক ঘাটতি থাকে’ – অনুমান করা যায়, কর্তৃপক্ষ এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, আইনশৃঙ্খলা-নিয়ন্ত্রণ/অপরাধ-দমন আর শিশুদের লেখাপড়ার প্রাথমিক পাঠ দেওয়া, দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ দূরত্ব নেই – সেখানে কোনও ব্যাপারেই আলাদা করে চমৎকৃত হওয়ার মানে হয় না। তাই না?