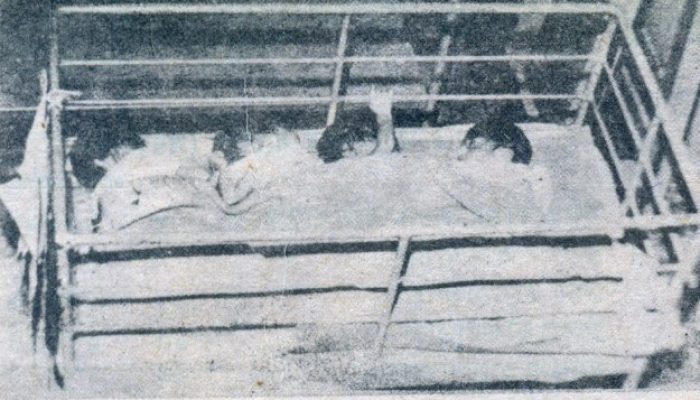১৯৭৯-এর শেষার্ধে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ ও এমসিডিএসএ-র উদ্যোগে হাসপাতালে এক অনুসন্ধান চালানো হয়। দেখা যায়—
• হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে সিনিয়র অফিসার অন ডিউটি-র পদ সাতটা, তার মধ্যে তিনটে পদ খালি। হাউসস্টাফদের ওপর বিরাট কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাদের দিয়ে জোর করে জুনিয়র অফিসার অন ডিউটি-র কাজ করানো হয়।
• গত এক মাস ধরে ইসিজি মেশিন খারাপ, হার্টের রোগীদের চিকিৎসা না করে পাঠাতে হয়েছে অন্য হাসপাতালে, রাস্তায় মারা গেছেন কিছুজন।
• ইমার্জেন্সিতে রক্ত পাওয়া যায় না, চোরাকারবারীতে অবশ্য পাওয়া যায়। (যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক কিন্তু ছিল মেডিকাল কলেজেই সিঁড়িওয়ালা এমসিএইচ বিল্ডিং-এর একতলায়।) অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাব। বহু জরুরী ও জীবনদায়ী ওষুধ হাসপাতালে নেই, ফলে রোগীরা বিনা ওষুধে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাচ্ছেন।
• হাসপাতালের আউটডোর বা ইনডোরে পেনিসিলিন বা সালফা ড্রাগ ছাড়া অন্য অ্যান্টিবায়োটিক নেই। চর্মরোগের বিভাগে আবার পেনিসিলিনও মেলে না।
• হাসপাতালে বার্ন ইউনিট নেই, পোড়া রোগীকে বারান্দায় রাখা হয়, ফলে ২০% পোড়া রোগীও জীবাণুসংক্রমণে মারা যান, যেখানে আধুনিক চিকিৎসায় নাকি ৮০% পোড়া রোগীকেও সারিয়ে তোলা সম্ভব।
• আউটডোরে ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করে রোগী ১ মিনিট ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান, (যাঁরা সৌভাগ্যবান তাঁরা পান বড়জোর ৩ থেকে ৪ মিনিট)। ওষুধের লাইনে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রতিদিনের জন্য গড়ে ২৫ পয়সার ওষুধ পাওয়া যায়। অনেক রোগী ওষুধ না পেয়ে খালি হাতে ফেরত যান।
• অপারেশন করতে হবে এমন রোগী আউটডোরে দেখানোর পর এক-দেড় বছর পর হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ পান।
• রোগীর খাবার দরকার দৈনিক কমকরে ৩০০০ ক্যালরি, ভর্তি রোগীদের দেওয়া হয় ১৫০০-১৭০০ ক্যালরির খাবার।
• স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ ইডেন হাসপাতালে একটা বেডে তিনজন অবধি রোগিনীকে থাকতে হয়। এক মা থেকে অন্য মায়ের, এক নবজাতক থেকে অন্য নবজাতকের জীবাণু-সংক্রমণ আকছার ঘটে।
• হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের যক্ষ্মারোগীকে রাখা হয় সবচেয়ে অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে।
• ১৫-২০ জন রোগীপিছু একজন নার্স, যেখানে থাকার কথা ৫ জনে একজন।
• ওষুধকোম্পানীগুলোর কাছে মেডিকাল কলেজের ধার ৫৫ লাখ টাকা।

সরকারী হাসপাতালের অবস্থা সুন্দর করে ফুটে উঠেছিল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতায়, যদিও সে কবিতা আরও বছর চারেক বাদে লেখা।
হাসপাতাল মানে
যখন শিশু ছিলাম, বড়দের মুখে শুনতাম, একবার হাসপাতালে
গেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না।
এ দেশ তখন ছিল ইংরেজদের রাজত্ব। গন্ডগোলটা কোথায় ছিল,
বড় হয়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে।
হাসপাতাল সবার জন্য নয়। যাঁরা এই দেশ শাসন করেন,
হাসপাতাল তাঁদের। এখানে তাঁরা থাকেন রাজার মতো, সবাই
বাড়ি ফেরেন বেশ গোলগাল হ’য়ে। যদিও তাঁরা এমনিতেই
গোল, কেননা এই দেশটাই তো তাঁদের।
বাকিরা কেউ বাড়ি, কেউ ফেরে না। সবটাই ভাগ্যির
ব্যাপার। যাদের কিছু নেই, হাসপাতালের দরজা তাদের জন্য
বন্ধ। সেখানে তারা ঢুকতেই পারে না। হাসপাতালের নোংরামী,
ভেতরের এবং বাইরের, তাদের স্পর্শ করে না। ওষুধ এবং
পথ্য নিয়ে এখানে কি চোরপুলিশ খেলা হয়, কানু-সিধুর
ভাই-ভাতিজারা তা বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারে না। যদিও
তাঁদের নামে কলকাতায় রাস্তা হয়…,
হাসপাতালে গেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না, কথাটা,
এখন বুঝতে পারি, অর্ধসত্য। কেউ কেউ ফেরে। তারা সত্যিই
ভাগ্যবান। হাসপাতালে ঢুকতে পেরেছে এবং সেখান
থেকে বেরুতে পেরেছে। ইংরেজ আমল
থেকেই এই ব্যবস্থাটা চলে আসছে। কোথাও কোনো
পরিবর্তন হয়নি। তবে ওষুধ আর পথ্যের কারচুপিটা
যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, ঠিক এতটা ছিল না।
ভিতরে এবং বাইরে এত ধূলো আর দুর্গন্ধ ছিল না।
এখন হাসপাতাল মানেই নরক গুলজার।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
‘জুনিয়ার ডাক্তারদের সমর্থনে
কবিকন্ঠ’ থেকে, ১৯৮৩
গ্রীক পুরান-বর্ণিত সেই আস্তাবলের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে, অবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে ১৯৭৯-তে মেডিকাল কলেজের ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররা এক আন্দোলনে নামেন, ‘Hospital Movement’ নামে তা পরিচিত। একই রকম আন্দোলনে নামেন আর জি কর মেডিকাল কলেজের ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররা। সে যাত্রায় তাঁদের দাবীগুলো অপূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু এই আন্দোলন ছিল পরের দশকের এক বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি।