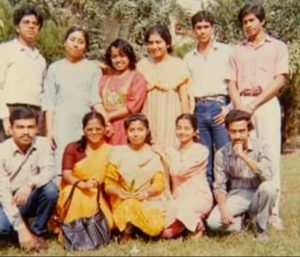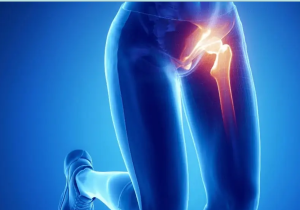১৮২০ সাল। বিদ্যাসাগরের জন্ম সাল। সেই বছরেই ব্রিটেনে এক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিবান পরিবারে জন্মাল একটি মেয়ে। সেই মেয়ে বড় হয়ে হল এক নার্স । উঁচু ঘর থেকে আসা প্রথম সেবিকা। ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার জন্মেছেন এর ৪১ বছর পরে।
এদেশেই হোক আর বিলেতে, তখন ডাক্তারি পেশাটা একেবারেই পুরুষের পেশা। আর নার্সিং? পেশা হিসেবে মেয়েদেরই বটে, কিন্তু হীন পেশা বলে ভারি বদনাম। এমন সময় জন্ম নেওয়া ইংল্যান্ডের এক উঁচুঘরের মেয়ে তার ১৭ বছর বয়সে হঠাৎ একের পর এক ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেতে ত্থাকল। ঈশ্বরের আদেশ অবশ্য অনেকেই সে সময়ে পেত, আর লোকে সেটা মেনেও নিত, আজকালকার মতো মনোবিদের কাছে পাঠাত না। কিন্তু ফ্লোরেন্সের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ছিল অদ্ভুত। ফ্লোরেন্সকে নার্স হতে হবে!
ঐসময়ে নার্স মানেই মাতাল, দুশ্চরিত্রা, সহজলভ্যা, ছোট ঘরের মেয়ে। অন্তত উঁচুঘরের লোকেরা পেশাটাকে তেমনভাবেই দেখত। কিন্তু ফ্লোরেন্স, মানে ঐ ১৭ বছরের মেয়েটি, যাকে আমরা পরে চিনব ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নামে, নার্স বা সেবিকা নামের ঠিক ঐ অপযশগুলো ঘোচাবার কাজটাই করতে নেমেছিলেন।
ছোটবেলায় ফ্লোরেন্স ইতালিয় ভাষা, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ক্লাসিকাল সাহিত্য পড়েছিলেন। আবার ইতিহাস ও দর্শনের পাঠও নিয়েছিলেন। তখনকার উঁচুঘরের ইংরেজদের মধ্যে এরকম শিক্ষা চালু ছিল, তবে মেয়েদের মধ্যে তেমন চালু ছিল না—ফ্লোরেন্সের পরিবার উদারমনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তবে একটা কথা বলা দরকার, ফ্লোরেন্স অঙ্কটাও ভালমতো শিখেছিলেন।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আজও খুব বিখ্যাত নাম। কিন্তু সেটা মূলত নার্সিং পেশাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, “লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প” হিসেবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর অঙ্ক কষায় পারদর্শিতা নিয়ে কথা বলছি কেন? বলছি, কারণ এই লেখাটি সেবাব্রতী ফ্লোরেন্সকে নিয়ে নয়। এই লেখা পুরুষতান্ত্রিক ডাক্তারি পেশার চালু ছককে ঝাঁকুনি দেওয়া এক নারীর কথা; পুরনো ধাঁচের খামখেয়ালি চিকিৎসাব্যবস্থা তছনছ করার ও নতুন করে গড়ে তোলার কারিগর ফ্লোরেন্সর কথা। এই ফ্লোরেন্সকে আমরা অনেকেই চিনি না।
ফ্লোরেন্সের নার্সিং-এর গল্প একটু আধটু আমরা সবাই জানি। ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্স বাড়ির বড়দের বাধ্য মেয়েটি হয়ে ছিলেন, নার্সিং-এর কাজে নেমে পড়েননি, কিন্তু তারপরেও তাঁর নার্সিং শেখা ও করার কাজটি সহজ হয়নি। তাঁর নার্স জীবনের বিখ্যাত জায়গাটি হল ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র। তখন ফ্লোরেন্স ত্রিশের কোঠায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে একপক্ষে ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন ও তখনকার অটোমান (তুরস্ক) সাম্রাজ্য, আর অন্যপক্ষে ছিল রাশিয়া। হাজার হাজার সৈন্য সেখানে কলেরা আর ম্যালেরিয়ায় মারা পড়ছিল।
১৮৫৪ সালে ফ্লোরেন্স তুরস্কের স্কুতারি শহরে (বর্তমানে ইস্তাম্বুল নগরের একটি অংশ) একটা হাসপাতালে কাজ শুরু করলেন। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো নোংরা, বিছানাপত্র ময়লা, খাবার পচা, আর ময়লা জমে ড্রেন বন্ধ থাকায় ভুরভুর করছে দুর্গন্ধ। এখানে আহত সৈন্যরা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হত। খুব শিগগিরই ফ্লোরেন্স বুঝলেন, আঘাতগুলোর জন্য তারা মরে না, মরে হাসপাতালে এই ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য।
সুতরাং নাইটিঙ্গেলের প্রথম কাজ হল রোগীদের জন্য ঠিকঠাক খাবার, পরিষ্কার বিছানা আর জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করা, ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা, আর জানলা খুলে বাইরের নির্মল বাতাস যাতে ওয়ার্ডের ঢোকে তার চেষ্টা করা। এক সপ্তাহে তিনি ২১৫-টি ঠেলাগাড়ি ভর্তি ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করলেন। নর্দমাগুলোকে পরিষ্কার করতে উনিশবার জল দিয়ে ধোয়াতে হয়েছিল, ফ্লোরেন্স কিন্তু তাতেও গঙ্গারামের মতো ঘায়েল হননি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরয়নি, কিন্তু হাসপাতাল চত্বর থেকে দুটি ঘোড়া, একটি গরু আর চারটি কুকুরের মৃতদেহ উদ্ধার করে কবর দেওয়া হয়েছিল।
আগে থেকে ওখানে যেসব ডাক্তার ও পরিচালকেরা ছিলেন, তারা এতে খুব অপমানিত বোধ করেন। হাসপাতালে নার্সিং করতে এসেছেন, নার্সিং করুন, খামোকা এত্তা জঞ্জাল সাফ করার কী দরকার? ওরা এতদিন ধরে আছেন, দরকার থাকলে কি আর ঐ কাজটা তাঁরা ফ্লোরেন্সের জন্য ফেলে রাখতেন? এটা হাসপাতাল, তায় মিলিটারি হাসপাতাল, সেখানে এইসব গন্ধ-নিয়ে-নাকউঁচু শৌখিন লোকেদের ঢোকার কী দরকার? যথাসাধ্য বাধা তারা দিয়েছিলেন, কিন্তু উঁচু মহলে ফ্লোরেন্সের যোগাযোগ ছিল, আর তিনি ছিলেন বাড়াবাড়ি রকমের স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ফলে নিজের মতো করে হাসপাতালের ভোল বদলানোর কাজটা তিনি করেই ফেললেন। তারপর শুরু হল আসল কাজ।
তিনি বসলেন কাগজ কলম নিয়ে। আজকের দিন হলে হয়ত একটা স্প্রেড শীট রাখতেন, কাজটা সহজ হত। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভর্তি হওয়া সৈন্যদের মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগ বীরগতি লাভ করেছে, মূলত জঞ্জালের সঙ্গে সম্মুখ সমরে। কিন্তু ঐ বছরের জুন মাসে মারা গেছে শতকরা মাত্র ২ ভাগ সৈন্য!
১৮৫৬ সালে ফ্লোরেন্স দেশে ফিরলেন। দেশে তিনি বীরের সম্মান ও প্রশংসা পেলেন। কিন্তু সেই প্রশংসা ছিল মূলত এক সেবাব্রতীর অক্লান্ত সেবার প্রশংসা। টাইমস সংবাদপত্রের ভাষায় “তাঁর করুণাঘন উপস্থিতি এমনকি দুরারোগ্য রোগীর মনেও আরামের সঞ্চার করত … তাঁকে দেখে রোগীদের মন কৃতজ্ঞতা আর আশায় ভরে উঠত।” এসব অবশ্যই খুব ভাল ব্যাপার, কিন্তু হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল ফেরানর যে কাজটা ফ্লোরেন্স করেছিলেন সেসবের তেমন উল্লেখ না করে সেবাব্রতীর এই একমুখী চিত্রটা দৃষ্টিকে কিছুটা অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। (তথ্যসূত্র ১)
ক্রিমিয়ার হাসপাতালে মৃত্যুহার কমানর সঙ্গে ফ্লোরেন্সের হাসপাতালের সাধারণ উন্নতির যোগসূত্র কিন্তু তারপরেও বড়কর্তারা বিশেষ মানতে চাইতেন না। আর্মির উচ্চতম ডাক্তার বললেন, হয়ত ঐ হাসপাতালে তখন যারা ভর্তি হয়েছিলেন, তাদের আঘাত কম গুরুতর ছিল, কিংবা তখন আবহাওয়া ভাল ছিল, বা অন্য কোনও ব্যাপার ছিল যেটা বোঝা যায়নি। আপত্তিগুলো কিন্তু কোনোটাই ফেলে দেবার মতো নয়। কিন্তু তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত উপায়গুলোর সাহায্যে এই প্রশ্নের ফায়সালা করা মুশকিল ছিল। তখনও পর্যন্ত ডাক্তারিতে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষ কেউ ভাবতে রাজি ছিলেন না।
এবং এখানেই আসে অঙ্কের প্রশ্ন। ফ্লোরেন্স ছোটবেলায় অঙ্কটা ভালই শিখেছিলেন, এবং তাঁর বাবা অন্তত এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে তৎকালীন ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদেরা ছিলেন। অন্যদিকে, হাসপাতালে বসে ফ্লোরেন্স কেবল সেবাই করেননি, তিনি সেখানকার নানা পরিসংখ্যান সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন। স্কুতারি হাসপাতাল পরিষ্কার করার আগে যেসব রোগী হাসপাতালে ভর্তি হত আর যেসব রোগী কোনও কারণে তাঁদের মিলিটারি ক্যাম্পেই থেকে যেত, তাঁদের মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান তাঁর সংগ্রহে ছিল। তিনি দেখালেন, ক্যাম্পে থাকা সৈন্যদের মৃত্যুহার (শতকরা ২.৭) হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সৈন্যদের মৃত্যুহারের (শতকরা ৪২.৭) চাইতে অনেক কম। এই পরিসংখ্যান দেখলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে পরিষ্কার করার আগে স্কুতারি হাসপাতাল আরোগ্যসদনের চাইতে যমের দক্ষিণ দুয়ারের বেশি কাছাকাছি ছিল। কিন্তু এই একটামাত্র পরিসংখ্যান দিয়ে সব কিছু প্রমাণ হয় না, আর ফ্লোরেন্স সেই চেষ্টাও করেননি।
তাঁর চেষ্টায় পুরো মিলিটারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য একটা রয়্যাল কমিশন তৈরি হয়। সেখানে তিনি কয়েকশ’ পাতার রিপোর্ট জমা দেন। তাতে শুকনো পরিসংখ্যান ছিল, তবে রাজনীতিবিদিদের ধৈর্য ও নতুন জিনিস বোঝার ইচ্ছে বোধহয় সর্বকালে ও সর্বদেশেই কম। ফ্লোরেন্স সেটা জানতেন, সুতরাং তিনি অঙ্কের পাশাপাশি বেশ সুন্দর করে চার্ট এঁকে দিলেন। অঙ্কের ধাক্কায়, বলা ভাল পরিসংখ্যান শাস্ত্রের প্রয়োগের ধাক্কায়, রাজনীতিবিদ ও মিলিটারি কর্তাদের টনক নড়ল। ফৌজি হাসপাতালগুলোতে এক বিপ্লবই এসে গেল যেন। রয়্যাল কমিশনের রিপোর্টের সূত্র ধরে একটি আর্মি মেডিক্যাল স্কুল তৈরি হল, আর তৈরি হল পরিসংখ্যান জোগাড় ও বিশ্লেষণের ধারা।
অবশ্য সৈন্যদলের বাইরেও চিকিৎসায় পরিসংখ্যানের প্রয়োগেও ফ্লোরেন্স পথিকৃৎ। সেই সময় নার্সদের ট্রেনিং দেওয়াকে সময়ের অপচয় মনে করা হত। অবশ্য তার কারণ যেটা দেখান হত সেটা শুনলে আপনারও মনে হবে, সত্যিই তো! টেনিং পাওয়া নার্সদের যত্নে যেসব রোগী থাকত তাদের মৃত্যুহার সত্যিই ট্রেনিং না-পাওয়া নার্সদের যত্নে থাকা রোগীদের চেয়ে বেশি ছিল! ফ্লোরেন্স-ই প্রথম তার কারণটা দেখালেন। তিনি দেখালেন, ট্রেনিং পাওয়া নার্সদের কাছে যায় বেশি অসুস্থ রোগী, আর ট্রেনিং না-পাওয়াদের কাছে যায় কম অসুস্থ রোগী—তাই এমন ফল। ফ্লোরেন্স সমান অসুস্থ দু’দল রোগীর একদলকে ট্রেনিং পাওয়া আর অন্যদলকে ট্রেনিং না-পাওয়া নার্সদের তত্ত্বাবধানে রাখলেন। পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল ট্রেনিং পাওয়া নার্সদের হাতে থাকলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে।
আরেকটা কাজ করে ফ্লোরেন্স ধাত্রীবিদ্যায় বেশ আলোড়ন ফেলেছিলেন। তিনি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান, ইংল্যান্ডে বাড়িতে বাচ্চা জন্মান হাসপাতালে জন্মানর চাইতে বেশি নিরাপদ। এর কারণ বোধহয় এই যে সেই সময়ে বাড়িতে যতটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকত, বেশির ভাগ হাসপাতাল ততটা পরিচ্ছন্ন থাকত না। মনে রাখতে হবে, এর কয়েক বছর আগে কলকাতায় ফিভার কমিটির কাছে প্রতিবেদন রেখেছেন ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত (১৮৩৭ সাল), এবং সেখানে তিনি হিন্দু ধাত্রী ও পরিচারিকা সহ একটি প্রসূতি হাসপাতাল তৈরির সুপারিশ করছেন। (তথ্যসূত্র ২) খুব সম্ভব সেই সময় এদেশে বাড়িতে প্রসবকালীন ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের চাইতে খারাপ ছিল, এবং সেই খারাপ অবস্থার কথা মধুসূদন ঐ প্রতিবেদনে বলেছেন।
ফ্লোরেন্স পরে গবেষণা করে দেখান, শান্তির সময়েও ব্রিটিশ সৈন্যদের মৃত্যুর হার অন্যদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ। এটার জন্য তিনি সেনাব্যারাকের খারাপ স্বাস্থ্যবিধিকে দায়ী করেন। হিসেব করে তিনি দেখান সেনাবাহিনীতে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য কীভাবে অপচয় করা হয়।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁর জীবদ্দশায় অজস্র স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা একজন মানবদরদী মহান নারী ও সেবিকা হিসেবেই চিনেছি। তিনি যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান প্রয়োগের অন্যতম পথিকৃৎ, আর তাঁর সময়ে পুরুষ-প্রধান চিকিৎসা জগতে এমনটা হওয়া খুব কঠিন ছিল, এই কথাটা প্রায়ই হারিয়ে যায়। আজকে যে প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা পরিসংখ্যানের প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার পেছনে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অবদান কারও চেয়ে কম নয়।
চিত্র পরিচিতি
১) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (চিত্রঋণঃ উইকিপিডিয়া)
২) নাইটিঙ্গেলের ব্যবহৃত চার্ট। রয়্যাল কমিশনের সামনে তিনি শুকনো পরিসংখ্যানের পাশাপাশি এইসব ব্যবহার করে রাজনীতিবিদ আর সেনানায়কদের তাঁর কথাগুলো বুঝিয়েছিলেন।
তথ্যসূত্র
১) Simon Singh & Edzard Ernst. Trick or Treatment? Corgi Books, 2008
২) ডা. শঙ্করকুমার নাথ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪