পূর্বপ্রকাশিতের পর
আগের পর্ব শেষ করেছিলাম র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল ওরফে আরসিটি-র সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে – যে পদ্ধতির উপযোগিতা বা যাথার্থ্য বড় অংশের হোমিওপ্যাথ মানেন না। তাঁদের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, আবারও, একটু হ্যানিম্যানসাহেবের কথাতে আসি।
Aphorism 22 : But as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health besides the totality of their signs and symptoms, and likewise medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons; it follows, on the one hand, that medicines only become remedies and capable of annihilating disease, because the medicinal substance, by exciting certain effects and symptoms, that is to say, by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present, to wit, the natural morbid state we wish to cure. On the other hand, it follows that, for the totality of the symptoms of the disease to be cured, a medicine must be sought which (according as experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly, and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptoms) have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms.
ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়, অসুখ থেকে সুস্থতায় ফেরানোর অর্থ অসুখের সামগ্রিক উপসর্গ দূর করা – এর বেশী কিছু নয়। তেমনভাবেই, ওষুধ বলতে এমন উপাদান, যা সুস্থ মানুষের দেহে উপসর্গ তৈরী করবে এবং অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে সেই উপসর্গ দূর করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, এককথায় বলতে হলে, ওষুধ তখনই কার্যকর, যখন তা সুস্থ মানুষের দেহে কৃত্রিমভাবে সেই উপসর্গ তৈরী করতে পারবে, যে উপসর্গ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পথে এসে আরেকজন মানুষের ক্ষেত্রে অসুস্থতার জন্ম দেয়। আরেকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, কোনো অসুখের (যা কিনা কিছু উপসর্গের সমষ্টির বেশী আর কিছু নয়) চিকিৎসার জন্যে যদি ওষুধ খুঁজতে হয়, তাহলে খুঁজতে হবে এমন উপাদান, যা সুস্থ মানুষের শরীরে অনুরূপ উপসর্গের জন্ম দিতে পারে।
কথাটা খুব নতুন কিছু নয়। হিপোক্রেটিস প্রায় একই কথা বলেছিলেন –
“By similar things a disease is produced and through the application of the like is cured”
অর্থাৎ, যে উপাদান সুস্থ মানুষের দেহে আলোচ্য অসুখ তৈরি করতে পারবে, সেই একই উপাদান অসুস্থ মানুষের অসুখ সারিয়ে তুলবে।
সমস্যাটা এই, হিপোক্রেটিস কথাটা বলেছিলেন খ্রীষ্টজন্মের চারশো বছর আগে – আর হ্যানিম্যান বললেন হিপোক্রেটিসের দুহাজার বছরেরও বেশী সময় বাদে – যার মধ্যে চিকিৎসার পিছনে যে অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, তা এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা, যদিও কার্যকরী চিকিৎসার খোঁজ তখনও সেভাবে মেলেনি।
অবশ্য, সেই সময়ের চিকিৎসাদর্শনে একই উপসর্গ তৈরী করে নিরাময় আবিষ্কারের চেষ্টাটা, অর্থাৎ এই লাইক-কিওর্স-লাইক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা ছিলই। ঠিক কোন পথে এগিয়ে হ্যানিম্যানের সমকালীন এডওয়ার্ড জেনার গুটিবসন্তের টীকা তৈরী করেছিলেন, এই মুহূর্তে বসে তা অনুমান করা কঠিন – কিন্তু, সেই টীকা আবিষ্কারের পিছনে যে দর্শন শেষমেশ কার্যকরী হয়েছিল, তার সাথে হ্যানিম্যানের ভাবনার মিল ছিল লক্ষ্যণীয় – যদিও, জেনারের টীকা আবিষ্কার আর হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের মধ্যে একটা বড়সড় ফারাক ছিল – জেনার খুঁজছিলেন প্রতিষেধক আর হ্যানিম্যান বলছিলেন ওষুধের কথা। তবে, সুস্থ দেহে উপসর্গ সৃষ্টিকারী উপাদানই কার্যকর ওষুধ, এই দর্শনের পুনরুদ্ধারের মুহূর্তে হ্যানিম্যান জেনারের সাফল্যের দ্বারা ঠিক কতোখানি উদবুদ্ধ হয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ আন্দাজ পাওয়া দুরূহ।
Cure and Prevention of Scarlet Fever বইয়ের ভূমিকায় হ্যানিম্যান লেখেন –
It is the only in accordance with my well known maxim (the new principle) that small-pox, to give one example from among many, had an important prophylactic in the cow-pox, which is an exanthematous disease, whose pustules break out after the sixth day of inoculation, with pain and swelling of the axillary glands, pain the back and loins, and fever, and surrounded by an erythematous inflammation – that is to say, constitute altogether a disease very similar to variola. And in like manner, medicine which causes symptoms so similar to those of the invasion of scarlet-fever, as belledona does, must be one of the best preventive remedies for this children’s pestilence.”
হ্যানিম্যানের কথাটুকু সংক্ষেপে অনুবাদ করতে গেলে দাঁড়ায় – এই (লাইক-কিওর্স-লাইক) তত্ত্বের (অর্থাৎ সুস্থ দেহে সম-উপসর্গ উৎপাদনে সক্ষম বস্তুই অসুস্থের ক্ষেত্রে ওষুধ) সমর্থনে দেখানো যেতে পারে, গুটিবসন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক পাওয়া গেল কাউ-পক্স-এর হাত ধরে – কেননা, অসুখদুটোর উপসর্গ খুব কাছাকাছি। ঠিক একইভাবে, যে ওষুধ সুস্থ মানুষের স্কারলেট-ফিভারের মত উপসর্গ তৈরী করবে – যেমন বেলাডোনা করে থাকে – তা এই অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।
মাথায় রাখা যাক, হ্যানিম্যান এই কথা যখন লিখছেন, অর্গ্যাননের প্রথম সংস্করণ বাজারে আসতে তখনও বাকি প্রায় এক দশক। অতএব, জেনারের সাফল্য হ্যানিম্যানকে নিজের তত্ত্বের ব্যাপারে বাড়তি আস্থা জুগিয়েছিল, এটুকু নিশ্চিত।
সেই সময়ের বিচারে এই তত্ত্বের মূল কথাটুকু আলাদা করে খুব বিভ্রান্তিকর নয় – আরো একবার বলে নেওয়া যাক, হ্যানিম্যান এক ইতিহাসের মানুষ – এবং যেকোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের মতোই তিনিও তাঁর সময়ের ফসল – তাঁর তত্ত্বের মূল উপপাদ্যও, বৈপ্লবিক হলেও, দোষগুণ মিলিয়ে তা-ই – বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চিন্তাপদ্ধতিও, সমকালীন চিন্তার যে গ্রাহ্য প্যারাডাইম, তার বাইরে চট করে যেতে পারে না। পাশাপাশি এও মনে রাখা যাক, জেনারের আবিষ্কার প্রসঙ্গে হ্যানিমান যত উচ্ছ্বসিতই হোন না কেন, অসুখের প্রতিষেধক ও অসুখের চিকিৎসা একই পথে কাজ করে না। প্রতিষেধক সুস্থ মানুষের জন্যে প্রযোজ্য – ওষুধ অসুস্থদের জন্য। মুখে খাওয়ানোর পোলিওর টীকার মাধ্যমে শরীরে যায় অসুখ সৃষ্টিতে অংশত অক্ষম পোলিও ভাইরাস – কিন্তু, পোলিও রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব নেই। তবু, সময়ের প্রেক্ষিত ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানের তৎকালীন শৈশবদশার কথা মাথায় রেখে, হ্যানিম্যানকে নিয়ে আমার সমস্যা নয় – আমার অনুযোগ তাঁদের নিয়েই, যাঁরা সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে সমকালে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করে চলেছেন।
তত্ত্বকে এরূপ অপরিবর্তনীয় ধরে এগোনোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার দিকে চোখ রাখা যাক। হ্যানিম্যানের কয়েক দশকের মধ্যেই লুই পাস্তুর এনে ফেললেন তাঁর জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ – অসুখের জীবাণু তত্ত্ব – যে তত্ত্ব অনুসারে রোগের পিছনে দায়ী বহিরাগত জীবাণু। হ্যাঁ, এই তত্ত্বের কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং পাইকারি হারে এ তত্ত্বের প্রয়োগ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ব্যাপারটাকে আক্রমণাত্মক চিকিৎসার সাথে একাকার করে ফেলতে সহায়ক হয়েছে – কিন্তু, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই – মোটের উপর একথা অনস্বীকার্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে জার্ম থিওরির মতো বৈপ্লবিক ও প্রভাবশালী তত্ত্ব খুব কমই এসেছে। হ্যানিম্যানের উত্তরসূরীরা এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে নিজেদের চিকিৎসাদর্শনের ঠিক কী বদল এনেছিলেন? বা কী বদল এনেছেন??
উনিশশো শতকের শেষদিকেই জার্ম থিওরিকে আরো সংহত চেহারা দিলেন রবার্ট কখ। জীবাণুঘটিত অসুখের ক্ষেত্রে তাঁর চারখানি বিখ্যাত পসচুলেটস বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় –
১. জীবাণুঘটিত অসুখের ক্ষেত্রে অসুস্থ মানুষের শরীরে জীবাণু পাওয়া যেতে হবে এবং সুস্থ মানুষের দেহে সেই জীবাণু পাওয়া যাবে না।
২. অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে সেই জীবাণুকে আলাদা করা যাবে এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম মাধ্যমে (artificial culture) সে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভবপর হবে।
৩. কৃত্রিম মাধ্যমে বংশবিস্তারের পর সেই জীবাণু সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করানো হলে, সেই সুস্থ মানুষটিও রোগে আক্রান্ত হবেন।
৪. কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত মানুষটির দেহ থেকে আবারও আলাদা করা যাবে এবং সেই জীবাণুকে পুনরায় গবেষণাগারের কৃত্রিম মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভবপর হবে – আর এই দফায় বংশবৃদ্ধি করা জীবাণু ও প্রাথমিকভাবে যে জীবাণু নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল, দুটি অভিন্ন হতে হবে।
এই তত্ত্বকে মান্যতা দিতে হলে হ্যানিম্যানের মূলগত বক্তব্য কোথায় দাঁড়ায়? ধরুন, কখ-এর তৃতীয় উপপাদ্য মানতে চাইলে?? অর্থাৎ, সুস্থ মানুষের দেহে অসুখ ও তৎসংক্রান্ত উপসর্গ সৃষ্টির সেরা ও সরলতম পথ তো তাঁর শরীরে সেই রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলে কি সংক্রামিত ব্যক্তির শরীরেও আরো খানিকটা জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া কার্যকরী নিরাময়ের পথ হিসেবে গণ্য হবে?? জীবিত ব্যাকটেরিয়াকে ঔষধ-উপাদান হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি থাকলে, আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক – ধরুক খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে সেই টক্সিন-যুক্ত খাদ্য আরো কিছুটা দেওয়া গেলে তিনি কি সুস্থ হয়ে উঠবেন (কেননা, সেই খাদ্য সুস্থ মানুষকে খাওয়ানো গেলে তাঁরও বমি-পায়খানা ইত্যকার উপসর্গ নিশ্চিত)?? না, ব্যাপারটাকে আমি হাস্যকর এঁড়ে তর্কের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছি না – কিন্তু, জার্ম থিওরির পরবর্তী সময়ে লাইক-কিওর্স-লাইক-এর তত্ত্ব কি একইভাবে বিশ্বাসযোগ্য থাকতে পারে?? এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি সাজানোর সুযোগ হ্যানিম্যান পাননি – কেননা, জার্ম থিওরি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার আগেই আগেই তিনি মারা গিয়েছেন – কিন্তু, গত সোয়াশো বছর ধরে হোমিওপ্যাথির গবেষকেরা কী বলছেন??
হোমিওপ্যাথি ওষুধের কার্যকারিতা যাচাই হয় সুস্থ মানুষের দেহে – যার প্রথাগত নাম প্রুভিং। সরল কথায় ব্যাখ্যা করতে হলে, এই প্রুভিং-এ সুস্থ মানুষের দেহে ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা হয়, তা অসুখের তুল্য উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারছে কিনা – হোমিওপ্যাথির দর্শন মানলে, যে ওষুধ সুস্থ দেহে উপসর্গ সৃষ্টিতে সক্ষম, সেই ওষুধ অসুস্থের শরীর থেকে অনুরূপ উপসর্গ দূর করতে অবশ্যই কার্যকর – স্বভাবতই, অসুস্থ শরীরে কার্যকারিতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা, আলাদাভাবে, থাকে না।
দ্বিতীয়ত, একই উপসর্গের সমষ্টি অর্থাৎ একই ব্যাধির ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে সবসময় যে একই ঔষধ প্রযোজ্য হবে, এমন কথা নেই। হ্যানিম্যানের কথা মনে রাখুন, রোগীর কী অসুখ হয়েছে জানার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঠিক কী ধরণের মানুষটির অসুখ হয়েছে। কাজেই, ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যেমন হয়, অসুস্থ মানুষদের দুভাগে ভাগ করে একদল একই ওষুধ পাবেন, আরেকদল আরেকপ্রকার ওষুধ পাবেন (অথবা কোনো ওষুধই পাবেন না – প্লাসিবো-কন্ট্রোলড ট্রায়াল) – ঠিক সেই পদ্ধতি একইভাবে অনুসরণ করা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে মুশকিল। যদিও, আরসিটি-র বিপক্ষে তাঁদের এই যুক্তি মানতে হলে, একদল মানুষের উপর প্রযুক্ত প্রুভিং-এর তথ্য কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠবে (হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে যেকোনো ওষুধই তাই – তারপরে সে তালিকা থেকে কোনটি আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তা বেছে নিয়ে প্রয়োগ করা), সে নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়।
তাহলে, তাঁদের চিকিৎসা যে সত্যিসত্যিই কার্যকরী, হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুরা সেটা ঠিক কীভাবে প্রমাণ করবেন?
সচরাচর তাঁরা ব্যক্তি-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখেন – অর্থাৎ একইধরণের রোগীর ক্ষেত্রে সে ওষুধ প্রয়োগ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথিতযশা হোমিওপ্যাথরা ঠিক কীধরণের কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছেন, সেই লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা। সমস্যা হল, অনুরূপ অভ্যাস অনুসরণ করে, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে, ব্যক্তি চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, সে যত প্রগাঢ়ই হোক না কেন, তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে – এবং তা প্রায়শই অনির্ভরযোগ্য। এই শতকে চিকিৎসার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যক্তি-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার কদর বেশ কমেছে। হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবুদের চলার পথটি ঠিক কী হবে?
আজ যখন বিশ্বজুড়ে একের পর এক ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং সেই ট্রায়ালের তথ্য জুড়ে মেটা-অ্যানালিসিস থেকে বলা হচ্ছে, প্লাসিবোর (যাকে সান্ত্বনা-চিকিৎসা বলা যেতে পারে) চাইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাড়তি কোনো সুবিধেই নেই – যখন বিভিন্ন দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ভিত্তিহীন ও অকার্যকরী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে – তখন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদেরই দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য, ঠিক কোন পথে তাঁদের চিকিৎসার নৈর্ব্যক্তিক কার্যকারিতা যাচাই করা যায়, সে বিষয়ে আরো গভীরে গিয়ে ভাবা – এবং তদনুযায়ী যাচাই-লব্ধ তথ্য সর্বসমক্ষে পেশ করা যায়।
(পরবর্তী পর্বে সমাপ্য)






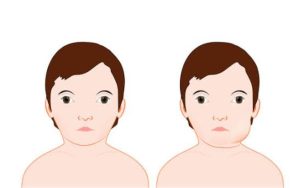
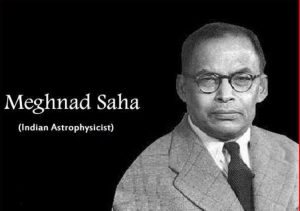






অবশেষে আলোচনাটা সেই পথে এসে পড়ল যেটা আশা করেছিলাম, এবং হোমিওপ্যাথির বেসিক জায়গাটা বুঝতেই যে একটা বড় ফাঁক থেকে গেছে সেটাও প্রকাশ হল। ঠিক এই কারণেই প্রথম দিন বলেছিলাম অর্গ্যানন পাঁচ বছর ধরে পড়ার পরও অনেক জায়গা প্রশ্ন থেকে যায়, সেখানে কিছু ভাসা ভাসা আলোচনা করে এর ভেতরে ঢোকা একপ্রকার অসম্ভব। প্রতিটি aphorism ফুটনোট সহ খুঁটিয়ে না পড়লে কিছু ওপর ওপর আলোচনা করলে বিশেষ কোন লাভ নেই। যাই হোক ছোট করে কয়েকটা কথা বলে যাই। জেনারের ভ্যাক্সিন তত্ত্ব যে হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের সঙ্গে এক নয় এটা হ্যানিম্যান নিজেও জানতেন, এইজন্য অর্গ্যাননে উনি Isopathy বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেন।
A third mode of employing medicines in diseases has been attempted to be created by means of Isopathy, as it is called – that is to say, a method of curing a given disease by the same contagious principle that produces it. But even granting this could be done, yet, after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized, and consequently, in an altered condition, the cure is effected only by opposing a simillimum to a simillimum.- aph 56 (footnote).
ছোট করে জানিয়ে যাই এই অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি অ্যান্টিপ্যাথি এই শব্দগুলি হ্যানিম্যানেরই তৈরি করা। আর আজকে যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে অ্যালোপ্যাথি বলা হয় তাকে হ্যানিম্যান আদৌ অ্যালোপ্যাথি বলেন নি, এই পদ্ধতিকে উনি বলেছিলেন অ্যান্টিপ্যাথি, কিন্তু কোন কারণে অ্যালোপ্যাথি কথাটাই চলে এসেছে। আর এই Antipathy কে উনি কোনভাবেই নাকচ করেন নি, বরং ওনার বক্তব্য ছিল, যে দুটি চিকিৎসা পদ্ধতি সরাসরি রোগের বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম তার একটি হোমিওপ্যাথি ওপরটি অ্যান্টিপ্যাথি যা আজ তথাকথিত মডার্ণ মেডিসিন নাম নিয়েছে। Antipathy কোন কোন জায়গায় অপরিহার্য তাও হ্যানিম্যান অর্গ্যাননে স্পষ্ট করে বলে গেছেন। শুধু ওনার বক্তব্য ছিল antipathic মেথডে সাময়িক আরাম মিললেও দীর্ঘমেয়াদী ফল পাওয়া সম্ভব নয় এবং দীর্ঘদিন ওষুধ চালিয়ে গেলে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আসবে, যা অন্য রোগের জন্ম দেবে শরীরে। এবিষয়ে আশা করি আজও কেউ দ্বিমত হবেন না। বস্তুত বর্তমান antipathic চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে হোমিওপ্যাথির কোন বিরোধ তো নেইই বরং হ্যানিম্যানের কথা ধরলে এরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে পারে, যা মানুষের জন্য এক অত্যন্ত উন্নত এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্হার জন্ম দেবে। তবু কিছু মানুষ কেন জানি না একটা মনগড়া বিরোধ শুধু নয় বিরোধিতার নামে নোংরামি করেন, যাই হোক সেপ্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।
এবার আসি পরের অংশে যেখানে বলা হচ্ছে একটা বিষ আটকাতে সেই বিষই কী আবার খাইয়ে দেওয়া হবে রোগ আটকাতে?? এই জায়গাটা সবচেয়ে বড় ভুল যা হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে চলে আসছে। আদপেই ব্যাপারটা বিষে বিষক্ষয় নয়, কখনোই পোলিও সারাতে পোলিওর ভাইরাস খাওয়ানো হবে না। কখনোই হোমিওপ্যাথি একথা বলেনা যে কাউকে সাপে কামড়ালে তাকে আবার সাপের বিষই খাওয়াতে হবে। এখানে similar আর same এই দুটোর পার্থক্য খুব ভাল করে বুঝতে হবে, যেটা এই পরিসরে লিখে বোঝানো অসম্ভব, অর্গ্যাননের দু তিনটে ক্লাস খরচ হয়ে যায় এই জায়গাটা বোঝাতে। তাই অনর্থক সে চেষ্টা করে লাভ নেই।
আর রইল বাকি RCT বা ভাইরাস বা অণুজীবের ওপর ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে, তো তাই নিয়ে গবেষণা হয়েছে, চলছে, ইচ্ছা আছে এই নিয়ে লেখার, কয়েকটা পেপার পড়তে হবে, তারপর যদি লিখি তো সেখানেই আলোচনা করা যাবে।
একদম সঠিক উত্তর,উনি উপর উপর পড়েছেন,কিন্তু কোনো কিছু ভাবেন নি,ধন্যবাদ ভুল টা ঠিক ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।
হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশ এটাই – আলোচনার শেষে জ্ঞানীগুণী হোমিও ডাক্তারবাবুরা বলবেন – ওই জায়গাটা আপনি বুঝতে পারেননি, আমাদেরই বুঝতে এত সময় লেগেছিল!!
অথচ, বারো ক্লাসের বায়োলজি পাশ করেই ডাক্তারি পড়া যায় – তুলনায় চূড়ান্ত মেধাবীরা হোমিওপ্যাথি বেছে নেন সম্ভবত – তবুও মেনে নেওয়া যাক, বারো ক্লাসের বায়োলজি পাঠের বিদ্যে নিয়েই অর্গানন পাঠ শুরু করা যায় – অন্তত ওঁরা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই শুরু করেন।
একমাত্র মাদ্রাসা ছাড়া আর কোথাওই পুরো কারিকুলাম জুড়ে একখানি কেতাবই পড়িয়ে চলার উদাহরণ নেই – এখন জানলাম, হোমিওপ্যাথিতেও ব্যাপারটা সেরকম – পাঁচবছর ধরে আনুষঙ্গিক ডাল-তরকারির সাথে মূল আইটেম সেই অর্গানন।
স্বাভাবিক – অত গভীরে গিয়ে পড়া হয়নি আমার।
মুশকিল আরেক, ওনাদের বারবার বলছি একখানা লেখা সাজিয়েগুছিয়ে লিখে দিন – আমরা এই ডক্টর্স ডায়ালগেই প্রকাশ করব – কিন্তু, সেও ওনারা করবেন না। বললেই পিছলে যান – বলেন, সময় নেই – অথবা, এই বিশাল জ্ঞানসাম্রাজ্যের কতটুকু জানি ইত্যাদি ইত্যাদি।
অথচ, ওনাদের সাবজেক্টখানা আদপেই বিজ্ঞান কিনা, সে নিয়ে লিখতে গেলে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হোমিও হয়ে উঠতে হয় না, এ জানার জন্যে মায়াজম-তত্ত্বে গভীর দক্ষ না হলেও চলে।
অবশ্য, আজ এক হোমিও গবেষক শেষমেশ জানালেন – হোমিওপ্যাথির অনেককিছুই অধ্যাত্মচর্চার সমতুল – এবং হোমিও ঔষধ তুচ্ছ অণু-পরমাণুর হিসেবনিকেশের উর্দ্ধে।
পূর্বতন দুজন হোমিও ডাক্তারবাবু যদি সেকথায় সমান আস্থাশীল হন, অর্থাৎ এই বিদ্যা প্রায় আধ্যাত্মিক ও তুচ্ছ জাগতিক রসায়নের উর্দ্ধে, তাহলে তাঁদের সাথে আর কথা বাড়ানোর মানে হয় না। আর যদি ওই হোমিওপ্যাথি গবেষকের সাথে সহমত না হন, তাহলে এখুনি ওনার কথার প্রতিবাদ করুন।
আশা করি, এক্ষেত্রে অন্তত সময়ের অভাবের অজুহাত দেবেন না।
Excellent !!!
আপনাদের অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে ।
সেম অর সিমিলার এর পার্থক্য বোঝেন।
আমার এতদিন ধারণা ছিল আপনারা অনেক জ্ঞানী কিন্তু এই বাচ্চা হাস্যকর পোস্ট গুলো দেখে আপনাদের সম্বন্ধে ধারণা আমার পাল্টে গেছে হ্যানিম্যান সাহেব কোথাও বলেননি সেম ওষুধ খাওয়ানোর জন্য বলেছেন সিমিলার ।
কারুর পক্স হয়েছে বলেই তাকে পক্সের জীবাণুর হোমিওপ্যাথি দেখানো হয় না এরকম মূর্খের মত পোস্ট করবেন না মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।
আর খুব jerm theory দিচ্ছনযে। অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই আপনার ওই থিওরি ফেল ,যেমন ধরুন একটি মানুষ শ্বাসকষ্টে ভুগছে আপনারা যে প্যাথলজিতে বলছেন তার কোন যন্ত্র শ্বাসকষ্টের jerm খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু রোগী সুস্থ হচ্ছেন না আপনাদের কাছে সব পয়সা শেষ করে সর্বশান্ত হয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছে, সে তার মানসিক পারিবারিক ইতিহাস জেনে জানলো মানসিক আঘাত তার মধ্যে আছে হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতি মেনে ওষুধ দিল রোগী সুস্থ থাকলো এখানে jerm কোথায় ? হোমিওপ্যাথিক এপ্লাইড ভালো করে একটু পড়বেন। একটি মানুষ অসুস্থ হলে তার সামগ্রিক চিত্র অনুরূপ অসুস্থতা তৈরি করে এমন কোন প্রাকৃতিক উপাদান তাকে দেওয়া হয় তা কোনদিনই সেম নয় ।crude material নয়।
প্রামাণিকবাবুর germ-এর বানান দেখেই জ্ঞানের গভীরতার চমৎকার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বস্বান্ত বানানটিও অভিনব।
দুই ভাষাতেই এমন অসামান্য দখল বড় একটা চোখে পড়ে না।
বাকি বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।