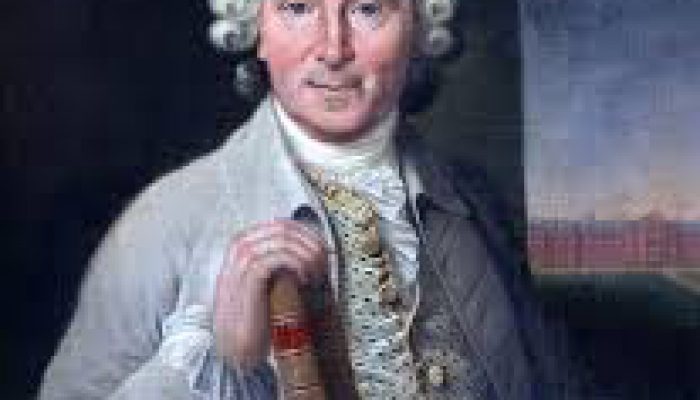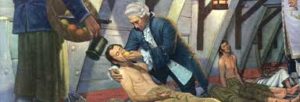সে বড় সুখের সময় নয়, অন্তত বৃটেনের পক্ষে। ফ্রান্সে তখন নেপোলিয়ানের রাজত্ব। তিনি ব্রিটেন আক্রমণের ছক কষছেন। ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সামনে ইংরেজ সেনাবাহিনী দাঁড়াতে পারবে না। ব্রিটেনের একমাত্র আশা, যদি বিভিন্ন বন্দরেই ফরাসী আর তাদের সঙ্গে থাকা স্প্যানিশ নৌবহরকে আটকে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বা হবে কী করে? ফরাসী নৌবহরকে বোতলবন্দী করে রাখতে গেলে ইংরেজদের জাহাজগুলোকে পাঠাতে হয় দূরে। কিন্তু কিছুদিন দূরে থাকবার পরেই নৌসেনা আর নাবিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ে—মাড়ি ফুলে গিয়ে রক্ত বেরোয়, দাঁত পড়ে যায়, হাঁটু ফোলে, পা দুটো যায় দুর্বল হয়ে, চামড়ায় লাল-লাল দাগ হয়ে যায়। কোনও কাজেই লাগতে পারে না তারা।
তবে ব্রিটিশ নৌবহর কাজটা করতে পেরেছিল। স্পেনের ক্যাডিজ-এর কাছে ফরাসি ও স্প্যানিশ নৌবহরকে বোতলবন্দী করে রেখেছিল বৃটিশ রয়্যাল নেভি। (তথ্যসূত্র ১) না পারলে বিশ্বের ইতিহাসটা অনেকটা অন্যরকম হতো। আর ভারতের ইতিহাস? তাতেও হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারত—অবশ্য সেটা ১৮০৫ সাল, ততদিনে ভারতেও ইংরেজ আর ফরাসীদের সাম্রাজ্য দখলের লড়াই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কথায় না গিয়ে, আসুন আমরা ব্রিটিশ নৌসেনাদের অবস্থা দেখি।
শুধু ব্রিটিশ কেন, সে সময়ে সমস্ত নৌসেনা আর নাবিকদের বড় সমস্যা ছিল এই অসুখ, আমরা এখন যার নাম জানি স্কার্ভি। ১৪৯৮ তে ভাস্কো দা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসেন, আর ঐ সময় থেকেই প্রথম এই রোগ আর তাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মেডিক্যাল রেকর্ড পাওয়া যায়। ভিটামিন ‘সি’ এর অভাবে এই রোগ হয়। ভিটামিন ‘সি’ আমাদের দেহের কোলাজেন তন্তু তৈরি করতে অপরিহার্য। আর কোলাজেন দিয়েই আমাদের রক্তনালী, পেশি, চামড়া — এ সবের ভেতরকার বাঁধন তৈরি। কোলাজেনের অভাবে রক্তনালীগুলো ফেটে যায়, চামড়া, পেশি ইত্যাদি যায় ভঙ্গুর হয়ে। আজ আমরা এসব জানি বটে, কিন্তু ১৮০৫ সালে অত কিছু জানা ছিল না। তবু ব্রিটিশ নৌসেনা আর নাবিকদের যে স্কার্ভি আক্রমণ করতে পারে নি, তার কারণ হলেন এক অন্যরকম স্কটিশ নৌ-ডাক্তার জেমস লিন্ড। তাঁর আগে পর্যন্ত ডাক্তাররা স্কার্ভি সারানোর নানারকম চিকিৎসা করেছেন–রক্তমোক্ষণ (যেটা সেকালে সব কিছুতেই করা হত), পারদ, ভিনিগার, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এমনকি রোগীদের খুব করে খাটানোও একটা চিকিৎসা বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এসব চিকিৎসায় বরং রোগীর ক্ষতি হয়েছে, উপকার হয় নি।
১৭৪৭ সাল, বাংলায় পলাশির যুদ্ধের দশ বছর আগে, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসতে তখনও বাকি পাঁচ দশক। ডাক্তার জেমস লিন্ড এইচএমএস সালিসবারি নামের রয়েল নেভির জাহাজে করে বহুদূর যাচ্ছিলেন। পথে যথারীতি অনেক নাবিকের স্কার্ভি হল। লিন্ড প্রথমে চালু চিকিৎসার কোনও একটা দিতে চাইছিলেন, কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি লোকটা ছিলেন একটু অন্যরকম। ভাবলেন, জানা ওষুধ যখন ধরছে না, তখন একটু পরীক্ষা করিই না কেন?
স্কার্ভিতে ভোগা নাবিকদের মধ্যে ১২ জনকে বেছে নিলেন তিনি। খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, সবার রোগের মাত্রা মোটামুটি একই রকম। তাঁদের প্রত্যেককে একই রকম খাবার দিলেন, তাঁদের বাসস্থানও যেন একই রকম হয়, সেটা নিশ্চিত করলেন। এবার ৬টা দলে ভাগ করলেন তাঁদের, প্রতি দলে দুজন নাবিক। প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদা ‘ওষুধ’ দিলেন। প্রথম দল পেল প্রতিদিন এক কোয়ার্ট ‘সিডার’। দ্বিতীয় দল পেল প্রতিদিন ২৫ ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণ, তৃতীয় দল দু’চামচ করে ভিনিগার, চতুর্থ দল আধ পাঁইট করে সমুদ্রের জল, পঞ্চম দল রসুন-সর্ষে ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটা ওষুধ, আর ষষ্ঠ দল পেল দুটো করে কমলালেবু আর একটা করে লেবু। এবার এদের স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করার পাশাপাশি, আরও একদল স্কার্ভি আক্রান্ত নাবিকের স্বাস্থ্যের নিয়মিত পরীক্ষা করে চললেন লিন্ড–শেষের দলের নাবিকরা কিন্তু কোনোরকম আলাদা ‘চিকিৎসা’ পেলেন না। লিন্ডের ইচ্ছে, চোদ্দদিন ধরে নাবিকদের ওপর পরীক্ষা চালাবেন। কিন্তু ছ’দিনের মাথায় তিনি জানতে পারলেন, আর লেবু জাহাজের ভাঁড়ারে নেই। বাধ্য হয়ে পৃথিবীর প্রথম ‘কন্ট্রোলড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’-এর ইতি টানলেন তিনি। কিন্তু তাতে বড় বেশি অসুবিধা হল না, কেন না কমলালেবু-লেবু খাওয়া নাবিকদের রোগ ইতোমধ্যেই প্রায় সেরে গেছে, ‘সিডার’ খাওয়া নাবিকদের অবস্থা সামান্য ভাল, আর বাকি সবার অবস্থার অবনতি হয়েছে। (তথ্যসূত্র ২)
আমরা আজ জানি, লেবু জাতীয় ফলে অনেক ভিটামিন ‘সি’ থাকে, সুতরাং স্কার্ভি তাতে সারবে। কিন্তু সে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে অনেক পরে, ডাক্তার লিন্ড-এর সেটা জানার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আমরা এবার দেখব, তাঁর পরীক্ষার ফল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর পরীক্ষা-পদ্ধতি তেমনই, বা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
কিন্তু জেমস লিন্ড যখন আবিষ্কারটা করছেন, তখনও ইউরোপে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক উন্নতি আনাচেকানাচে ছড়িয়ে যায় নি। বিভিন্ন ভদ্রলোক ন্যাচারালিস্ট নানা সোসাইটি তৈরি করে তাতে নিজেদের গবেষণা নিয়ে আলোচনা সবে শুরু করছেন। কিন্তু লিন্ড সেই পরিবেশের লোক নন। জাহাজে নাবিকদের ডাক্তার, পদমর্যাদায় তেমন কিছু নন। ফলে এইসব সোসাইটিতে তাঁর পাত্তা পাওয়া শক্ত। ১৭৪৭ সালের বছর ছয়েক পরে তিনি নিজেই একটা বই লিখলেন। বইটা যথাযোগ্য সমাদর পেলে কী হত বলা যায় না—কারণ এর কয়েক বছর পরে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ শুরু হয়, ফ্রান্স-বৃটেনের সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধ। ১৭৬৩ সালে সেই যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায় বৃটিশ তরফে সৈন্য মারা গেছে এক লক্ষের কিছু বেশি। এর মধ্যে এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে স্কার্ভি রোগে। আর মাত্র দেড় হাজার সৈন্য মরেছে যুদ্ধক্ষেত্রে!
কিন্তু লিন্ডের বইটা কেউ নজরই করল না। একে অখ্যাত লেখক, তার ওপরে ৪০০ পাতার অকারণ মেদবহুল বই—কে আর দেখবে। দেখলেও খুব কদর করত এমন মনে হয় না, কারণ লিন্ড সরাসরি লেবু বা কমলালেবু না খাইয়ে তার ঘন করা রস খাওয়াতে বলেছিলেন। ভেবেছিলেন একগাদা ফলের বদলে ঘন রস হলে জাহাজে সহজে নেওয়া যাবে। কিন্তু রস তৈরির জন্য যে জ্বাল দেবার প্রক্রিয়া, তাতে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই লিন্ডের পদ্ধতি কেউ অনুসরণ করে থাকলেও ফল ভাল হবার কথা নয়। এবং আবিষ্কারের দশ বছর পরে সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে এক লক্ষ বৃটিশ সৈন্যের মৃত্যু আটকাতে লিন্ডের আবিষ্কার কাজে লাগেনি।
সৌভাগ্যক্রমে লিন্ডের আবিষ্কারের বছর ত্রিশ-চল্লিশ পরে ডাক্তার গিলবার্ট ব্লেন-এর চোখ পড়ল লিন্ডের বইয়ের দিকে। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে বৃটেনের সঙ্গে স্পেনের উপনিবেশ দখলের লড়াই চলছে—মূলত নৌযুদ্ধ। ডা. ব্লেনের ওপর নৌসেনাদের দেখাশোনার ভার। বারো হাজার নৌসেনার মধ্যে ষাটজন মারা পড়ল যুদ্ধে, আর দেড়হাজার জন মারা পড়ল রোগে—অধিকাংশই স্কার্ভি। তাদের খাবারে লেবু যোগ করলেন ব্লেন—ফল মিলল হাতেনাতে—রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। পরে বড় লেবুর বদলে ছোট লেবু বা লাইম (Lime) দেওয়া হতো, আর তাই থেকে বৃটিশ নৌসৈন্যদের ডাকনাম হয়ে গেল ‘লাইমি’।
এখনও বৃটিশদের ডাকনাম লাইমি। আর, এখনও স্কার্ভি আটকানোর মূল পথ লেবুজাতীয় ফল খাওয়া।
চিত্র পরিচিতি (কেবলমাত্র অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য)
১। জেমস লিন্ড
২। জেমস লিন্ডের পরীক্ষার কল্পিত চিত্র
তথ্যসূত্র
১. How the British defeated Napoleon with citrus fruit. Andrew George. The Conversation. May 19, 2016 https://theconversation.com/how-the-british-defeated-napoleon-with-citrus-fruit-58826
২। Trick or Treatment: Alternative Medicine on Trial. Simon Singh & Edzard Ernst. Corgi Books, 2009.
৩। How Wars Are Won: The 13 Rules of War from Ancient Greece to the War on Terror. Bevin Alexander. Crown Publishers, 2002