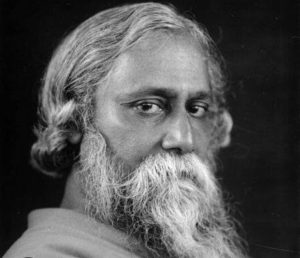স্কুল থেকে ফিরেই প্রত্যয় বুঝল আজও গোলমাল হয়েছে। নইলে বাবা বিকেলবেলা বাড়ি ফিরেছে কেন? কাজের জায়গায় গোলমাল শুরু হবার পর থেকে বাবা রোজ আরও দেরি করে বাড়ি ফেরে। আজকাল প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ই হয় না, শনিবার-রবিবার করে বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখা, খেলতে যাওয়া, এমনকি পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে গেছে। মা-বাবার কথায় যতটা বুঝেছে, বাবার বন্ধুরা — সব্যসাচী আঙ্কল আর সৌমিত্র আঙ্কল, ব্যবসাটা চালাতে পারছে না। বাবাকে বলতে শুনেছে, বিলেত থেকে ফিরে ভেবেছিল ওদের একটু সাহায্য করলেই হবে, তাই ব্যবসায় অনেক টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যবসা চলেনি। শুনেছে বাবা বলছে, “ওদের দ্বারা হবেই না। এটা আগে আন্দাজ করলে এতগুলো টাকা দিতাম না…” শুনেছে, সোমিত্র আঙ্কলের মেয়েকে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে বের করে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। শৈলী নাকি সে দিন থেকে আর বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। প্রত্যয়েরও আজকাল ভয় করে। যদি ওকেও এমন কোনও স্কুলে ভর্তি হতে হয়? ও অবশ্য আজ অবধি অনেক স্কুলেই পড়েছে, ইংল্যান্ডেই তো তিনটে। তবে আর যাই হোক, বাবা এর আগে কখনও এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে আসেনি।
প্রত্যয় একটু অপেক্ষা করল। একটা বুদ্ধি এসেছে। চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে উঠলে মা-বাবার কথা শোনা যেতে পারে। এভাবে আড়িপাতা উচিত না, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী? মা-বাবা তো ওকে কিছু বলছেই না। এমনকি ক-দিন আগে বাবা একটানা বারো দিনের জন্য কোথায় চলে গেছিল, মা ওকে কিছু বলেইনি। ভয়ে প্রত্যয় রোজ কেঁদে কেঁদে ঘুমোত। মনে হত, ইংল্যান্ডে জিমির বাবা যেমন চলে গিয়েছিল সবাইকে ফেলে, আর আসেনি, তেমন বাবাও যদি আর কোনওদিন… তবে বাবা ফিরে এসেছিল। যদিও ফিরে এসে বলেনি কিছুই। গম্ভীর মুখে, সকালে খাবার টেবিলে প্রত্যয়কে পড়াশোনা ঠিক মতো হচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করে অফিস চলে গিয়েছিল।
দুজনকে কতদিন হাসতে দেখেনি প্রত্যয়! এর আগে বাড়িটা সারাদিন হাসাহাসিতে ভরা থাকত। সেদিন স্কুলের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে হাসতে হাসতেই প্রত্যয় ফিরেছিল। মাকে বলতে যাওয়ামাত্র মা কেমন গম্ভীর গলায় বলেছিল, “আচ্ছা, এখন এসো, নোনতা সুজি করেছি, খেয়ে নাও।”
ফলে লুকিয়ে শোনা ছাড়া আর গতি কী?
পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত লাভ হল না। সিঁড়ির মাথা অবধি যাওয়া মাত্র শোবার ঘরের দরজা খুলে দুজনে বেরিয়ে এল। মা বলছে, “প্রত্যয় এল বলে…” বলতে বলতে প্রত্যয়কে দেখে বলল, “আরে, তুই এসে গেছিস? আয়, চাউ মিন করেছি।”
পরদিন ছুটি। সকালে খেতে বসে বাবা বলল, “স্কুলে সবচেয়ে ভালো কী লাগে তোর?”
হঠাৎ প্রশ্নে প্রত্যয়কে একটু ভাবতে হল। কী ভালো লাগে? পড়াশোনা? না। সেটা ভালো লাগে বাবা যখন পড়ায় তখন। এখানে খেলাধুলোর ব্যবস্থা নেই, তাই সেটা বলা যাবে না… বন্ধু? তাই হবে। সেই উলটন প্রাইমারী স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হবে বলে বাচ্চা প্রত্যয়ের হাপুস নয়নে কান্না…
বাবা বলল, “কী হল?”
প্রত্যয় খেয়াল করল, মা বাবা এতক্ষণ খাওয়া থামিয়ে দুজনেই চুপ করে ওর দিকে চেয়ে আছে। মার হাতে চায়ের কাপ ধরা, ঠোঁট অবধি পৌঁছয়নি। বাবার টোস্টও আকাশে। কেমন যেন সিনেমার দৃশ্য স্টিল হয়ে গেছে। থতমত খেয়ে বলল, “বন্ধু…”
বাবা-মা মুখ তাকাতাকি করল। প্রত্যয় এবার আরও একটু ঘাবড়ে গেল। বাবা বলল, “এদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে, বিল্টু?”
ঠিক ধরেছিল। বন্ধু ছেড়ে যাবারই কথা হচ্ছে। তার মানে কি আবার ইংল্যান্ড?
প্রত্যয়ের প্রশ্ন শুনে বাবা-মা হাসল। বলল, “ইংল্যান্ড না। ওখানে আর আমার ফেরার ইচ্ছে নেই। তবে এখানে আর থাকা যাবে না। তাই ভাবছি — আমরা পোনাপোতায় চলে যাব। ওখানে তুই আমার স্কুলেই পড়বি — একটু অসুবিধা হবে…”
পোনাপোতা! বাবার গ্রাম! ছোটোবেলায় বাবা যে বাড়িতে থাকত! ছোটোবেলায় বাবা যে স্কুলে পড়েছিল! ছোটোবেলায় বাবা যে মাঠে ফুটবল খেলত! ছোটোবেলায় বাবা যে বাগানে ফল চুরি করত, ছোটোবেলায় বাবা যে নদীতে সাঁতার কাটত, নৌকো চালাত, মাছ ধরত…
প্রত্যয়ের কতদিনের ইচ্ছে ওই গ্রামে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বাবা মা হাসত। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার সময়েই বলেছিল, ওখানে অনেক অসুবিধে — তাই শহরেই যেতে হবে…
প্রত্যয় আনন্দে “ইয়াহুউউউউউউউউউ” বলে চিৎকার করে খাবার টেবিল ছেড়ে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে খাটে ডিগবাজি খেতে শুরু করল বলে শুনতেও পেল না, মা বলছে, “এখনও অবশ্য ওখানে সব ঘরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই — সেগুলো আমরা যাওয়ার পরে…”
প্রত্যয়ের ইচ্ছে ছিল বাবার ছোটোবেলার মত রেলগাড়ি করে পোনাপোতা যাবে। বাবারা যখন ছোটো ছিল, তখন সকাল বেলার ট্রেন কু-ঝিকঝিক করে দুপুরের পরে এসে পৌঁছত। কিন্তু বাবা বলল তাতে অসুবিধা। লটবহর নিয়ে স্টেশনে যাওয়া, ব্রেকভ্যানে মাল তোলা, তার পরে রায়সিংহ থেকে তো সেই গাড়ি করেই হবে। ঝামেলা বেশি।
প্রথমে মন খারাপ হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝল আজকাল তো কয়লার ইঞ্জিনের দিন নেই। ইলেকট্রিক ট্রেন রায়সিংহ পৌঁছে যায় দু-ঘণ্টায় — মজা হবার সময় কই? বাবা একটা মস্তো জীপের মত গাড়ি ভাড়া করল, তার ছাদে আর পেছনে বসার জায়গায় মালপত্র তোলা হল, আর তার পরে ভোর থাকতেই ওরা রওয়ানা হয়ে গেল।
শীতের শেষের কুয়াশা মাখা ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যখন হাইওয়ে ছেড়ে গাড়ি গ্রামের রাস্তায় নামল, প্রত্যয়ের উত্তেজনা আর বাধ মানে না। কালো পিচের রাস্তা উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা। দু-ধারে বড়ো বড়ো গাছ ঝুঁকে পড়ে রাস্তার ওপর চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। এই পুকুরপাড়ে মস্তো গাছ, ওই পথের ধারে ছোট্টো এইটুকুনি ছটফটে বাছুর, সেই মাঠের মধ্যে কাঠির মাথায় একটা ওলটানো হাঁড়ির গায়ে সাদা চুনের চোখ-নাক, কোথায় রাস্তার পাশ থেকে উড়ে গেল একটা নীল পাখি, কোথাও দূরের পুকুরে বেগনে ফুল, প্রত্যয় তাকায় আর দেখে, দেখে আর ফুরোয় না।
“মা, ওগুলো ধানগাছ?”
মা বলল, “গাছ কই রে? ধান তো কাটা হয়ে গেছে। ওগুলো ক্ষেতে কেবল ধানের খড় পড়ে আছে। ভালো করে দেখ।”
বাবা বলল, “পোনাপোতা পৌঁছোই, চল, কাছ থেকে দেখবি।”
“পোনাপোতা দেখতে এরকম?” জানতে চাইল প্রত্যয়।
বাবা বলল, “প্রায়। গ্রামের মধ্যে এরকম খোলা নয়, তবে শহরের মতো ঘিঞ্জি তো নয়ই। আর গ্রামের বাইরে এরকম — তবে নদী আছে খানিক দূরেই।”
“আর এরকম আকাশ?”
“আকাশ!” বাবা হা-হা করে এমন হাসল যে প্রত্যয় চমকে উঠল। তারপরেই মনে হল, বাবাকে অনেকদিন এত হাসতে শোনেনি। গ্রামে যাচ্ছে বলে বাবারও খুব আনন্দ হচ্ছে।
আড়চোখে মা-র দিকে তাকাল প্রত্যয়। মা-ও বাইরে তাকিয়ে। তবে মা কি খুশি? প্রত্যয় বোঝার জন্য মা-র দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হঠাৎ মা ওর দিকে ফিরতেই চোখাচোখি হয়ে গেল, আর মা জিজ্ঞেস করল, “কী রে?”
প্রত্যয় বলল, “গ্রামে যাচ্ছি বলে তোমার আনন্দ হচ্ছে?”
উত্তরে মা ওকে বুকে জড়িয়ে ডান হাত দিয়ে থুতনি ধরে শব্দ করে গালে চুমু খেল। প্রত্যয় লজ্জায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি তাকাল আয়নার দিকে — ড্রাইভারের নজর রাস্তার দিকে। নিশ্চিন্ত হয়ে মায়ের থেকে একটু সরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মা যে কী না! ড্রাইভারের সামনে… একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে!
পোনাপোতার রাজবাড়ি অবশ্য এখন নামেই রাজবাড়ি। বাবা বলেছিল, তালপুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না। মা পরে কথাটার মানে বলে দিয়েছিল। পৌঁছনো-মাত্র বাবার কথাটা বুঝল প্রত্যয়। বাইরের গেট থেকে ভেতরের প্রাসাদ, সবই ভাঙাচোরা। গেটের দুপাশের থামের ওপর মস্ত দুটো সিংহ ছিল — এখন আর কী প্রাণী তা-ও চেনার উপায় নেই। ভাঙা লোহার গেটের অর্ধেক ক্ষয়ে গেছে, বাকিটা ঝুলে পড়ে মাটিতে গেঁথে আছে। খোলা-ই থাকে, বন্ধ হয়ই না। গেট থেকে নুড়ি ফেলা রাস্তা গাড়িবারান্দা অবধি, সেও আগাছায় ভর্তি। বাবা সাবধান করে দিল, বিশাল বাগান এখন কেবল জংলি আগাছা আর সাপের বাসা। বাগানের মাঝখানে বিরাট পুকুরে জল নেই এক ফোঁটা, মাঝখানে একটা ফোয়ারার মাঝখানে একটা পরী দাঁড়িয়ে আছে একা।
জ্যেঠু বেরিয়ে এসেছে। জ্যেঠু প্রত্যয়ের প্রিয় খেলার সাথীও বটে। এক সময়ে ওরা ইংল্যান্ডে খুব কাছাকাছিই থাকত। জ্যেঠু, জেঠিমা ওদের ছোট্টো মেয়েকে নিয়ে আসত ওদের বাড়িতে। ওরাও যেত প্রায়ই। অ্যাকসিডেন্টে জেঠিমা আর রিক্তা মরে গেছিল। জ্যেঠুর একটা পা কাটা গেছিল। তার পরে জ্যেঠু দেশে ফিরে এসে এই বাড়িতে থাকে। এতদিন একাই থাকত, এখন ওরা-ও থাকবে।
বিশাল বাড়ি। সামনের বাড়ির একতলায় কাছারি — “আগে এখানে অফিস ছিল,” বলল জ্যেঠু — বৈঠকখানা, আর খাবার ঘর। ঘরটায় ফুটবল খেলা যায়! খাবার টেবিলটাই একটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের সাইজ! দোতলায় লাইব্রেরী, আর বলরুম। “বলরুম অবশ্য পরে। তারও আগে বাইজী নাচত,” বলল জ্যেঠু। “আমরা জমিদার ছিলাম তো!”
ভেতর-বাড়ির দুটো ভাগ। পুবের মহল আর পশ্চিমের মহল। জ্যেঠু বলল, “আমরা ছোটোবেলায় থাকতাম পুবের মহলের নিচতলায়। আমি এখনও তাই থাকি। কিন্তু অন্য মহলগুলো পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে বলে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা পশ্চিম মহলের দোতলায়।”
জ্যেঠুর সঙ্গে পুবের মহলের একতলার বসার ঘরে ঢুকে প্রত্যয় অবাক। জ্যেঠু যে বলল, লাইব্রেরী দোতলায়! প্রত্যয়ের মুখ দেখে জ্যেঠু বলল, “আমার পক্ষে ক্রাচ নিয়ে রোজ বাহান্নটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই এই বৈঠকখানাই আজ আমার লাইব্রেরী। এখানেই পড়াশোনা করি। বই-টই যা লাগে নামিয়ে আনে আমার সেক্রেটারি অনুপ, আর কাজের লোক বাঞ্ছা। এখন তুমিও পারবে আমার জন্য বই নিয়ে আসতে।”
জ্যেঠু ইংল্যান্ডে প্রফেসর ছিল। এখনও সারাদিন পড়াশোনা করে। প্রত্যয় ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “বাহান্নটা সিঁড়ি! সে তো অনেক উঁচু!”
জ্যেঠু হেসে বলল, “আগের দিনে এমনই উঁচু উঁচু, বড়ো বড়ো সব বাড়ি হত।”
মা লেগে গেল বাগানের কাজে। বাবা ব্যস্ত সকাল থেকেই জমি আর চাষবাস সামলাতে। প্রত্যয় স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মাস্টারমশাইরা সকলেই প্রকাশের ছেলেকে পেয়ে উত্তেজিত। সারা দিন কাটে স্কুলে, তার পরে ফুটবল মাঠে। স্পোর্টস স্যার অনিমেষদা আসে রোজ। তালিম হয়। অনিমেষদা বলে, “প্রকাশ আমার সময়ে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলত। তুই যা খেলছিস, স্কুল টিমের স্ট্রাইকার হওয়া আটকাবে কে!” এ ছাড়া গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে হইচই, নদীতে নৌকা বাওয়া, সাঁতার কাটা, এ সব তো আছেই। তার পরে বাড়ি ফিরে পড়াশোনা। খানিকটা বাবার সঙ্গে, খানিকটা জ্যেঠুর সঙ্গে। জ্যেঠু শুধু বই থেকে পড়ায় না। জ্যেঠুর ইতিহাসে গল্পই বেশি। শুধু আকবর বাদশার সঙ্গে যোধপুরের রাজার যুদ্ধের বা ক্লাইভের কাছে সিরাজদৌল্লার হারার গল্প না, সেই সঙ্গে স্থানীয় ইতিহাস। ওদের নিজেদের পরিবারের ইতিহাস। ইংরেজদের সঙ্গে পোনাপোতার রাজাদের লড়াইয়ের ইতিহাস, ফরাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস… সেই সঙ্গে…
“তোর ঘরে একটা রাজার ছবি আছে দেখেছিস? কোলে তরোয়াল, মাথায় পাগড়ি?”
“দেখেছি জ্যেঠু। বাপরে, না দেখে উপায় আছে? প্রায় ছাদ অবধি!”
“যা বলেছিস। কে জানিস? পৌণ্ড্রনারায়ণ।”
“বাপরে কি নাম!”
“তখনকার দিনে অমনিই নাম হত।” তারপর গলা নামিয়ে বলল, “পৌণ্ড্রনারায়ণ ডাকাত ছিলেন, জানিস?”
“ডাকাত! আমাদের পূর্বপুরুষ?”
“ইংরেজরা তাই বলত,” বলল জ্যেঠু। “ওদের ট্যাক্সের টাকা লুঠ করে নিত। পরে সেই টাকা দিয়ে ইংরেজদেরই খাজনা দিত। রাজার কাহার-পেয়াদারা অন্য গ্রামে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জমিদারদের ওপর লুঠপাট চালাত। তাকে ডাকাত বলবে না তো কী বলবে?”
প্রত্যয় ভেবে পেল না কী বলবে। কথায় কথায় স্কুলে ইতিহাস শিক্ষক নিহার-স্যারকে বলল কথাটা। ইতিহাস স্যারও গ্রামেরই লোক। স্যার প্রায়ই ওদের পোনাপোতার ইতিহাস সম্বন্ধে ছোটো ছোটো গল্প বলেন। সবই লোকমুখে শোনা কথা, সত্যি ইতিহাস কি না কেউ জানে না। বললেন, “তোর জ্যাঠামশাই ঠিকই বলেছেন, আবার ঠিক নয়ও। অনেক সময় কোন দিক থেকে দেখছি না বুঝলে ভালো মন্দ বোঝা যায় না। ধর রঘু ডাকাত — সে তো ডাকাতি করে গরিবদের সব দিয়ে দিত। বা ইংল্যান্ডের রবিন হুড। সেও তো ডাকাতিই করত, তাই না?”
প্রত্যয়ের সব গুলিয়ে গেল।
একদিন প্রত্যয় বলল, “ডাকাতি করে পাওয়া টাকা-কড়ির কিচ্ছু বাকি নেই? বাবা বলছিল টাকার অভাবে সব আটকে যাচ্ছে…”
জ্যেঠু মাথা নেড়ে বলল, “তোর বাবার ইচ্ছে ছিল এই বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে রাজবাড়ির ইতিহাসটা কাজে লাগিয়ে একটা মিউজিয়াম করবে। আমাদের পারিবারিক ইতিহাস তো কম না, সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারলে একটা ভালো কিছু হতে পারত।”
প্রত্যয়ের দারুণ মজা লাগল। কিন্তু জ্যেঠু পারত বলল কেন? পারবে না? জিজ্ঞেস করল, “কোনও টাকা নেই?”
মাথা নাড়ল জ্যেঠু। বলল, “না। এই এত বড়ো বাড়ি সারিয়ে তুলে, বাগান বানিয়ে তাতে নতুন করে মিউজিয়াম বানানো আমাদের সাধ্য নয়।”
খানিকক্ষণ দু-জনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে জ্যেঠু বলল, “বাড়িটা একটু সারাতে না পারলে চলবে না। বাগানটাও জঙ্গল। সেখানেই তো খরচ অনেক।”
দিনের শেষে শোবার সময় পৌণ্ড্রনারায়ণের ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। এমন ভাবে আঁকা, যে-দিক থেকেই তাকাও, মনে হবে রাজামশাই তোমারই দিকে চেয়ে আছেন। এ ক-দিনে অভ্যেস হয়ে গেছে, আগে অস্বস্তি হত। মনে মনে বলল, “এত ডাকাতি করেছ ইংরেজ রাজার ধন, কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখতে পারনি?”
মনে হল পৌণ্ড্রনারায়ণ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। অন্ধকার ঘরে কত কী মনে হয়!

পরদিন সকালে, স্কুলে যাবার আগে সবাই ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে, তখন প্রত্যয়ের কথা শুনে জ্যেঠু হেসে খুন। বলল, “ওরে, গুপ্তধন কী অতই সহজ? তখনকার দিনে ডাকাতি করে কতটুকু পাওয়া যেত? ও সবই খরচ হয়ে গিয়েছে। নইলে এই এত বড়ো বাড়ি, তার কত কাজের লোক, সহজে মেনটেন হত?”
প্রত্যয় কিছু বলল না, তবে কথাটা ওর পছন্দ হল না। কিছুদিন আগে জ্যেঠুই বলেছিল, কেমন করে লর্ড ক্লাইভ মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ৩ লক্ষ পাউন্ড নিয়ে রিটায়ার করে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। সে তো তিনি ভারতবর্ষ থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে?
বাবা কিন্তু হাসল না৷ বরং গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, “দাদা, হাসিস না। আমাদের ছোটোবেলায় নায়েব বিশ্বম্ভরবাবু বলতেন মনে নেই — এ বাড়িতে গুপ্তধন আছে।” তারপর প্রত্যয়কে বলল, “আগে যখন এসব জায়গার দখল নিয়ে ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধ লেগেই থাকত, শোনা যায় তখন এক ফরাসি ব্যারন আমাদের কাছে খুব দামি কিছু পাথর গচ্ছিত রেখে যুদ্ধে গেছিল। বলেছিল পরে নিয়ে যাবে, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। মরে-টরে গেছিল হয়ত… নামটাও মনে আছে। গ্রেফিন রিউক্স…”
জ্যেঠু বাবাকে থামিয়ে বলল, “ব্যারন গ্রিফাঁ রু। ওটাই উচ্চারণ। সে গল্প তো আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সত্যিই কি উনি কিছু দিয়ে গেছিলেন? এ খবর কে জানে? আর যদি দিয়েও থাকেন তাহলে সেগুলো গেল কোথায়? তখনকার দিনে তো ব্যাংকের লকার-টকার ছিল না। দামি সোনা-দানা-গয়না, হীরে-মুক্তো মানুষ বাড়িতে সিন্দুকেই রাখত। এমন সিন্দুক এ বাড়িতে সাতটা এবং সেগুলো কম খোঁজা হয়নি। ছোটবেলা থেকেই তো জানতাম সে সিন্দুকে কিছু নেই।”
বাবা বলল, “সিন্দুকে হয়ত নেই। তোর মনে নেই, একবার আমরা সিন্দুকের ভেতরে ঢুকে খুঁজেছিলাম? বড়মামা বলেছিল সিন্দুকে লুকােনো খুপরি থাকে! সেই শুনে আমরাও গল্পের বইয়ের সিন্দুকের মতো লুকােনো খুপরি খুঁজেছিলাম সারাদিন — কিছুই পাইনি। হয়ত অমন লুকোনো খুপরি অন্য কোথাও আছে…”
অমন লুকোনো খুপরি অন্য কোথায় থাকতে পারে, তা অবশ্য বাবা বলতে পারল না।
সেদিন ইতিহাস ক্লাসে আবার নিহার-স্যার যেই ওদের পোনাপোতা রাজবাড়ীর গল্প বলতে আরম্ভ করেছেন, প্রত্যয় গুপ্তধনের কথা জানতে চাইল। প্রথমে স্যার খুব হাসলেন। বললেন, “এসব গল্প আগে অনেক শুনেছি। আমার দাদা বলত। দাদা তোর বাবার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত, আর কিছুদিন পরে পরেই সবাই মিলে নাকি গুপ্তধন খুঁজতে যেত রাজবাড়ির এখানে ওখানে। তখন আমি ছোটো। এমনকি এমনও গল্প ছিল যে তোদের বাড়ির সামনের বড়ো পুকুরটার নিচে বিশাল গুপ্তধনের ভাণ্ডার! তা সে পুকুর তো শুকিয়ে এখন কাঠ। নিচে কত পলিমাটি জমে ছিল, তোর জ্যাঠামশাই পুকুরটাকে সংস্কার করবে ভেবে লোক লাগিয়ে অনেকটা গভীর করেই কেটেছিলেন। জানি না গুপ্তধনেরও আশা ছিল কি না। তারপর দেখা গেল সরু যে নালাটা দিয়ে নদী থেকে পুকুর অবধি জল আসত, সেটা শুধু বুজে গেছে তা নয়, সেটা যেখান দিয়ে আসতো সে সব জায়গায় এখন মানুষের বাড়িঘর, বাগান। আবার নতুন করে নালা কাটার উদ্যোগ করা গেল না… যাক সে কথা, মোদ্দা ব্যাপার, ফরাসি সাহেব দামী দামী মণিরত্ন রেখে গেছেন এ গল্প আমরাও শুনেছি, আমাদের বাবা ঠাকুরদারাও শুনেছে। তোরাও শুনলি। হয়ত সত্যি ছিল, কিন্তু ফরাসিরা যুদ্ধে হারার পর ইংরেজরা তো পোনাপোতাও আক্রমণ করেছিল। রাজবাড়ীর রক্ষা করার মতো সৈন্যসামন্ত, বন্দুক, গোলাবারুদ তো ছিল না, তাই রাজামশাই পৌণ্ড্রনারায়ণ বাধ্য হয়ে ইংরেজদের নেমন্তন্ন করে ডেকেছিলেন। ইংরেজরা নাকি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দামি যা কিছু পেয়েছিল সবই লুঠ করে নিয়ে যায়। সুতরাং সে সব রত্নভাণ্ডার নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেছে। হয়তো কোনও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সেগুলো শোভা পাচ্ছে। কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছিস তোর জ্যাঠামশাই থাকতে? উনি তো এসে-থেকে পোনাপোতার রাজবাড়ি নিয়ে প্রচুর রিসার্চ করছেন। গ্রামের সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠকে ইন্টারভিউ করেছেন। আমাদের ধারনা ছিল খুব শিগগিরই সেটা বই হয়ে বেরোবে — তার কি হল?”
জেঠু বই লিখছে জানত না প্রত্যয়। ভাবল সেটা হয়তো সিক্রেট, ওর জানার কথা নয়, তাই বুদ্ধি করে বিকেলে জানতে চাইল, “জ্যেঠু আমাদের বাড়ির কোনও ইতিহাস কোথাও লেখা নেই? কোনও বই-টই…?”
জ্যেঠু একটু ভুরু কুঁচকে বলল, “বই? মুশকিলে ফেললি। যদি বলিস পোনাপোতার রাজবংশের ইতিহাস বলে কোনও বই আছে কি? তাহলে তার উত্তর হল — না। কিন্তু সে বাদেও তো রেকর্ড হয়। হয় না? তা থেকে ইতিহাস তৈরি করা যায়। আসলে আমি এখন তা-ই করছি।”
“কী রকম?” নিজের রিসার্চ এর কথা জেঠু নিজেই বলল বলে, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জানতে চাইল প্রত্যয়।
“এই দেখ…” বলে জ্যেঠু টেবিল থেকে কয়েকটা হিসেবের খাতা তুলে দেখাল। “এগুলোই পোনাপোতা রাজবাড়ির ইতিহাস। আমাদের তো নিজেদের ইতিহাস লিখে রাখার রেওয়াজ ছিল না, এখনও নেই… বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলেছেন। নিজেদের বিষয়ে আমরা কিছুই ভাবি না, কিছুই করি না। আমরা মরে গেলে আমাদের কথা জানে কেবল আমাদের ছেলেমেয়ে-রা, আর কেউ না। নাতি নাতনিরাও দাদু-ঠাকুমা-দিদার সময়ের কথা জানে না…”
প্রত্যয় আর অপেক্ষা করতে পারল না। বলল, “এইসব লেখায় কোথাও ওই দামি পাথরের কথা লেখা নেই? আমাদের হিস্ট্রি স্যার বলছিলেন সেগুলো হয়তো সাহেবরাই নিয়ে গেছে নিজেদের মিউজিয়ামে।”
আবার হাসলো জেঠু। বলল। “কবেকার কথা জানিস? ক্লাইভ চন্দননগর জয় করেছিলেন ১৭৫৭ সালে। তারপরেই ইংরেজরা ফরাসিদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন আশেপাশের সব জমিদারি আক্রমণ করে। পোনাপোতার ওপর আক্রমণও সেই সময়ই হয়েছিল। মানে আজ থেকে আড়াইশো বছরেরও বেশি আগে। তখনকার হিসেবপত্র, খাতা-টাতা নেই বললেই চলে। অতি কষ্টে কিছু দলিলের টুকরো পেয়েছি, তা থেকে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করে কার সাধ্যি! আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম তখন ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর্কাইভে অনেক ঐতিহাসিক দলিল খুঁজে পেয়েছি যেগুলোতে পোনাপোতা আক্রমণের ইতিহাস লেখা রয়েছে। সব জেরক্স করে এনেছি। তাতেও তেমন কিছু নেই। সাহেবরা পকেটে ভরে চুরি করলে তার নথিপত্র থাকার সম্ভাবনা কম, তবে এ কথা ঠিক যে যতটুকু সেগুলো ঘেঁটেছি পোনাপোতা থেকে কোনও মিউজিয়ামে মণিমুক্তো গেছে এমন তথ্য পাইনি।”
প্রত্যয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। আশা করেছিল বুঝি কিছু একটা জানা যাবে যা থেকে বাড়িতে লুকোনো ধনরত্নের খোঁজ পেয়ে ওদের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। জ্যেঠু ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে হাত দিয়ে ওর মাথায় চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, “তোকে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলি, যেটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়েছি। এ বাড়িতে এখানে ওখানে দেখেছিস, আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস্ট্ রয়েছে — বাংলায় যাকে বলে আবক্ষ মূর্তি?”
বাস্ট্ কাকে বলে জানে প্রত্যয়। মাথা থেকে বুক অবধি মূর্তি, কাঁধ আছে, হাত নেই — তাকেই বলে বাস্ট। বুক অবধি, তাই আবক্ষ। জ্যেঠু বলল, “ওই বাস্টগুলো সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করেছিলেন ওই সময়কার একজন সেনাধ্যক্ষ্য। এক্ষুনি এত কাগজের মধ্যে খুঁজতে সময় লাগবে, কিন্তু বক্তব্য ছিল এরকম, যে ইন্ডিয়ানরা আমাদের নকল করতে আগ্রহী, কিন্তু আদব কায়দা জানে না। তাই কী করে কোনও ঠিক নেই। বাস্ট্ বানিয়েছে, তার চোখগুলোকে আলকাতরার কালি দিয়ে কালো করে রেখেছে, দেখাচ্ছে বীভৎস, কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।”
প্রত্যয় জানে। আবক্ষ মূর্তিগুলো দেখেই ওর খটকা লেগেছিল। ছোটো থেকে এমন মূর্তি ও যত দেখেছে সবারই চোখ হয় নেই, নয়ত খোদাই করেই আঁকা। ওদের বাড়ির সব মূর্তিতেই চোখের জায়গাটা কুচকুচে কালো। শুধু মণিটুকু নয়, চোখের সাদাটাও কালো। ফলে দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগে। ভয়ও করে।
জিজ্ঞেস করল, “কেন কালো?”
জ্যেঠু ঠোঁট ওলটাল। বলল, “হবে পৌণ্ড্রনারায়ণের ইচ্ছে। রাজা তো, কখন মাথায় কী খেয়াল চাপে… নে, এবার বইখাতা খোল। মা যদি এসে পড়ে দেখে আমরা কেবল গ্যাঁজাচ্ছি, তাহলে মোটেই খুশি হবে না।”

জ্যেঠু তখনকার মতো বাড়ির আবক্ষ মূর্তি নিয়ে কথা বলা থামিয়ে দিল বটে, কিন্তু রাতে খেতে বসে নিজেই আবার রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণের অদ্ভুত খেয়ালের কথা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল। মা বলল, মার-ও প্রথম প্রথম মূর্তিগুলো দেখলে সত্যিই খুব আশ্চর্য লাগত, ঠিক ভয় না পেলেও একটা অস্বস্তি তো হত বটেই। এখন সয়ে গেছে।
বাবা আর জ্যেঠুর অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ছোটোবেলা থেকে কালো রঙের মূর্তির চোখ দেখে অভ্যস্ত দুটো ছেলে যখন প্রথম বাইরে গেছিল, তখন সব জায়গায় কালো-চোখ-হীন আবক্ষ মূর্তি দেখে চমকে উঠত। ভাবত, এ কি সব অন্ধ মানুষের মূর্তি নাকি?
বাবা বলল, “কিন্তু চোখ পুরো কালো হবেই বা কেন? রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ যা-ই করে থাকুন, আমরা তো আজ আমাদের মতো বদলাতেই পারি। চোখগুলো সাধারণ মূর্তির মতো করে দিলেই হয়?”
জ্যেঠু হেসে বলল, “রাজামশাইয়ের চোখ কালো করার একটা প্রবণতা ছিল জানিস? আমি জানতাম না। জেনেছি অনুপের কাছ থেকে।”
অনুপ? বাবা অবাক। অনুপ জানল কী করে?
জ্যেঠু বলল, “অনুপ তো বাবার বুড়ো নায়েব বিশ্বম্ভরবাবুর নাতি। অবশ্য নায়েবগিরি করতে হত না কিছু… সে কথা থাক, আমি গ্রামে ফিরে জানলাম বিশ্বম্ভরবাবু মারা যাবার পর ওঁর পেনশন-বাবদ বাবা যে টাকা দিত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনুপের নিয়মিত কাজ নেই, এটা ওটা করে চালাচ্ছে — ওরা তো বংশানুক্রমিক আমাদের নায়েবি-ই করেছে। ওর বাবা অল্প বয়সে মারা না গেলে বিশ্বম্ভরবাবু রিটায়ার করার পরে আমাদের নায়েবই হতেন। তাই ওকে বললাম, লেখাপড়া শিখেছিস, আজকাল নায়েব লাগে না, আমার সেক্রেটারি হবি?…
“তা একথা অনুপই বলেছিল। সেই রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণের সময় থেকেই নাকি দস্তুর, পঁচিশ বছর পরে পরে সব মূর্তির চোখ কালো করতে হবে। সব, মানে সব। এমনকি দেউড়ির ওপরের সিংহ, আর পুকুরের মাঝখানের পরীর চোখও।”
“কী আশ্চর্য! কেন?” জানতে চাইল মা।
জ্যেঠু বলল, “কে জানে! রাজারাজড়ার সখ। অনুপ বলেছিল, শেষ রং হয়েছে আমাদের জন্মের আগে, ঠাকুর্দার সময়ে। বাবা কখনও করায়নি, আর তারপর তো হয়ইনি।”
“তাহলে চল, রং তুলে দিয়ে আমরা নর্মাল মূর্তি করে দিই,” বলল বাবা।
জ্যেঠু বলল, “আরে দূর, কত কাজ আছে — মূর্তির চোখ নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। তাছাড়া ওটা এমনি কালো রং নয়, আলকাতরা। আলকাতরার প্রলেপ কী করে তুলতে হয় জানিস?”
আঁতকে উঠে বাবা বলল, “আলকাতরা! কেন, আলকাতরা কেন? এমনি রঙে হচ্ছিল না?”
এ কথার উত্তরও কেউ জানে না।
পরদিন, আশ্চর্য ব্যাপার, ইতিহাস ক্লাসে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিহার-স্যার আবার মূর্তির কথাই বললেন।
বললেন, “চন্দননগরে ফরাসিদের হারিয়ে তার তিন মাসের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ জয় করে ক্লাইভের তখন পোয়া বারো। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা বাংলা তখন ওর। রাগ দেখানোর একটা বড়ো জায়গা ছিল ফরাসিদের যারা সমর্থন করেছিল, তাদের ওপর। পোনাপোতার রাজবাড়ি ছিল সেই লিস্টে। কিন্তু রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। জমিদারি রক্ষা করতে রাতারাতি সায়েবি কায়দা ধরলেন। শুধুমাত্র পোশাক-আশাক বদলে ফেললেন না, শোনা যায় তিনি কয়েক মাসের মধ্যে বাড়িটাই সাহেবি করে ফেলেছিলেন। এমনিই ফরাসি স্থাপত্যের আদলে তৈরি রাজবাড়ি — এই কয় মাসে রাজা ফরাসি আর্টিস্ট, যারা চন্দননগর থেকে পালিয়েছিল, তাদের আশ্রয় দিয়ে তাদের দিয়েই নতুন ফটক তৈরি করে তোরণের ওপর ব্রিটিশ সিংহের আদলে সিংহ বসালেন, বাড়ি ভরিয়ে ফেললেন সাহেবি স্টাইলে তৈরি আগেকার রাজাদের আবক্ষ মূর্তি দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, শোনা যায় তিনি নাকি এ ক-মাসে এতটাই ভালো ইংরেজি শিখে নিয়েছিলেন, যে ইংরেজরা এসে থতমত। এরা কি সত্যিই ইংরেজ বিরোধী? ফরাসিদের সাহায্য করেছিল? তা বলে লুটতরাজ করতে বাধেনি ওদের। তবে জমিদারিটায় হাত দেয়নি। আর তার পরেই লোকজন, পেয়াদা, কাহার, লাঠিসোঁটা, বন্দুক-টন্দুক জুটিয়ে রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ ইংরেজদেরই লুঠতে আরম্ভ করলেন।”
সুযোগ বুঝে প্রত্যয় জিজ্ঞেস করল, “তাহলে মূর্তিগুলোর চোখ কেন কালো? ফরাসিরাই যদি বানিয়েছিল, তাহলে চোখ সাধারণ বাস্টের মতো হল না কেন?”
নিহার-স্যার জানেন না। বলতে পারলেন না কিছু।
ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবে প্রত্যয়, ততই মনে হয় কিছু একটা আছে, যেটা কেউ জানে না। রাজার খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়াটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না।
আজ সায়েন্সটা মন দিয়ে পড়া দরকার। কাল ক্লাস টেস্ট। হেডস্যার পড়ান। ফাঁকি দিলে চলে না। তারপর অঙ্ক হোমওয়ার্ক, রোজকার পড়া — আজ বাবা পড়াচ্ছিল। খেতে ওঠার আগে প্রত্যয় অন্য কিছু ভাবার সময়ই পেল না।
পড়া শেষ করে বই খাতা গুছিয়ে এক ছুটে গেল জ্যেঠুর মহলে। জ্যেঠু-ও খেতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। প্রত্যয় বলল, “উলটনে আমার স্কুলে মিঃ জন বার্টন বলতেন, সায়েন্সের সমস্যা মেটাতে হলে ঠিক ঠিক প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন করার ভুলেই মানুষ সায়েন্টিফিক সমস্যার সঠিক সলিউশন পায় না।”
জ্যেঠু ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, “ঠিকই বলেছেন মিঃ বার্টন। সায়েন্স পড়তে গিয়ে খেয়াল হল?”
প্রত্যয় বলল, “ঠিক তা নয়। ভাবছিলাম, আমরা সবাই ভাবছি মূর্তির চোখ কালো কেন? তার উত্তর হল, রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ বলেছিলেন বলে। কিন্তু কেন বলেছিলেন, সেটা হয়ত ভাবা উচিত।”
জ্যেঠু চমকে বলল, “তুই পরীক্ষার পড়া না করে এসব ভাবছিলি?”
প্রত্যয় বলল, “না, না! আগেই ভেবেছিলাম। কিন্তু পড়ছিলাম বলে বলতে পারিনি।”
জ্যেঠু আড়চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা, বেশ, প্রশ্নটা তাহলে কী?”
“জানি না তো,” বলল প্রত্যয়, তারপর দুজনে খাবার ঘরে ঢুকল।
পাতে খাবার দেওয়া শুরু হওয়ামাত্র জ্যেঠু বলল, “প্রত্যয় কী বলছে জানিস? রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ মূর্তির চোখ কালো কেন করেছিলেন — এই প্রশ্ন করে যদি উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে কী জিজ্ঞেস করতে হবে?”
বাবা বলল, “মানে? পৌণ্ড্রনারায়ণ মূর্তির চোখ কালো করেননি?”
জ্যেঠু বলল, “করেছিলেন তো। কেন? সেটা প্রশ্ন। কিন্তু তার উত্তর পাচ্ছি না। অন্য কী ভাবে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পেতে পারি?”
মা বলল, “কোনও কিছুতেই কালো রং করা কেন হয়?”
বাবা বলল, “কালো জিনিসের ছবিতে কালো রং দেওয়া হয় — যেমন মাথার চুল বা চোখের মণি…”
প্রত্যয় বলল, “প্রোটেকশনের জন্য কালো রং করা হয়…”
গত সপ্তাহে নিতাইদা এসেছিল কোল্যাপসিব্ল গেটগুলো রং করতে। বাড়ির সামনের দিকের কোল্যাপসিব্ল গেটে সাদা, আর পেছনে সব কালো। তখনই প্রত্যয়কে নিতাইদা বলেছিল, কালো রং বেশিদিন টেঁকে। সামনের দিকে দেখতে ভালো হবে বলে সাদা রং করা হয়, সে টেঁকে না বেশি দিন।
জ্যেঠু বলল, “দুটোর কোনওটাই হবে না। চোখের মণি কালো হয় মানলাম, সাদা জায়গাটাও কালো কেন? আর শুধু চোখের জায়গাটা কালো করে মার্বেলের মূর্তিতে কি প্রোটেকশন দেওয়া হয়?”
বাবা বলল, “তখন হয়ত ভালো করে চোখ আঁকতে পারত না?”
জ্যেঠু মাথা নাড়ল। “তখন দুর্গাপুজো হত এ বাড়িতে। তার ইতিহাস আছে। দুর্গা ঠাকুরের ছবি নেই, কিন্তু কুমোর নিশ্চয়ই মায়ের মুখে পুরো কালো চোখ আঁকত না?”
মা বলল, “প্রোটেকশন শত্রুর নজর থেকে বাঁচানোর জন্যও হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পুরো কালো করে দেওয়া হয়েছিল যাতে রাতে আকাশ থেকে জাপানি বোমারু বিমানের পাইলটরা দেখতে না পায়।”
জ্যেঠু এবারে খুব হেসে বলল, “তাহলে তো সাদা মার্বেলের মূর্তিতে কালো চোখ আঁকা হলে লুকোনোর জায়গায় নজর পড়ার ব্যবস্থা হবে!”
বাবা, মা আর জ্যেঠু এর পর কী বলল, কী আলোচনা করল, প্রত্যয়ের কানেই ঢুকল না। খালি মায়ের কথাগুলো মাথায় ঘুরতে থাকল — শত্রুর নজর থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যও কালো রং করা যায়… কালো রং… শত্রুর নজর…
খেয়ে উঠে রোজের মতো প্রত্যয় মা-বাবার জন্য অপেক্ষা করল না, কাল পরীক্ষা বলে শুতে চলে গেল। পশ্চিমের মহলের দোতলার বারান্দায় বাবা-মায়ের শোবার ঘর আর ওর ঘরের দরজার মাঝামাঝি একটা আবক্ষ মূর্তি আছে, কোনও এক পূর্বপুরুষের, সেই আড়াইশো বছর আগে রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ ফরাসি ভাস্করদের দিয়ে বানিয়েছিলেন। তিন-চার মাসের মধ্যে বাইশটা মূর্তি বানিয়েছিল কজন ভাস্কর? তা ছাড়াও, গেট বানানো, তার ওপর সিংহ বসানো, বাগানে পুকুরে ফোয়ারা, পরী, ইংরেজি শেখা… জমিদারিই বলো, রাজত্বই বলো — বাঁচানোর জন্য কত ব্যবস্থা!
বারান্দায় আগেকার দিনে লম্ফ জ্বলত, শুনেছে প্রত্যয়। কাজের মাসি গল্প করে মায়ের সঙ্গে ছোটোবেলায় যখন আসত, মিটমিটে আলোয় ভয় করত কেমন। তারপর যখন ইলেক্ট্রিসিটি এল, তখন কেবল বাড়ির সামনের বারমহল, কাছারি, আর জ্যেঠু আসার পরে পুবের মহলের নিচের তলায় বিদ্যুতের কানেকশন আসে। পশ্চিমের মহলের দোতলার মাত্র দুটো ঘরেই এখন বিজলিবাতি জ্বলে — ওদের দুটো শোবার ঘরে। বারান্দায় তো কোনও আলোই নেই। সিঁড়িও অন্ধকার। মা রাতে একটা টর্চ নিয়ে ওঠে, সকালে নিচে গিয়ে সিঁড়ির নিচে রেখে দেয়, পরদিন রাতের জন্য।
ওর ঘরেও একটা টর্চ থাকে। নিয়ে এসে ভালো করে মূর্তির চোখ দুটো দেখল প্রত্যয়। তারপর শোবার আগে চট করে কম্পিউটার চালিয়ে দেখল আলকাতরার দাগ কী করে তোলা যায়। নানা পদ্ধতির মধ্যে একটা মোটামুটি সহজ দেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে এক্কেবারে ঘুমিয়ে পড়ল।
পরদিন পরীক্ষা শেষ করে প্রত্যয় খেলার মাঠের দিকে না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরল। এখন মা বাগানে, বাবা মাঠে। জ্যেঠু দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম করছে।
এক-ছুটে বাড়ির পেছনের সেই ঘরটায় ঢুকল, যেখানে বাগানের সব যন্ত্রপাতি থাকে। একটা ডাব্লু ডি ফর্টি স্প্রে-ক্যান, আর কিছু চটের থলের টুকরো — আপাতত এই দিয়েই কাজ চালানো যাবে। কাল ইউ টিউবে দেখেছে, ডাব্লু ডি ফর্টি স্প্রে করলে গাড়ি থেকে পিচের ছোপ তোলা যায়। এমনিতে এই স্প্রে দিয়ে যাবতীয় আটকে থাকা জিনিস খোলা যায়। তালা, দরজার ক্যাঁচক্যাঁচে কবজা, মেশিন পত্র, আরও কত কিছু। আলকাতরার অনেক পরত — তুলতে হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু …
ঘরে ব্যাগ নামিয়ে রেখে বারান্দার মূর্তির এক চোখে ডাব্লু ডি ফর্টি স্প্রে করে আধ মিনিট অপেক্ষা করতে না করতেই আলকাতরা গোলা স্প্রে নামতে লাগল মূর্তির গাল বেয়ে। চটের টুকরো দিয়ে প্রাণপণে ঘষতে আরম্ভ করল প্রত্যয়।
বার পাঁচেক স্প্রে করে জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে প্রত্যয়ের মনে হল যেন জায়গায় জায়গায় আলকাতরা একেবারে পুরোই উঠে গেছে। কালো রং আর দেখাই যাচ্ছে না। ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখল। ভেতরের রং কি সাদা? না। বরং হলদেটে। বুকটা ধড়াস করে উঠল প্রত্যয়ের। চোখে আলকাতরার আড়ালে মার্বেল নেই। অন্য কিছু আছে। অন্য চোখে? ওর ঘড়ি নেই, মোবাইলও না। বাবা-মায়ের শোবার ঘরে দেওয়াল ঘড়ি, আর ওর টেবিলে একটা ঘড়ি আছে। উঁকি মেরে দেখল… এখনও সময় আছে। স্কুলের পরে খেলার মাঠে যতটা সময় ওর থাকার কথা, তার অর্ধেকও যায়নি। কিন্তু জ্যেঠুর ওঠার সময় হল প্রায়। এমনিতে ক্রাচ নিয়ে চলতে হয় বলে জ্যেঠুর নজর থাকে নিচের দিকেই, তবু, বলা যায় না — কোনও কারণে ওপরে তাকিয়ে যদি পশ্চিমের মহলের বারান্দায় প্রত্যয়কে দেখতে পায়, তখন কী বলবে প্রত্যয়? কী করছে এখানে?
সময় নষ্ট করে কাজ নেই, প্রত্যয় মন দিল মূর্তির ডান চোখে।
এ চোখে সময় লাগল বেশি। আট বার স্প্রে করতে হল। ঘষতেও হল অনেক বেশি। সবে প্রত্যয়ের মনে হচ্ছিল, এ চোখটা কি পুরোটাই আলকাতরার? শেষে যখন মনে হচ্ছে যেন আলকাতরার পেছনে একটা অন্য রং দেখা যাচ্ছে। সবে কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে যাবে, এমন সময় দোতলার সিঁড়ির দরজা থেকে শুনল, “কী রে, কী করছিস?”
বাবা! বাবা এখন কী করে এল? বাবা তো আরও এক ঘণ্টা পরে ফেরে। এখন আর কিছু লুকোনোর সময় নেই। ডাব্লু ডি ফর্টি স্প্রে-ক্যান, চটের থলের টুকরো — সবই দেখে ফেলেছে বাবা। বলল, “তুই আলকাতরা তুলছিলি?” বলে হেসে ফেলল। “কত ডাব্লু ডি ফর্টি খরচ করেছিস? বাকি আছে কিছু? কী পেলি নিচে?”
প্রত্যয় কিছু বলছে না। বাবা এসে পড়েছে। এখন বাবা নিজেই দেখতে পাচ্ছে। একটা চোখ হলদে, ডান চোখটা নীল।
“মাই গড!” বাবা কেন জানি এদিক ওদিক তাকাল। তারপর ভালো করে আঙুল দিয়ে চোখের জায়গাটা ঘষে ঘষে কী দেখল। তারপর বলল, “বুঝেছি, দাঁড়া…” বলে ঘরে ঢুকে গেল।
বাবার সঙ্গে সবসময় কোনও না কোনও যন্ত্রপাতি থাকেই। শোবার ঘরে থাকে একটা সুন্দর চামড়ার বাক্সে ছোটো ছোটো যন্ত্র — ছোট্ট হাতুড়ি, ছোট্ট ছেনি, ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, তুরপুন, উখো, আরও কত কী। বাবা স্ক্রু-ড্রাইভারটা দিয়ে চোখের গর্তের সাদাটে জায়গাটা একটু ঘষে বলল, “প্লাস্টার জাতীয় কিছু। শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বেরোচ্ছে।” তারপর স্ক্রু-ড্রাইভারটা জায়গা মতো বসিয়ে চাপ দিতেই প্লাস্টার টুকরো টুকরো হয়ে বাবার হাতে এসে পড়ল।
ঘরে ঢুকে বাবা সবটাই প্রত্যয়ের পড়ার টেবিলে রেখে এসে ফাঁকা চোখের গর্তটা ডাব্লু ডি ফর্টি দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে বলল, “আর কিছু নেই।” তারপর বাঁ চোখটাও একইভাবে খালি করে বলল, “চল, এবারে ভালো করে দেখি…”
প্রত্যয়ের পড়ার টেবিলে একটা বড়ো কাগজের ওপর বাবার ছোট্টো হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে প্লাস্টারগুলো একেবারে পাউডার করার পরে দেখা গেল দুটো চকচকে পাথর। একটা নীল, একটা হলদে। বাবা বলল, “হবে নীলা আর পোখরাজ টোখরাজ কিছু। দাম? পাথরই চিনি না, তার আবার দাম। তবে এগুলোই বোধহয় সেই ফরাসি সাহেবের গচ্ছিত পাথর, আর এগুলোই পোনাপোতার গুপ্তধন। এখনই কাউকে কিছু বলবি না। জানাজানি হলে বাড়িতে ডাকাতও আসতে পারে। জ্যেঠুকেও না। রাতে সবকটা মূর্তি খুঁজব। তারপর কাল সকালে যা পাওয়া যায়, জ্যেঠুকে দেখাব।”

তিন বছর পর। পোনাপোতা হাইস্কুল দিল্লি থেকে সুব্রত কাপ জিতে ফিরল, আজ গ্রামে প্রত্যয় হিরো। রায়সিংহ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর ছেলেরা ওকে কাঁধে করেই গ্রামে ফেরার তাল করছিল। গোটা টুর্নামেন্টে ওর ষোলোটা গোল, তার মধ্যে একটা হ্যাট-ট্রিক, আর ফাইনালে দু-দুটো গোল!
বাড়ি ফিরেও হইচই। জ্যেঠু ছটফট করছিল। বলল, “তোর বাবার চেয়েও ভালো রেজাল্ট রে! সুব্রত কাপে প্রকাশের বেস্ট পনেরো। আর তিন বার খেলে ফাইনালে একটাই গোল।”
প্রত্যয়ের সেদিকে মন নেই। বলল, “মিউজিয়ামের কী হল?”
বাবা হেসে বলল, “হবে। মিনিস্ট্রি অব কালচার অ্যাপ্রুভ করেছে। সবকটা হীরা, চূনী, পান্নার নকল বানিয়ে ওরা দেবে আমাদের। আসলগুলো তো এখানে রাখা যাবে না… ওই এক-রাতেই যা অবস্থা হয়েছিল আমাদের!”
এক রাত নয়, বেশ কয়েক রাতই ওদের ঠিক মতো ঘুম হয়নি। সেদিনই রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ওরা তিনজনে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সব মূর্তির চোখ থেকে আলকাতরা পরিষ্কার করে প্লাস্টারে গাঁথা দামি পাথরগুলো বের করেছিল। বাইশটা মূর্তি, চুয়াল্লিশটা চোখ, আটচল্লিশটা পাথর। বাবা আন্দাজে বলেছিল সাতটা পোখরাজ, আটটা করে চূনী আর পান্না, এগারোটা নীলা আর বাকি সব হীরা। বেশিরভাগই বড়ো বড়ো। অত বড়ো হীরা ওরা কেবল ছবিতেই দেখেছে। ছটা ছোটো পাথর।
সারা রাত প্রায় জেগে থেকে ওরা ভোর না-হতেই জ্যেঠুকে ডেকে তুলেছিল। ব্যাপার জেনে জ্যেঠু বলেছিল, “কাজের লোক কেউ আসার আগেই সব সিন্দুকে তুলে রাখ। ওদের কাউকে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ওরা বাড়ি গিয়ে গল্প করলে দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়বে।”
জ্যেঠুর এক বন্ধু কলকাতার যাদুঘরে কাজ করেন। তাঁকে ফোন করে জ্যেঠু সব জানিয়েছিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলেন, দিল্লি থেকে মিনিস্ট্রি অব কালচার থেকে ফোনে জানিয়েছিল এখনই বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জিপ নিয়ে হাজির রায়সিংহ থানার ওসি। সব দেখেশুনে বলেছিলেন, “বাড়িতেই রাখবেন সব? কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে রেখে এলে হত না? আমাকে তো সরকার বলল পাহারার ব্যবস্থা করো… তা করব কোত্থেকে? আমার নিজের কি দশ-বিশটা এক্সট্রা লোক আছে? একজনকে বসিয়ে রেখে যাচ্ছি।”
জ্যেঠু আঁতকে উঠে বলেছিল, “একজন? এত দামি সব হীরে-জহরতের খোঁজে ডাকাত এলে কী একজন কী করবে? আর পুলিশের পাহারা মানেই তো লোককে ডেকে বলা — এখানে কিছু একটা রয়েছে। তার চেয়ে আপনি সবাইকে নিয়েই চলে যান।”
ওসি মাথা নেড়ে বলেছিলেন, “উঁহু, সে হবে না। আমাকে পাহারার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পাহারা না বসালে ডেরিলিকশন অফ ডিউটি হবে। শো কজ্ করবে। তবে আপনার ভয় নেই। এসব হীরে-জহরতের কথা তো পেয়াদাদের বলব না, আপনিও বলবেন না। তাহলেই হবে।”
ওসি চলে গেলেন, পাহারা রইল দরজায়। সে রোজ রাতে বারোটা রুটি, ডাল-তরকারি আর মুরগির ঝােল খেয়ে ভোঁসভোঁসিয়ে চাদর-মুড়ি দিয়ে ঘুমোত, আর রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিত জ্যেঠু, বাবা আর প্রত্যয়।
ভাগ্যিস, তিন দিন পরই মিনিস্ট্রি অব কালচার থেকে বন্দুকধারী পাহারাদার সঙ্গে করে এসে সব হীরে-জহরত নিয়ে গেছিল। যাবার আগে অবশ্য মূর্তিগুলো ভালো করে দেখে গেছিল — যদি অন্য কোথাও, নাকের বা কানের ফুটোর মধ্যে — আরও কিছু পাওয়া যায়! গেটের ওপরের সিংহ, পুকুরের মাঝখানের পরীর চোখের কালোও ঘষে তুলে দেখেছিল, আরও হীরা আছে?
নাঃ, আর পাওয়া যায়নি কিছুই। জ্যেঠু বলেছিল, “রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণের বুদ্ধি যে তুখোড়, তাতে তো সন্দেহ নেই। কেমন ইংরেজদের ঠকিয়েছিল! সেই বুদ্ধিতেই সব মূর্তির চোখই কালো। পরী আর সিংহেরও। যাতে কেউ না ভাবে, আলাদা করে বাড়ির মানুষের মূর্তির চোখই কেন কালো?”
এখন হীরেগুলো না হলেও সরকার তার নকল পাঠিয়েছে পোনাপোতা মিউজিয়ামের জন্য। আর বেশ কিছু টাকা। তা দিয়ে বাড়ির একটা অংশে মিউজিয়াম হয়েছে। পাঁচিল সারানো হয়েছে। গুপ্তধনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দলে দলে লোক যেখান থেকে খুশি বাড়িতে ঢুকে পড়ছিল। সবাই গুপ্তধন খোঁজে! শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত গুপ্তধন খোঁজার টিকিট চালু করল। রায়সিংহ থেকে যত রিকশ, টোটো, অটো, আর সরাসরি হাইওয়ে থেকে যত গাড়ির সারি, সবাইকে গ্রামে ঢোকার আগে গুপ্তধন খোঁজার ফি দিতে হবে জেনে অর্ধেক লোক বিরক্ত হয়ে এমনিই ফিরে যেত, আর বাকি অর্ধেক টিকিট কেটে খানিক ঘুরঘুর করে চলে যেত খালি হাতে। আজও অনেকেই আসে। তারা মিউজিয়ামে টিকিট কিনে ঢোকে। তারা পোনাপোতার রাজবংশের ইতিহাস জেনে রাজা পৌণ্ড্রনারায়ণ কেমন ইংরেজদের ঠকাতেন, লুটপাট করে তাদেরই টাকায় তাদের ট্যাক্স দিতেন জেনে খুশি হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, কী সাংঘাতিক বুদ্ধি বাবা! আবক্ষ মূর্তির চোখের জায়গার গর্তগুলো খুঁটিয়ে দেখে বলে, কেমন লুকোনোর জায়গা ভেবেছিল, আহা!
জ্যেঠু এখন ইংল্যান্ড থেকে আনা সব কাগজপত্র আর নিজের লেখা স্থানীয় ইতিহাসের ওপর একটা সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শোয়ের ধারাভাষ্য লিখছে। এর পর তা-ও দেখা যাবে রাজবাড়ির মিউজিয়ামে।