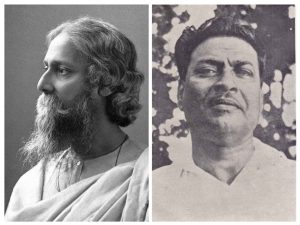কিছুটা মজা করে, কিছুটা অভিমানে বলতাম—আমি নিয়োগীর ‘বি’-টিমের লোক। ‘এ’-টিমে ছিলেন বিনায়কদা (সেন), আশীষদা (কুমার কুন্ডু)। শৈবালদা (জানা), চঞ্চলাদি (সমাজদার) আর আমি হাসপাতাল সামলাতাম। ওঁরা করতেন সংগঠনের কাজ—বিনায়কদা পূণর্ত, আশীষদা অংশত। ১৯৮৬-র ডিসেম্বরে আমি শহীদ হাসপাতালে যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিন পর পারিবারিক দায়িত্ব সামলাতে আশীষদা বিদায় নিলেন, কয়েক মাস পর চঞ্চলাদি। ১৯৮৭-এর শেষদিকে দল্লী-রাজহরা ছাড়লেন বিনায়কদা-ইলিনাদি। হাসপাতালে ডাক্তার বলতে রইলাম আমি আর শৈবালদা। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবী বলতে আমরা দু-জন ছাড়া অনুপ সিংহ। অনুপ ’১৯৮৭-তে মুক্তি মোর্চায় যোগ দেয় সবর্ক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য।
লোক কম, তাই হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-আন্দোলনের কাজ ছাড়াও সংগঠনের কাজে সময় দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল এই সময়, লোক বেশি থাকার সময় যার দরকার পড়েনি।
শংকর গুহনিয়োগী সম্বন্ধে, ছত্তিশগড় আন্দোলন সম্বন্ধে প্রথম জানি ১৯৭৯-এ, তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। যতদূর মনে পড়ে কাটের্ন নামের এক পত্রিকায় পড়েছিলাম সেসব কথা। ১৯৮২-তে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় এক সিনিয়র দাদা শুনিয়েছিলেন ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ-এর সাফাই আন্দোলন, শহীদ ডিস্পেন্সারি, শহীদ হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন…। তিনি ডা. পবিত্র গুহ, ১৯৮১ থেকে কয়েক মাস তিনি কাজ করেছিলেন সি এম এস এস-এর সঙ্গে। ( নিয়োগী শহীদ হওয়ার পর ১৯৯২-এ তিনি চাকরি ছেড়ে আবার ফিরে যান শহীদ হাসপাতালে। ১৯৯৪ অবধি সে হাসপাতালে ছিলেন। এখনও তিনি দল্লী-রাজহরায় থাকেন।) সেই গল্প শোনার পর থেকেই দল্লী-রাজহরা আমার স্বপ্নের দেশ, আমার স্বপ্ন সি এম এস এস-এর সঙ্গে কাজ করা।
স্বপ্নের দেশের অন্যতম রূপকারের সঙ্গে প্রথম দেখা ১৯৮৫-র জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে। ভোপালের গ্যাসপীড়িতরা ইউনিয়ন কার্বাইড প্রাঙ্গণে এক গণ-হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৩ জুন । আর কলকাতা ও বম্বে থেকে আসা জুনিয়ার ডাক্তারদের সহায়তায় শুরু হয় জন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ, সেখানে গ্যাসপীড়িতদের বিষ-গ্যাসের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন লাগানো হত এবং তাঁদের উপসর্গে উন্নতি নথিবদ্ধ করা হত। থায়োসালফেটে গ্যাস-পীড়িতদের উপসর্গে উন্নতি মানে বিষ-গ্যাসে সায়ানাইডের উপস্থিতি, তাতে ইউনিয়ন কার্বাইডের অপরাধের দায় বাড়ে। তাই ২৪শে জুন রাতে রাষ্ট্রের সন্ত্রাস নেমে আসে, গ্রেপ্তার হন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সংগঠকরা। বন্ধ কেন্দ্র চালু করতে কলকাতা থেকে জুনিয়ার বন্ধু ডা জ্যোতির্ময় সমাজদারের সঙ্গে গেছিলাম আমি। সেদিন জামিনে ছাড়া পাবেন বন্দিরা—এক টিলার ওপর ভোপাল জেলের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত এক দীঘর্দেহী পুরুষের স্লোগানে স্লোগান তুলছিল সমবেত জনতা—‘জেলকা তালা টুটেগা, হামারা সাথী ছুটেগা’—ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতা শংকর গুহনিয়োগী। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল, জানালাম তাঁর আন্দোলনে আমার কাজ করার স্বপ্নের কথা। হিন্দির টান-মেশানো বাংলায় বললেন—‘রাজনাদগাঁও-এ আরেকটা হাসপাতাল খোলার কথা ভাবছি, চলে আসুন…।‘
রাজহরা গেলাম ১৯৮৬-র অক্টোবরে এক সহপাঠীর সঙ্গে, আন্দোলনের চাক্ষুষ পরিচয় পেতে। নতুন বাসস্ট্যান্ডে দুর্গ থেকে আসা বাস নামাল। শহীদ হাসপাতাল কতটা দূরে জানি না, হাঁটছি। ট্রাক চলছে লাল-সবুজ পতাকা লাগিয়ে। ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ লেখা একটা জিপকে হাত দেখালাম। হাসপাতালে পৌঁছে দিল। একটা টিলার ওপরে হাসপাতাল, সামনে উঁচু ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে লাল-সবুজ পতাকা উড়ছে। অল্প দূরে বিশাল ইউনিয়ন অফিস, আন্দোলনে ব্যস্ত নিয়োগীর সঙ্গে কথা বলার সময় পেয়েছিলাম আধ-ঘণ্টটাক। ইউনিয়ন দপ্তরে বসে শুনিয়েছিলেন সে সব স্বপ্নের কথা, যা বাস্তব হয়ে চলেছে ছত্তিশগড়ের বুকে। ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরোতে বেরোতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম—দল্লী-রাজহরাই হবে আমার ভবিষ্যৎ কমর্ক্ষেত্র। মাসিক ভাতা কতো পাব জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়েছিল (জেনেছিলাম মাস তিনেক পর, শ্রমিকদের এক লম্বা হরতালের শেষে তিনমাসে ভাতা যখন একসঙ্গে পেলাম।)। কেবল বিদ্যুৎ আর পাকা শৌচাগার আছে কিনা, এ-দুটো ছিল আমার জানার বিষয়, আজন্ম কলকাতা শহরে লালিত আমার এ দুটো জিনিস ছাড়া চলত না।
১৯৮৬-র ডিসেম্বরে কলকাতা ছেড়ে এলাম। কলেজে পরিবতর্নকামী ছাত্র-রাজনীতি করতাম, স্বপ্ন দেখতাম শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, কিন্তু সমাজ-পরিবতর্নের রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক পড়াশুনা ছিল প্রায় শূন্য। সদা-ব্যস্ত নিয়োগীর সঙ্গে যখন দেখা হত, তাঁকে দেখতাম, তাঁর কথাগুলো শুনতাম, বোঝার চেষ্টা করতাম। আমার জীবনে রাজনীতির প্রধান শিক্ষক নিয়োগীজীই।
১৯৮৭-র ১ বা ২ জানুয়ারি হবে, দল্লী মাইন্সের শ্রমিকরা হরতালে ছিলেন। সে সুযোগে ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট মেশিনীকরণ না করার চুক্তিভঙ্গ করে ডাম্পার চালানোর চেষ্টা করে। ডাম্পার আটকাতে গিয়ে সি আই এস এফ-এর লাঠিচার্জে আহত হন ২১ জন শ্রমিক বা শ্রমিক নেতা—কারুর মাথা ফেটেছে, কারুর হাত ভেঙেছে। তাঁদের শহীদ হাসপাতালে আনা হল, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তাঁরা, বেদনানাশক ইঞ্জেকশনে সেরকম ফল হচ্ছে না। খবর পেয়ে ঘর থেকে ছুটে এসেছেন নিয়োগী, রাগে দাঁতে দাঁত চাপা। সহানুভূতির হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আহতদের শরীরে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—বেদনানাশক ইঞ্জেকশনে যে কাজ হয়নি, তা হল নিয়োগীর স্পর্শে—আহতরা যেন তাঁদের ব্যথা ভুলে শান্ত হয়ে গেলেন। (মায়ের কোলের স্পর্শে যেমন বাচ্চা তার পেটের ব্যথা ভুলে যায়, তেমনই যেন।) তারপর দ্রুত পদক্ষেপে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিজে জীপ ছোটালেন খনির দিকে। পরে শুনেছিলাম নিয়োগী রাগে সি আই এস এফ-এর কমান্ড্যান্টের কলার চেপে ধরেন, জওয়ানরা গুলি চালানোর জন্য বন্দুক উঁচিয়ে ধরে, মাঝখানে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এসে না পড়লে হয়ত নিয়োগীর ওপর গুলি চলে যেত। সেদিন বুঝেছিলাম সহযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, তাঁর অসম সাহসিকতা ও শ্রেণিঘৃণা। আর দেখেছিলাম একজন সত্যিকারের নেতাকে মানুষ কত ভালোবাসে।
যখন ছত্তিশগড়ে এলাম হিন্দি প্রায় জানতামই না, বাঙালি পেলে বাংলায় কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। নিয়োগীজীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলে সুবিধা হত না, উনি হিন্দিতে কথা চালিয়ে যেতেন, বলতেন ভুল হিন্দিতেই কথা বলতে। কেমন করে নিজে হিন্দি শিখলেন সে কথা শুনিয়েছিলেন—আত্মগোপন করে থাকার সময় প্রায় দশটা বছর সচেতনভাবে কোনো বাংলা বা ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেননি। আমাকে বলেছিলেন—‘হিন্দিতে ভাবনা-চিন্তা করুন, হিন্দিতে স্বপ্ন দেখুন, দেখুন হিন্দি আপনার আয়ত্তে এসে যাবে।’ হিন্দিতে স্বপ্ন দেখাটা হয়ে ওঠেনি, তবে ওঁর পরামর্শ অনুসরণ করে অবশ্যই ফল পেয়েছিলাম—হিন্দিতে বলা, হিন্দিতে লেখা, ছত্তিশগড় ছাড়ার প্রায় একুশ বছর পরও হিন্দিতে কথা বলায় আমি ইংরেজিতে কথা বলার চেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ।
নিয়োগী কো্নো আত্মজীবনী লেখেননি, সময় পেলেও লিখতেন বলে মনে হয় না। কাউকে পূর্ব জীবনের কথা এমনভাবে বলতেন না, যাতে সে authorized biography লিখতে পারে। কিন্তু জীবনের নানা পর্যায়ের গল্প, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭-এ ইমার্জেন্সির শেষ অবধি নানান গল্পের টুকরো আমি শুনেছি অনেকবার, অন্যরাও শুনেছেন।
এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম শংকরের (শংকর তাঁর আসল নাম নয়, আসল নাম ধীরেশ), বাবা হেরম্বকুমার, মা কল্যাণী। আসামের নওগাঁও জেলার যমুনামুখ গ্রামে বাবার কর্মস্থলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা, আসামের সুন্দর প্রকৃতি তাঁকে প্রকৃতিপ্রেমী করে তোলে। আর আসানসোলের সাঁকতোরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থেকে মাধ্যমিকের পড়াশুনা, যেখানে খনিশ্রমিকদের জীবন কাছ থেকে দেখে তিনি বুঝতে শেখেন কেমন করে বড়োলোক আরও বড়োলোক, গরিব আরও গরিব হয়। জলপাইগুড়িতে আই এস সি পড়ার সময় তিনি ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন, হয়ে ওঠেন ছাত্র ফেডারেশনের একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯৫৯-এর বাংলাজোড়া খাদ্য আন্দোলনের ঢেউ তাঁকে ভাসিয়ে নেয়। কুশল ছাত্রসংগঠক হিসেবে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। রাজনীতিতে মেতে থাকায় আই এস সি-র ফল ভালো হয়নি। তাও পারিবারিক সুপারিশে উত্তরবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি সীট পান। এই অন্যায়কে মেনে নিতে না পেরে তাঁর ঘর ছাড়া।
১৯৬১-র কথা—তখনও ভিলাই ইস্পাত কারখানায় চাকরি পাওয়া দুষ্কর ছিল না। নিয়োগীর কাছ থেকে শোনা—কারখানার রিক্রুটিং অফিসার দুর্গ স্টেশনে টেবিল পেতে বসে থাকতেন ট্রেন থেকে নামা, কাজের খোঁজে আসা মানুষজনকে কারখানার কাজে লাগাতে। ধীরেশের বয়স ছিল সে সময় সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর থেকে কয়েকমাস কম, তাই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। তারপর প্রশিক্ষণের শেষে কোক ওভেন বিভাগে দক্ষ শ্রমিকের চাকরি পেলেন তিনি। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষাও ছিল, তিনি দুর্গের বিজ্ঞান কলেজে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে বি এস সি এবং এ এম আই ই পড়তে লাগলেন। সে কলেজে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ধীরেশ। সেই কুশল নেতৃত্বের খবর পেয়ে এলেন দুর্গ পুরসভার সাফাইকর্মীরা। তাঁর নেতৃত্বে সফল ধমর্ঘট করে সাফাই কর্মীরা দাবিদাওয়া আদায় করেন। ইস্পাত কারখানার স্বীকৃত ইউনিয়ন ছিল আই এন টি ইউ সি-র। তারপর বড়ো ইউনিয়ন এ আই টি ইউ সি। নিয়োগী এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে থেকেও স্বাধীনভাবে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানে সংগঠিত করতে থাকেন।
১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে দু-টুকরো হয়, সি পি আই এম-এর সাথে আসেন ধীরেশ। সে সময় এক প্রবীণ কমিউনিস্ট চিকিৎসক ডা বি এস যদুর কাছে তাঁর প্রথাগত মাকর্সবাদ-লেনিনবাদের পড়াশুনা। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ির গণঅভ্যুত্থান মধ্যপ্রদেশকেও আলোড়িত করেছিল, রাজ্যের প্রায় সমস্ত সি পি আই এম কর্মী নকশালবাড়ির রাজনীতিতে প্রভাবিত হন। ধীরেশ অল ইন্ডিয়া কো-অডির্নেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভোলিউশনারিস-এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৯-এর ২২ এপ্রিল সি পি আই এম-এল গঠিত হওয়ার পর কিছুদিন তিনি তার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পার্টির গণসংগঠন-গণআন্দোলন বজর্নের লাইনের সঙ্গে নিজের কাজকর্মকে মেলাতে না পারায় তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। (উল্লেখ্য, যে বর্ষীয়ান কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে নিয়োগীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পরবতীর্কালে তিনিও কিন্তু একই প্রশ্নে পার্টি-লাইনের বিরোধিতা করেন।)
ইতিমধ্যে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে—১৯৬৮-তে ভিলাই ইস্পাত কারখানার প্রথম সফল ্ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়ে চাকরি খুইয়েছেন ধীরেশ। অন্যদিকে ‘নকশালপন্থী’ তকমা লাগিয়ে খুঁজছে পুলিশ। এই সময় তিনি আত্মগোপন করে একটা হিন্দি সাপ্তাহিকের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্য নিয়ে যেতে থাকেন, লেনিনের ‘ইস্ক্রা’র অনুপ্রেরণায় সেই পত্রিকার নাম রেখেছিলেন ‘স্ফুলিঙ্গ’। অন্যদিকে চলে গ্রামে যাওয়ার প্রস্তুতি। এই সময় তিনি বুঝতে পারছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত ছত্তিশগড়ী জাতিসত্ত্বার মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না। ছত্তিশগড়ী জাতি-সমস্যা নিয়ে রচিত তাঁর সে সময়কার একটা পুস্তিকা মহারাষ্ট্র থেকে ছেপে আসার পথে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।
ছত্তিশগড়কে জানার জন্য, ছত্তিশগড়ী জনতাকে জানার জানার জন্য, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য ১৯৬৮ থেকে তিনি গ্রামে-গ্রামে আত্মগোপন করে দিন কাটাতে থাকেন। কখনও ছাগল বিক্রেতা—গ্রাম থেকে ছাগল কিনে বিক্রি করতে যান দুর্গ-ভিলাইয়ে, সেখানে সাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায় সেভাবে। কখনও ফেরিওয়ালা, কখনও জেলে, কখনও বা পি ডাব্লু ডি-র শ্রমিক। এর সাথে সাথে চলে মানুষকে সংগঠিত করার কাজ—দৈহান বাঁধ তৈরীর আন্দোলন, সেচের জলের দাবীতে বালোদের কৃষকদের আন্দোলন, মোঙ্গরা বাঁধ তৈরীর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলন…। নিয়োগীর কাছে শোনা—ছত্তিশগড়ী ভাষা শেখার জন্য, ছত্তিশগড়ীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য প্রায় দশ বছর তিনি সচেতনভাবে কোনো বাংলা বা ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেননি তিনি।
১৯৭১-এ কাজ পেলেন ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের দানীটোলা কোয়ার্জাইট খনিতে এক ঠিকাদারি শ্রমিক হিসেবে, কোক ওভেনের দক্ষ শ্রমিক হাফপ্যান্ট পরে পাথর ভাঙ্গেন। যে নামে তিনি খ্যাত সেই ‘শংকর; এই সময়কারই ছদ্মনাম। এখানেই পরিচয় ও পরিণয় সহশ্রমিক সিয়ারামের কন্যা আশার সঙ্গে। তাঁর তৈরী প্রথম খনিশ্রমিকদের ইউনিয়নও দানীটোলায়, যদিও তা এ আই টি ইউ সি-র ব্যানারে। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় মিসা-এ গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অবধি দানীটোলাতেই শ্রমিক সংগঠন করতেন নিয়োগী।
ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের সবচেয়ে বড়ো লোহাপাথর খনি দল্লী-রাজহরায়। নিয়োগী যখন রায়পুর জেলে বন্দি, তখন দল্লী-রাজহরার ঠিকাদারি খনিশ্রমিকরা উত্তাল স্বতঃস্ফূর্ত এক আন্দোলনে। আই এন টি ইউ সি ও এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব ভিলাই ইস্পাতের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এক বোনাস সমঝোতা করে—চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী শ্রমিকরা পাবেন ৩০৮ টাকা আর ঠিকাদারী শ্রমিকরা ৭০ টাকা, যদিও দুই ধরনের শ্রমিকরা একই ধরনের কাজ করেন। অন্যায় চুক্তির প্রতিবাদে শ্রমিকরা এই দুই ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এলেন। জরুরি অবস্থার শেষ সময় সেটা—১৯৭৭-এর ৩রা মার্চ শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে লাল ময়দানে শুরু করেছেন অনির্দিষ্টকালীন ধর্না। তাঁরা খুঁজছেন কে হবেন তাঁদের সেনাপতি, কে নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের। শ্রমিকদের উগ্রমূর্তি দেখে সি আই টি ইউ, এইচ এম এস, বি এম এস—কোনো ইউনিয়নের নেতাই ধারে ঘেঁষার সাহস পেলেন না। কয়েকদিন পর জরুরি অবস্থার শেষে জেল থেকে ছাড়া পেলেন শংকর। দল্লী-রাজহরা থেকে দানীটোলার দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। এ আই টি ইউ সি থেকে বেরোনো কিছু শ্রমিক সৎ লড়াকু শ্রমিক নেতা হিসেবে নিয়োগীকে জানতেন। তাই দল্লী-রাজহরার শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদল নিয়োগীকে দল্লী-রাজহরার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করতে দানীটোলা গেল। তাঁদের অনুরোধে নিয়োগী দল্লী-রাজহরা এলেন, গঠিত হল ঠিকাদারী খনিশ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠন—ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ (সি এম এস এস)। নতুন ইউনিয়নের পতাকা লাল-সবুজ—লাল শ্রমিকশ্রেণির আত্মবলিদানের রং, সবুজ কৃষকের।
শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে খনিশ্রমিকদের প্রথম লড়াই ছিল মর্যাদার লড়াই—তাঁরা দালাল নেতাদের সই করা চুক্তি মানবেন না। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে তাঁরা ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে ৭০ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা বোনাস বাবদ নিলেন।
১৯৭৭-এর মে মাসে শুরু হলে আইডল ওয়েজ (মালিক শ্রমিককে কাজ দিতে না পারলে যে বেতন দেওয়া উচিত) এবং বর্ষার আগে ঘর-মেরামতের বাঁশবল্লী বাবদ ১০০ টাকার দাবিতে আন্দোলন। আন্দোলনের চাপে ৩১ মে শ্রমবিভাগের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদাররা সি এম এস এস-এর সঙ্গে চুক্তিতে এই দুই দাবি মেনে নেয়। কিন্তু ১ জুন শ্রমিকরা যখন ঘরমেরামতের টাকা আনতে যান তখন ঠিকাদাররা তা দিতে অস্বীকার করে। আবার শুরু হয় শ্রমিক ধমর্ঘট।
পরের দিন অর্থাৎ ২ জুন রাতে দুটো জিপ ভর্তি পুলিশ আসে নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করতে। ইউনিয়নের ঝুপড়ি থেকে নিয়োগীকে তুলে নিয়ে একটা জিপ বেরিয়ে যায়। অন্য জিপটা বেরোনোর আগে শ্রমিকদের ঘুম ভেঙে যায়, তাঁরা বাকি পুলিশদের ঘিরে ফেলে নেতার মুক্তির দাবী করতে থাকেন। ঘেরাও ভাঙতে পুলিশ গুলি চালিয়ে নারী-শ্রমিক অনুসূইয়া বাই ও বালক সুদামা সহ মোট ৭ জনকে হত্যা করে সে রাতে, কিন্তু নিজেরা মুক্ত হতে পারে না। অবশেষে ৩ জুন দুর্গ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে আরও ৪ শ্রমিককে হত্যা করে আটক পুলিশদের মুক্ত করে। এই ১১ জনই হলেন লাল-সবুজ সংগঠনের প্রথম শহীদদের দল।
পুলিশি অত্যাচার কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। ১৮দিন লম্বা ধমর্ঘট চলার পর খনি-ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদাররা আবার শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। জেল থেকে ছাড়া পান নিয়োগী।
এই বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের অন্যান্য খনি দানীটোলা, নন্দিনী, হিররী গড়ে ওঠে সি এম এস এস-এর শাখা। সব শাখা মিলে আবার আন্দোলনের ঢেউ, আবারও বিজয়…।
দল্লী-রাজহরা দুর্গ জেলায়, পাশের জেলা বস্তার। বস্তারের বাইলাডিলা লোহাখনিকে পূর্ণত মেশিনীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি যার অবশ্যম্ভাবী ফল। মেশিনীকরণকে ঠেকাতে এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্বে বাইলাডিলার সংগ্রামরত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় জনতা সরকারের পুলিশ, ১৯৭৮-এর ৫ এপ্রিল। সেই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান দল্লী-রাজহরার শ্রমিক, পাশাপাশি নিয়োগী তাঁদের অনুভব করান দল্লী-রাজহরার আসন্ন মেশিনীকরণের বিপদ সম্পর্কে। শ্রমিকরা মেশিনীকরণ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে ম্যানেজমেন্টকে বাধ্য করে ইউনিয়নের ‘অর্ধ-মেশিনীকরণের প্রস্তাব’ মেনে নিতে—যাতে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না, অথচ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান উন্নত হবে। তাঁরা মেশিনীকরণ রুখে রেখেছিলেন ১৯৯৪ অবধি। (১৯৯৪-এ নেতৃত্বের একাংশ শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দল্লী খনিকে পূর্ণ মেশিনীকরণের জন্য ম্যানেজমেন্টের হাতে তুলে দেয়।)
ইউনিয়নের একের পর এক অথর্নৈতিক আন্দোলনে বিজয়ের ফলে দল্লী-রাজহরার শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়, কিন্তু তার ফলে বাড়ে না জীবনযাত্রার মান। বরং আদিবাসী শ্রমিকরা মদের পেছনে পয়সা খরচ করা বাড়িয়ে দেন। নিয়োগী প্রশ্ন তোলেন—তাহলে কি শহীদদের রক্ত মদের ভাটিখানার নালায় বইবে? এক অভিনব শরাববন্দী আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ মানুষ মদের নেশা থেকে মুক্ত হন। অবশ্য এ আন্দোলন চালাতে গিয়ে ১৯৮১-তে নিয়োগী এন এস এ-তে বন্দী হতে হয় শংকর গুহনিয়োগীকে।
নিয়োগী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দেন। এত দিন অবধি কোনো ইউনিয়নই বেতন-বৃদ্ধি, বোনাস দাবি করা বা চাজর্শিটের জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করত না, অর্থাৎ শ্রমিকের কমর্ক্ষেত্র সংক্রান্ত বিষয়গুলোই ছিল কেবল ট্রেড ইউনিয়নের আওতায়। নিয়োগী বললেন ট্রেড ইউনিয়ন কেবল শ্রমিকের দিনের আট ঘণ্টা (কর্মসময়)-এর জন্য নয়, ইউনিয়নকে হতে হবে ২৪ ঘণ্টার জন্য। এই ভাবনা নিয়ে দল্লী-রাজহরায় অনেকগুলো নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালায় নতুন ইউনিয়ন।
শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতির জন্য গঠিত হয় মোহল্লা কমিটি। ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের চালানো স্কুলে ঠিকাদারি শ্রমিকদের শিশুদের পাড়ার ব্যবস্থা ছিল না, তাদের শিক্ষার জন্য ইউনিয়নের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ৬টা প্রাইমারি স্কুল, নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার কমর্সূচি নেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য আন্দোলনের চাপে সরকার ও খনি-ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয় শহরে অনেকগুলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল খুলতে। স্বাস্থ্য আন্দোলন শুরু হয় সাফাই আন্দোলনের রূপ নিয়ে, ১৯৮২-র ২৬ জানুয়ারি শুরু হয় শহীদ ডিস্পেন্সারির কাজ, ১৯৮৩-র শহীদ দিবসে ১৯৭৭-এর শহীদদের স্মরণে শহীদ হাসপাতাল। শ্রমিকদের অবসর-বিনোদন এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারের জন্য গড়ে ওঠে নয়া আঞ্জোর (নতুন রোশনি)। শরীর-চর্চার জন্য গড়ে ওঠে শহীদ সুদামা ফুটবল ক্লাব, রেড-গ্রিন অ্যাথলেটিক ক্লাব । নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য গড়ে ওঠে মহিলা মুক্তি মোর্চা। ছত্তিশগড়ের শোষণ-মুক্তি ও ছত্তিশগড়ে শ্রমিক-কৃষকের রাজ স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয় ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা। সরকারের জনবিরোধী বননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউনিয়ন দপ্তরের পিছনে এক মডেল বন-সৃজন করা হয়।
১৯৭৮ সালে গঠিত ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের ১৭ টি বিভাগ
১। ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগ
২। বকেয়া ও ফল-ব্যাক বেতন নিয়ে কাজ করার বিভাগ
৩। কৃষক বিভাগ—১৯৭৯ এ ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চায় পরিণত
৪। শিক্ষা বিভাগ
৫। সঞ্চয় বিভাগ
৬। স্বাস্থ্য বিভাগ
৭। ক্রীড়া বিভাগ
৮। নেশাবন্দী বিভাগ
৯। সাংস্কৃতিক বিভাগ
১০। শ্রমিক-বস্তি উন্নয়ন বিভাগ
১১। মহিলা বিভাগ—১৯৮০-তে মহিলা মুক্তি মোর্চা
১২। মেস বিভাগ (ইউনিয়ন দপ্তরের সামূহিক রান্নাঘর)
১৩। নির্মাণ বিভাগ
১৪। আইন বিভাগ
১৫। লাইব্রেরী বিভাগ
১৬। প্রচার বিভাগ
১৭। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বিভাগ
১৮। পরিবেশ বিভাগ গঠিত হয় ১৯৮৪-তে।
ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার আন্দোলনে বড়ো ভূমিকা ছিল মহিলাদের। শ্রমিক সংগঠনের যে মুখিয়া মিটিং-এ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় থাকতেন মহিলারা, তবে ঠিক ৫০% নয়। কেন না, খনিতে ঠিকাদারি শ্রমিকরা করতেন দুই ধরনের কাজ—রেজিং অর্থাৎ পাথরভাঙার কাজ করতেন মহিলা-পুরুষ উভয়েই, ট্রান্সপোর্টিং অর্থাৎ ট্রাকে পাথর লোড করার কাজ করতেন কেবল পুরুষরা। প্রতি রেজিং এলাকা থেকে সমসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা নিবার্চিত হতেন, ট্রান্সপোর্টিং থেকে কেবল পুরুষরা, মোহল্লা থেকে মহিলা-পুরুষ সমসংখ্যায়। তার ফলে সব মিলিয়ে মুখিয়া মিটিং-এ পুরুষদের থেকে মহিলারা সংখ্যায় কিছু কম হতেন। শ্রমিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন মহিলা শ্রমিকরা। আবার মহিলা মুক্তি মোর্চা সংগঠনে নারী শ্রমিকরা অন্য নারীদের সংগঠিত করতেন। (দ্রষ্টব্যঃ ছত্তিশগড়ের নারী জাগরণ—চন্দনা মিত্র, সংঘর্ষ ও নির্মাণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনা)
নিয়োগীর অভিনব নেতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ লাল-সবুজ পতাকা হাতে তুলে নিতে থাকেন। সে সময় ছত্তিশগড় ছিল মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সাতটা জেলা নিয়ে, তার মধ্যে পাঁচটায়—দুর্গ, বস্তার, রাজনাদগাঁও, রায়পুর, বিলাসপুরে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সংগঠন ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এদের মধ্যে ছিলেন ছত্তিশগড়ের সবচেয়ে পুরোনো কারখানা রাজনাদগাঁও-এর বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলস-এর শ্রমিকরাও, তাঁদের আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালায় ১৯৮৪-র ১২ সেপ্টেম্বর, শহীদ হন চার জন, কিন্তু আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।
শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে লড়া শেষ সংগ্রাম ছিল ভিলাই শ্রমিক সংগ্রাম। ছত্তিশগড়ের শোষণের কেন্দ্র ভিলাইয়ে ১৯৯০-এ শুরু এ লড়াই কারখানা মালিকদের আতঙ্কিত করে তোলে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ছিল শ্রমিকদের দাবিগুলো—বেঁচে থাকার মতো বেতন, স্থায়ী শিল্পে স্থায়ী চাকরি, ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার। খনিজ, বনজ ও জল সম্পদে ভরপুর ছত্তিশগড় আবার সস্তা শ্রমেরও জোগানদার। সেখানে শ্রমিকদের এ ধরনের দাবি মেনে নেওয়ার ফল সুদূরপ্রসারী ও মালিকপক্ষের পক্ষে ভয়ংকর। তাই আন্দোলনকে ভাঙতে হাত মেলায় পুলিশ-প্রশাসন-প্রায় সব রাজনৈতিক দল।
শ্রমিক নেতাদের ওপর গুন্ডা ও পুলিশের হামলা, ১৯৯১-এর ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ এপ্রিল পুরোনো মামলার ওয়ারেন্ট বার করে নিয়োগীকে বন্দী করে রাখা, নিয়োগীকে পাঁচ জেলা থেকে বহিষ্কারের প্রয়াস—কোনো কিছুই আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। আন্দোলনের পক্ষে দেশের জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বরের নিয়োগীর নেতৃত্বে এক বিশাল শ্রমিক দল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দিয়ে এল। তার পক্ষকাল পরে ২৮ সেপ্টেম্বর নিয়োগীকে হত্যা করে কারখানা মালিকের গুপ্ত-ঘাতক।
তাঁর হত্যার অনেক আগেই নিয়োগী জানতে পেরেছিলেন হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা, লিখে গিয়েছিলেন ডায়েরিতে, বলে গিয়েছিলেন একটা ক্যাসেটে। তবু আসন্ন অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি ছিলেন অবিচল, কেননা—‘মৃত্যু তো সবারই হয়, আমারও হবে। আজ, নয় তো কাল।…আমি এ পৃথিবীতে এমন এক ব্যবস্থা স্থাপন করতে চাই যেখানে শোষণ থাকবে না…। আমি এ সুন্দর পৃথিবীকে ভালোবাসি, তার চেয়েও ভালোবাসি আমার কর্তব্যকে। যে দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি, তাকে সম্পন্ন করতেই হবে। …আমাকে মেরে আমাদের আন্দোলনকে শেষ করা যাবে না।’
কলেজ-জীবনে আমার বেড়ে ওঠা যে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনে তাঁর নেতৃত্বে ছিলেন মাকর্সবাদী-লেনিনবাদীরা। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই নিয়োগীকে মেলাতে পারতাম না, সন্দেহ হত লোকটা সংশোধনবাদী নয়তো! ১৯৮৭-র মে মাসে নিয়োগী পড়ে গিয়ে পা ভাঙেন—ফ্রাকচার নেক ফিমার—অপারেশন হয়েছিল ৩ জুন। এই একবারই কেবল তিনি ৩ জুন শহীদ দিবসে দল্লী-রাজহরায় ছিলেন না। অপারেশনের পর সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন শহীদ হাসপাতালে ভর্তি রইলেন তিনি। নিয়োগীর পা-ভাঙা আমার কাছে যেন বর হয়ে এল। আস্তে আস্তে অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল এই সময় থেকে।
তারপর বারবার নানা প্রশ্ন নিয়ে গেছি, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছি, তর্ক-বিতর্ক করেছি, ঝগড়াও করেছি কখনো-সখনো। ভোর হোক বা গভীর রাত—কখনো তাঁকে রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক আলোচনায় ক্লান্ত হতে দেখিনি। আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক করার সময় কখনো তিনি বুঝতে দিতেন না যে, আমি তাঁর চেয়ে আঠেরো বছরের ছো্টো, তত্ত্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম। রাজনৈতিক আলোচনায় কেবল যুক্তির স্থান ছিল, বিন্দুমাত্র অহমিকার স্থান থাকত না। ( ছত্তিশগড় থেকে ফিরে আমি নব্বই দশকের গোড়ায় বাংলা আন্দোলিত করা এক শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হই, স্বাস্থ্য-কমর্সূচির দায়িত্ব নিয়ে। তখন সে আন্দোলনের উপদেষ্টা নামকরা ক-জন মধ্যবিত্ত শ্রমিক-নেতার কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। দেখতাম কমরেড নিয়োগীর সঙ্গে তাঁদের আকাশ-পাতাল তফাত।)
১৯৭৯-এ ছাত্র রাজনীতি করা শুরু করার সময় থেকেই আমি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের সদস্য থেকেছি জীবনের নানা পর্যায়ে। ছমুমো-তে গণতন্ত্রের যে প্রয়োগ দেখেছি তেমনটা দেখিনি অন্য কোনো সংগঠনে। ‘ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা’ নামক প্রবন্ধে নিয়োগী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা নিয়ে এক ছোট অথচ মূল্যবান আলোচনা করেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে সংগঠন চালানোর প্রয়াস দেখেছি ছমুমো-র সংগঠনগুলিতে। আন্দোলনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত, সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হতো আর এইসব সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করা হত কেন্দ্রীকতার মাধ্যমে।
বাস্তবে ব্যাপারটা কীভাবে হত? সপ্তাহে একটা দিন বিকেল নিদির্ষ্ট থাকত মুখিয়া মিটিং-এর জন্য। খনি-র প্রতিটা এলাকা, শহরের প্রতিটা মোহল্লা থেকে তিনশতাধিক মুখিয়া থাকতেন সে মিটিং-এ। আলোচ্য বিষয় নিয়ে যত ব্যাপক সম্ভব আলোচনা করা হত। পিছিয়ে থাকা শ্রমিক প্রতিনিধিরা যদি তাঁর উপস্থিতিতে মুখ খুলতে সংকোচ বোধ করেন, তাই আলোচনার প্রথম পরযায়ে অনেক সময়ই নিয়োগী থাকতেন না। সেদিন মিটিং-এ যে সিদ্ধান্ত হত, তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। পরের দিন কাজ শুরুর আগে মুখিয়ারা নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং করে আগের দিনের আলোচনার রিপোর্টিং করতেন। সাধারণ শ্রমিকরা আগের দিনের সিদ্ধান্তকে মঞ্জুর করলে তা সংগঠনের সিদ্ধান্ত হত, নতুবা তাঁদের মত নিয়ে আবার মিটিং-এ বসতেন মুখিয়ারা। এইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তা কারযকর করার জন্য সমস্ত শ্রমিক দায়বদ্ধ থাকতেন। ইউনিয়নের নেতা চাঁদা ধারয করলেন, কিছু শ্রমিক দিলেন, কিছু দিলেন না—এমনটা দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। ছমুমো-র সংগঠনে তেমনটা হত না, ১০০% শ্রমিক চাঁদা দিতেন তা হোলটাইমারদের ভাতার জন্য শ্রমিকপিছু ১টাকাই হোক বা সংসদীয় নিবার্চনের ছমুমোর লড়ার জন্য এককালীন দেড়শ’ টাকা। আন্দোলন বা অন্য কমর্সূচিতে অংশগ্রহণ করতেন অসুস্থ মানুষ ছাড়া সবাই-ই।
পাঁচটা বছর নিয়োগীকে দেখেছি। দেখেছি একজন মানুষ কীভাবে মাকর্সবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করে চলেছেন জীবনে, কাজ-কর্মে, প্রতিটি আন্দোলনে। আমার আগে দেখা মাকর্সবাদী-লেনিনবাদীদের মতো তাঁকে কথায় কথায় উদ্ধৃতি আওড়াতে শুনিনি কখনো। মাকর্সবাদ তাঁর কাছে কোনো গোঁড়ামি ছিল না, ছিল ‘মূর্ত পরিস্থতির মূর্ত বিশ্লেষণ’-এর এক দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
ছত্তিশগড়ে এসেছিলাম পেশা হিসেবে ডাক্তারি করার পাশাপাশি রাজনীতি করব বলে। রাজনীতি করা বলতে বুঝতাম মিটিং-মিছিল, কিছু অ্যাকশনে অংশ নেওয়া। ১৯৮৮-তে একবার এক মারামারির ঘটনায় আমি ও অনুপ সিংহ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে যাই। খবর পাওয়া মাত্র নিয়োগীজী ছুটে এসে আমাদের সরিয়ে দেন, নিজে ঘটনাটা সামলান। ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম—কেবল ডাক্তারি করার জন্য ছত্তিশগড়ে এসেছি নাকি! আমাদের মাথা ঠান্ডা হলে নিয়োগী আমাদের নিয়ে বসলেন, সরল অথচ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন সমাজ-পরিবতর্নকামী বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা—‘আপনারা হিরো নন, আসল বীর তো সংগ্রামী জনগণ…আপনাদের কাজ শিক্ষকের…পড়াশুনা করেছেন, যে বিজ্ঞানে আপনি পারদর্শী সে বিজ্ঞানের কথা, সমাজবিজ্ঞানের কথা শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আপনাদের কর্তব্য…।’ সেদিনের পর থেকে এ ধরনের ভুল না করার চেষ্টা করেছি, নিয়োগী যে দায়িত্বের কথা বলেছিলেন আজও সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে চলেছি।
কিছু সহকর্মীর সমালোচনায় নিয়োগীকে ক্ষমাহীন মনে হত, তাদের সামান্যমাত্র ভুলত্রুটি তাঁর চোখ এড়াত না। দেখতাম নিয়োগীজী আমার ছোটো একটা ভুল হলে তীব্র সমালোচনা করেন, অথচ আরেক বুদ্ধিজীবী একই ধরনের বড়ো ভুল করলেও তিনি কিছুই বলেন না। ক্ষোভ জমছিল, ভাবতাম নিয়োগীজী পক্ষপাতিত্ব করছেন। একদিন এ নিয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন—‘যাকে আমি ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার সহযোদ্ধা ভাবি, তার ভুলভ্রান্তির তীব্র সমালোচনা করে তাকে শোধরানো আমার দায়িত্ব . . . । যে যুক্তফ্রন্টে আমার সহযোদ্ধা তার প্রতি আমার ব্যবহার অবশ্যই অন্যরকম হবে . . . ।’ সেদিন থেকে তাঁর প্রত্যেকটা সমালোচনা আমার কাছে কাম্য হয়ে উঠেছিল।
সহকমীর্দের ছোটোখাটো কষ্ট-অসুবিধা তাঁর চোখ এড়াত না। একটা ঘটনা বলি—আমি যখন শহীদ হাসপাতালে যোগ দিই তখন দল্লী-রাজহরা ও রাজনাদগাঁও-এ লম্বা হরতাল চলছে, ফলে ডাক্তারদের মাসিক ভাতা অনিয়মিত। একবার বাড়ি যাব, কাছে আসা-যাওয়ার ট্রেনভাড়া ছাড়া আর কিছু নেই। সংকোচে কাউকে বলিনি আমার প্রয়োজনের কথা। বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছি, রাস্তায় এক মোটরসাইকেল সারানোর দোকানে নিয়োগী বসেছিলেন, ডাকলেন আমাকে। বসিয়ে আড্ডা মারতে লাগলেন, বাসের সময় হয়ে আসছে, আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি। এমন সময় এক সাথী দু-হাজার টাকা নিয়োগীকে এনে দিলেন, তিনি তুলে দিলেন আমার হাতে। আমি বাড়ি যাব অন্য কারুর কাছে জানতে পেরে তিনি এক জায়গা থেকে ধার করে এনেছিলেন টাকাটা। কেবল আমার জন্য নয়, সব সহকর্মী, সংগঠনের সাধারণ সদস্যের সুখ-দুঃখের প্রতি একই রকম নজর রাখতেন তিনি।
১৯৯১-এর জানুয়ারি মাসে আমি আর নিয়োগী কলকাতা যাব—২৫ জানুয়ারি কৃষ্ণনগরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী সমিতির কনভেনশন, ২৬ স্টুডেন্টস’ হলে মতপ্রকাশ পত্রিকা ও নাগরিক মঞ্চ আয়োজিত সেমিনার। বোম্বে মেলে একটাই মাত্র রিজার্ভেশন পাওয়া গেছিল। নিয়োগী জবরদস্তি আমাকে শোয়ালেন তাঁর বার্থে তাঁর পাশে।
নিয়োগীজীকে বারবার বলেছি—‘আপনার ভাবনাচিন্তাগুলো লিখুন’। উনি কমই সময় পেতেন লেখালিখি করার। বেশ কয়েকবার বলেছেন উনি—‘ডাক্তারসাব, আপনার সঙ্গে যেসব আলোচনা হয়, লিখতে থাকুন’। কিছু কিছু লিখেছি, ততটা গুরুত্ব দিইনি কথাটাকে, জানতাম না এত তাড়াতাড়ি উনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।
কমীর্দের বিকাশের প্রতি অসম্ভব যত্নশীল ছিলেন। যে কেউ সৃজনশীল কোনো পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে অপরিসীম সাহায্য পেত। নিজে স্বপ্ন দেখতেন, অন্যদের স্বপ্ন দেখতে শেখাতেন, কেউ স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে চাইলে খুশি হতেন।
নিয়োগীজীর অনুপ্রেরণায় অনেকটা আন্দোলনেরই প্রয়োজনে আমি লিখতে শিখলাম, কিছুটা ছবি তুলতে, কিছুটা ছবি আঁকতে শিখলাম। ভিলাই আন্দোলনের শুরু থেকে সে আন্দোলনের খবর ছত্তিশগড়ের বাইরে পৌঁছাতে শুরু করলাম Update from Chhattisgarh পত্রিকায়। গড়ে তুললাম ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার প্রকাশন বিভাগ—‘লোক সাহিত্য পরিষদ’। শহীদ হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য-শিক্ষার উদ্দেশ্যে দু-মাস ছাড়া বেরোতে লাগল ‘লোক স্বাস্থ্য শিক্ষামালা’-র পুস্তিকা। নিয়োগী পারতপক্ষে নাক গলাতেন না, অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রকাশনার প্রচার-প্রসারে সাহায্য পেতাম সাবলীলভাবে।
বেড়াতে আমি খুব একটা ভালোবাসি না। কিন্তু নিয়োগীজীর সঙ্গে বেরোনোর সুযোগ আমি হারাতে চাইতাম না, কেননা সেটা হত এক প্রাণবন্ত ক্লাস। ১৯৯১-এর ৮ সেপ্টেম্বর, ভিলাই থেকে নিয়োগীর ফোন এল ইউনিয়ন দপ্তরে—‘ডা গুণকো ভেজো, মেরে সাথ দিল্লি জানা হায়।’ সারা রাস্তা নানা পরিকল্পনা করতে করতে গেছি আমরা—নিয়োগী, জনক (জনকলাল ঠাকুর—ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সভাপতি, ডোন্ডী-লোহারার ভূতপূর্ব বিধায়ক) ও আমি। Update from Chhattisgarh-এর কোয়ালিটি ভালো করতে হবে, ছত্তিশগড়ী ভাষা-প্রসারের জন্য ‘লোকসাহিত্য পরিষদ’-এর ‘ছত্তিশগড়ী ভাষা প্রসার সমিতি’ গড়তে হবে, শ্রমিক-কবি ফাগুরাম যাদবের ক্যাসেট বানাতে হবে, আন্দোলনে বিজয়ের পর ভিলাইয়ে হাসপাতাল তৈরি হবে . . . । ট্রেনে চা খেলাম এমন এক মাটির খুরিতে যার মুখটা ছোটো, চা চলকায় না। নিয়োগীজী একটা খুরি নিয়ে নিতে বললেন, ছত্তিশগড়ের কুমোরদের দিয়ে বানাতে হবে . . . ।
১৩ সেপ্টেম্বর জনক অন্য সাথীদের নিয়ে ফিরে এল, নিয়োগীজী আমাকে একদিন রেখে দিলেন, পরিচয় করালেন আন্দোলনের সমথর্ক অনেক সাথীর সঙ্গে। পরে মনে হত, যেন তিনি নিজের কাজগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছিলেন। দিল্লি যাওয়ার আগে এক মিনি ক্যাসেটে নিয়োগী রেকর্ড করে গিয়েছিলেন নিজের মনের ভাবনা—তিনি জানতেন তাঁকে হত্যার চক্রান্ত চলছে। সংগঠনের তিন বুদ্ধিজীবী ও ছয় শ্রমিক নেতাকে নিয়ে এক কেন্দ্রীয় নিণার্য়ক সমিতি গঠনের পরামর্শ ছিল তাঁর…। ক্যাসেটটা প্রথম শুনি ৫ অক্টোবর। আশ্চর্য লাগছিল—নিজের আদর্শের প্রতি কতটা নিষ্ঠা থাকলে একজন মানুষ আসন্ন মৃত্যুর সামনে এত নির্বিকার থাকতে পারেন!
জীবিত নিয়োগীর সঙ্গে শেষ দেখা ২৪ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার, তাই হাসপাতালে ছুটি, সারা সকাল অফিসে কাটিয়ে অপরাহ্নে কোয়ার্টারে এসেছি রাতের রান্না সেরে রাখব বলে। আনসার (রাজনাদগাঁও-এর সংগঠক) এসে খবর দিল—‘ডাক্তারসাব, নিয়োগীজী বুলা রহে হ্যাঁয়’। হাতের কাজে বাধা পড়ায় একটু বিরক্ত হয়ে অফিসে গেলাম। নিয়োগীজী ভিলাই যাবেন (এটাই ছিল তাঁর শেষবারের মত দল্লী-রাজহরা থেকে ভিলাই যাওয়া), তাঁকে কয়েকটা ফাইল তৈরি করে দিতে হল—টেলিফোন নাম্বারের, দিল্লিতে ধরনার, ভিলাই আন্দোলনের ছবির, বনখেড়ী কাণ্ডের . . . । তারপর নিয়োগী বলতে থাকলেন দিল্লি থেকে ফেরার পথে বনখেড়ী যাওয়ার কথা, ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী পাটওয়া ও শ্রমমন্ত্রী লীলারাম ভোজওয়ানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার . . . । পরিবেশ নিয়ে তাঁর লেখা বই করা হবে, তার প্রচ্ছদ কেমন চান—বিস্তারে বললেন (না, তেমনটা করতে পারিনি)। Update–এর কোয়ালিটি ভালো করতে হবে, ইলেক্ট্রনিক টাইপরাইটার আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সন্ধ্যার রাউন্ডের সময় হয়ে যাচ্ছিল, উঠতে চাইছি, নিয়োগীজী বলছেন—‘আপসে আউর কুছ বাত করনী হ্যাঁয়’। এমন সময় এক ঠিকাদারের ম্যানেজার এল কিছু সমস্যা নিয়ে। আমার দেরী হচ্ছে, এবার উঠবই, নিয়োগী বললেন—‘যাতে ওয়ক্ত হাসপাতালমেঁ আপসে মিলকর যাউঙ্গা’। যেকোনো কারণেই হোক সেদিন নিয়োগী আসতে পারেননি, সেদিন নয়, আর কোনো দিনই নয়।
২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তিন শ্রমিক-সাথীর সঙ্গে মিলে দুর্গের মর্গ-ঘরের টেবিল থেকে নামিয়েছি তাঁর রক্তে ভেজা মরদেহ। মৃত্যুর পর তখন প্রায় নয় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ তখনও তাঁর পিঠের গুলির ক্ষত থেকে ঝরে পড়ছে তাজা লাল রক্ত। আমার নেতা, আমার সহযোদ্ধা, আমার শিক্ষক শংকর গুহনিয়োগী শহীদ হলেন। বীর কমরেডের মরদেহ আমরা ঢেকে দিলাম ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার লাল-সবুজ পতাকা দিয়ে।
মৃত নিয়োগীর সঙ্গে ছিলাম ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর। দেশি পিস্তলের বুলেটের ছ-টা ছররা পিঠ ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিয়েছে, অথচ মুখে কোনো যন্ত্রণার ছাপ নেই, স্বপ্নদ্রষ্টা আমার নেতা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখছেন, মুখে হালকা একটা হাসি! যেন ‘নিয়োগীজী’ বলে ডাকলেই চোখ খুলে বলবেন ‘কেয়া খবর ডাক্তারসাব’!
নিয়োগী-হত্যার ৫ মাস বাদে প্রথম তাঁর স্মৃতিচারণ করেছিলাম। তখন কম লোকই মনে করত নিয়োগী নেই। দল্লী-রাজহরায় আমাদের মনে হত তিনি যেন ভিলাইয়ে আছেন, ভিলাই-এর সাথীদের মনে হত নিয়োগী যেন রাজহরায়! আমাদের অস্তিত্বতে এমনভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। মৃত্যুর পরও একজন মানুষ কিভাবে তাঁর চিন্তাধারায়, কাজ-কর্মে বেঁচে থাকেন—দেখিয়েছিলেন কমরেড শংকর গুহনিয়োগী।
কমরেড নিয়োগী শহীদের জীবন কামনা করেছেন বারবার। ১৯৭৭-এ যে এগারো জন তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে জীবন দেন, রাজনাদগাঁও-এ শ্রেণিসংগ্রামে শহীদ চার শ্রমিকসাথী—এঁদের আত্মদান নিয়োগী সবসময় মনে রাখতেন। নিয়োগীর মৃত্যুতে আমি দুঃখ পাইনি, কেননা যে জীবনে যে মৃত্যু তিনি চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন—শ্রেণিসংগ্রামে শহীদ হয়েছেন।
আমরা নিয়োগীর যে সাথীরা রয়ে গেছিলাম, আমাদের ও ছত্তিশগড়ের লাখো মেহনতী মানুষের দায়িত্ব ছিল তাঁর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার, ‘নয়া ছত্তিশগড়’ গড়ার লড়াইকে তীব্রতর করার। সে কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছি তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। যাঁরা তাঁর চিন্তাভাবনাকে কোনো-না-কোনোভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছে, তাঁদের মধ্যেই বেঁচে আছেন কমরেড শংকর গুহনিয়োগী।
ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সঙ্গে নানান পরবে কাজ করেছেন গাজী এম আনসার, বিজ্ঞান-শিক্ষক অরবিন্দ গুপ্তা, অবিনাশ দেশপান্ডে, আইনজীবী রাকেশ শুক্লা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সীতারাম শাস্ত্রী, আশীষ কুন্ডু-চঞ্চলা সমাজদার বিনায়ক সেন-ইলিনা সেনের মতো বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের অনেকেই শেষ অবধি আন্দোলনের সঙ্গে থাকেননি। কাউকে পারিবারিক দায়-দায়িত্বের জন্য ছাড়তে হয়, কেউ অথর্নৈর্তিক কারণে ছাড়তে বাধ্য হন, কেউ ছাড়েন ব্যক্তিকে সমষ্টির অধীনে আনতে না পেরে। কিন্তু এক-দু’জন ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের সঙ্গে নিয়োগী বা সংগঠনের সম্পর্ক যে নষ্ট হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিয়োগী-হত্যার পর তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে। (দ্রষ্টব্যঃ সংগ্রাম ও সৃজনের নেতা “নিয়োগী”—সীতারাম শাস্ত্রী; নিয়োগী একটি নতুন মডেল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—বিনায়ক সেন, সংঘর্ষ ও নির্মাণ, অনুষ্টুপ প্রকাশন, ১৯৯২)
ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার ভাঙন এবং সেই ভাঙনে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে নানা জনের নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আছে। সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করছি। নিয়োগী হত্যার আভাস পাওয়ার পর এক মাইক্রোক্যাসেটে রেকর্ড করে যান তাঁর শেষ বক্তব্য। তিনি যখন থাকবেন না তখন সংগঠনের হাল ধরার জন্য সাময়িকভাবে এক কেন্দ্রীয় নিণার্য়ক সমিতি (Central Decision-making Committee) গঠনের প্রস্তাব দিয়ে যান। সেই কমিটির সদস্য হিসেবে তিন বুদ্ধিজীবী ও পাঁচ শ্রমিক নেতা এবং এক যুব নেতার নাম তিনি প্রস্তাব করেন। এই কমিটিতে প্রথম মতাদশর্গত সংগ্রাম শুরু হয়—শ্রেণিসংগ্রাম বনাম শ্রেণিসমঝোতা। তারপর মতাদশর্গত সংগ্রাম—সংগঠন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিতে চলবে নাকি সংগঠনের অগ্রণী নেতৃত্বই সব সিদ্ধান্ত নেবেন। এই দু-টি সংগ্রাম চলাকালীন তোলা হয়েছে সংগঠনের নেতৃত্ব অছত্তিশগড়ীরা কবজা করতে চাইছেন এমন বিতর্ক। (ঘটনাচক্রে নয় জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন বাঙালি, একজন হরিয়ানাভী—যিনি এই বিষয়টি তোলেন, অন্য পাঁচজন জন্মসূত্রে ছত্তিশগড়ী।) শেষে ১৯৯৪-এর মাঝামাঝি দল্লী খনিতে মেশিনীকরণের চুক্তির বিরোধিতা করায় কেন্দ্রীয় নিণার্য়ক সমিতির দুই সদস্যকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়, তাঁদের বহিষ্কারের বিরোধিতা করে ভিলাইয়ের সংগঠনের লড়াকু এবং অগ্রণী অংশ সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসায় প্রথম ভাঙন হয় ছমুমো-এ, ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা (নিয়োগীপন্থী) গঠিত হয়। দীঘর্জীবী হয়নি ছমুমো (নি), কিন্তু যে বিষয়গুলি তারা বিতর্কে তুলে এনেছিল সেগুলিকে কেন্দ্র করেই আরও দুটি ভাঙন হয় ছমুমো-এ। এখন ছমুমো নামে তিনটি সংগঠন কাজ করে।
আজকের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের, গণআন্দোলনের এই খরার দিনে যখন সাধারণ মানুষজন বিভ্রান্ত; যখন একদিকে ডান-বাম নির্বিশেষে ‘ভোটসবর্স্ব’ রাজনৈতিক দলগুলো জনবিরোধী নীতিগ্রহণে ও তাঁর প্রয়োগে সদাব্যস্ত আর অন্যদিকে আর এক গোষ্ঠী ‘সংঘর্ষ ও নির্মাণ’-এর সংঘর্ষকেই কেবল ধরতাই ধরে নিয়ে, সাধারণ মানুষের সৃজনশীল আশাআকাঙ্ক্ষাকে, নিমার্ণকে উজ্জীবিত করার বদলে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সবর্নাশা খেলায় মত্ত; তখন শংকর গুহনয়োগী এবং তাঁর কমর্কাণ্ড মানুষের সংগ্রামের স্বার্থে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
প্রাসঙ্গিক যে হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মেলে গুহনিয়োগীকে নিয়ে নতুন করে আলাপ-আলোচনায়; তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিশ্লেষণ করে লেখালেখিতে; তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র নিমার্ণে। বহুদিন অমুদ্রিত-থাকা গুহনিয়োগীর লেখা এবং আন্দোলনের সংকলন সংঘর্ষ ও নিমার্ণ (অনুষ্টুপ) নবরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেকেই তাঁদের স্মৃতিচারণে নিয়োগী এবং দল্লী-রাজহরার আন্দোলনকে বিবৃত করেছেন। যেমন ড. ইলিনা সেন-এর Inside Chhattisgarh—A Political Memoir (Penguin)। বলাই বাহুল্য, এঁদের সকলের দৃষ্টিকোণ এক নয়; না-হওয়াটাই স্বাভাবিক—এঁদের মধ্যে অনেকেই যেমন গুহনিয়োগীর পরীক্ষানিরীক্ষাকে সংগ্রামের প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি না তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে মগ্ন, তেমনি আবার অনেকেই নিয়োগীর ব্যক্তি-আচরণ এবং তাঁর কমর্কাণ্ডকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি, নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করতে চেয়েছেন। কিন্তু যেভাবেই নিয়োগীর মূল্যায়ন হোক না কেন (এ কথা স্পষ্ট যে মানুষের সাথী এবং তার শত্রুরা মূল্যায়নে সদাই পরস্পর বিরোধী অবস্থান নেবে।) তিনি যে এ-দেশের জনজীবনে, সংগ্রামের দিক নিণর্য়ের ক্ষেত্রে ক্রমশই বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন—এ সত্যকে তাঁর বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারেন না কেননা তাহলে এতদিন বাদে নতুন করে তাঁদের নিয়োগীর বিরুদ্ধে কলম ধরতে হত না।
অনেক সময়েই নিয়োগীর কাজ-কর্মকে বহু রাজনৈতিক লোকজন অর্থনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নবাদী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এই মতামত ভুল। শ্রমিকদের মধ্যে সরকার ও ব্যবস্থা বদলের লক্ষ্যে শ্রেণীগত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি ধারাবাহিক ভাবে প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দাবী, প্রচারপত্র—এসবের মধ্যে তার ছাপ আছে। তাঁর সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতির প্রথম কথা—সংঘর্ষ অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম আর নির্মাণ হল ভবিষ্যৎ সমাজের নির্মাতাদের সৃষ্টিপ্রয়াস—এ কোনও এনজিও-মার্কা সংস্কারমূলক কাজ নয়, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর যুদ্ধের স্লোগান। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে এই ধারণাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।
আরেকটা বিষয় অনেক সময় প্রশ্ন আকারে উঠে আসে যে সর্বহারার অগ্রণী বাহিনী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে তিনি কি ভাবতেন, তিনি কি লেনিনবাদী পার্টির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা বক্তব্যে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বাম হঠকারিতা আর সরকার-সর্বস্বতা বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি বহু সময়েই অন্যান্য বন্ধু কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতাদের ছত্তিশগড়ে থেকে পার্টি গড়ার কাজ হাতে নিতে তিনি বলেছেন। তাই এসব নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁদের কমরেড নিয়োগী সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে।