চিকিৎসকের সাথে আমজনতার দূরত্ব বাড়ছে। কিন্তু কেন? চিকিৎসকের জগৎ আর অন্য পেশার মানুষের জগৎ ভিন্ন হয়ে গেল ঠিক কোন পথে?
না, একদিনে হয় নি – হয়েছে ধাপে ধাপে। সব ধাপ এককথায় খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন নয় – কিন্তু, সেই দূরত্বের ধাপগুলোর কিছুটা আঁচ না পাওয়া গেলে দূরত্বের উপশম হওয়া মুশকিল। আবার, সময়ের চাকা ঘুরিয়ে সেই ধাপগুলো মুছে ফেলে পুরোনো সময়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে, এমনও নয় – তবু ধাপগুলোর সন্ধান জরুরী, না হলে পারস্পরিক দোষারোপ আর অবিশ্বাসের এই পরিবেশের উন্নতি সম্ভব হবে না।
যেমন, একটা ধাপ হিসেবে ধরা যায়, চিকিৎসকেরা যেদিন বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা কমিয়ে দিলেন, সেই দিন দূরত্বের একটা ধাপ বাড়িয়ে নেওয়া গেল। কেননা, বাড়িতে গিয়ে না দেখে হাসপাতালে এনে দেখার মধ্যে একজন মানুষের অবস্থানের মূলগত পরিবর্তন ঘটে যায়। একজন মানুষকে তাঁর বাড়ি, তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রায় উৎপাটিত করে হাসপাতাল বা চেম্বারে এসে স্রেফ পেশেন্টে পরিণত করার শুরু হয়ত সেখানেই। বর্তমানে হাউজকলে না যাওয়ার পক্ষে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটি হয়ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে – কিন্তু, বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা কমে এসেছে যে সময় থেকে, সেই সময়ে চিকিৎসকের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা খুব বেশী ঘটত না।
হয়ত যুক্তিটা ছিল অর্থনৈতিক – বাড়িতে গিয়ে একজন রোগীকে দেখার সময়টুকুতে চেম্বারে চারজন বা তারও বেশী রোগী দেখা সম্ভব। হয়ত যুক্তিটা ছিল ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপ – একজন ডাক্তারকে দেখতে হতে থাকল অনেক বেশীসংখ্যক রোগী – একজন অসুস্থ মানুষকে দেখে তাঁর বাড়িতে বসে চা খেয়ে গল্প করে আসার অবকাশ চিকিৎসকের আর থাকল না। হয়ত যুক্তিটা ছিল কোনোভাবে পরিকাঠামোর – হাসপাতালে এসে দেখালে জরুরী পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে নেওয়া সম্ভব চটজলদি, যা বাড়িতে সম্ভব নয়। কিন্তু, যুক্তি যা-ই হোক, চিকিৎসকের চোখে সামনে বসা মানুষটি পেশেন্টে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আবার অসুস্থ মানুষটির চোখেও তাঁরই মতো একজন মানুষের স্রেফ ডাক্তারে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রেও তা-ই।
অসুস্থ মানুষ বাড়ির পরিচিত পরিবেশে চিকিৎসা পাওয়ার পরিবর্তে গিয়ে হাজির হলেন হাসপাতালে – সে এক নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ – আশেপাশে সবাই হয় অসুস্থ, নয়ত পেশাদার। হাসপাতাল হয়ে উঠল এক আতঙ্কের জায়গা – না, শুধু আকাশছোঁয়া খরচের ভয় নয়, চিকিৎসা করাতে গিয়ে ঘটিবাটি বিক্রি হওয়ার পরিস্থিতি সে তো সাম্প্রতিক ব্যাপার – এ আতঙ্ক পরিচিত পরিবেশ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্রেফ একটি বেড নম্বরে পরিণত হওয়ার, সেও সবচেয়ে অসহায় ও অক্ষম মুহূর্তে – আর সেই আতঙ্কের মুখ হয়ে থাকলেন চিকিৎসক – অবিশ্বাস অবাঞ্ছিত হলেও, সম্ভবত, অস্বাভাবিক নয়।
হাসপাতালে হাজির হওয়া মানুষটি পরিণত হলেন রোগীতে – একজন মানুষকে মাপা হয় আগাপাশতলা মানুষ হিসেবেই, কিন্তু রোগীকে? রোগ তো শরীরের কোনো বিশেষ অংশে, কোনো প্রত্যঙ্গে – অতএব, রোগী আর সম্পূর্ণ মানুষ রইলেন না – তাঁর ভাগ হতে থাকল রোগগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচারে – অসুখের ধরণ ও রোগগ্রস্ত অঙ্গ হিসেবে বেড়ে উঠল চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখা – ডাক্তারবাবুদের হয়ে উঠতে হল স্পেশালিস্ট – হাসপাতালে রোগীদের ভাগ হতে থাকল রোগগ্রস্ত অঙ্গের বিচারে – গুরুত্ব পেতে থাকলেন স্পেশালিস্ট – যে স্পেশালাইজেশনের অর্থ নোয়িং মোর অ্যান্ড মোর অ্যাবাউট লেস অ্যান্ড লেস।
একজন বাড়িতে আসা মানুষ – যাঁকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বাড়িতে ডাকতে হয় – বাড়িতে বাচ্চা থেকে বুড়ো, এমনকি পোয়াতি মহিলা, যারই প্রয়োজন পড়ুক, ডাক পড়ে যাঁর – তাঁকে নিজেদের একজন, পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবার সুযোগ যতোখানি, একইসাথে অনেক চিকিৎসককে সেইভাবে দেখার সম্ভাবনা কি তেমনটা হতে পারে? অথচ, স্ত্রীর প্রয়োজনে গাইনোকোলজিস্ট, বাচ্চার জ্বর হলে পেডিয়াট্রিশিয়ান, বয়স্ক বাবার সুগারের জন্যে ডায়াবেটোলজিস্ট আর প্রেশারের জন্যে কার্ডিওলজিস্ট – প্রয়োজন অনুসারে ডাক্তারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।
হাসপাতালে নিয়োগ হতে থাকলেন স্পেশালিস্ট – রোগ সম্পর্কে সবার ধারণা বদলে যেতে থাকল সেইভাবেই – সবরোগের চিকিৎসা করতে চাওয়া জেনারেল প্র্যাক্টিশনার, ওরফে জিপি, হতে থাকলেন কোণঠাসা – পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে ডাক্তারি ছাত্ররাও হতে থাকলেন স্পেশালিস্ট বা স্পেশালিস্ট না হয়ে উঠতে পারা পর্যন্ত ভুগতে থাকলেন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে – এসবই এমবিবিএস ডাক্তারদের “পাতি এমবিবিএস” ভাবা বা “তুমি এমডি করবে না” প্রশ্নের অনেক আগের সময়ের গল্প – বাজার-অর্থনীতি এসে চিকিৎসাকে পণ্য করে তোলা বা চিকিৎসককে নিছকই একজন পেশাদার ভাবার প্রবণতা বা ডাক্তারের চোখেও চিকিৎসা স্রেফ একটি পেশা হয়ে যাওয়া, এতখানিও তখন ঘটে নি – কিন্তু, এই পথে যাত্রার সূচনা এভাবেই।
আজ যখন গ্রামাঞ্চলে অনেকসময় দেখা যায়, পাশ-করা মডার্ন মেডিসিনের ডাক্তারের চাইতে তথাকথিত হাতুড়ের উপর গরীব মানুষের ভরসা বেশী – তখন সেখানে অর্থনৈতিক কারণ খোঁজা বা বিষয়টিকে তদনুসারী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সাথে সাথে যেকোনো অসুস্থতার প্রয়োজনে একটিমাত্র মানুষের শরণাপন্ন হতে পারার যে আবহমান প্রবণতা, তার প্রতিফলন হিসেবে দেখতে চাইলেও অন্যায় হবে না – প্রায় ঠিক যেভাবে অনেক হাসপাতাল বিপণন করে থাকেন, এক ছাদের তলায় সমস্তরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে, এইমর্মে – কিন্তু, সে তো কোনো মানুষ নয়, এক বিপুল নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো।
চিকিৎসা হল নৈর্ব্যক্তিক – ডাক্তার হলেন স্পেশালিষ্ট – চিকিৎসাবিজ্ঞান হয়ে উঠল “সায়েন্টিফিক” ও টেকনোলজি-নির্ভর। বিশেষজ্ঞের হাতে বিজ্ঞানমুখী চিকিৎসা – বাড়ল পরীক্ষানিরীক্ষা, হাইটেক যন্ত্রপাতির ব্যবহার – চিকিৎসার প্রয়োজনে যন্ত্র – তার থেকে ধীরে ধীরে চিকিৎসাটাই যান্ত্রিক হয়ে গেল – ব্যক্তিচিকিৎসকের ভূমিকা কমে বাড়তে থাকল পরিকাঠামোর গুরুত্ব।
আজ আপনার ডাক্তারবাবু আপনার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলেন না, বা আপনাকে টিপেটুপে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেন না, এই নিয়ে আপনার অনুযোগ অনেক। অথচ বিশ্বাস করুন, আপনাকে চিনতে বা আপনার অসুখের প্রকৃতি বুঝতে সেই কথোপকথনের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও – আপনার অসুখের “ডায়াগনোসিস” করতে টেকনোলজি দিব্যি কার্যকরী – অতএব, আপনার ডাক্তারবাবু যে আপনার মুখের দিকে তাকানোর চাইতে আপনার সিটি স্ক্যানের দিকে অনেক বেশীক্ষণ ধরে চেয়ে থাকবেন – এতে অবাক হবেন না, বা এইটাকে দূরত্বের কারণ হিসেবে ভাববেন না, প্লীজ – দূরত্বের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আজ এইখানে এসে দাঁড়ানো গেছে। এবং, আমি সেইভাবে উল্লেখ না করলেও, খেয়াল করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, প্রতিটি ধাপের পেছনে অর্থনীতির যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ – আর সেই আর্থিক লাভের গুড় যতখানি পাচ্ছেন চিকিৎসক, তার চাইতে বহুগুণে বেশী তাঁরা, যাঁদের মুখ আপনি কখনোই দেখেননি সামনাসামনি। পরবর্তী ধাপ হয়ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ওরফে এআই – যাতে আপনার সমস্যা বললে কম্পিউটার জানিয়ে দেবে কী কী পরীক্ষা জরুরী – আর পরীক্ষার রিপোর্ট আপলোড করলেই বেরিয়ে আসবে প্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন – বড় বড় কোম্পানি জোরকদমে গবেষণা চালাচ্ছে এই পথ ধরেই – চিকিৎসক স্রেফ একজন স্বাক্ষরকারীতে পরিণত হবেন শেষমেশ, লক্ষ্য এইটাই।
অতএব, এই বর্তমান অবস্থায় নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে, বাজারের উপযুক্ত করে তুলতে ডাক্তারির ছাত্রের পক্ষে, সামনে শুয়ে থাকা রোগীর চাইতে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ এমডি-তে ঢোকার পরীক্ষার প্রস্তুতি। অবশ্য, সেইভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রস্তুতি হয়েই যায়। চিকিৎসাবিদ্যা পঠনের সময়েই আস্তে আস্তে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একটি ছাত্র – না, হয়ত, মেডিকেল পড়ার সুযোগ পাওয়ার কোচিং-এর সময় থেকেই শুরু – সেই ফাটল বাড়তে বাড়তে প্রতি চিকিৎসক হয়ে পড়েন একজন একক দ্বীপের সমান। দূরত্বের সেই পর্যায় আসে কোন পথে?
নাঃ, সে আলোচনা পরে কখনও হবে। আগের লেখাখানা লম্বা হয়ে যাওয়ার জন্যে বড্ডো অনুযোগ-অভিযোগ শুনতে হয়েছে।




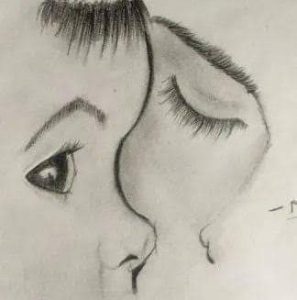

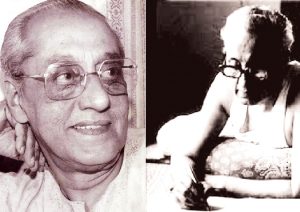
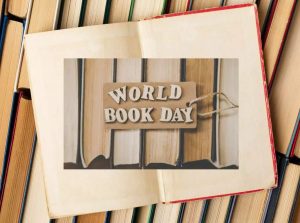





বিষাণের এই বিস্লেষণ টি খুব যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলে আমি মনে করি। General Physician. দের নতুন করে ভীষণ প্রয়োজন। যুক্তিহীন specialisation ই corporatisation.কে ত্বরান্বিত করছে। Pharma industry গোটা পৃথিবীর স্বাস্স্থ্যের বাজার নিয়ন্ত্র্ন করে।
এক সময় IMA বাংলায় presriptioer directions. লেখা(যেমন বাংলাদেশে আছে) জিপি দের treatment update দেওয়া এগুলো ধারাবাহিক করত। এই সবই খুব জরুরী নতুন করে। সম্পর্কের দুরত্ব কমাতে চিকিত্সকদেরি আগিয়ে আসতে হবে।
স্যার, প্রণাম নেবেন।
জেনারেল প্র্যাক্টিশনার, ওরফে জিপি, তাঁরাই চিকিৎসাব্যবস্থার মূল কাঠামো। সেইখান থেকে সরে আসার ফলে চিকিৎসা হয়েছে ব্যয়বহুল – রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক ঠেকেছে তলানিতে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার উপদেশ দিয়েছেন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কনসেপ্টে ফিরতে – আমরা শুনলাম কই? উল্টে ফ্যামিলি মেডিসিনে ডিএনবি করে তাঁদের কর্পোরেট হাসপাতালে চাকরি করতে দেখছি।
অথচ, এই দিকটা নিয়ে আরেকটু গভীরভাবে না ভাবলেই নয়।
This is an issue that is true to the problem of deteriorating doctor-patient relationship and is analysed in depth by a doctor who is no less than a senior successful specialist in oncology and a master of Radiotherapy in a frontline medical institution of Kolkata. But his analysis is more powerful than that a social scientist and I have no hesitation to say that the paper must be credited with high honor for giving the space to the writer.
Dr. D6ipankar Mukherjee, HOD,Department of Cardiology, SSKM Hospital
দীপঙ্করদা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ভালোবাসা।
বিষাণবাবু নমস্কার জানিয়ে বলি আমি একজন পাড়াতুতো ডাক্তার । পাড়ায় বসে রোগী দেখি ।
১) আমাদের পাড়ার বহু মানুষের আমার থেকে ঢের বেশী আয় । তাঁরা চেম্বারে না এসে কল দিয়ে আমাকে বাড়িতে দেখানো পছন্দ করেন । কিন্তু আমি টুকটাক বিষয়ে বাড়িতে গিয়ে এ বয়সে আর পারি না ।
২ ) দুপুর ঠাকুরপো ধরণের কিছু মানুষ আছেন যাঁরা পাড়ার বৌদিদের মাথা ধরলেও এসে ডাক্তার ডাকেন । এগুলোতে কি করবো ?
৩ ) সত্যিকারের হার্ট অ্যাটাক হলে বা মাথা ফেটে গেলে বাড়ি গিয়ে কি করা যাবে আর বুকে ব্যথায় ইসিজি এবং আনুষঙ্গিক কিছু পরীক্ষা ছাড়া কি ভাবে মানুষকে বাঁচাবো সেটা জানা নেই ।
৩ ) ইউরিন ইনফেকশন হলে সেটা ই . কোলাই না সিউডোমোনাস – রোগী সেপ্টিসিমিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে কিনা অথবা সোডিয়াম না পটাশিয়াম – কোনটা কমেছে বা বেড়েছে কি করে ঘরে বসে বুঝবো সেটা জানালে বাধিত হবো ।
ধন্যবাদান্তে দীপঙ্কর ।
ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা বাড়িতে গিয়েই রোগী দেখতেন, এমনটাই শুনেছি – দেখেছিও। স্বাভাবিকভাবেই, ছোট এবং বড় দুধরণের অসুস্থতার ক্ষেত্রেই তাঁদের ডাক পড়ত। “দুপুর ঠাকুরপো” বিষয়ক অনুযোগটা ঠিক ধরতে পারলাম না।
স্টুল বা ইউরিন পরীক্ষার জন্যে ল্যাবের টয়লেটে গিয়েই পটি বা হিসু করতে হবে – ঠিক সেই টয়লেটের ইস্তেমাল না হলে ল্যাবের লোকেরা খুব অভিমান করেন – এমনটাও তো শুনিনি। বাড়ি থেকে পেচ্ছাপ-পায়খানা-রক্ত সবই সংগ্রহ করা হয়, এরকমই তো জানি। আপনি ইউটিআই-এর উদাহরণ দিয়েছেন, সেও আবার সিউডোমোনাস – বাড়িতে থাকা রোগীর মধ্যে তার সম্ভাবনা কতোখানি? সীমিত জ্ঞানে জানতাম, সিউডোমোনাস মুখ্যত হাসপাতালের সূত্রে প্রাপ্ত অসুখের মধ্যে পড়ে। যতজন রোগী দেখেন, তার ঠিক কত শতাংশের নিয়মিত সোডিয়াম-পটাশিয়াম চেক করার দরকার পড়ে? আপনার রোগীদের মধ্যে কি সবাই হাড়গোড় ভেঙে বা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসেন? বাকিরা? লেখার মধ্যে কি একবারও হাসপাতাল গুটিয়ে সব রোগীর চিকিৎসা বাড়িতে হবে, বাড়িতেই থাকবে এক্সরে-সিটি-ভেন্টিলেটর, এমন কল্পনাশক্তির পরিচয় রাখা হয়েছে?
আমার এক মাসি মেসোমশায়ের চাকরির সুবাদে রাজ্যের বাইরে থাকতেন। তখন হলুদ ট্যাক্সির রমরমা। বাড়ি ফেরার সময় সোদপুরে যেতে কোনো ট্যাক্সিই রাজি হত না, কেননা সোদপুর অনেক দূর। শেষমেশ মেসো যখন কলকাতায় বদলি হলেন, মাসিরা থাকতেন হাওড়া স্টেশনের কাছেই – কিন্তু, সেইখানেও ট্যাক্সি যেতে রাজি হত না, কেননা, সেটা খুব কাছে। মাসি খুব বিস্মিত হতেন, সোদপুর দূরে বলে যায় না – এইটা খুব কাছে বলে যায় না – তাহলে ট্যাক্সিওয়ালারা যায় কোথায়!!!!
না, এই গল্পের মধ্যে ডাক্তারদের হেয় করা বা তাঁরা ট্যাক্সিড্রাইভারদের সাথে তুলনীয় এর কোনোটাই বলা হয়নি। শুধু বলার, গুরুতর অসুস্থতা ছাড়া ডাকলে দুপুর ঠাকুরপো এবং বিরক্তি – হার্ট এটাক বা হাড় ভাঙলে গিয়ে লাভ নেই – ক্রনিক অসুস্থতা হলে মনিটরিং লাগে, বাড়িতে হয় না – পরীক্ষানিরীক্ষাও বাড়িতে হবে কী করে – তাহলে বোধহয়, অসুখ হলে বাক্সপেটরা-বেডিং গুটিয়ে হাসপাতালমুখো হওয়া ছাড়া আমজনতার আর পথ নেই – তাই না??
বিশাণবাবু বক্তব্য অবশ্যই ঠিক । তবে বুকে ব্যথায় বাড়িতে ডাক প্রচুর আসে । পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার ডাকও আসে । মাঝরাতে জ্বরের বা মরণাপন্ননের অন্তিম ডাক । এগুলোর ক্ষেত্রে কি কর্তব্য ?
আজকাল সোডিয়াম পটাসিয়াম বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায়ই পাই ।
আর দুপুর ঠাকুরপো ? সুন্দরী মহিলাদের সামান্য কিছু হলেই অত্যুৎসাহী পাড়ার হীরোদের ডাক্তার ডাকার ধুম্পড়ে যায় । আমি এটা প্রচুর পাই । রাজনৈতিক নেতাদের তো … নাঃ এটা ওনারা সব বিষয়েই করেন … সুতরাং উহ্য থাক ।
বিষাণ বাবুকে ধন্যবাদ ও অভিন ন্দন। আরও বড় করে লিখুন।
আমরা চারপুরুষ ডাক্তার। কিন্তু সব দেখেশুনে ভীষণ
লজ্জা করে।
প্রধানমন্ত্রী প্রথম সারির ওষুধ-কোম্পানির মালিকদের ডেকে মেয়েমানুষ , বিদেশ ভ্রমণের খরচা ও দামী গ্যাজেট উপঠৌকন —ডাক্তারদের দিতে বারণ করেছেন। এটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র।