২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখে নেচার-এর মতো মান্য জার্নাল জানালো যে রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্সেস ২,৫৭৮টি প্রকাশিত গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ওগুলোর আর কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। সেদিনই মস্কো টাইমস পত্রিকার শিরোনাম “Russian Journals Retract Almost 900 Papers After Falsification Probe”। ১২ ডিসেম্বর, গ্লোবাল টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে এ খবর – “Scientific journal retracts paper over fawning content on author’s mentor’s nobility”।
তাহলে কি দাঁড়ালো? ধরুন একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র আরো অনেক গবেষণার জন্ম দিয়েছে। তাহলে ফলশ্রুতিতে সে গবেষণালব্ধ ফলাফলও ভ্রান্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার ভাবুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হলে একরকমের সমস্যা। কিন্তু মেডিসিনের জগতে এরকমটা ঘটে? মেডিসিনের বড়ো ট্রায়ালের ওপরে নির্ভর করে আন্তর্জাতিক গাইডলাইন তৈরি। গাইডলাইনের ভিত্তিতে তৈরি হয় চিকিৎসার নিয়মকানুন, চিকিৎসার ব্যাকরণ। আবার তার ভিত্তিতে তৈরি হয় কি ওষুধ লেখা হবে, কি কি লেখা হবেনা। এগুলো মানুষের জীবন-মরণ-সুস্থতা-অসুখের সাথে জড়িয়ে আছে বলে অত্যন্ত জরুরি এদের বিশ্বাসযোগ্যতা। এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রায়াল যদি পরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়? যদি দেখা যায় হাঙ্গর সদৃশ বহুজাতিক ফার্মা কোম্পানিগুলো (যারা নিজেরা একাধিক দেশকে কিনে নিতে পারে) বিভিন্ন ট্রায়ালের নির্মাণ করতে পারে নিজেদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ওষুধের বিক্রী বাড়াবার জন্য? এবং যখনই এভাবে গাইডলাইন নির্ধারণ করা হবে সেগুলো ভ্রান্তিপূর্ণ শুধু নয়, অনৈতিকও বটে। আমাদের মতো “বেচারা” ডাক্তারবাবুরা কি করবেন সেক্ষেত্রে? আমরা তো রয়েছি গ্রহীতার ভূমিকায়, আমাদের নিজস্ব কোন গাইডলাইন প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের চিন্তাভাবনার প্রায় পুরোটাই একটু শ্লেষ নিয়ে বললে “derivative discourse”। যেখানে গাইডলাইনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি অনেক বড়োভাবে অনৈতিক সেখানে চিকিৎসকের নৈতিকতা-অনৈতিকতার বিষয়টি আরেকভাবে দেখা যেতে পারে। আরেকটা বিষয় ভেবে দেখার মতো। আমরা চিকিৎসক সমাজ এখন যে প্রয়োগ-পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি তাকে বলা হয় এভিডেন্স-বেসড মেডিসিন (EBM) বা প্রমাণ-নির্ভর চিকিৎসা। যদি গোড়াতেই যদি সমস্যা থাকে তাহলে প্রমাণ-নির্ভর চিকিৎসাও তো নড়বড়ে হয়ে যাবে।
একটা উদাহরণ দিই। কয়েকবছর আগে ব্লাড প্রেসারের মাত্রা, এর ফলাফল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও তার মাত্রা ইত্যাদি যে আন্তর্জাতিক কমিটি রয়েছে তারা সবাই মিলে ঠিক করেছিল ১৪০/৯০ মিমি পারদ অব্দি স্বাভাবিক রক্তচাপের উর্দ্ধসীমা ধরা যাবে। কয়েকবছরের ব্যবধানে তা কমে দাঁড়ালো ১৩০/৮০-৯০-এ। এবার ধরুন আবার কয়েকবছর বাদে বিভিন্ন দেশের কয়েক হাজার মানুষকে নিয়ে বিভিন্ন সেন্টারের করা স্টাডি দেখালো ১৪০/৯০ মাপকাঠি ঠিক। তখন কি হবে? মজাটা হল এই কয়েকবছরে রক্তচাপ ১৩০/৮০-তে বেঁধে রাখবার জন্য কয়েক’শ হাজার অ্যান্টি-হাইপারটেন্সিভ পিল বিক্রী হয়েছে। বিলিয়ন ডলারের মুনাফা কার হবে? বলার অপেক্ষা রাখেনা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর। তাহলে এদের তরফে যে প্রবল চাপ থাকবে গাইডলাইন, ড্রাগ ট্রায়াল, নীতি-নির্ধারক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপরে এ কথা সহজে অনুমান করা যায়। এর জন্য কেউকেটা কোন বুদ্ধিজীবী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি হবার প্রয়োজন নেই।
নিউ ইংল্যান্ড জার্নালের মতো সর্বজনমান্য পত্রিকায় (NEJM, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর – ৭৯.২৫৮!) ২৩ নভেমর, ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছিল বর্তমানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ওষুধ রোফিকক্সিব নিয়ে বিখ্যাত বা কুখ্যাত VIGOR স্টাডি – Comparison of Upper Gastrointestinal Toxicity of Rofecoxib and Naproxen in Patients with Rheumatoid Arthritis। ১৬ মার্চ, ২০০৬-এ NEJM-এ প্রকাশিত হল একগুচ্ছ চিঠি “Response to Expression of Concern Regarding VIGOR Study” শিরোনামে। জুলাই ১৫, ২০০৬-এ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ লেখা হল “NEJM “failed its readers” by delay in publishing its concerns about VIGOR trial”। এ ওষুধের ব্যবহারে ডাক্তারি পরিসংখ্যানে বিচারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীর হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে শুরু করলো। যে ব্র্যান্ড নামে দানবীয় বহুজাতিক মার্ক কোম্পানির রোফিকক্সিব দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করেছিল তাহল Vioox। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোম্পানি মার্কের কাছ থেকে কিনে বিভিন্ন নামে ব্যবসা করেছে। আমরাও সেসময়ে লিখেছি এই ওষুধ। কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাত্রা এত বিপুল হওয়াতে অবশেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪-এ মার্ক কোম্পানি সরকারিভাবে “announced a voluntary worldwide withdrawal of VIOXX(R) (rofecoxib), its arthritis and acute pain medication”। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল “Despite Warnings, Drug Giant Took Long Path to Vioxx Recall”। কারণ এ চার বছরে মার্কের এ ওষুধের ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি, অর্থাৎ এখনকার হিসেবে ৩৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি!
এরকম আরেকটি সুবৃহৎ স্টাডি FRAMINGHAM Heart Study. সংক্ষেপে বললে, এই স্টাডি শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, শেষ হয় ১৯৭১-এ। এর লক্ষ্য ছিল হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার অসুখের কারণ এবং ফলাফল সম্বন্ধে জানা। সেখানে রক্তের এবং খাদ্যের কোলেস্টেরলকে “naughty list”-এ রাখা হয়। ফলে ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে রক্তে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ হিসেবে স্ট্যাটিন জাতীয় ওষুধের রমরমা শুরু হয়। ফাইজার এবং মার্কের মতো আরও কিছু দানবের সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২০.৫ বিলিয়ন ডলার বা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকার আশেপাশে। এর ৪৪ বছর পরে আমেরিকা থেকে সরকারিভাবে কোলেস্টেরলকে “naughty list”-এর বাইরে রাখা হল। এসময়ের মধ্যে ২০.৫ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা কিন্তু হয়ে গেছে। এবং বিভিন্ন গাইডলাইনও তৈরি। আমরা চিকিৎসকেরাও সে অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন করেছি। এজন্য কিছু কিছু গবেষকের মতে ফ্রামিংহাম স্টাডি হল বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারি। এরপরে আবার বহুজাতিক কোম্পানির চাপে কোলেস্টেরলকে “দুষ্টু” বানানোর চেষ্টা চলে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে জানানো হয় – “the AHA statement gives no specific dietary cholesterol target and instead recommends that dietary guidance emphasize healthy dietary patterns, such as the Mediterranean or DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diets.” এবার DASH-এর ব্যবসা হয়তো শুরু হবে! আমরা কোথায় যাবো?
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ কিছু কিছু পদ্ধতির ফলে কত সংখ্যক মানুষের মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন তথা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য EXCEL Study-তে চেপে যাবার জন্য “The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) is formally withdrawing their support for the current treatment recommendations for left main coronary artery disease following an investigative report by BBC Newsnight alleging that critical data were concealed in public reporting of the EXCEL trial.” বিচার করুন মেডিসিনের জগতের গুপ্ত জগতের কথা।
একদিকে আমেরিকার মতো দেশে গবেষণায় সরকারি অনুদান কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে Big Pharma-র বিনিয়োগ বেড়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে Big Pharma ৬,৫৫০টি ট্রায়ালের জন্য টাকা ঢালে, বিপরীতে সরকারি সংস্থা National Institute of Health (NIH) মাত্র ১,০৪৮টি ট্রায়ালের জন্য অনুদান দেয়। পরিণতি? সবাই সহজেই অনুমান করতে পারবে।
২০০৫ সালে (২১ এপ্রিল) NEJM-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল দু’জন ভারতীয় চিকিৎসকের লেখা – “A New Colonialism? — Conducting Clinical Trials in India” শিরোনামে। আমরা বর্তমান বিশ্বে মেডিসিনের জগতে (সমস্ত শাখা সহ, যেম সার্জারি, ক্যান্সার চিকিৎসা ইত্যাদি) কি এক নয়া-উপনিবেশের মধ্যে বাস করচ্ছি?
ভেবে দেখার সময় এসেছে। (পুনশ্চঃ পাঠকদের আগ্রহ থাকলে medical-industrial complex নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কিছু কথা বলা যাবে।)



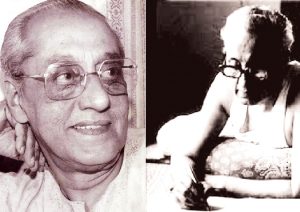
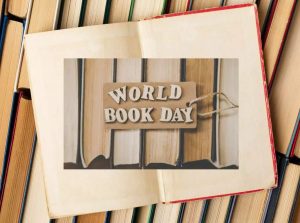
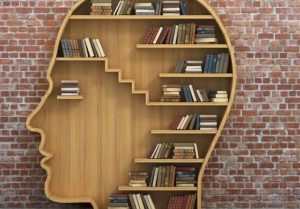







বা অনেক কিছু নতুন জানা গেল.. অভিনন্দন ডাক্তার বাবু
চিকিত্সা শাস্ত্রের মতো বিজ্ঞান “মুনাফা নির্দেশিত ” হবার ফলে ক্রমশ অবিজ্ঞান নাবিজ্ঞান সম্মত চিকিত্সার দিকে মানুষের প্রবণতা বাড়ছে ।
মানুষ বিভ্রান্ত চিকিত্সক বিভ্রান্ত–সাধারণ লোক বলবে আমাদের হোমিওপ্যাথিই ভালো ছিল বাপু !!!
মানুষ বিভ্রান্ত চিকিত্সক বিভ্রান্ত —
আমরা যাবো কোথায়?
Congratulations for presenting these
informations.People are quite ignorant about
the matter. Patients are required to attend doctors for their treatment and early recovery.
But under the circumstances as stated how a
patient would recover early in spite of taking such medicines. Doctors co operation in this
regard are urgently needed to avoid the crisis.
Every time we get worthy information from your awesome writing.
যারা মতামত দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বিষয়টি সত্যিই গভীর সংকটের এবং বিপজ্জনক। মেডিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আজ সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝার বাইরে। এ ইতিহাস আমাদের জানা দরকার।
জানা দরকার কিভাবে কর্পোরেট পুঁজির প্রয়োজনে WHO-র স্বাস্থ্যনীতি ১৯৭৮ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়েছে, সরে এসেছে সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা comprehensive primary health care-এর অবস্থান থেকে।
এর জন্য মেডিক্যাল সিলেবাস বদলে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী সিলেবাসের যে বিপুল পরিবর্তন আসছে তাতে কোথাও ফ্যামিলি প্র্যাকটিস, ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান, জেনারেল প্র্যাকটিস ইত্যাদি শব্দগুলো নেই।
সামাজিক সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের চিকিৎসা কে করবে এরপরে? কার কাছে যাবে আর্ত মানুষটি? পাঁচতারা, চকচকে, বহুমূল্য কর্পোরেট হাসপাতালগুলো একমাত্র গন্তব্য? প্রতিবছর প্রায় ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার সমান (৬ কোটির ওপরে) ভারতবাসী তলিয়ে যাবে দারিদ্র্যের অতলে ঘটিবাটি বিক্রি করে? বাঁধা পড়বে মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপে?
একটিই প্রশ্ন – কেন?