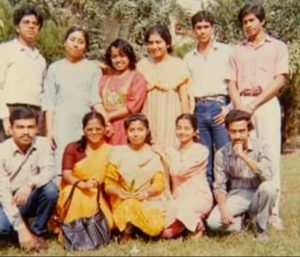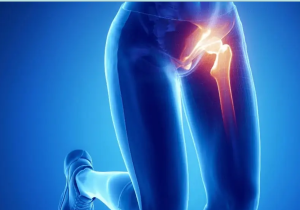কানাডার অন্টারিয় প্রদেশের দক্ষিণে ছোট্ট মফস্বল অ্যালিস্টন[১১]। অ্যালিস্টনের উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে এক সচ্ছল কৃষিজীবী পরিবারে ১৪ই নভেম্বর ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিঙ। মা মার্গারেট গ্রান্ট বান্টিঙ ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। পেশায় চাষা, বাবা উইলিয়ম থম্পসন বান্টিঙ বেশ বড় একটা পশু খামারেরও মালিক ছিলেন। গরু, ছাগল, গাধা, মুরগী, ঘোড়া প্রভৃতি থেকে ভালো রোজগার ছিল তাঁর। খুব বেশি দূর পড়াশুনা করার সুযোগ পান নি উইলিয়ম, কিন্তু সনাতনী মূল্যবোধ, নিষ্ঠা, সততা, প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। মার্চ ১৯৩১ সালে নিজের বাবা প্রসঙ্গে ডায়েরিতে ফ্রেড লিখেছেন, “দর্শন পড়ার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না [তাঁর] এবং সম্ভবত তা করে উঠার সুযোগও পান নি তিনি, কিন্তু তাঁর উদার দর্শন, সহনশীলতা ও কাজ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছিল”।
চার পুত্র ও এক কন্যা[১২] সন্তানের অভিভাবক ছিলেন বান্টিঙ দম্পতি। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে ফ্রেডই কনিষ্ঠ। ‘ফ্রেড’- এই ফ্রেড নামেই পরিজনরা ডাকাতেন তাঁকে। ছোটো থেকেই ভীষণ মুখচোরা ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন ফ্রেড। তাঁর মা, মার্গারেট গ্রান্টের বয়ানে- “ফ্রেড খুব জলি ছিল না”।
| বান্টিঙ পরিবার। পিছনে দাঁড়িয়ে তিন দাদা: (বাঁদিক থেকে) কেনিথ বান্টিঙ, নেলসন বান্টিঙ, থম্পসন বান্টিঙ। মাঝ চেয়ারে বসে বাবা উইলিয়ম বান্টিঙ ও মা মার্গারেট বান্টিঙ। বাবার পাশে বসে দিদি এস্থার বান্টিঙ। মায়ের পাশে বসে ফ্রেড। |
অ্যালিস্টন শহরে ‘দ্য পাবলিক অ্যান্ড হাইস্কুল’এ প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন ফ্রেড। সেই সময়ের এক শিক্ষকের বয়ানে, “বান্টিঙ ছিলেন লাজুক প্রকৃতির, অন্তর্মুখী কিন্তু পরিশ্রমী”। শিক্ষকের মতে, “নজরে পড়ার মতো ছাত্র ছিলেন না বান্টিঙ। … কিন্তু একথা সত্যি, সে যা করত সব সময়েই তাঁর সেরাটা দিয়েই করত”। একথা সত্যি যে ছোটোবেলায় ছাত্র হিসেবে নজরে পড়ার মতো ছিলেন না বান্টিঙ। ছোটোবেলার এই পড়াশুনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বান্টিঙ লিখেছেন, “একনাগাড়ে একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম আমি, এই বুঝি ক্লাসে পড়া ধরে [আমায়]। যদি উত্তরটা আমার জানাও থাকতো আমি কখনও ক্লাসে তা বলতে পারতাম না। রচনা ও ভূগোল ভালো লাগতো আমার কিন্তু পৃথিবীর যে জিনিসটা সব থেকে বেশি বিব্রত করতো আমায় তা হলো বানান। আমি বানান করতে পারতাম না। প্রত্যেকটা শব্দের তিন চার রকমের বানান মনে আসতো [আমার]। একটা অনুমান করতাম এবং অবধারিত ভাবে তা ভুল হতো”।
| অ্যালিস্টনে বান্টিঙের পারিবারিক বাড়ি |
এই বানান ভুলের কারণেই প্রত্যেক বিষয়েই অনেকটা নম্বর কাটা যেত ফ্রেডের। ফলে স্কুল জীবনের কোনো ক্লাসেই উল্লেখযোগ্য কোনো রেজাল্ট ছিল না তাঁর। আর পাঁচটা সাধারণ ছাত্রের মতো, কোনো রকমে পাশ করে যেতেন তিনি। শুধু বানানই নয়, কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আড়ষ্ট ছিলেন ফ্রেড। এমনিতেই বড় একটা মিশুকে ছিলেন না তিনি। তার উপরে কথাও বলতেন কম। ফলে স্কুল জীবনে কারও সাথেই সেভাবে বন্ধুত্বও গড়ে উঠে নি তাঁর। একা একাই থাকতে ভালোবাসতেন তিনি। বন্ধুদের সাথে হৈহৈ করে খেলার থেকে বরং মাঠে ঘাটে আনমনে ঘুরে বেড়াতে বেশি ভালো লাগত তাঁর। এই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য বন্ধুবান্ধবরা টিটকারি করতো তাঁকে। ‘মেয়েলি স্বভাব’ বলে খেপাতো তাঁকে। এই টিটকারি সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়তেন তিনি।
এভাবেই একদিন স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলো ফ্রেডের। জুলাই ১৯০৮, জুনিয়র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করলেন ফ্রেড। সমস্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে, গড় করে, ১০০ নম্বরে গ্রেড দেওয়া হতো সেই সময়ে। ফ্রেডের গ্রেড হলো ৩৩। খুবই সাধারণ মানের নম্বর। যাহোক, জুনিয়র স্কুলের পর, এবার সিনিয়র স্কুলে পড়ার পালা। হাইস্কুলে ভর্তি হলেন ফ্রেড। দু’বছর পর শেষ হলো সিনিয়র স্কুলের পাঠও। এবারও খুবই সাধারণ মানের ফল হলো তাঁর।
সিনিয়র স্কুল পাশ করার পর, আর বিশেষ পড়ার ইচ্ছা নেই ফ্রেডের। পড়তে যে মোটেও ভালো লাগে না তাঁর। অথচ তাঁর বাবা মায়ের একান্ত ইচ্ছা, ধর্মশাস্ত্র নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করুক ফ্রেড। তাঁরা চান পরবর্তী জীবনে যাজক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রেড। এক প্রকার বাবা মায়ের ইচ্ছাতেই উচ্চতর শিক্ষার জন্য টরন্টো যেতে হলো বান্টিঙকে। সেপ্টেম্বর ১৯১০, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ভিক্টোরিয়া কলেজে ঈশ্বরতত্ত্ব (ডিভিনিটি) নিয়ে আর্টস বিভাগে ভর্তি হলেন ফ্রেড। প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার সুবাদে, টরন্টোর পরিবেশ অ্যালিস্টনের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানকার পরিবেশ, চালচলন, যুক্তিবোধ অনেকটাই খোলামেলা, উদার। এই বাঁধনহীন খোলামেলা পরিবেশে নিজেকে একেবারে অন্য ভাবে মেলে ধরলেন ফ্রেড। গান বাজনার সাথে যুক্ত হলেন তিনি। কলেজের ‘ভিক গ্লি ক্লাব-এর (ভিক = ভিক্টোরিয়া, কলেজের নাম) সাথে যুক্ত হলেন তিনি। জলদ গম্ভীর কন্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন ফ্রেড। এই কন্ঠস্বরের দৌলতেই ক্লাবের কনসার্টে নিয়মিত সদস্য হলেন তিনি। কলেজ সোশ্যালে তাঁর পারফরমেন্স ছিল বাঁধা। আর পড়াশুনা? ধুস্স্, ওসব নিয়ে কে ভাবে? ওসব পরে দেখা যাবে।
১৯১১ সালের গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের ছুটিতে অ্যালিস্টনের বাড়িতে এলেন বান্টিঙ। অ্যালিস্টনের চার্চে একদিন দেখা হলো ছিপছিপে চেহারার তরুণী এডিথ রোচের সাথে। ২০ বছরের যুবক বান্টিঙের মনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেলেন রোচ। সুযোগ বুঝে একদিন আলাপ পরিচয়ও হলো রোচের সাথে। এই পরিচয় থেকে ক্রমেই এক নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হলেন তাঁরা। পরস্পরের প্রেমে আসক্ত হলেন রোচ ও বান্টিঙ। এক নিবিড় প্রেমের বন্ধনে আবব্ধ হলেন তাঁরা।
অবকাশান্তে টরন্টো ফিরলেন বান্টিঙ। আগের মতোই মসৃণ ভাবে বয়ে চলল বান্টিঙের জীবন। গান, গল্প, খেলা সবই যথাযথ ভাবেই বয়ে চলেছে বান্টিঙের জীবনে। সাথে আছে নব যৌবনের প্রেম। এত কিছুর মাঝে, বিরক্তিকর শুধু পড়াশুনা। পড়তে কি আর মন বসে তখন? এদিকে সামনেই কিন্ত বার্ষিক পরীক্ষা! সেই দিকে কোনো হুঁশই নেই বান্টিঙের।
| এডিথ রোচ |
পরীক্ষা! তাই তো! সামনেই পরীক্ষা, আর তেমন ভাবে কিছু পড়াই হয় নি এখনও তাঁর। তাড়াতাড়ি করে পড়তে শুরু করলেন বান্টিঙ। ওই নমো নমো করে পাশ করার জন্য যতটুকু পড়া প্রয়োজন ততটুকুই আর কি। কিন্তু বান্টিঙের সেই প্রস্তুতি আদৌ সময়োপযোগী ছিল না। ফলও ফলল সেই রকমই। বাৎসরিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন বান্টিঙ। ডাহা ফেল করলেন তিনি। পড়তে ভালো না লাগলেও এতোদিন কিন্তু সব পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করে এসেছিলেন তিনি। এবার একেবারে ফেল?! এমন রেজাল্ট আগে কখনও হয় নি বান্টিঙের। ইস্স্স্, বাবা-মাকে মুখ দেখাবো কী করে? লজ্জায়, দুঃখে, হতাশায় মনে মনে কুঁকড়ে গেলেন তিনি। হতোদ্যম হয়ে ঠিক করলেন আর পড়বেন না, ছেড়েই দেবেন পড়াশুনা। বাবা-মায়ের ইচ্ছায়, জোর করে পড়তে গিয়েই এই হাল হয়েছে আজ তাঁর। পরক্ষণেই আবার ভাবছেন, ফেল করেছেন তো কী হয়েছে, সামনের বছর তো আবার পরীক্ষা দেওয়াই যায়। আবার কখনও ভাবছেন, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার ভর্তি হলে কেমন হয়? এই ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে যে পড়তে একেবারেই ভালো লাগে না তাঁর।
এলো নতুন বছর, ১৯১২ সাল। বড় একটা সুখের সময় যাচ্ছে না বান্টিঙের। ভীষণ মনমরা তিনি। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ রকমই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনি। ভবিষ্যতের নানান ভাবনায় তখন তিনি অস্থির। ঠিক সেই সময় জানতে পারলেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় নতুন বছরের জন্য ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। সহসা কী মনে হলো তাঁর কে জানে, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সোজা গিয়ে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হবার আবেদন করে বসলেন। আর কী আশ্চর্য! গৃহীতও হয়ে গেল তাঁর আবেদন পত্র। এক মুহূর্ত দেরি না করে, কারো সাথে কোনো পরামর্শ না করে, নিজের একক সিদ্ধান্তে, ডাক্তারি বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলেন বান্টিঙ। সময়টা, ফেব্রুয়ারি ১৯১২।
পড়াশুনা করতে মোটেও ভালো লাগত না যে ছেলের, কিছুদিন আগেও যিনি ভাবতেন পড়াশুনা ছেড়েই দেবেন, হঠাৎ কী এমন ঘটল তাঁর জীবনে যে ডাক্তারি পড়াতে ছুটলেন তিনি? বিষয়টা কৌতূহলোদ্দীপক তো বটেই। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই নিরসন করেছেন এই কৌতূহল। তিনি লেখেছেন, “একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখি একটা নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদের পাটাতনের উপর দুটো লোক দাঁডিয়ে আছেন। আমি দেখলাম, যে পাটাতনটার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা হঠাৎই তা ভেঙ্গে পড়ে। দুজনেই মাটিতে পড়ে যান এবং ভীষণ রকমের আঘাত পান তাঁরা। একজন তো নড়তেই পারছিলেন না; অন্যজন হাতটা নাড়ালেন আর তারপরই স্থির হয়ে গেলেন। আমি ডাক্তারের খোঁজে দৌড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি [ডাক্তার] উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতি সকলকে আশ্বস্ত করলো। তিনি যখন আহত দুজনকে পরীক্ষা করছিলেন, কাটা, ক্ষত ও ভাঙ্গা হাড়ের যত্ন নিচ্ছিলেন, আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর দক্ষ হাতের দিকে নজর রাখছিলাম। সেই উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলোতে আমি অনুভব করি যে চিকিৎসাই হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। সেই দিন থেকে আমার [জীবনের] পরম লক্ষ্য ছিল চিকিৎসক হওয়া”।
এই ‘স্কুল থেকে ফেরা’ মানে, তাঁর ছোটোবেলায় অ্যালিস্টন শহরের দ্য পাবলিক অ্যান্ড হাইস্কুল থেকে ফেরার কথা বলেছেন বান্টিঙ। সে বহুদিন আগের ঘটনা। তাঁর নিকটজনের কেউই কিন্তু জানতেন না এই ঘটনার কথা। ছোটোবেলার সেই স্কুল থেকে ফেরার ঘটনা, তাঁর মনের গহনে কী যে এক স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়েছিল, বাইরে থেকে কেউই বুঝতে পারেন নি তা। দীর্ঘদিন ধরে মনের গভীরে, নির্জনে, লালিত হয়েছিল সেই স্বপ্ন। আর আজ, এক মাহেন্দ্রক্ষণে সহসাই মাথা চাড়া দিয়ে মহীরূহ বেশে ডালপালা মেলে প্রকাশিত হয়েছে সেই সুপ্ত বাসনা। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে তাই নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারেন নি বান্টিঙ। আগুপিছু না ভেবে, স্বপ্নাদেশের মতো সোজা গিয়ে ভর্তি হয়ে এলেন ডাক্তারি কোর্সে। তাছাড়াও আমরা দেখেছি, ঈশ্বরতত্ত্ব পড়তে মোটেও ভালো লাগতো না বান্টিঙের। এই বিষয় থেকে মনেপ্রাণে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ এক পরিত্রাণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল তাঁর জীবনে। তখন তাঁর সামনে ছিল মুক্তি, পিছনে ছিল বাঁধন। ফলে, ডাক্তারি পড়া নিয়ে দ্বিতীয়বার আর ভাবতে হয়নি তাঁকে।
ফেব্রুয়ারি মাসে ডাক্তারি পড়ার জন্য নিজের নাম নথিভুক্ত করিয়ে এলেন বান্টিঙ। ক্লাস কিন্তু শুরু হবে সেই সেপ্টেম্বর মাসে। মাঝে মাস ছয়েকের অবকাশ। এই অবকাশে অ্যালিস্টনের বাড়িতে এলেন বান্টিঙ। ছুটির এই অবসরে এবার তলিয়ে ভাবার সময় পেলেন তিনি। এবার তাঁর মাথায় আসছে দুশ্চিন্তা। পড়ছিলেন আর্টস নিয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজে। হঠাৎই মেডিক্যাল পড়ার জন্য ভর্তি হলেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যাপারটা হঠকারী হয়ে গেল না তো? ক্ষণিক উত্তেজনার বশে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন নি তো তিনি?
অ্যালিস্টনে তাঁর এক বন্ধু, পরে এই বিষয়ে বলেছেন, আর্টস পড়া ও মেডিক্যাল পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে আলোচনা করেতেন ফ্রেড। আলোচনা করতেন স্থানীয় পাদ্রি রেভারেন্ড পিটার এডিসনের সাথেও। তাঁর বাবা মা যে ঈশ্বরতত্ত্ব পড়ার জন্য টরন্টো পাঠিয়ে ছিলেন তাঁকে সেকথা অজানা ছিল না রেভারেন্ড এডিসনের। রেভারেন্ড এডিসন ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি। বান্টিঙের মানসিক অবস্থা ভালোই বুঝতে পারছিলেন তিনি। তাই বান্টিঙের ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নি তিনি। তাঁর নিজের পছন্দের বিষয়, নিজের ভালোবাসার বিষয় নিয়ে পড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন পাদ্রি এডিসন। পাদ্রি এডিসনের উপর অগাধ আস্থা ছিল বান্টিঙের। এডিসনের কথায় অনেকটা ভরসা পেলেন বান্টিঙ। মনের জোর যেন ফিরে পেলেন তিনি। এবার একবার বাবা-মায়ের সাথেও আলোচনা করা দরকার বলে ভাবলেন তিনি। না, ফ্রেডের সিদ্ধান্তে অমত নেই বাবা-মায়েরও। ডাক্তারি পড়াতে কোনো আপত্তি নেই তাঁদের। এবার যেন কিছুটা চাপ মুক্ত হলেন ফ্রেড। অবকাশান্তে, খুশি মনে টরন্টোয় ফিরলেন বান্টিঙ, ডাক্তারি পড়তে।
(চলবে)
[১১] ১৯৯১ সালে, অ্যালিস্টনের সাথে পার্শ্ববর্তী টটেনহ্যাম, বিটন এবং আরো কিছু সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে ‘নিউ টেকুম্সেত’ শহর গড়ে উঠেছে। ফলে অ্যালিস্টন এখন নিউ টেকুমসেত নামে পরিচিত।
[১২] উইলিয়ম বান্টিঙ এবং মার্গারেট বান্টিঙের পুত্র সন্তানরা হলেন, এঙ্গাস নেলসন বান্টিঙ (১৮৮১-১৯৪১), উইলিয়ম থম্পসন বান্টিঙ [পিতার মতো একই নাম (১৮৮২-১৯৬৪)], আলেক্সান্দার কেনিথ বান্টিঙ (১৮৮৪-১৯৩০) এবং ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিঙ (১৮৯১-১৯৪১)। তাঁদের একমাত্র কন্যার নাম এস্থার এলিনা বান্টিঙ (১৮৮৭-১৯৩৬)। আলফ্রেড গ্রান্ট বান্টিঙ (১৮৮৬) নামে বান্টিঙ দম্পতির আরেক পুত্র জন্মগ্রহন করেছিলেন, যিনি মাত্র ২ মাস বয়সে হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।