পঞ্চম অধ্যায়—নার্সিং নিয়ে আরও কথা
আগের অধ্যায়ে বলেছিলাম যে ভারতে নার্সিং প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের বক্তব্য সম্ভবত একটি পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে কাজ করে থাকবে মেডিক্যাল কলেজে নার্সিং ট্রেনিংয়ের জন্য আলাদা বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে। নাইটিংগেল ইউরেশিয়ান এবং ইউরোপীয় মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন যারা মেডিক্যাল কলেজে নার্স হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু নাইটিংগেল অন্য একটি চিঠিতে (২০ জুলাই, ১৮৬৯) পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছেন যে ইংল্যান্ডে একজন মহিলা নার্স হিসেবে কাজ করার জন্য প্রত্যাখ্যাত হয় এবং “took only a month’s certificate from one of the lying-in hospitals in London, and went out to India to practise, this plus a few lectures being her whole course of medical education.” (Florence Nightingale on Women, Medicine, Midwifery and Prostitution, ed., Lynn McDnald, 2005, পৃঃ ৫৫) অর্থাৎ, ইংল্যান্ড থেকে আগত এবং সাদা চামড়ার নার্স মানেই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত এমন ভাবার কোন বাস্তব কারণ ছিলনা (যদিও সাধারণ মানুষের মাঝে এরকম ধারণাই ছিল বলে মনে হয় এবং বাস্তব জগতে এটা গভীরভাবে বিদ্যমানও ছিল)।
নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নাইটিংগেল জানাচ্ছেন – In my humble little midwifery school at King’s College Hospital we gave a not less than six months’ practical course, plus lectures. Yet we would not certify the pupils as midwives, but only as midwifery nurses, i.e., they were to know enough to know when a case of ‘‘abnormal parturition’’ was past their skill, in their future practice (and that is more than most English midwives know) and to call in ‘‘the doctor.’’ (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫)
এর আগে (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫) তিনি বলছেন – “যদি আমরা ভারতের জন্য নার্সদের প্রশিক্ষিত করি তাহলে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং মহিলাদের এ কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪) তাঁর বন্ধু খ্রিষ্টান প্রব্রাজিকা মেরি জোন্সকে লেখা চিঠিতে তিনি এ বিষয়টি জানান। এ চিঠির প্রত্যুত্তরে জোন্স লেখেন – “ভারতের অবশ্যই আমাদের ওপরে পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কি করা যেতে পারে? It makes me mad with shame that the brave and good governor general’s demand for nurses cannot be promptly met.’’ (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১)
এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে ভারতে মৃত্যুহার ছিল প্রতি মাইলে ৪০.৭ এবং life expectancy ২৪.৬ বছর। শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০-এ ২৫০-এর কাছাকাছি। প্রসূতি মৃত্যুর হারের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়না। (Ira Klein, “Death in India, 1871-1921”, Journal of Asian Studies, Vol. 32, No. 4 (Aug., 1973), pp. 639-659) ইংল্যান্ড সেসময়ে নিজেদের পৃথিবীর “সভ্যতম দেশ” বলে দাবী করত।
ফলে আন্তর্জাতিকভাবে এ পরিসংখ্যান খুব সুখের নয়। শুধু তাই নয়, নিজেদের দেশেও উদারমনা মানুষদের তরফে এ অবস্থার প্রতিকার করার একটা দাবী ছিল। এরসঙ্গে যুক্ত করতে হবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলা দেশেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন বিদ্বৎসভা এবং শিক্ষিত গোষ্ঠীর মাঝে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদের মানবিক মুখ হিসেবে মেডিসিনকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও মেডিসিনের আভ্যন্তরীন তাগিদে প্রশিক্ষিত নার্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রসূতি মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো একটি সরকারি অ্যাজেন্ডা হয়ে ওঠে।
আরেকটি প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে ভেবে দেখা যায়। ব্রিটিশ কর্তারা চাইত ভারতীয় সরকারি আমলাদের স্ত্রীরা যাতে ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবধারায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। কারণ, অশিক্ষিত নারী কিংবা শুধুমাত্র দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত নারীরা “would split the household into two worlds. Just as the British were certain that rebellious plots were hatched and nurtured in inaccessible zenanas”। (Geraldine Forbes, Women in Modern India (The New Cambridge History of India, IV.2), 1996, পৃঃ ৬০) মোদ্দা কথা হল, “অগম্য” অন্তঃপুরকে গম্য করে তুলতে হবে যাতে ইংরেজি ভাবধারায় সিঞ্চিত মহিলারা সন্তানদেরও “anglophile” করে গড়ে তুলতে পারে। বিদ্রোহীদের আঁতুরঘর না হয়ে ওঠে অন্তঃপুর। বিপরীতে, আধুনিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রসবের আঁতুরঘর হবে অন্তঃপুর। সরকারি আমলাদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ছিল সে একই কথা প্রযোজ্য ছিল শিক্ষিত, ওপরতলার বাসিন্দা বাঙ্গালি তথা ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। অন্তঃপুরে প্রবেশের এবং একে “গম্য” করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল আধুনিক প্রসব-ব্যবস্থা এবং অন্তঃপুরে পুরুষ চিকিৎসকের প্রবেশ। এবং এসবকিছুর অন্যতম ভরকেন্দ্র ছিল মেডিক্যাল কলেজে আধুনিক মেডিসিনের চিকিৎসার সূচনা, বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং ১৮৪১ সালে মিডওয়াইফারি বিভাগের আত্মপ্রকাশ।
মিডওয়াইফারি থেকে প্রশিক্ষিত দাই
১৮৫০-এর দশক থেকে বটতলায় ছাপা শুরু হয় বিভিন্ন ঘরোয়া চিকিৎসার বই “পাঠকদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টায়, বা গরিবদের চিকিৎসায় নিযুক্ত ডাক্তারদের সুবিধার্থে”। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় দুই আনা দামের চিকিৎসার্ণব – এ বইটি কয়েকহাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। এরও আগে ১৮৪৩ সালে হলধর সেন রচিত চিকিৎসা রত্নাকর প্রকাশিত হয়েছিল। (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, ২০১৩, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬) এ ধরণের বইয়ের বিপুল চাহিদা থেকে বোঝা যায় জনমানসে তথা শিক্ষিত সমাজের অন্তত একাংশের মাঝে বাংলা ভাষায় আধুনিক চিকিৎসাশিক্ষার বই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একে গবেষকেরা অভিহিত করেছেন “print capitalism” নামে।
প্রশিক্ষিত দাই বা ধাত্রী তৈরি করার প্রস্তাব, আমার জ্ঞানত, প্রথম আসে ১৮৩৭ সালে মধুসূদন গুপ্তের তরফে। ১৮৩৭ সালে টাউন হলে ফিভার হাসপাতাল তৈরির জন্য কমিটির সামনে ১৮৩৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৪ মার্চ এবং ২৬ এপ্রিল ৩ দফায় তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করেন।
প্রথম দিনের (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭) সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান দু’ধরণের রোগীকেই তিনি দেখেন। তিনি জানান যে সমস্ত মিডওয়াইফরা প্রসূতিদের দেখে থাকে তারা “perfectly ignorant of their profession. The danger that occurs is partly from their ignorance, and partly from the Native customs.” (“Municipal Enquiry: Second Sub-Committee”, Abridgement of the Report of the Committee Appointed by the Right Honourable the Governour (sic) of Bengal for the Establishment of a Fever Hospital, and the Inquiries into Local Management and Taxation in Calcutta (Calcutta: Bishop’s College Press), 1840), reprinted 1845, পৃঃ ৮৬-৮৭)
দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যে (৪ মার্চ, ১৮৩৭) তিনি প্রসূতি গৃহের অবর্ণনীয় অবস্থার বিশদ বিবরণ দেন। এই ঘর “small damp room, ill ventilated, with one small door only”। প্রসবের পরেই ঘরের বিভিন্ন প্রান্তে কাঠ জ্বালানো হয়, ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। ২০ জনের মধ্যে ৩ থেকে ৪ জন নারী মারা যায়। তাঁর মন্তব্য ছিল – “If we had a sufficient number of well qualified female Hindoo Midwives, whose charges were very moderate, I think they might accomplish a great deal by good advice.” যদি একটি হাসপাতালে lying-in ward তৈরি করা যায়, যেখানে উপযুক্ত হিন্দু ধাত্রী থাকবে, তাহলে নীচু জাতের মহিলারা খুশি মনে এই সুবিধে নেবে এবং বহু প্রাণ বাঁচবে। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮) এর ফলে অনেক দাইয়ের কর্মসংস্থানও হবে। ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন অনুযায়ী এরা কাজ করবে। (পৃঃ ৮৯)
১৮৪১ সালে মেডিক্যাল কলেজে মিডওয়াইফারি ওয়ার্ড খোলা হল। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে প্রসবের জন্য ২৪৪ জন মহিলা ভর্তি হয়েছিল। ১৮৪১ সালে ভর্তি হয়েছিল ৩০ জন। ১৮৪৬-এ ৪৮ জন। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডানকান স্টুয়ার্ট তাঁর রিপোর্টে (“Statistical History of the Female Hospital”) জানান যে যদিও পরিসংখ্যানের দিক থেকে অল্পসংখ্যক মহিলা ভর্তি হয়েছে কিন্তু “is sufficient to prove the extreme importance of the study of midwifery.” (GRPI 1846-47, Appendix E, p. clxxv)
১৮৪৭-৪৮ সালের “Report of the Obstetric practice of the Medical College, Female Hospital, from 1st March 1847 to 1st March 1848”-এ বলা হয়, হিন্দুদের মধ্যে পুরুষ ডাক্তারদের প্রসবের করানোর বিরুদ্ধে যে তীব্র কুসংস্কার ছিল সেটা আর অবশিষ্ট নেই। এক্ষেত্রে ফিমেল হাসপাতালের “হাউস সার্জন” প্রসন্নকুমার মিত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কলেজের আরেকজন গ্র্যাজুয়েট গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কলকাতাবাসীদের মধ্যে “extensive practice” করছেন। ২২ জন মহিলার প্রসব করিয়েছেন। (GRPI 1847-48, Appendix E, No. VII, p. clix) এ রিপোর্টে আরও বলা হয়, ৬ জন বা তার চেয়ে বেশিসংখ্যক কলেজ গ্র্যাজুয়েট যারা এখন কলকাতায় ভালোভাবে প্র্যাক্টিস করছে “are habitually called to take charge of the women of the families they attend during their confinements … they are requested to undertake the medical management of every case, both during and after delivery”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ cl)
১৮৪৯-৫০-এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, মেডিক্যাল কলেজে প্রসব করানোর ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য “to hold out many little advantages to them, in the shape of clothes for themselves and their children when they depart, allowances for tobacco”-এর মতো উপঢৌকন দেওয়া প্রয়োজনীয়। (GRPI 1849-50, পৃঃ ১২৯)
এসব রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে ইউরোপীয় মেডিসিন একদিকে মেডিক্যাল কলেজের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করছে, অন্যদিকে মহিলাদের দেহ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে (বিশেষ করে প্রসব করানোর মতো সংবেদনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে) যে অচলায়তন এবং ঐতিহ্যগত কুসংস্কার ছিল তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক মেডিসিন হয়ে উঠছে সর্বব্যাপী। এরপরের ধাপে যদি মহিলাদেরই প্রশিক্ষিত দাই হিসেবে কাজ করানো যায় তাহলে বিষয়টি আরও জনগ্রাহ্য হয়ে উঠবে।
১ অক্টোবর, ১৮৭০-এ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ প্রকাশিত “Native Midwives” শীর্ষক রিপোর্ট থেকে জানতে পারছি – “At Shahjehanpore there is also a Midwifery Class established in the Dispensary for the instruction of native dhaies; it was organized early in 1869, and is proving successful. Five wo- men have been in constant attendance, receiving Rs. 3 as subsistence allowance monthly; one woman is now qualified to practice midwifery”। (পৃঃ ২১৪) একই রিপোর্টে বলা হচ্ছে – “This system of instruction has also been actively taken up in the Lower Provinces, and with the pecuniary assistance granted by Government, the classes ought in a year or two to provide efficient midwives for many of the large towns. Classes at present are only formed at the Medical College, Calcutta, and at the Mitford Hospital, Dacca”। অর্থাৎ, শাহজাহানপুরের ডিসপেনসারিতে ১৮৬৯ সালে প্রথম দেশীয় দাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। সম্ভবত এর সাফল্য দেখে ১৮৭০ সালে প্রায় একইসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ এবং ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হয় দেশীয় দাইদের দেশীয় সমাজের উপযোগী আধুনিক মেডিসিনের মিডওয়াফারি ট্রেনিংয়ের।
১৮৬৭-৬৮ সালে বামাবোধিনী পত্রিকা অন্তত ১০ কিস্তিতে “ধাত্রীবিদ্যা” নিয়ে বিস্তৃত লেখা প্রকাশ করে। ধারাবাহিক এ প্রবন্ধের একটি কিস্তিতে বলা হল – “ধাত্রী-বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে বস্তিদেশ, জনন-ইন্দ্রিয় এবং গর্ভ সঞ্চার, জরায়ু মধ্যে শিশুর ক্রমশঃ পরিবর্তন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি অগ্রে শিক্ষা করা আবশ্যক কিন্তু বামাবোধিনীতে সে সকল বিষয় লেখা যুক্তি সঙ্গত হয় না। ধাত্রী-বিদ্যার যে সকল বিষয় স্ত্রীলোকেরা পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, সেই সকল বিষয় কেবল ইহাতে লিখিত হইবে।” (“ধাত্রী বিদ্যা”, বামাবোধিনী, ৫০শ সংখ্যা, আশ্বিন বঙ্গাব্দ, ১২৭৪, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৫৯৭) ইউরোপের বিপরীতে মহিলাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (বিশেষ করে জননাঙ্গ) এবং সন্তানধারণ পরবর্তী নানা বিষয়ে অনুপুঙ্খ লেখার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক, in-built সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা করছে নিশ্চয়ই। যে কারণে স্ত্রীলোকদের “কুণ্ঠিত” না হবার বিষয় এখানে লেখা হবে – একথা গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হল।
আরেকটি অংশে বলা হল – “আমাদের দেশের লোকেরা কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ বাসগৃহে সন্তান প্রসব হইতে দেয়না। এজন্য সূতিকাগৃহ নির্মাণ প্রথা প্রচলিত আছে … কোথায় এসময় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়মে থাকা উচিত, তাহা না হইয়া বরং যাহাতে স্পষ্ট অপকার হয় সেই প্রকার কার্য করা হয়। সূতিকাগারের দোষে অনেক শিশু ও প্রসূতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে।” (৫২ সংখ্যা, অগ্রহায়ন বঙ্গাব্দ ১২৭৪, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৬৩৬) “এমন কি ধাত্রীর দোষে প্রসূতির ও শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে … নানা দেশের বিজ্ঞা ধাত্রীরা প্রসবের উপযোগী অস্ত্র, ঔষধ সঙ্গে লইয়া যান … এদেশের ধাত্রীরা নিতান্ত মূর্খ বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে না। সুতরাং সঙ্গে লইয়াও যায় না।” (“ধাত্রী বিদ্যা”, ৫৪ সংখ্যা, মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৪, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৬৭৬)
পরবর্তী সংখ্যায় বলা হল – “প্রসব বা পরীক্ষার সময় প্রসূতিকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া হাত দুই খান মস্তকের উপর তুলিয়া দিবে এবং দুই আটু বক্ষঃস্থলে রাখিবে। এই অবস্থায় প্রসূতি সহজেই প্রসব হইতে পারে … এ অবস্থায় সমুদয় শরীর বিবস্ত্র করিয়া সুদ্ধ একখান কাপড় ঢিলা করিয়া পরিধান করা ভাল, কিন্তু সর্ব্বশরীর উলঙ্গ হইলেও ক্ষতি নাই।” (৫৫ সংখ্যা, ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৪, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৬৮৯-৬৯০)
এরপরের সংখ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল – “সূতিকাগারে আবশ্যক দ্রব্যগুলির আয়োজন রাখা উচিত, যথা – কাঁচি একখান, রেশম একটু, ফেলানেল কাপড় এক বর্গহস্ত প্রমাণ। যেমাত্র “জল ভাঙ্গিল” তখনি দ্বিতীয় অবস্থা। জল ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরেই শিশুর মস্তক নির্গত হইতে থাকে। প্রসূতিকে প্রসব শয্যায় শয়ন করাইয়া একবার পরীক্ষা করিবে। যতক্ষন পর্য্যন্ত শিশু নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রসূতির নিকট বসিয়া থাকা উচিত।” (৫৬ সংখ্যা, চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৪, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭১০)
স্মরণে রাখা দরকার, বামাবোধিনী পত্রিকা কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম তরুণের উদ্যোগে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের আগস্ট মাসে (বাংলা ১২৭০ সনের ভাদ্র মাসে) এই পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। ব্রাহ্ম সমাজ সেসময় নারীদের শিক্ষা, জনসমাজে নারীর উপস্থিতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে সেসময়ে বাংলায় প্রসূতিদের যে অবর্ণনীয় অবস্থা ছিল সে সংকট মোচনের লক্ষ্যে “ধাত্রী বিদ্যা” আলোচনার অবতারণা। নিরাপদ এবং “বৈজ্ঞানিক” ধাত্রীবিদ্যার সূচনা হল বাংলা ভাষাতে।
এরকম এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ১৮৭০ সালে মেডিক্যাল কলেজে চালু হল আলাদা করে মহিলাদের জন্য নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। “Initially, twelve women were enrolled for a one-year training course. As usual, concern was expressed that all women selected for the course should be “respectable.” Special purdah arrangements were considered necessary to attract such women, and extra vigilance was required to deter those of “bad repute.” (Meredith Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal: 1849-1905, 1984, পৃঃ ৩২৭) ১৮৭৯ সালে শ্রীমতী জে এল ঘোষ এবং শ্রীমতী টি এম রায় ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিওন পত্রিকায় (৭ আগস্ট, ১৮৭৯) এঁরা যে ১০৩ কলেজ স্ট্রিটে প্র্যাকটিস করছেন সে ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেন “midwives, holding diploma of the Calcutta Medical College Hospital”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭)
এ বিজ্ঞাপন থেকে অনুমান করা যায়, সেসময়ে সম্পন্ন গৃহে প্রশিক্ষিত দাইদের চাহিদা তৈরি হচ্ছিল। একইসঙ্গে প্রশিক্ষিত দাইদের কাজে নিযুক্ত হবার উপযুক্ত একটি মানসিকতরাও জন্ম হচ্ছিল, অনুমান করা যায়। শিক্ষা জুড়তে শুরু করল বাজারের সাথে, আয়ের নতুন উৎস হিসেবে। বইয়েরও নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে। এক নতুন সমীকরণ তৈরি হল – মেডিক্যাল কলেজে আধুনিক ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষা > সামাজিকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রসবের আকাঙ্খা, অন্তত সমাজের ওপরতলার শিক্ষিত সমাজের মাঝে > হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরে পুরুষ চিকিৎসকের প্রবেশাধিকার > সমাজের সাধারণ দাইদের প্রশিক্ষিত দাই করে গড়ে তোলা > তৈরি-হওয়া নতুন “মেডিক্যাল বাজার”-এ এদের চাহিদা > এর জন্য নতুন পত্রিকা এবং পুস্তকের প্রকাশ > সর্বোপরি সমাজের সব প্রান্তে ইউরোপীয় ধারণার বিস্তার।
বইয়ের বাজারের কেমন চাহিদা সেসময় তৈরি হয়েছিল তার দুটি নমুনা দেখা যাক। (১) ১৮০০ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক যত গ্রন্থ প্রকশিত হয়েছিল তার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থ ছিল সর্বাধিক – ৪৬। আবার ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৭৭৬। এর মধ্যে শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থ সংখ্যা ৪৭২। (প্রদীপ বসু, সম্পাদনা, সাময়িকীঃ পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৯৮, পৃঃ ১৬) (২) ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতিশিক্ষা অর্থাৎ কথোপকথন ছলে ধাই এবং প্রতিদিগের প্রতি উপদেশ। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় (প্রথম সংস্করণ) অন্নদাচরণ খাস্তগির রচিত মানবজন্মতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রসূত শিশু ও স্ত্রীজাতির ব্যাধিসংগ্রহ। এ পুস্তকের বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়। সম্ভবত শেষ সংস্করণ হয় ১৮৭৮ সালে। (অম্বালিকা গুহ, Modernizing Childbirth in Colonial Bengal: A History of Institutionalization and Professionalization of Midwifery, c. 1860-1947, Ph.D. thesis, Victoria University of Wellington, 2015, পৃঃ ৫২)
লক্ষ্যণীয় হল, “native dhais” ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজের ১৮৭০ পরবর্তী বার্ষিক রিপোর্টে ধারাবাহিকভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ১৮৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের রিপোর্টে ঊল্লেখ পাচ্ছি – “Two native dhais passed in midwifery, against three last year, and received certificates of qualification, and eight pupil nurses passed out as midwives, against six in 1884-85.” বিগত শিক্ষাবর্ষে যেখানে ৩ জন মিডওয়াইফ পাস করেছিল, সেখানে এই শিক্ষাবর্ষে ২ জন পাস করেছে। এছাড়া “pupil nurse” বা ছাত্রী-নার্স পাস করেছে ৮ জন, যেখানে ১৮৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ জন পাস করেছিল। (GRPI 1884-85, পৃঃ ৮৬) এখানে একটা খটকা থাকে যে ১৮৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে কেন তুলনায় ১৮৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষকেই আনা হয়েছে? উত্তর জানিনা।
১৮৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের রিপোর্টে জানানো হচ্ছে – “Three native dhais passed in midwifery and received certificates of qualification. Five pupil-nurses passed as midwives.” (GRPI 1885-86, পৃঃ ৭২) লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, একেক বছরে একেক সংখ্যক মহিলা বা ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে ট্রেনিংয়ের জন্য, যে ঘটনা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সম্ভবত প্রশিক্ষিত দাইদের “বাজার” যতটা বৃদ্ধি পাবে অনুমান করা হয়েছিল ততটা বৃদ্ধি পায়নি কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্বিধাও এক্ষেত্রে কাজ করে থাকতে পারে।
যাহোক, ১৮৮০ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে ১২ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রী প্র্যাকটিস করছিলেন। এদের সাফল্য মফস্বল থেকে অন্যদেরও আকৃষ্ট করছিল। এর ফলে “expansion of the training program was recommended because of the increasing supply of the recruits. Many “Hindoo widows of the respectable families” were prepared to take up midwifery.” (Meredith Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal, পৃঃ ৩২৮)
এরকম এক পটভূমি এবং মহিলাদের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য সামাজিক আন্দোলন মেডিক্যাল কলেজে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের রাস্তা সুগম করল। এ বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। মেডিক্যাল শিক্ষার জগতে, বাংলার প্রেক্ষাপটে, এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল।
তবে অন্য একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। সেসময়ে চিন্তা এবং মানসিক গ্রহণযোগ্যতার স্তরে যে শোরগোল পড়েছিল, যে রূপান্তর হচ্ছিল তাতে বাংলা ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক অন্তর্নিহিত নিষিদ্ধতা দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। আমরা বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। ১৮৮৮ সালে চিকিৎসা সম্মিলনী পত্রিকায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা এমবি ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল “বিবাহ-বিচার” প্রবন্ধে লিখলেন – “পাছার অস্থি দুই খানি ২৫ বছরে পূর্ণ হয়। ঊরুদেশের অস্থি খানি পরিপক্ক হইতে বিশ বৎসর আবশ্যক … শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন জীবগণের জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য অনেক বয়সে আরম্ভ হয়। বাস্তবিক শরীরের অন্যান্য যন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক না হইলে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উপস্থিত হয় না।” (সাময়িকীঃ পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ ১৭৫)
বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এরকম নিশ্ছিদ্র এবং শক্ত বায়োলজিক্যাল যুক্তি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে না বেরোলে আশা করা দুর্লভ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অদৃশ্য উপস্থিতি রইল মেডিক্যাল কলেজের – সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, চিন্তা-চেতনা-ভাবনা-বোধের রূপান্তরের ক্ষেত্রে।

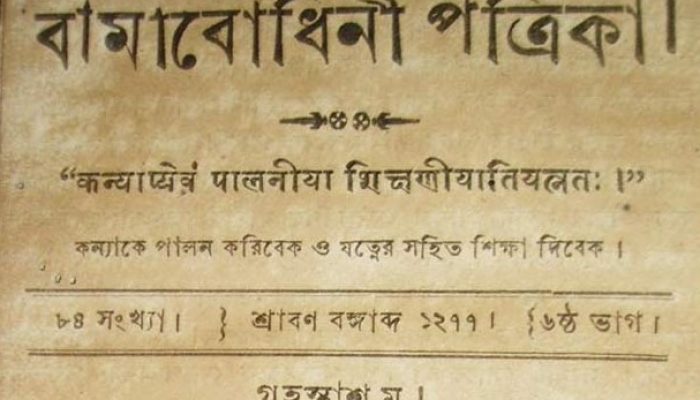

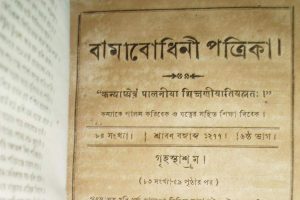

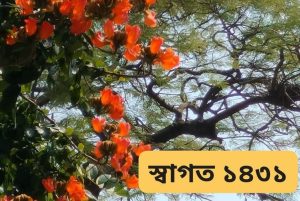








চিত্তাকর্ষক, অভিনব প্রচেষ্টা, বাংলায় দখল আছে
Excellent one sir
আপনার সান্নিধ্যে অনেক অজানা বিষয়ে সম্পর্কে জানলাম, ধন্যবাদ
শিক্ষিত নার্স বা ধাত্রী তৈরী না করলে ভারতে আধুনিক চিকিৎসার সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা কখনই সম্ভব হোত না, কারণ মহিলাদের চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পরিবার থেকেই বন্ধ করে দিত। শিশু ও সদ্যমাতৃ মৃত্যু বাড়তেই থাকত। ১৫০ বছর আগে মেডিকাল কলেজের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং চেষ্টা সফলভাবে শুরু করেছিলেন। ভাল নার্স একজন মরণাপন্ন রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ এবং নিজ অভিজ্ঞতামত সেবা করলে চমৎকার ঘটে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী আমরা অনেকে।
ধন্যবাদ ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে এই বিষয়ে এত সুন্দর আলোচনা করার জন্য।
ধন্যবাদ!