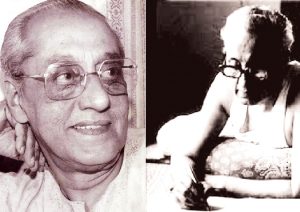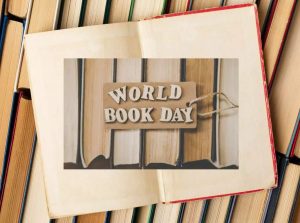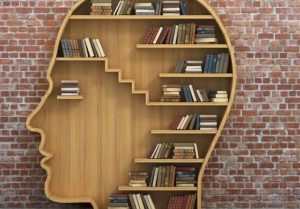~এক~
ষোলো বছর পরে দেশে ফিরে সপ্তক অবাক হয়ে গেলেন। কলেজের পুরোনো বন্ধুরা হইহই করে ধরল। সবাই বলে “আয়, আড্ডা দিয়ে যা।” একটা আড্ডায় গেলে হয় না। তারা আরও আরও আড্ডা চায় – ভাবেনইনি এতদিন পরে বন্ধুরা এ ভাবে মনে রাখবে, ডাকবে…
অবশ্য আরও অবাক হলেন যখন কেউ প্রতিমের খবর দিতে পারল না। মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসে দেড়শো জন ছিলেন – তার মধ্যে আশি নব্বই জন নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। যারা মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখে, তাদের ধরলে সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায়, এবং ক্কচিৎ কদাচিতের দলে আরও জনা বিশেক তো বটেই। কেউ জানে না প্রতিমের খবর? আশ্চর্য নয়? সপ্তকের জন্য আয়োজিত স্পেশাল রি–ইউনিয়নে জনে জনে জিজ্ঞেস করে বুঝলেন, সত্যিই কেউ জানে না। কেবল কাঁধ ঝাঁকানো আর ঠোঁট ওলটানো। শেষে সূর্য যখন বলল, “আমি তো প্রতি বছর ওকে রিইউনিয়নে ডাকি মেসেজ করে। ফোনও করতাম। বছর কয়েক আগে অবধি ফোন ধরে হুঁ–হাঁ করে রেখে দিত, আসব না বলত না, কিন্তু আসতও না। তারপরে বন্ধ করে দিয়েছি… এখন কোথায় আছে–টাছে আর জানি না।…” তখন সবাই অন্নপূর্ণার দিকে তাকিয়েছিল। পূর্ণা সরকারী চাকরিতে বেশ উঁচু পদে রয়েছে। কোনও বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর। পরদিনই ফোন করে জানাল, প্রতিম ওই সেই গ্রামেই আছে, যেখানে ষোলো–সতেরো বছর আগে ওর প্রথম পোস্টিং হয়েছিল। ফুলপুকুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। সপ্তক জিজ্ঞেস করেছিলেন, “ষোলো বছরে প্রোমোশন, ট্রানসফার – কিছুই হল না? ওই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে এখনও?” পূর্ণা বলেছিল, “ট্রানসফার অর্ডার হয়েছিল দু–বার। জয়েন করার পাঁচ আর সাত বছর পরে। দু–বারই রিফিউজ করেছিল। ফাইলে রয়েছে।”
~দুই~
অন্য উপায় নেই বুঝে সপ্তক ঠিক করলেন, নিজেই যাবেন। কলেজে থাকাকালীন উনিই ছিলেন প্রতিমের বেস্ট – না, একমাত্র বন্ধু। মনে হল এটা শুধু বন্ধুপ্রীতি নয়, খানিকটা কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে। প্রতিম যখন ওই সুদূর জঙ্গলের রাজ্যে লঞ্চ আর ভটভটি নৌকো করে প্রথম গিয়েছিল, সপ্তক–ই সঙ্গে ছিলেন। সকাল থেকে লটবহর নিয়ে বেরিয়ে প্রথমে লোক্যাল ট্রেন, তারপরে সুদূর বন্দর শহর থেকে লঞ্চ – ওসব অঞ্চলে নদীপথই ছিল চলাচলের একমাত্র উপায়। সন্ধেবেলা ব্লক প্রাইমারি হাসপাতালে ওদেরই কলেজের সাত বছরের সিনিয়র এক্স–স্টুডেন্ট ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের বাড়িতে রাত্রিবাস, গল্প–আড্ডা, তারপরে পরদিন জয়েনিং রিপোর্ট না–দিয়েই (বি–এম–ও–এইচ বলেছিলেন, “আগে গিয়ে দেখে আয় কী অবস্থা। আমি যতদূর জানি, তোর থাকারই জায়গা নেই। সুতরাং আটঘাট বেঁধে যাবি। জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে দিলে আবার ছুটি পাবার সমস্যা…”) আবার ভটভটি নৌকোয় রওয়ানা, মাঝপথে কোথায় যেন থেমে নৌকো বদলে আর একটা ভটভটিতে দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছনো ফুলপুকুর গ্রামে। গ্রামের লোক উপচে পড়েছিল নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখতে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে ফুলপুকুরে ডাক্তার এল। সুতরাং আপ্যায়নটা দু–বন্ধুর আশ্চর্য লাগেনি, বরং ভালোই লেগেছিল।
পড়ন্ত রোদে ফুলপুকুর প্রাইমারির প্রথম দর্শনে দু–বন্ধুই চমকে গেছিলেন। হলুদ রোদে লাল হাসপাতাল–বাড়ির দেওয়াল জ্বলজ্বল করছিল যেন পলার তৈরি। সামনের বিরাট চারকোনা পুকুরটা ঝকঝক করছিল। চাকরিটা প্রতিমের ভীষণই প্রয়োজন ছিল। বাবা সবে রিটায়ার করে দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করছেন, এমন সময় মায়ের ক্যানসার ধরা পড়ায় এক ধাক্কায় করণিক জীবনের সামান্য সঞ্চয় প্রায় শূন্য – এরকম সময় চাকরিটা তো হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান। তা–ও বলেছিল, “এরকম একটা হাসপাতালে পোস্টিং হবে, ভাবতেই পারিনি রে।” পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে নার্সের এনে দেওয়া চা খেতে খেতে সপ্তকও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলেন হেলথ–সেন্টারের বিল্ডিং–টার দিকে। ভাবছিলেন, নিজের কথা। ডাক্তার বাবা–মায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতার কল্যাণে ওঁকে বিদেশযাত্রা নিয়ে ভাবতে হবে না, তবু ভাবছিলেন, এখানে থাকতে পারলে কী ভালোই না হত।
সমস্যা সত্যিই হয়েছিল প্রতিমের থাকার জায়গা নিয়ে। ফুলপুকুর পি–এইচ–সি–তে তিনটে কোয়ার্টার। একটা ডাক্তারের, একটা নার্সের, আর একটা ফার্মাসিস্টের। বহুদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তিনটিরই খুব ভগ্নদশা। কোনওটাই সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য নয়। তার মধ্যে ফার্মাসিস্টের কোয়ার্টারটা একেবারেই অব্যবহার্য। ফলে – বিশেষ করে সাড়ে তিন দশক ধরে ডাক্তার না থাকার দরুণ – ফার্মাসিস্টরাই ডাক্তারের কোয়ার্টারে থাকে। তখন যে ফার্মাসিস্ট ছিল, সে কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল, “আপনারা এখানেই থাকুন।” দরজা খুলে পালিয়েছিল, বিকেলে চা এনে দিয়েছিল, রাতের খাবার এনে দিয়েছিল থালায় করে, কিন্তু তারপর আর দেখা পাওয়া যায়নি। প্রতিম অনেক রাত অবধি বসেছিল। বলেছিল, “বিছানা তো একটাই। আমরা এখানে শুয়ে পড়লে ছেলেটা শোবে কোথায়?” সপ্তক হেসে বলেছিলেন, “তুই একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেলি। ও শোবে নার্সের কোয়ার্টারে। রোজই হয়ত শোয়। বালিশটা একেবারেই নতুন, দেখ। প্রায় ব্যবহারই হয়নি।”
পরদিন ভোর ভোর এসেছিলেন গ্রাম–প্রধান। বলেছিলেন, “ডাক্তারবাবু, কোয়াটারটাই বড়ো সমস্যা। এজন্যিই ডাক্তার থাকতে চায় না। দেখুন, এই তো কোয়াটারের ছিরি। নামেই ডাক্তারের কোয়াটার। চারটে ঘরের দুটো কোনওক্রমে ব্যবহারযোগ্য। এখানে থাকতে পারবেন না। গাঁয়েই থাকতে হবে। মনে যদি কিছু না করেন, অধমের বাড়িতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করি – যতদিন না সরকারীভাবে কিছু হয়?”
প্রধান চলে যাবার পরে এসেছিল ফার্মাসিস্ট ছেলেটা। ওর নাম এখন আর মনে নেই সপ্তকের। বলেছিল, “কী বললেন, প্রধান?” শুনে চোখ কপালে তুলে বলেছিল, “আপনি ওনার বাড়িতে থাকবেন? মুসলমান তো?” প্রতিম অবাক হয়ে বলেছিল, “তাতে কী হবে? আমি যদি বলি আমি এই কোয়ার্টারে থাকব, তাহলে আপনি কোথায় যাবেন?” ছেলেটা মানেনি। বলেছিল, “তা বলে মুসলমানের বাড়িতে? খাওয়া–দাওয়ার কী হবে?” সপ্তক বলেছিলেন, “সে কিছু ব্যবস্থা একটা হবে’খন। দরকার হলে মুসলমানের বাড়ির খাবারই খেতে হবে। ভালো ভালো মাংস, কালিয়া, পোলাও, বিরিয়ানি, গোস্ত–টোস্ত হবে, কী বলেন? এখন তো অত বন্দোবস্ত করে, জমি কিনে, বাড়ি বানিয়ে তবে ডাক্তারবাবু এসে থাকতে পারবেন না, তাই।”
ছেলেটা কিছু একটা বলতে গিয়েও না–বলে চলে গেছিল। পরে দু–বন্ধু মিলে গ্রামপ্রধানকে বলে এসেছিলেন যে প্রতিম এসে প্রধানের বাড়িতেই উঠবে। যতদিন না সমস্ত ব্যবস্থা করে আসছে, ততদিন কি ওর সুটকেস–দুটো আর হোল্ড–অল–টা প্রধানের বাড়িতে রেখে যেতে পারে?
প্রধান খুশি হয়ে রাজি হয়েছিলেন।
প্রতিম যেদিন জয়েন করার জন্য রওয়ানা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়নি। সপ্তকের ভিসা ইন্টারভিউ ছিল। সকালে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, সন্ধেবেলা মেসেজ করেছিলেন। সে মেসেজ ডেলিভারি হয়নি। সপ্তক আন্দাজ করেছিলেন ব্লক প্রাইমারি পৌঁছে গেছে প্রতিম। আগেরবারই খেয়াল করেছিলেন, ওখান থেকেই সিগন্যাল ক্ষীণ হতে থাকে। ফুলপুকুরে কোনও সিগন্যালই ছিল না।
বিলেত থেকে চিঠি লেখালেখি হত। প্রথম দিকে প্রতিমের সব খবরই পেয়েছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে মায়ের মৃত্যু, তারপরে দিদির বিয়ে হতে না হতে সেখানেও বিপর্যয়, বছর ঘুরতে না ঘুরতে বাবার চলে যাওয়া… সবই জানেন। তারপর যোগাযোগ কমতে থাকে। শেষে সপ্তকের পক্ষ থেকে বছরে একটা গ্রিটিং কার্ড এবং প্রতিমের তরফ থেকে কিছুই–না… কতদিন লেগেছিল? বছর পাঁচ–ছয়েক? ইমেইল–এর যুগে কাগজে কলমে চিঠি লেখা, নিয়ে গিয়ে লেটারবক্সে পোস্ট করা – এ সবের সময় কোথায়?
~তিন~
এবারে নৌকোয় যেতে হল না। সম্পূর্ণ নতুন পথে এলেন গাড়িতে। ফুলপুকুর অবধি জিপ চললেও গাড়ি এখনও যায় না, তাই শেষ প্রায় একঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হল ভ্যান রিকশায়।
ভ্যানচালক ছেলেটার সঙ্গে আলাপচারিতা জমে উঠল চট করে। জানলেন, ডাক্তারবাবু খুব ভালো। আগের ডাক্তারদের মতো চলে যেতে চেয়ে দরখাস্ত করেননি। রোজ মন দিয়ে কাজ করেছেন নিয়মমাফিক। ছুটিও নেন না, কথায় কথায় বাড়িও যান না। দুবেলা আউটডোর করেন, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছেন, অপারেশন করেন না বটে, কিন্তু তাতে কী…
একাই থাকেন… না, কোয়ার্টার নেই। দুটো কোয়ার্টার সরকার সারিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু ওই একটা, যেটার কী না খুবই ভগ্নদশা ছিল, সেটার কিছু করা হয়নি। ডাক্তারবাবুই বারণ করেছেন, ফলে কম্পাউন্ডার এখনও ডাক্তারের কোয়ার্টারেই থাকেন, আর ডাক্তারবাবু থাকেন গ্রামে। না, না, প্রধানের বাড়িতে নয়। মানে, প্রধানেরই বাড়ি বটে, তবে গ্রাম–প্রধানের আর একটা বাড়ি আছে, খালি। সেটাতে এখন থাকেন ডাক্তারবাবু। লোকে বলে প্রধান সে বাড়ি ডাক্তারবাবুকে লেখাপড়া করে দিয়েছেন। তবে ডাক্তারবাবু টাকা দিয়ে কিনেছেন কি না তা অবশ্য…
রিকশাচালক বলে চলল, “আসলে সে বাড়ি পোধান বেচতেও পারতেননিকো। ফলে দিয়ে দিয়েই ভালো করেছেন।”
সপ্তক জিজ্ঞেস করলেন, “বেচতে পারবেন না কেন? ভালো বাড়ি না?”
একটু থতমত খেল যেন রিকশাচালক ছেলেটা। বলল, “না… বাড়ি খারাপ না… কিন্তু এ–গাঁয়ে অমন বাড়ি কেনার লোক কই? ওই যে, ওই দেখা যায়, হাসপাতাল। দ্যাখেন, আমাদের হাসপাতাল কেমন সুন্দর!”
আগের বারে হাসপাতাল প্রথম দেখেছিলেন অন্য দিক থেকে। দুপুরের গনগনে সূর্য ছিল পেছনে, হাসপাতাল উজ্জ্বল ছিল অনেক। আজ শীতের বেলা, সূর্য অনেক নরম, আর সপ্তকের সামনে থেকে এসে পড়েছে। হাত তুলে চোখ আড়াল করলেন সপ্তক। একই রকম রয়েছে। সেই লাল দেওয়াল, সেই রোদের আলোয় উজ্জ্বল সোনালী পুকুর… ভ্যানওয়ালা প্যাডেল করা থামিয়ে ভ্যানটা গড়াতে দিয়ে বলল, “ডাক্তারবাবু আছেন কি হাসপাতালে? এতক্ষণে তো শেষ করে বাড়ি যাওয়ার কথা…” বলতে বলতে আবার প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, “নাঃ, বাড়ি গেছেন। চলুন বাড়িই নিয়ে যাই আপনাকে…”
সপ্তক বললেন, “আরে, এখান থেকেই বুঝে গেলে ডাক্তারবাবু নেই? কতো তো লোক।”
মাথা নেড়ে ছেলেটা বলল, “সাইকেল নেই যে! হাসপাতালে সারাক্ষণ লোক থাকে। এস্টাপ, পেশেন্… ভর্তি হয় না, সরকার বেড চালু করেনি। বলেছে তাহলে কমপক্ষে তিনজন ডাক্তার চাই। পাড়াগাঁয়ে কেউ আসতেই চায় না এখনও। কিন্তু পেশেন দেরি করে আসলে ফিরতে পারে না – থেকে যায় ওখানেই, দাওয়ায় শোয়, বা উলটো দিকের চায়ের দোকানগুলোর একটাতে।”
হাসপাতালের চৌহদ্দি পেরোনোর আগে হাত তুলে দেখাল, “ওই দ্যাখেন, কলাগাছগুলোর সামনে, ওই ভাঙাটাই কোয়াটার, যেটা সারানো হয়নিকো।”
ভ্যানরিকশা এসে থামল একটা বেশ বড়ো বাড়ির সামনে। চালক বলল, “দ্যাখেন। ডাক্তারবাবুর সাইকেল।” বাড়িটা গ্রামের অন্যান্য বাড়ির মতো মাটির না। ইঁটের। সপ্তকের মনে পড়ল আবছা, আগের বারে দেখেছিলেন প্রধানের বাড়িও মাটির ছিল। গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়ি ছিল পি–এইচ–সি আর কোয়ার্টারগুলো।
একটা কাঁটাতারের বেড়ায় একটা বাখারির গেট। তার সামনে কালভার্টে বসে থাকা ছেলেটাকে ভ্যানওয়ালা বলল, “সাকিম, যা রে ডাক্তারবাবুরে ক’, বন্ধুলোক এয়েচেন শহর থেকে।”
রিকশাভাড়া দিয়ে সপ্তক গেট দিয়ে ঢুকে দেখলেন সাকিম সিঁড়ির নিচেই দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় ওঠেনি। কেন? কাজের লোক বলে? পা চালিয়ে যেতে গিয়ে খেয়াল করলেন সাকিম হাত বাড়িয়ে থামতে বলছে। একটু থতমত খেয়ে বললেন, “কী হল?”
ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, “ডাক্তারবাবু সাড়া দেননি। ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু, বলি আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে এয়েছেন।”
সাড়া দেননি? তাতে কী? বললেন, “আরে, দরজায় কড়া নেড়েছ?”
আবার মাথা নাড়ল সাকিম। বলল, “দরজা খোলা। খোলা থাকলে বারান্দায় উঠে উঁকি দেওয়া বারণ…”
ছোটোবেলার বন্ধুর বাড়িতে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে? বিরক্ত হয়ে ভাবছেন সাকিমকে ঠেলে ঢুকে পড়বেন, এমন সময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রতিম।
প্রতিমকে দেখে সপ্তক এমনই থমকে গেলেন, যে কিছুই বলতে পারলেন না। প্রতিম কখনওই মোটাসোটা ছিল না। বরং বন্ধুরা ওর রোগা চেহারা নিয়ে মজা করত, বলত, “ম্যালনারিশড!” সেই প্রতিমের চেহারা এখন বেশ খোলতাই। এমনকি গালদুটোও গোলগাল। এবং গেঞ্জির নিচ থেকে যে ভুঁড়িটা ঠেলে বেরোচ্ছে, সেটা নেয়াপাতির চেয়েও বড়ো।
প্রতিমও বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে একবার অস্ফূটে, “সপ্তক…” বলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। জড়িয়ে ধরে দম বন্ধ করে দিয়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে একাকার! খালি বলে, “বিশ্বাসই করতে পারছি না… বিশ্বাসই করতে পারছি না… তুই সত্যি এসেছিস? এত বছর পরে শেষে মনে পড়ল…? চিঠিও তো লিখিস না…”
কোনও রকমে হাত ছাড়িয়ে সপ্তক বললেন, “ব্যাটা, আমার মনে পড়ার কথা বলছিস, নিজে কটা চিঠির উত্তর দিয়েছিস? লিখিস তো না–ই, উত্তরও দিস না। শেষে ভাবলাম, হয়ত ট্রানসফার হয়ে গেছিস…”
একটু বোকা–বোকা হেসে প্রতিম বলল, “আরে, আগে ভেতরে তো আয়…”
ছোটো মতো ঘর। একটা টেবিল, আর চারটে চেয়ার। গার্ডেন চেয়ারের মতো, র’ট আয়রণের ফ্রেমে প্লাস্টিকের বেত লাগানো। এক কোণে একটা কাঠের পড়ার টেবিল–চেয়ার। একটা বই খোলা। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।
“বোস, আমি চা নিয়ে আসছি… চা হয়ে গেছে। আমিও এক্ষুনি খেতাম।”
প্রতিম চলে গেল ভেতরের দরজার পর্দার আড়ালে। সপ্তক টেবিলে খোলা বইটা উঁকি দিয়ে দেখলেন। হ্যারিসন। এটাই কি… হ্যাঁ। তাই তো! এই এডিশনটাই ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন ওঁরা। সপ্তক ষোলো বছরের পুরোনো বই–ই পড়ছে। কেন? নতুন পায়নি, না কি কেনার ক্ষমতা নেই? যা জানেন সপ্তক, তাতে দ্বিতীয়টা হবার কথা নয়। কিন্তু…
পরে জিজ্ঞেস করবেন। বইটা যেখানে খোলা ছিল সেখানেই খুলে রেখে ঘুরে দেখলেন বেতের টেবিলে একটা ট্রে, তাতে ধোঁয়া ওঠা দু–কাপ চা, আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট। কখন রেখে গেল প্রতিম? না কি আগে থেকেই ছিল? তাহলে বাড়িতে আর কেউ রয়েছে…
ভাবতে ভাবতে প্রতিম ঢুকল। হাতে একটা পিরিচের ওপর আর একটা ধূমায়িত চায়ের কাপ। “নে,” বলে বাড়িয়ে দিল সপ্তকের দিকে। “বোস। দাঁড়িয়ে কেন?”
সপ্তক কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, “ওখানেই তো দু–কাপ চা রয়েছে…”
প্রতিম যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, “ওহ, ওটা… ওটা…” হাত বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে থমকে বলল, “নাহ্, থাক…”
তারপরে চেয়ারে বসে বলল, “আমি এ ঘরে বিকেলের চা–টা খাই। বাইরেটা দেখা যায় জানলা দিয়ে। ওদিকটায় নদী। আগেরবারে যে নদী দিয়ে আমরা এসেছিলাম… মনে আছে?”
চায়ে চুমুক দিয়ে সপ্তক তাকালেন জানলা দিয়ে। নদী দেখা যায় না। বললেন, “মনে আছে। তুই আর এখান থেকে ফিরিসনি কেন? শুনলাম তুই ট্রানসফারও ডিক্লাইন করেছিস…”
প্রতিম মাথা নাড়ল। বলল, “কী করব ট্রানসফার নিয়ে? আমার তো ফেরার দরকার নেই। বাবা–মা নেই। দিদি–র খবর জানিস, তোকে লিখেছি।”
“হ্যাঁ। মনে আছে। কেমন আছে টুনিদি?”
মাথা নাড়ল প্রতিম। “কোনও খবর নেই। সেই যে জামাইবাবু লিখেছিল, ‘তোমার দিদি আমাকে জানাতে বলেছে যে তুমি ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবে না,’ সেই শেষ। বিশ্বাস করবি না, কটা চিঠি আমি লিখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। শেষ অনেকগুলো চিঠি না–খোলা ফিরে এল। তারপরে কবে আমিও লেখা বন্ধ করে দিয়েছি।”
প্রতিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে সপ্তক দেখলেন একটা খোলা জুতোর বাক্স ঘরের দরজার আড়ালে একটা র্যাকের নিচের তাকের কোণায় পড়ে রয়েছে। তাতে অজস্র চিঠি। মাথা ফেরাতে যাচ্ছিলেন, কী চোখে পড়ল, আর একবার তাকালেন জুতোর বাক্সটার দিকে। তারপরে ফিরলেন প্রতিমের দিকে।
প্রতিম ট্রেতে রাখা বিস্কুটের প্লেটটা দেখিয়ে বলল, “বিস্কুট নে।”
বিস্কুটের দিকে হাত বাড়িয়ে সপ্তক এমন চমক খেলেন যে হাতে ধরা কাপ থেকে চা প্রায় চলকে পড়ে গিয়েছিল। প্রতিম ট্রে–র দুটো কাপের মধ্যে একটা কাপ তুলে নিয়েছিল। সেটা ওর হাতেই রয়েছে, কিন্তু পাশের কাপটা যেটা এখনও ট্রের ওপরেই রয়েছে, সেটার চা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে!
প্রতিম কি দুটো কাপ থেকেই চা খেয়েছে? কেন? একা থেকে থেকে মানুষ খামখেয়ালী হয়ে যায় যেমন? যেমন পনেরো–ষোলো বছর পুরোনো বই পড়ছে? সপ্তক জানতে চাইলেন, “তুই ওই আদ্যিকালের হ্যারিসন পড়ছিস কেন?”
তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রতিম বলল, “এর বেশি লাগে না। আমিও খুব বিরাট ডাক্তারি কিছু করি না। কেস গোলমেলে হলে রেফার করে দিই। আগে যাতায়াত করতে অনেক সময় লাগত। আজকাল অত লাগেও না। তবে সার্জারির কেস হলে প্রবলেম হয় এখনও। আগে সুবিধা ছিল – নীল ছিল বেলডাঙায়। নীলকে মনে আছে? কানিংহ্যাম স্কলারশিপ পেয়েছিল, ডিসেকশনে? নীল ওখানে কী দারুণ দারুণ সার্জারি করেছে জানলে তুই অবাক হয়ে যাবি। জানিস? ও। তখন এখান থেকে বেলডাঙা নৌকোয় লাগত ছ’ঘণ্টা। তা–ও আমি পাঠিয়ে দিতাম। এখন রাস্তা হয়ে গেছে। আড়াই ঘণ্টায় যাওয়া যায়। কিন্তু এখন নীল আর বেলডাঙায় নেই। যাক গে… লাগে গাইনেকলজির বই। সেগুলো সব নতুন আছে। ও ঘরে।” হাতে ধরা কাপ দিয়েই দেখাল ভেতর দিকে। সপ্তকের গাইনেকলজিতে ইন্টারেস্ট নেই। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিলেন। প্রতিমও চা শেষ করে বলল, “দে কাপটা। সুটকেসে কী কী এনেছিস? পাজামা–টাজামা এনেছিস? না–হলে আমার একটা নিবি।”
সপ্তক পাজামা, তোয়ালে সবই এনেছেন। প্রতিম বলল, “দাঁড়া, বোস… আসছি।” ট্রে হাতে ভেতরে চলে গেল। সপ্তক স্থানুর মতো বসে রইলেন। প্রতিম ট্রে–টা তোলার সময় দেখতে পেয়েছেন, তাতে তৃতীয় কাপটাও খালি। কখন হল? অর্ধেক হবার পরে সপ্তক নজর রেখেছিলেন। প্রতিমকে সে কাপে হাত দিতে দেখেননি। কখন খেল?
এবারে প্রতিমের ফিরতে বেশি সময় লাগল। ততক্ষনে বাইরের আলো নিভে এসেছে। প্রতিম এসে একটা সুইচ টিপল। আলো জ্বলে উঠল সপ্তকের মাথার পেছনে। বললেন, “আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না।”
প্রতিম বলল, “এখনও নেই। এ গ্রামে সব সোলার ল্যাম্প। হাসপাতালেও। এটা প্রধানের বাড়ি। মনে আছে, সেই প্রধান – যিনি আমাকে বলেছিলেন ওনার বাড়িতে থাকতে?”
মনে আছে। “উনি আছেন এখনও?”
প্রতিম বলল, “অতিবৃদ্ধ, তবে আছেন। এবং এখনও গ্রামপ্রধান। লোকে মান্য করে খুব।”
“তুই বাড়িটা কিনে নিয়েছিস?”
মাথা নাড়ল প্রতিম। “না। বিক্রি করেননি, তবে বলেছেন, আমি যতদিন গ্রামে আছি, ততদিন থাকতে পারি।”
“বলেছেন?” ভুরু তুলে জানতে চাইলেন সপ্তক।
“বলেছেন। এবং ওঁর ছেলেরাও রাজি। ভেতরে চল।” কথা বলতে বলতে প্রতিম সপ্তকের বাক্সটা দেওয়ালের পাশ থেকে তুলে ভেতরে গেছে। সপ্তকও গেছেন পেছনে। ঢুকেই একটা ড্রয়িং রুম। চমকে থামলেন সপ্তক। চমৎকার সোফা সেট, দারুণ কার্পেট, দেওয়ালে আয়না, সাইডবোর্ড! এটা গ্রামের বাড়ি? প্রায় রাজপ্রাসাদের মতো। তারপরে খাবার ঘর। সুন্দর করে গোছানো, সবই মুসলমানী কায়দায়। দরজার ওপরে দেওয়ালে লাগানো কার্পেটে উর্দু, বা আরবি লেখা, দেওয়াল–সজ্জা, সোফার ওপরের ঢাকনা, মেঝের কার্পেট…
প্রতিম একটা দরজা দেখিয়ে বলল, “ওটা আমার শোবার ঘর। আর এটাতে তুই শুবি। আয়।”
একটা বড়ো, উঁচু খাট, মশারী খাটানো। অনেক ট্রাঙ্ক, তোরঙ্গর ভীড়। কিন্তু বন্ধ ঘরের ড্যাম্প গন্ধ নেই। বরং একটা হালকা আতরের গন্ধ। একটা নিচু টেবিলে সপ্তকের বাক্সটা রেখে প্রতিম বলল, “চেঞ্জ করে নে। আমি বসার ঘরে আছি। হাত মুখ ধুতে হলে এবাড়িতে অ্যাটাচড টয়লেট নেই। রানিং ওয়াটারও না। এই যে, খাটের রেলিঙে দেখ, তোয়ালে।”
সপ্তক বললেন, “এখনই পাজামা পরে নেব? একটু বেরোব না?”
অবাক হয়ে প্রতিম বলল, “বেরোবি? কোথায় বেরোবি অন্ধকারে?”
সপ্তক বোকার মতো হেসে বললেন, “আরে, কোথায় আর যাব? ভেবেছিলাম তোর পি–এইচ–সি দেখব। ওই পুকুরটার পাড়ে বসে চা খাব… সেই সেবারের মতো।”
প্রতিম হাসল, বলল, “কাল সকালে দেখিস। তবে মজা পাবি না। এখন হাসপাতাল আর অত ফাঁকা ফাঁকা নেই। রাত–দিন লোক থাকে। ঘাটটাও অত পরিষ্কার নয়। লোকে চান–টান করে, কাপড় কাচে… গ্রামের লোকও আসে – ওই সামনের দোকান–টোকানের লোকজন। যদিও বাসন মাজা বারণ করে দিয়েছি, তবু… এখন পাজামা পরে নে, কাল বেড়াবি। সক্কাল সক্কাল।”
বাক্স খুলে সপ্তক একটা কাগজে মোড়া বোতল বের করে বললেন, “তোর জন্য একটা ভালো হুইস্কি এনেছি। সিংগ্ল মল্ট… হস্টেলের ঘরে বসে সস্তা হুইস্কি খাওয়ার কথা মনে আছে?”
প্রতিম শুকনো মুখে বলল, “তুই নিয়মিত মদ খাস?”
নিয়মিত? ব্রিটেনে তো মদ খাওয়াটা নিয়মের পর্যায়ে পড়ে! কিন্তু প্রতিমের মুখ দেখে থতমত খেয়ে বললেন, “তুই ছেড়ে দিয়েছিস?”
প্রতিম বলল, “আসলে গ্রামটা মুসলমান প্রধান। তা বলে মদ খায় না কেউ তা নয়, তবে ভদ্রলোকে খায় না। আর তাছাড়া…” বলে একটু থেমে বলল, “আমাকে বাড়িতে থাকতে দেওয়ার আগে ওরা বলে দিয়েছিল, মদ যেন না ঢোকে…”
আরও অপ্রস্তুত সপ্তক বোতলটা আবার বাক্সে ঢুকিয়ে বললেন, “এটা যে এসে গেল…”
“সে ঠিক আছে, না খুললেই হল। তুই পাজামা পরে নে…”
~চার~
“রান্না করে কে? লোক আছে?”
অনেকক্ষণ আড্ডা হয়েছে। মাঝে সপ্তকের জোরাজুরিতেই দুজনে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরেও এসেছেন। অনেক বছরের গল্প করতে হয়েছে। সপ্তকের গল্পই বেশি। বিলেত, পড়াশোনা, বিয়ে, সংসার, বিবাহ বিচ্ছেদ, একমাত্র ছেলের দূরে চলে যাওয়া… সে তুলনায় প্রতিমের কথা কম। সবটাই সপ্তকের জানা–ও বটে। মা–বাবা মারা যাবার পরে, দিদির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর কিছুই নেই। ডাক্তারি, আর রিটায়ার্মেন্টের অপেক্ষা। রিটায়ার করার পরেও এখানেই থাকবে। এ গ্রামে ডাক্তার আসবে না। ও বাড়িতে বসেই ডাক্তারি করবে। “বাইরের ঘরটা, যেখানে চা খেলি, সেখানে যদি চেম্বার বানাই? চলবে না? খুব চলবে।”
হয়ত। কিন্তু সপ্তকের একটা অন্য চিন্তা শুরু হয়েছে। বাড়িতে যদি আর কেউ না থাকে, রাতের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে? প্রতিম তো উচ্চবাচ্য করছে না… শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন…
“রান্না করে কে? লোক আছে?”
মাথা নাড়ল প্রতিম। বলল, “নাহ, এ গাঁ–দেশে রান্না করতে পারে না লোকে। বাড়িতে যা খায় তা–ই রেঁধে দিয়ে যায়। সে মুখে তোলা যায় না। তাই আমি, মানে নিজেই ব্যবস্থা করে নিই আরকি!”
কী ব্যবস্থা করে? রাত্তির আটটা বেজে গেছে। কখন ব্যবস্থা করে? ভাবছেন কী জিজ্ঞেস করবেন, আর ওদিকে প্রতিম নানা গল্প করেই চলেছে, এমন সময় বাইরে থেকে একটা গলা এল, “ডাক্তারবাবু?”
প্রতিম কথা থামিয়ে বলল, “কে রে? সাকিম? আয়।”
দরজায় দাঁড়াল সাকিম। “ডাক্তারবাবু, একটা কেস এসেছে… মানে দুটো। রোডের ওপর বাইক উলটে চোট লেগেছে।”
“সিরিয়াস?” চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল প্রতিম।
“একজনের টিচ লাগবে,” নিজের কপালের দিকে আঙুল তুলে বলল সাকিম। “আর কিছু ডেসিং। সেটা আমি পারব। কিন্তু অন্যজনের মনে হচ্ছে কাঁধের হাড় ভেঙেছে…”
“তুই গিয়ে ড্রেসিং শুরু কর। আমি এসে স্টিচ করছি,” বলে সপ্তকের দিকে ফিরে প্রতিম বলল, “তুই কি আসবি? অবশ্য করার কিছু থাকবে না।”
গেঞ্জি এবং পাজামার ওপরে ড্রেসিং গাউন পরিহিত অবস্থায় সপ্তক প্রাণ গেলেও কোনও হাসপাতালেই যাবেন না। মাথা নাড়লেন। বললেন, “আমার জন্য চিন্তা করিস না…” মাথায় একটা চিন্তা অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে…
প্রতিম যাবার পরে বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ ওর সাইকেলের আলো মিলিয়ে যাওয়া দেখে সপ্তক ভেতরে এলেন। মাথায় যে আইডিয়াটা ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা হল এই – এ বাড়িতে একটা মহিলা–উপস্থিতি আছে। প্রথমে বোঝেননি। কিন্তু ক্রমেই সেটা পরিষ্কার হচ্ছে। প্রতিম বেশ অগোছালো মানুষ। এটা দেখাচ্ছে – সেটা সেখানেই পড়ে থাকছে। ওটা আনছে – ধরে টানা মাত্র হুড়মুড়িয়ে আরও সাতটা জিনিস পড়ে যাচ্ছে। আলমারি খুলছে, দরজা খোলা–ই থেকে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে সপ্তক জানেন, যে এরকম হলে সাত দিনে বাড়িটা নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। জায়গার জিনিস জায়গায় রাখা, কিছু বের করে আনলে সেটা তক্ষুনি গুছিয়ে রাখা, এগুলো একটা ডিসিপ্লিনের অঙ্গ, যেটা প্রতিমের কোনও দিনই ছিল না। ওর মা রাগারাগি করতেন। স্কুল জীবন থেকেই নাকি পড়ার টেবিল থাকত ঢিবি হয়ে। সপ্তকও অবাক হতেন, কী করে ওরই মধ্যে পড়াশোনা করত। আজও একই দশা। হ্যারিসনটা এখনও বাইরের ঘরে ওই খোলা অবস্থাতেই রয়েছে। এই মাত্র জুতো বের করতে গিয়ে দুটো আলাদা জোড়ার এক পাটি করে জুতোর বাক্সের বাইরে ফেলে রেখে গেল – সে–ও বোঝা–ই যাচ্ছে, পুরোনো, ছেঁড়া জুতো। ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। কী একটা গিঁট খুলতে না পেরে রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসে, ওটাকে সোফার হাতলেই রেখে দিয়েছিল, সপ্তক বলাতে সেন্টার টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখল।
অর্থাৎ, প্রতিমের পেছনে পেছনে কেউ বাড়িটাকে সাজাতে সাজাতে, গোছাতে গোছাতে ফেরে, আর সপ্তকের ধারণা হয়েছে তিনি একজন মহিলা। ঘরে আতরের গন্ধটায়ও একটা মেয়েলি ভাব ছিল।
বাড়িটা বড়ো। কিন্তু ঘরের সংখ্যা বেশি না। বাইরের ঘরের পরে বসার ঘর, খাবার ঘর, প্রতিমের শোবার ঘর, ও–পাশে যে ঘরে সপ্তক ঘুমোবে সেটা… প্রতিমের ঘরের পরে আর একটা ঘর কি আছে?
ঘরগুলোতে সোলার ল্যাম্প জ্বলছে। তা–ও, খানিকটা বাড়িটার বানানোর ঢঙে, খানিকটা কম পাওয়ারের এল–ই–ডি আলোর রোশনাইয়ের অভাবে আলোর সামনেটা যত উজ্জ্বল, একটু দূরেই আর অতটা নয়। সপ্তক সন্ধে থেকে টর্চটা হাতের কাছে রেখেছিলেন। সেটাই নিয়ে নিলেন। প্রথমে ঠিক করলেন প্রতিমের ঘরটাই দেখবেন। প্রতিম একবারও ‘বাড়িটা দেখে যা’, ‘এটা আমার শোবার ঘর, আয়’ – এ ধরণের কথা বলেনি।
সব দরজাতেই ভারি পর্দা। এরকম পর্দা সাধারণ বাড়িতে দেখা যায় না। যদিও জানেন ঘরে কেউ নেই, তবুও দরজার বাইরে গলা খাঁকরে একটু অপেক্ষা করে ঢুকলেন। আসবাবের আধিক্য। সপ্তকের ঘরের খাটের চেয়েও বেশি ভারি, বড়ো, উঁচু খাট। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক, তোরঙ্গ…
সব আলমারিই তালাবন্ধ। চাবি নিশ্চয়ই কোথাও আছে? এ ঘরে তিনটে, সপ্তকের ঘরে তিনটে, বসার ঘরে একটা – সবশুদ্ধ সাতটা আলমারির সব চাবি, সেই সঙ্গে বাড়ির চাবি – প্রতিম নিশ্চয়ই সারাক্ষণ পকেটে নিয়ে ঘোরে না? বালিশের নিচে? হাত দিতে অস্বস্তি হল। শুধু প্রতিমের প্রাইভেসি বিঘ্নিত হবে বলে নয়, অত টানটান করে চাদর আবার ঠিক করে রাখতে পারবেন কি না জানেন না।
ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে?
একটা ড্রয়ার খুললেন। অজস্র প্রসাধন–সামগ্রী। সবই মহিলার। নেল পালিশ, লিপস্টিক, মাস্কারা, কী নেই! প্রথমে থতমত খেয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চারিদিকে তাকিয়েছিলেন চমকে। তারপরে আবার খুললেন। বের করলেন লিপস্টিক, কয়েকটা নেল পালিশ… সবই পুরোনো। নেল পালিশগুলো সব শুকনো। একটা লিপস্টিকের ঢাকনা খুলতে ভেতর থেকে মাথাটা ভেঙে পড়ে গেল। তুলতে গিয়ে আরও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেগুলোকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে আবার সব রেখে দিলেন ড্রয়ারে। সবই কেমন অনেক পুরোনো। অনেক বছরের পুরোনো।
ড্রেসিং টেবিলের ওপরে চারটে চিরুনী। একটা কাঠের স্ট্যান্ডে তিনটে – সুদৃশ্য, মেয়েলি। আর পাশে পড়ে আছে একটা হাতলওয়ালা, দাঁতভাঙা – যেটা নিশ্চয়ই প্রতিমের। অন্য তিনটে চিরুনী কি ব্যবহার হয়? চুল–টুল কিছু লেগে নেই। সাফসুতরো পরিষ্কার। তাতে অব্যবহৃত বোঝায় না। বাড়ির সব কিছুই সাফসুতরো পরিষ্কার।
প্রতিমের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গোয়েন্দাগিরি করতে আসেননি। আলমারি না খুললেও চলবে। নিজের ঘরটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু প্রতিমের ঘরের পরে আর একটা ঘর আছে কি? করিডোরটা অন্ধকার মতো। টর্চটা জ্বালাতেই দেখতে পেলেন। করিডোরের শেষে দরজা। বন্ধ। তালা দেওয়া। তবু পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে। তালাটা পুরোনো। নদীতটবর্তী গ্রামের জলো হাওয়ায় মর্চে পড়েছে। অনেকদিন খোলাও হয়নি। হুড়কোটারও একই অবস্থা।
দরজাটা আঙুল দিয়ে আলতো করে ঠেলে বুঝলেন, ফাঁকও হবে না। ভেতরটা দেখার জো নেই। ফিরলেন। খাবার ঘরের পেছনের দেওয়ালে ছিটকিনি বন্ধ দরজা। এর বাইরেই বিকেলে দেখেছেন টিউবওয়েল। এ বাড়ির জলের সোর্স। পাশে রান্নাঘরের দরজা। তারও শিকল তোলা। শিকল খুলে ঢুকলেন সপ্তক। ধোয়ামোছা পরিষ্কার। কোণের উনুনটাও পরিষ্কার। খাবারদাবারের চিহ্নমাত্র নেই। আবার চিন্তাটা ফিরে এল। খাবে কী প্রতিম? সপ্তককেও খাওয়াবে কী? ঘড়িতে সাড়ে আটটা। তেমন দেরি হয়নি। একটা ছোটো গ্যাসের সিলিন্ডার রয়েছে। মাথায় বার্নার লাগানো। এমন ব্যবস্থা আগে দেখেননি সপ্তক। এতে ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ করতে দেরি হবার কথা নয়।
দরজা বন্ধ করতে গিয়ে মনে হল, চাল–ডাল–আলুই বা কোথায়? রান্নাঘরেই থাকার কথা নয় কি? আবার দরজা খুললেন। কই, কিছু তো নেই… রান্নাঘরের তাকগুলো একেবারে খালি। তাতে চাল–ডাল দূরের কথা, মশলা, বা নুনটাও নেই। রান্না করে কি প্রতিম? না কি শুধুই চা বিস্কুট? কিন্তু সে চা–বিস্কুটও তো থাকতে হবে কোথাও?
খাবার ঘরে একটা সাইডবোর্ডে অনেক থালা–বাটি–গেলাস, আর কাপ ডিস। বিকেলে এতেই চা খেয়েছেন? তাহলে ধুয়ে রাখল কে? হয়ত যেগুলোতে খেয়েছেন, সেগুলো ধোয়া হয়নি এখনও। কোথাও আছে – রান্নাঘরে নয়, হয়ত বাইরের কলতলায়… রান্নার লোক নেই বলেছে প্রতিম। ঘরের কাজ করার লোক নিশ্চয়ই আছে? এত বড়ো বাড়ির সব ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা, ধুলো ঝাড়া নিশ্চয়ই সপ্তক করে না?
পেছনের দরজা খুললেন। দরজার পাশে একটা আলোর সুইচ। জ্বালালেন। বাইরের দেওয়ালে আলো জ্বলল। এটা আরও কম উজ্জ্বল। তার ওপর খোলা জায়গা বলে আলোটা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। টিউবওয়েলটুকু দেখা যাচ্ছে।
বিফলমনোরথ হয়ে পেছনের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে, ফিরে এলেন বসার ঘরে। প্রতিমকে জিজ্ঞেস করতে হবে বাড়ির রহস্য। কিন্তু প্রতিম এখনও অবধি বাড়ির কোনও কথাই বলেনি। সপ্তকের প্রশ্নের উত্তর না–দেবারই চেষ্টা করেছে।
আর একটা জিনিস দেখতে হবে। চিঠিগুলোর বাক্সটা। সপ্তক বাইরের দিকে দেখলেন। না, কোনও টর্চ বা সাইকেলের আলো এদিকে আসছে না। বাক্সটা ঘাঁটতে শুরু করলেন। অনেকগুলো চিঠি প্রতিমের। দিদিকে লেখা। টুনিদির উত্তর এই বাক্সে নেই। শুধু তাই নয়, যা ভেবেছিলেন – সপ্তকের লেখা তিনটে চিঠি আর ছটা গ্রিটিং কার্ড–ও খাম না–খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। খামের ওপর মোহরের ছাপ ভারতীয় ডাকেরগুলো অস্পষ্ট হলেও, ব্রিটেনেরগুলো সহজেই পড়া যায়। সবচেয়ে পুরোনো চিঠি এবং কার্ড দুই–ই ন’ বছরের পুরোনো। আর সবচেয়ে নতুন গ্রিটিং কার্ডটা তিন বছরের। এর পরেই সপ্তক কার্ড পাঠানো বন্ধ করেন। চিঠি বন্ধ হয়েছিল তার অনেক আগেই।
কেন সপ্তকের চিঠিগুলো না–পড়া, না–খোলা? অভিমান হল। বন্ধুত্ব বদলে যায়। কিন্তু তাই বলে… জিজ্ঞেস করবেন, কেন? না। জিজ্ঞেস করবেন না। কৈফিয়ত চাওয়া বন্ধুত্বের কাজ নয়। জুতোর বাক্সটা জায়গামতো রেখে বসার ঘরে গিয়ে বসলেন।
সবশুদ্ধ ঘণ্টাখানেক একা থাকতে হলো। প্রতিমের বাড়িতে করার কিছু নেই। গল্পের বই নেই, ম্যাগাজিন নেই, চারটে গাইনি বই আর ওই আদ্যিকালের হ্যারিসনের মেডিসিন। অনেক খুঁজে নিজের ঘরে একটা মাস ছয়েকের পুরোনো খবরের কাগজ পেয়ে সেই নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময়, “কী রে, অনেকক্ষণ লাগল, না?” বলে ঘরে ঢুকল প্রতিম। সপ্তকের হাতের কাগজ টেনে নিয়ে বলল, “কী করছিস? এটা কোত্থেকে পেলি? খুব বোর হলি, না?”
সপ্তক হেসে বললেন, “নাঃ, তবে করার তো কিছু নেই। তাই…”
প্রতিম বলল, “দাঁড়া, হাত মুখ ধুয়ে, চেঞ্জ করে নিই। এই রাত নটা–টটা অবধিই এমার্জেনসি আসার সম্ভাবনা বেশি। তাই ততক্ষণ জামা–কাপড় ছাড়ি না। এবারে আমিও গেঞ্জি–পাজামা। তারপরে কপাল। আবার কেউ বাইক উলটে পড়বে না আশা করি।”
হাতমুখ ধুয়ে, পাজামা–গেঞ্জি পরে ফিরে এল প্রতিম। কাঁধের তোয়ালেটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে বলল, “বল। খিদে পেয়েছে? খাবি? তুই খাস কটার সময়?”
নিজের বাড়িতে সপ্তক তাড়াতাড়িই খেয়ে নেন। তারপরে হয়ত হাঁটতে বেরোন আকাশ পরিষ্কার থাকলে। দেশে ফিরে দেখেছেন লোকে দেরি করে খাচ্ছে। রাত দশটা, সাড়ে দশটা, এগারোটা – মনে করতে পারেননি নিজেও এরকম সময়ে কখনও খেয়েছেন কি না। বললেন, “তুই কখন খাস?”
প্রতিম বলল, “আমি এরকম সময়েই খেয়ে নিই। কাজ থেকে ফিরে।”
সপ্তকের তাড়া নেই, কিন্তু খাবার ব্যাপারটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড বলে বললেন, “খেতে পারি। খেয়েই ঘুমোবি?”
প্রতিম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “করার তো কিছু নেই। শুয়ে পড়ি। ভোরবেলা উঠি। আজকাল ভোরে নদীর ধারে বেড়াতে যাই। যাবি?”
ঘাড় নাড়লেন সপ্তক। বললেন, “তাহলে তো তাড়াতাড়ি শুতে হয়?”
“চ’, খেয়ে নিই,” বলে প্রতিম সোফা ছেড়ে উঠে ভেতরে চলে গেল। ওর পেছনে গিয়ে খাবার ঘরের দরজায় আবার থমকাতে হল সপ্তককে। টেবিলে তিনজনের বসার জায়গা করা। কেন? তিন কাপ চায়ের কথা মনে পড়ল। তার চেয়েও বড়ো কথা, কাজটা করল কে? কখন? পেছনের দরজা বন্ধ করে সপ্তক হয় বসার ঘর, নইলে বাইরের ঘরে ছিলেন। যতটুকু সময়ের জন্য বাইরের দরজা খোলা রেখে নিজের ঘরে গেছিলেন, ততক্ষণে কেউ এসে টেবিলে চাদর পেতে, ম্যাট দিয়ে, তাতে তিনটে থালা–গেলাস রেখে, জগে জল ভরে, নেটের সুদৃশ্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে, সাজিয়ে গুছিয়ে বেরিয়ে গেছে, এ হতেই পারে না।
এখন অবশ্য পেছনের দরজাটা খোলা। তার মানে প্রতিম যখন হাতমুখ ধুতে গেছে, তখন খুলেছে, আর পেছনের দরজা দিয়ে কাজের লোক এসে টেবিল সাজিয়ে গেছে। এবার খাবারের কী হবে?
প্রতিম একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, “তুই ওটায় বোস। আমি খাবারটা আনি।”
লম্বাটে টেবিলের এক মাথায় একটা থালা, তার দু–পাশে আরও দুটো। সপ্তক বসলেন। প্রতিম এসে দুটো থালা সোজা করে গেলাস সোজা করে জগ থেকে জল ঢালল। সামনের পিরিচের ওপর রাখা নেটের ঢাকনা তুলে লেবু আর লঙ্কা দিল পাতে। ছিল কোথায় এগুলো?
ঝনাৎ করে দরজার শিকল খুলে রান্নাঘরে ঢুকল প্রতিম। রান্নাঘরে কী আছে? রান্না বসাবে? সপ্তককে টেবিলে বসিয়ে?
এক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল প্রতিম। দু–হাতে একটা হাঁড়ি। মুখ ঢাকা হাঁড়িটা সপ্তকের সামনে রেখে বলল, “দাঁড়া। আরও আছে…” বলে ফিরে গেল রান্নাঘরে। এবারে এক হাতে একটা কাণা–উঁচু থালা, অন্য হাতে একটা বড়ো বাটি। দুটোই সামনে রেখে বলল, “হাঁড়িতে বিরিয়ানি, এটা কাবাব, আর এটা রায়তা। ফিরনি আছে। আমি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে আসি। বেড়াল ঢুকলে ফিরনি আর খেতে হবে না।”
~পাঁচ~
“রান্না কি প্রধানের বাড়ি থেকে এসেছে?”
বিরিয়ানিটার তুলনা হয় না। এরকম গ্রামে এরকম কোয়ালিটির বিরিয়ানি পাবেন ভাবতে পারেননি সপ্তক। কাবাবগুলোও অসাধারণ।
একটু হাসল প্রতিম। বলল, “একরকম তা–ই। ভালো হয়েছে?”
কত ভালো হয়েছে বললেন সপ্তক। আবার হাসল প্রতিম। বলল, “যাক। তোর ভালো লাগলেই হল। আর একটু বিরিয়ানি নিবি? খেলি তো ওইটুকু।”
আর থাকতে না পেরে সপ্তক প্রশ্নটা করে ফেললেন। “একটা করে এক্সট্রা চা, থালা কেন?”
প্রতিম হা–হা করে হেসে বলল, “আর একটা কাবাব নে,” বলে সপ্তক কিছু বলার আগে একটা কাবাব তুলে দিল থালায়। সপ্তক বহু বছর সাহেবদের সংস্রবে থেকে সহজে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারেন না। বিশেষত যদি তার উত্তর না আসে, তাহলে তো আরও–ই না। তাও বললেন, “তোর বাড়ির রহস্যটা বলবি? এটা তো তোর বাড়ি বলে মনেই হচ্ছে না। প্রধানের বাড়ি তোকে ছেড়ে দিয়ে সব জিনিসপত্র রেখে গেছেন? কেন?”
এক মুহূর্ত কী ভাবল প্রতিম। তারপরে বলল, “বাড়িটার হিস্ট্রি একটা আছে। এটা প্রধান তৈরি করেছিলেন নিজে থাকবেন বলে। ওদের বাড়িটা তখন কাঁচা বাড়ি ছিল।”
সপ্তক মাথা নাড়লেন।
“প্রধান চেয়েছিলেন এই বাড়িতে উঠে এসে আমাকে ও–বাড়িতে নিজের অংশে থাকতে দেবেন। কিন্তু তার মধ্যে একটা সমস্যা হল। বাড়ি তখনও শেষ হয়নি, এমন সময়, দুবাই, না ওমান কোত্থেকে প্রধানের মেয়ে জানাল ওর বরের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ওরা দেশে ফিরবে। বর শহরে ব্যবসা করবে, যতদিন না দাঁড়ায়, ততদিন মেয়ে এখানে থাকবে।
“সাজ সাজ রব। প্রধানের মেয়ে এ–বাড়িতে থাকবে। সব প্ল্যান নতুন করে করা হল। শহর থেকে ফার্নিচার এল মেয়ের ইচ্ছেমাফিক। মেয়ে নিজে এসে ওই সব দেওয়ালের সাজানোর জিনিসপত্র লাগাল – ওগুলো সব বিদেশী। ওখান থেকে আনা। ওই যে সাদার ওপরে এমব্রয়ডারি, ওটা কিন্তু সোনার সুতো। সবই নাকি খুব দামী। মেয়েটা থাকতে শুরু করল।”
“তুই তখন এখানে?”
“হ্যাঁ, তো,” বলে চলল প্রতিম। “আমি তখন নতুন। কাজ নিয়ে হিমসিম। মাসে চারবার করে দৌড়ই ব্লক পি–এইচ–সি, দু–বার যেতে হয় ডিস্ট্রিক্ট হেড–কোয়ার্টার। বেলডাঙায় ছুটি নীলের বুদ্ধি নিতে। ভাবতে পারবি না এই যেটুকু করি, সেটা করতেই কী ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে…
“যাক সে কথা… সমস্যা হল, মেয়েটা এখানে এসে ঘরদোর গুছিয়ে বসার মাস তিনেকের মাথায় ছেলেটা ওকে জানাল, সে আর সংসার করতে রাজি না, তালাক দিচ্ছে। ব্যাস, এক সপ্তাহের মাথায় মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল।”
“সুইসাইড?” সপ্তকের ফিরনি খাওয়া থেমে গেল। “কোথায়?”
প্রতিম মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, “এই বাড়িতেই। সে এক কাণ্ড। প্রধানের বাড়িতে কান্নাকাটি – বাবা, ভাই, হুমকি দিচ্ছে, জামাইকে দেখে নেবে, লাশ ফেলে দেবে, এই সব… কিন্তু বুঝতেই পারছিস, এই এঁদো গ্রামের প্রধানের পক্ষে শহরে গিয়ে জামাইকে শাসন করা সম্ভব নয়। কিছুই হল না। বছর দুয়েক বাদে বাড়ির লোকেরা ঠিক করল, এখানে ওদের ফ্যামিলির কেউ থাকবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি থাকব কি না। তখনই বলেছিল যে আমার জীবদ্দশায় আমার এখানে থাকার অধিকার থাকবে, কিন্তু আমি কিছু বদলাতে পারব না। এই সাজসজ্জা, এই ফার্নিচার, সব কিছু একই রকম রাখতে হবে…”
“সে আবার কী? এই সব আরবী ভাষায় কোরাণের বয়েত নিয়ে তুই থাকছিস, তোর অসুবিধে হচ্ছে না?”
প্রতিম মাথা নাড়ল। “আমার চোখেই পড়ে না। আর তাছাড়া আমি তো আর ওখানে শিব–দুর্গার ছবি লাগাতাম না, খালিই পড়ে থাকত। আছে কিছু ডেকোরেটিভ পিস… ক্ষতি কী?”
সপ্তক বললেন, “ওরা কেউ যদি না–ই থাকে, তাহলে তোকে লিখে দিতে আপত্তি কী?”
প্রতিম হাসল। “ওরে, প্রপার্টি কেউ এভাবে হাতছাড়া করে না। আর আমার তো দরকারও নেই।”
সপ্তক বলল, “তোর যদি সংসার থাকত, ছেলেপিলে থাকত? তাহলে বলতে পারতি?”
প্রতিম আরও জোরে হেসে বলল, “তাহলে ডাঃ ঘোষের কথাটা মনে করাই। ‘এই সিমটম থাকলে সেই ডায়াগনসিস হত, ওই সিমটম–টা না হলে ওটা হতে পারত, এসব বলে লাভ নেই। যা আছে তা দিয়ে ডায়াগনসিস করতে হবে। আমার পকেটে দুটো টাকা আছে। তাই দিয়ে চালাতে হবে। একশো টাকা থাকলে কী কী করতে পারতাম তার লিস্টি করে লাভ আছে?’ আমারও তাই কথা। আমার যদি ওয়ারিশ থাকত, তাহলে তাদের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হত। যা নেই তা নিয়ে ভাবব কেন?”
সপ্তক বলল, “কেন, এখনও তো হতে পারে। তোর বয়সই বা কত আর?”
প্রতিম গম্ভীর হয়ে গেল। তারপরে মাথা নেড়ে বলল, “না। আর সম্ভব না।”
সপ্তকের আরও একটু তর্ক করার ইচ্ছে হচ্ছিল। পশ্চিমে শিখেছেন, মানুষ এই বয়সে নতুন করে শুরু করে। ডিভোর্সের পর সেটা নিজেকে দিয়েই অনুভব করেছেন। কিন্তু প্রতিমের মুখ দেখে কিছু বললেন না। আরও কিছু আছে যেটা প্রতিম এখনও বলছে না। একটা অস্বস্তি কাজ করতে থাকল। কবে মারা গেছে প্রধানের মেয়ে, এই বাড়িটা এখনও তার স্মৃতির মিউজিয়াম, আর সে মিউজিয়ামের দায়িত্ব ওরা দিয়ে রেখেছে প্রতিমের ওপর। প্রতিমের পক্ষে কি সেটা ভালো হচ্ছে?
শুতে গেলেন দুজন। প্রতিম বলে গেল, ভোর বেলাই চা নিয়ে ডাকবে। সারা দিনের ধকলে ক্লান্ত ছিলেন, বিছানায় পড়ামাত্র ঘুম এসে গেল।
~ছয়~
ঘুমটা ভাঙল মাঝরাতে কোনও সময়ে। বালিশের পাশে হাতড়ে খেয়াল হল মোবাইলটা নিয়ে শোননি। ব্যাটারি চার্জ দেবার উপায় নেই বলে সুইচ অফ করে রেখেছেন। কটা বাজে দেখার উপায় নেই। পেছন দিকে জানলা, বাইরে তাকালে কি সময় আন্দাজ করা যাবে?
ঘাড়টা ঘোরাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলেন। ঘরে কেউ আছে? সকালে প্রতিম চা নিয়ে আসবে বলে দরজায় ছিটকিনি দেননি সপ্তক। পায়ের দিকে সামান্য নড়াচড়া? না মনের ভুল? টর্চটা বালিশের ওপাশে। নিতে গিয়ে যে নড়াচড়া হল, তাতেই বোধহয় ঘরে যে রয়েছে সে কিছু আন্দাজ করল। বলল, “সপ্তক, জেগে আছিস?”
প্রতিম। সপ্তক মশারীর মধ্যে উঠে বসে বললেন, “হ্যাঁ। কটা বাজে?”
প্রতিম আলো জ্বালাল। “বেশি হয়নি। প্রথম রাত। এগারোটা দশ। তোর সঙ্গে কটা কথা বলার আছে।”
প্রথম রাত হতে পারে, কিন্তু প্রায় দেড়ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। সপ্তক ঘুম–ভাঙা অবস্থায় বেশি কথা বলতে পারেন না। তবু মশারী থেকে বেরিয়ে খাটের পাশে বসে বললেন, “বল।”
মশারীটা সরিয়ে পাশে বসল প্রতিম। বলল, “কথাটা বলাটা কঠিন। কিন্তু তোকে শুনতে হবে। না হলে আমার কথা শোনার কেউ নেই এখানে।”
হাত দিয়ে হাই ঢেকে সপ্তক বললেন, “বল। শুনছি।”
প্রতিম কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। সপ্তক বলতে যাবেন, “কী হল?” এমন সময় হঠাৎ মুখ তুলে হুড়মুড়িয়ে বলতে শুরু করল, “তোকে একটা কথা ভুল বলেছি। ওরা আমাকে জোর করে এইসব আসবাব, ঘর সাজানোর জিনিস রাখতে বলেনি। আমি নিজেই এগুলো সরাইনি।”
মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে করার মতো স্বীকারোক্তিই বটে। “কেন সরাসনি?”
প্রতিম বেকুবের মতো নাকটা চুলকে বলল, “আসলে কী জানিস, এখানে আসার আগে ওরা বলেছিল যে সব খালি করে দেবে। কিন্তু এত জিনিস কোথায় নিয়ে যাবে? তাই আমি বলেছিলাম, আপাতত থাক।”
বেশ। তারপর?
“কিন্তু কী হল জানিস, এখানে থাকতে শুরু করে আমার খালি মনে হত, যে মেয়েটা এখানেই আছে।”
সপ্তক আধ–ঘুমন্ত মস্তিষ্কে ধরতে পারলেন না। বললেন, “আছে মানে? মারা যায়নি?”
মাথা নাড়ল প্রতিম। “মারা যাবে না কী করে? পোস্ট মর্টেম হয়েছে, বাড়ির পেছনেই গোর দেওয়া হয়েছে…”
দুটো বিষয় খট্ করে লাগল সপ্তকের। “গ্রামে কোনও কবরস্তান নেই? বাড়ির পেছনে গোর দেয়া হল কেন?”
“আছে। কিন্তু প্রধান বললেন মেয়ে যেহেতু আত্মহত্যা করেছে, ওর স্থান ওই পবিত্র জায়গায় হবে না। এ বাড়িতে আত্মহত্যা করে বাড়িটাও অপবিত্র করে গেছে। তাই বাড়ির পেছনেই গোর দেওয়া হয়েছে।”
“তাহলে আছে বললি যে?”
প্রতিম একটু অসহিষ্ণুর মতো বলল, “আহ, ওরকম না। মরে গিয়েও চলে না যাওয়ার মতো আছে।”
ওর স্মৃতি? “তুই মেয়েটাকে চিনতি? কতটা চিনতি, যার জন্য ওর স্মৃতিকে সৌধ বানিয়ে রেখেছিস?”
“না, না, স্মৃতি না… তুই বুঝছিস না কেন? ও মরে গিয়েও চলে যায়নি। এ বাড়িতেই রয়েছে। ওর প্রেজেনস আমি সারাক্ষণ টের পাই। প্রথম দিন থেকেই…”
হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সপ্তক। কত বছর এই বাড়িতে একা রয়েছে প্রতিম। দশ, বারো, পনেরো? একা একা থাকতে থাকতে… সপ্তক যেটা ভয় করেছিলেন সেটাই হয়েছে।
বললেন, “তারপর?”
প্রতিম বলল, “আসলে কী জানিস, আমি না কখনওই ভয় পাইনি। বুঝতে পেরেও না। আমি বুঝতাম শবনম বাড়িতেই থাকে। প্রায়ই আমার আসেপাশে ঘোরাঘুরি করে। শেষে একদিন ভীষণ ঝড়জলের রাতে, এসে বিছানায় উঠেছে। কাঁদোকাঁদো গলায় বলেছে, বাজ পড়লে ওর ভীষণ ভয় করে। আমি যেন ওকে তাড়িয়ে না দিই।”
সপ্তকের আর ঘুম পাচ্ছে না। হাসি পাচ্ছে। কোনও রকমে হাসি চেপে বললেন, “বলেছে মানে? তুই শুনতে পেয়েছিস?”
প্রতিম বলল, “ঠিক তোর কথা যেমন শুনছি তেমন না। তবে নিজের মতো করে স্পষ্ট শুনেছি।”
সপ্তক বললেন, “তারপর?”
“ওয়েল, তারপরে আমি সারাক্ষণই শবনমকে কাছে পাই। দেখতে পাই না। ফিল করি। আস্তে আস্তে মেটিরিয়াল জগতে শবনমকে পেতে শুরু করি। হসপিটাল থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরদোর গোছানো, পরিষ্কার। তারপর একদিন দেখি আমাকে আর রান্না করতে হচ্ছে না। দুপুরবেলা ভাত ডাল তৈরি থাকে। বিকেলে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে গরম ধোঁয়া ওঠা চা তৈরি।”
সপ্তক বললেন, “তার মানে কালকের ডিনারও…”
ঘাড় নাড়ল প্রতিম। “নইলে অত রান্না করল কে? তুই তো সারা সন্ধে ছিলি।”
সারা সন্ধে ছিলেন, খাবার কোত্থেকে আসবে সেটাও সারাক্ষণ ভেবেছেন, কিন্তু উত্তরটা যেটা ভেবেছেন, সেটা অন্য। বললেন, “সেই জন্য তিন কাপ চা? আর তিনটে থালা?”
প্রতিম ঘাড় নাড়ল। বলল, “ঠিক।”
সপ্তক বললেন, “চা–টা তার মানে…”
প্রতিম বলল, “ও–ই খেয়েছিল।”
“কিন্তু ডিনারে তো কেউ খায়নি?”
প্রতিম হাসল। “লজ্জা পেয়েছিল। চা–ও খেতে চাইছিল না। বলেছিল ভেতরে নিয়ে আসতে। আমি বলেছিলাম, আমার বন্ধু এসেছে, তুমি ওখানেই চলো। তাই এসেছিল। তোর পাশের চেয়ারে বসেছিল। তুই দেখতে পাসনি, আমি পেয়েছি। তবে খেতে কিছুতেই বসল না। আমরা উঠে আসার পরে খেয়েছে।”
কী বলবেন সপ্তক? চুপ করে রইলেন।
প্রতিম আবার শুরু করল। “উই বিকেম ভেরি ক্লোজ। সারাক্ষণ গল্প–আড্ডা, কথাবার্তা… সেই সময়েই নিয়ম করে দিলাম, যে আমি বাড়িতে থাকলে কেউ যেন হুট করে ঢুকে না পড়ে। আই ফেল ইন লাভ উইথ হার… মানে উই ফেল ইন লাভ উইথ ইচ আদার…” কথাটা বলতে বলতে আড়চোখে সপ্তকের দিকে তাকিয়ে নিল প্রতিম। প্রতিমের মুখে চোখে অবিশ্বাস? না বিস্ময়? “যত দিন যেতে লাগল, তত শবনম আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। ক্রমে ক্রমে আমি ওকে আবছা দেখতেও শুরু করলাম। তুই বিশ্বাস করবি না, জানি। তাতে কিছু এসে যায় না। আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তারপরেই ওদের বললাম, যে ওরা চাইলে বাড়িটা শবনমের স্মৃতির জন্য এরকম রাখা যেতেই পারে। ওরা এই ফার্নিচার, পর্দা, সাজানোর জিনিস নিশ্চয়ই চাইবে না? তাহলে বিক্রি করতে হবে। শহর থেকে কিনে আনা এ সব কে নেবে এই গ্রামে? আর বাড়িটারও বদনাম, সুইসাইড বাড়ি। সুতরাং…”
“এ সব কবেকার কথা?”
প্রতিম একটু ভেবে বলল, “আমি এখানে আসার পরে সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এ সব হয়ে গেছে। আমি তদ্দিনে ঠিক করেছি শবনমকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। তার পর থেকেই আমি ট্রানসফার রিজেক্ট করতে আরম্ভ করি। আরও সাত আট বছর পরে আমরা একসঙ্গে থাকব ঠিক করি।”
চমকে সপ্তক বললেন, “মানে, এই সাত আট বছরে একসঙ্গে ছিলি না? কোথায় থাকতি?” তারপরেই আরও চমকে ভাবলেন, এসব কী বলছেন? নিজের মাথাটাও গেল না কি?
প্রতিম একটু হাসল। বলল, “এটা একটু অদ্ভুত। ছিলাম। রাতে ও এসে আমার পাশেই শুত। নারী–পুরুষের মতোই। কিন্তু ও চাইত আরও কিছু। চাইত কমিটমেন্ট যে আমি চলে যাব না। আমি বলতাম, এটা তো মৌলবী ডেকে, পুরুত ডেকে, কলমা পড়ে, মন্তর পড়ে বিয়ে হবে না। তাহলে এর চেয়ে বেশি কী চাও?”
“কী বলত?”
“ওই যে বললাম, কমিটমেন্ট। শেষে একদিন আমি বললাম, বেশ। লেট আস লিভ টুগেদার লাইক ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ। আমি এখান থেকে যাবই না। চলাফেরার পরিধি হবে কেবল হাসপাতাল আর বাড়ি। কালেভদ্রে হাসপাতালের কাজে শহরে যাব।”
“তারপর?” উৎসুক সপ্তক জানতে চাইলেন।
“তারপর আর কী? আছি দুজনে স্বামী–স্ত্রীর মতো। কেউ জানে না। কেবল আজ তুই জানলি। কাউকে বলিস না। কেউ বিশ্বাস করবে না, তারপরে আমাকে পাগল বলে গাঁ–ছাড়া করলে খুব বিপদ হবে।”
সপ্তক বললেন, “তোর ট্রানসফার হলে কী করবি?”
প্রতিম দুলে দুলে হাসল। বলল, “হবে না। এখানেই থাকব।”
“শবনমকে নিয়ে কোথাও যেতে পারবি না?”
“না,” মাথা নাড়ল প্রতিম। “হাসপাতালেও দেখিনি কখনও। আমার ধারণা সেটা এই ভিটেয় ওর কবর আছে বলে। ওকে যদি গোরস্তানে কবর দেওয়া হত, আমার সঙ্গে দেখা হতই না।”
হতভাগা গ্রামপ্রধান…
কী বলবেন সপ্তক? বলা উচিত, প্রতিম, আমার সঙ্গে ফিরে চল। শহরে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আলোচনা করি। একা থাকিস বছরের পর বছর, একটু হেল্প লাগবে মনে হচ্ছে।
কিন্তু কী করে বলবেন? ভেবে ভেবে সারা রাত ঘুম এল না।
~সাত~
দু–বন্ধু যখন শেষ পর্যন্ত প্রায় রাত দেড়টায় শুতে গেছেন, তখনই ঠিক করেছেন, এ যাত্রা ভোরবেলা নদী দেখা হবে না। প্রতিম চলে গেলেও সপ্তকের ঘুম আসতে আরও দেরি হয়েছে। প্রায় আটটায় যখন ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরোলেন, একটা ছেলে এসে বলল, “স্যার, আমি নাসির। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে। ভোর রাতের থেকে একের পর এক লেবার কেস এসেছে। বলেছেন, আপনাকে চা দিতে, আর তারপরে আপনাকে নিয়ে ওখানে যেতে। ওখানেই খাবেন।”
একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সপ্তক দাঁত মাজতে গেলেন। অন্তত রান্নাঘর থেকে ধূমায়িত ভৌতিক চা, গরম ডিম–টোস্ট উদয় হবে না, যাতে প্রতিম পরে বলতে পারে শবনম বানিয়েছিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভেতরে ঢুকছেন, চায়ের ভাঁড় হাতে নাসির এল। বলল, “আমি বাথরুমে জল তুলে রেখেছি, আপনি চান করে রেডি হয়ে আসুন, আমি বাইরে ওয়েট করছি।”
বাধ্য ছেলের মতো সপ্তক স্নান সেরে রেডি হয়ে বাক্স নিয়ে বেরোলেন। নাসির হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে বাইরের দরজায় হুড়কো লাগাতে লাগাতে বলল, “চলুন স্যার।”
“তালা দিতে হয় না?” যেতে যেতে বললেন সপ্তক।
বরাভয়ের সুরে নাসির বলল, “না–আ–আ–আ, স্যার। বেড়ালের জন্যই বন্ধ করা। নইলে ঢুকে নোংরা করে রাখে।”
সুযোগ পেয়ে জানতে চাইলেন, “কে পরিষ্কার করে?”
নাসির অবাক সুরে বলল, “কেন, হাসপাতালের সুইপার…” তারপরে বোঝানোর সুরে বলল, “ডাক্তারবাবু বারণ করেন, কিন্তু আসুরা বিবি শোনে না। রোজ ডাক্তারবাবুর বাড়ি ধোয়া–মোছা করে।”
রান্না কে করে জিজ্ঞেস করবেন? না। থাক। ঘর সাফ করার কথাটা অটোমেটিকালি এসেছিল। রান্নার কথা সেভাবে আসেনি। তারপরে প্রতিমকে যদি বলে, “আপনার বন্ধু জানতে চাইছিলেন বিরিয়ানি কে রেঁধেছে…”
আরও মিনিট চল্লিশেক বাদে বেরোতে পারল প্রতিম। সপ্তক ততক্ষণে পুকুরের পাড়ের বাঁধানো ঘাটে বসে দু–কাপ চা খেয়েছেন, উলটো দিকের দোকানীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন, বাগানে পায়চারি করেছেন, কলাগাছের দিকে গিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়া ফার্মাসিস্টের কোয়ার্টার দেখে এসেছেন। এক লহমার জন্য ভেবেছিলেন, যদি স্বাস্থ্য ভবন ডাক্তারবাবুকে অর্ডার দেয়, নিজের কোয়ার্টারেই থাকতে হবে… অন্নপূর্ণাকে বলবেন কি? তারপরে বুঝেছিলেন, হবে না। এত দূরে কারওর ওপরে অত নজরদারি সম্ভবই না।
পুকুরপাড়ে বসে চা খেয়ে দু–বন্ধু দোকানের কচুরি আর আলুর দম দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিলেন। তারপরে টা–টা বলে একজন গেল হাসপাতালে, অন্যজন চড়লেন রিকশায়। আগের দিনেরই রিকশাচালক। খানিকটা গিয়ে বলল, “মানোয়ার আলি সায়েব আপনারে ডাকসেন।”
কী উত্তর পাবেন জানতেন, তাও জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলেন যে মানোয়ার আলিই প্রধান। রিকশ গিয়ে থামল প্রধানের বাড়ির সামনে। বেরিয়ে এল তাঁর ছেলে। আদাব তসরিফের পর জানাল, বাবা এখন আর বিশেষ বেরোতে পারেন না। তবু, ষোলো বছর আগে গ্রামে যখন তিন যুগ পরে ডাক্তার এসেছিল, তাকে নিয়ে এসেছিলেন যে ডাক্তারবাবু, তাঁকেও প্রধান মনে রেখেছেন। দেখা করতে চেয়েছেন।
আলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে লাভ হল না। উনি, বা তাঁর বাড়ির অন্য যাদের সঙ্গে দেখা হল, কেউ মনে হল না প্রতিমের অবস্থার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপ সেরে আবার রওয়ানা দিলেন। পথে রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথায়, এবং রাস্তার মোড়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে চায়ের দোকানের আড্ডায় জানা গেল, যে শবনমের কাহিনি সত্যি। সে দুবাই–তে থাকত, তাকে দেশে পাঠিয়ে বর তালাক দিয়ে হারিয়ে যায়, এবং তার পরেই, ওই বাড়িতেই শবনম সুইসাইড করে।
বাকিটা অবশ্য কেউ জানে না।
~আট~
ফিরতে ফিরতে কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, ওঁদের ব্যাচে সাইকিয়াট্রি করেছিল কে। কপিলের সঙ্গে ছেলেটার খুব বন্ধুত্ব ছিল। মোবাইল বের করে কপিলকেই ফোন করলেন।
“সাইকিয়াট্রিস্ট? কেন রে? তোর হঠাৎ সাইকিয়াট্রিস্টের দরকার পড়ল কেন? পঙ্কজ উদানি তো ইউ–এস–এতে।”
যাঃ।
“তাছাড়া ও এখন ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট। হুইচ ইজ ওয়ার্স দ্যান অটপ্সি সার্জন, ইফ ইউ আস্ক মি,” কপিল বলে চলেছে। “আমার হসপিটালে ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট আছে। আমাদের কলেজের না, কিন্তু রয়্যাল কলেজের ডিগ্রি…”
কপিলকে থামিয়ে সপ্তক বললেন, “ব্যাপারটা সিরিয়াস। তবে আমার না, প্রতিমের। ও ক্লেম করছে, ও একজন মৃত মানুষের সঙ্গে সংসার করছে…”
“হোয়াট!” টেলিফোনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কপিল। বাধ্য হয়ে সবটাই সংক্ষেপে বলতে হল। কপিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “সপ্তক, ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস। প্রতিমকে যতটা না চিকিৎসা করানো উচিত, তার চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ওই আত্মার ইস্যুটা। সুইসাইড হয়েছে এমন বাড়িতে প্রতিম থাকতে গেল কেন?”
আরও কিছুক্ষণ কথা বলে সপ্তক বুঝলেন কপিলের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। মডার্ন সায়েনসের যুগেও ওর মানসিকতা প্রাচীন। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলাই–বা যায়। এমন কারওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই যে কপিলের মতো ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেবে, বা পরে প্রতিমকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। প্রতিম বার বার করে বলে দিয়েছিল কাউকে না বলতে, কিন্তু এর মধ্যেই সপ্তক কপিলকে বলে দিয়েছেন…
সন্ধেবেলা কপিল ফোন করল। “সপ্তক, তুই কাল আমার বাড়ি আসবি – খুব আর্জেন্ট। দশটা থেকে বারোটার মধ্যে আসবি। বারোটার আগে ছাড়া পাবি না। সুতরাং তোর কাল কোনও কাজ থাকলে সকালে বা বারোটার পরে রাখিস। খুব আর্জেন্ট কিন্তু। দেরি করে এলে আপত্তি নেই, কিন্তু বারোটার আগে। মনে থাকবে? সিরিয়াসলি নিস…”
মনে হল কিছু সলিউশন বেরোবে। সকালে কাজ ছিল না, তাই একটু সকালেই গেলেন কপিলের বাড়িতে। শহরের মধ্যে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। গিয়ে দেখেন জমজমাট ব্যাপার। অনেক লোকের ভীড়। কপিল বেরিয়ে এল।
“আয়, আয়, আমার বাড়িতে আজ একটা পুজো… আয়, এ ঘরে বোস…” ভেতরের একটা বসার ঘরে একটা রিক্লাইনারে বসিয়ে বলল, “ব্রেকফাস্ট খাবি? না? খেয়ে এসেছিস? তাহলে বোস, আমি চা পাঠাচ্ছি। প্রসাদ খেয়ে যাবি…”
অস্বস্তিতে পড়লেন সপ্তক – বাড়ি ভর্তি লোক, কপিল ছাড়া কাউকে চেনেন না। কেন ডাকছে জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল। তাহলে আর একটু দেরি করে বা একেবারেই না–ও আসতে পারতেন। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। তবু ঘরে আজকের তিনটে খবরের কাগজ আছে। কপিলের স্ত্রী এসে নমস্কার করে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দিয়ে গেল, নানা জনে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, বাচ্চারা কলতান করতে করতে হঠাৎ অপরিচিত মানুষ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে – সপ্তক কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন। কপিল এসে ঢুকল।
“তোর গোত্র জানিস?”
জানেন, বললেন। তার পরের প্রশ্নে অবাক হলেন।
“প্রতিমের গোত্র জানা নেই বোধহয়?”
“প্রতিমের গোত্র দিয়ে কী হবে?”
কপিল একটু থতমত খেয়ে বলল, “না, ভাবলাম এতদিন পরে যখন সবার নামে পুজো দিচ্ছি, ওর নামেও দিই। ঠাকুরমশাই বলছে, গোত্র না জানলেও চলবে, যথানামে বলে দেওয়া যায়… কিন্তু জানলে ভালো…”
অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল। সেই কোন সেকেন্ড ইয়ারে মা–বাবার সঙ্গে পুরী যাচ্ছিলেন, তখন প্রতিমের মা একটা কাগজে ওদের সবার নাম লিখে ওপরে গোত্রটা লিখে দিয়েছিলেন পুজো দেবার জন্য।
“পরাশর গোত্র।”
“থ্যাঙ্ক ইউ,” বলে উঠে গেল কপিল।
এর পরে আর বেশি সময় লাগল না। একটু পরেই ঘরে ঘরে শান্তি–জল ছেটালেন পুরোহিত, তারপরেই কপিল এসে বলল, “হয়ে গেছে। একটু বোস। আমি কিছু গেস্ট বিদায় করেই আসছি…”
কথাবার্তা–নড়াচড়ার শব্দে বুঝলেন লোকে একে একে বিদায় নিচ্ছে। তা–ও ঘড়িতে প্রায় একটা তখন বাজে, কপিল ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “বাপরে, এই গেল বাইরের লোকজন। এখন শুধু আত্মীয় আর খুব ক্লোজ কেউ কেউ আছে। লাঞ্চ খেয়ে যা?”
মিথ্যে করে বললেন, “না, রে। খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতে লাঞ্চ। অনেকটা যেতে হবে। বলেছি দেরি হবে, কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম বারোটায় বেরোব…”
কপিল অনেকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, “না না, ঠিক আছে। দেরি করে দিয়েছি। তোকে আর আটকাব না। তুই… এই নে…” বলে একটা মিষ্টির বাক্স বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “এটা তোর। খাবি। প্রসাদ। আর এটা…” আর একটা একই রকম বাক্স বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “প্রতিমের। ওকে দিস। দেখ, ওপরে নাম লেখা আছে…”
অবাক হয়ে সপ্তক বললেন, “কিন্তু…” কিন্তু বলা হল না। একটা হোমিওপ্যাথি শিশির মতো ছিপি আঁটা শিশি কপিল বাড়িয়ে দিল সপ্তকের দিকে।
“শোন, এটা তোকে বলছি। কাউকে বলিনি। আমার বউও জানে না। এই পুজোটা আসলে স্বস্ত্যয়ন করেছি একটা। প্রতিমের জন্য…”
অবাক হয়ে সপ্তক বললেন, “কাউকে বলিসনি, স্বস্ত্যয়ন করেছিস…”
কপিল চট করে একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিল। বলল, “আরে অনেকে বাড়িতে স্বস্ত্যয়ন করা পছন্দ করে না। বলে ক্ষতি হয়…”
আরও অবাক হয়ে সপ্তক জানতে চাইলেন, “তাহলে করলি কেন?”
একটা তাচ্ছিল্যের ছিক্ শব্দ করে কপিল বলল, “আরে আমি ও সব বিশ্বাস করি না। নে, এটা স্বস্তয়নের জল। তুই এটা নিয়ে গিয়ে ওর বাড়ির সব ঘরে ছিটিয়ে দিবি। ওকে আবার কিছু বলতে যাস না। অবশ্য পুরোহিত বললেন, বিদেহী আত্মা যখন মুসলমান, তখন মৌলবীকে দিয়েই কাজটা করানো উচিত। কী একটা ওরা পড়ে জানি না। কিন্তু সে আর কে করবে? প্রতিম তো হিন্দু, তাই এতে ওর রক্ষা হবে। তুই ভাই দেরি করিস না। আমি জানি তুই প্রতিমকে খুব ভালোবাসিস…”
সপ্তক ভাবলেন কপিলকে জিজ্ঞেস করেন ও কী কী বিশ্বাস করে, আর কী কী করে না, তার লিস্ট দিতে। তারপরে কিছু না–বলে উঠে পড়লেন। গাড়িতে যেতে যেতে মনে হল, দু–দিন হয়ে গেছে। এখনও কিছুই করেননি। কেন? পুরোনো বন্ধুর জন্য একজন সাইকিয়াট্রিস্ট খুঁজে পেতে এত সময় কেন…
নীল! এতক্ষণ কেন নীলের কথা মনে হয়নি? নীলই এরকম সময়ে বুদ্ধি দিতে পারবে। ওর মাথা সাফ। ওর জিভ ধারালো। একসময়ে কাছাকাছি কাজও করত। প্রতিম ওকে কেস পাঠাত। নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল। নীল খুব গালাগালি দিয়ে লোককে কাজ করাতে পারে…
~নয়~
“কোনও যোগাযোগই ছিল না। ও শালা অপারেশন করতে পারে না, তাই আমাকে পাঠাত, আমি অপারেশন করে ফেরত পাঠাতাম। ব্যাস।”
অবাক হয়ে সপ্তক বললেন, “পোস্ট–অপারেটিভ কেয়ার টেয়ার কী হবে, কিছু বলে দিতি না?”
হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়ে নীল বলল, “আমি অপারেশন করলে পোস্ট–অপারেটিভ কেয়ার লাগে না। কজন প্রতিম আছে রে ও সব এলাকায়? মাইলের পর মাইল, গ্রামকে গ্রাম, কোনও ডাক্তার নেই। আমি পেশেন্টের বাড়ির লোককে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার শেখাতাম। এখনও শেখাই। তাতে রেজাল্ট ভালো হয়…”
একটু হতাশ সুরে সপ্তক বললেন, “আমি ভেবেছিলাম যদি তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস, মানে…”
নীল সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে ঘর ভর্তি করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “যেতে আমি পারিই। কিন্তু গিয়ে হবেটা কী? প্রতিম আমার কথায় সুরসুরিয়ে ফিরে আসবে নিজের চিকিৎসা করাতে? ও শালা…”
আরও কিছু বলত, কিন্তু আঁখি সেই মুহূর্তে চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল বলে চুপ করে গেল। সেই কলেজের দিনগুলো থেকেই একমাত্র আঁখি থাকলেই নীলের মুখ বন্ধ থাকত।
“তুই কী রে?” ঘরে ঢুকেই আঁখি ফেটে পড়ল নীলের ওপরে। “ছেলেটা ইংল্যান্ড থেকে এসে প্রতিমের খোঁজ নিয়েছে। আমরা পাশে থেকেও এতদিন নিইনি। এসেছে সামান্য একটা হেল্পের জন্য। সেটা দিতেও এত ধানাইপানাই কেন তোর? প্রতিম তো আমাদেরও ক্লাসমেট ছিল। না রে, সপ্তক, চল আমি যাব তোর সঙ্গে। নীলও যাবে।”
নীল একটু মিনমিন করে, “আহা, আমি কি বলেছি, যাব না?” বলতে শুরু করেছিল, ওকে পাত্তা না দিয়ে আঁখি বলল, “পরশু শনি, তরশু রবিবার চল। আর দেরি করে কাজ নেই। তারপরে তুই আবার চলে যাবি কবে–জানি? নেক্সট উইকেই, না?”
নেক্সট উইকে না, কিন্তু দেরি করতে চান না সপ্তকও। না, ওদের গাড়ি নিতে হবে না, সপ্তকের ভাড়া করা গাড়ি আছে, ড্রাইভার থাকবে… তাহলে রবিবার সকালে সাতটায় সপ্তক গাড়ি নিয়ে হাজির হবেন ওদের বাড়ি…
~দশ~
ফুলপুকুরের পথে স্বস্ত্যয়ন আর শিশিতে জলের গল্প আর কপিলের বিশ্বাস–অবিশ্বাসের খবর শুনে নীল আর আঁখি হেসে মরে। নীল বলল, “তুই সত্যি ওই সব নিয়ে যাচ্ছিস?”
“আরে, আমাকে ধরিয়ে দিল, আমি কি রেখে আসব? ওই তোর হাঁটুর সামনে গাড়ির সিট–পকেটে আছে। প্রসাদী প্যাঁড়াটা ভালো ছিল। ফ্রিজে রেখেছিলাম। ওটাও এনেছি।”
শিশিটা বের করে আবার একদফা হাসাহাসি হল, নীল ওটা তক্ষুনি ফেলে দিতে চায়, আঁখি বলল, “থাক না, কপিল ভেবেচিন্তে দিয়েছে, সপ্তক ভেবেচিন্তে সঙ্গে নিয়েছে… তুই ওটা ফেলতে যাচ্ছিস কেন?”
হাসিতে গল্পে এবারের রাস্তা ফুরোল তাড়াতাড়ি। ফুলপুকুর যাবার মোড়ে চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়াল, নীল নেমে বলল, “দাঁড়া, আগে চা খাই। ভ্যানরিকশা তো নেই একটাও। অপেক্ষা করতে তো হবেই।”
দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নীল সবে বলেছে, “ভাই চারটে চা দেখি…” আর তখনই দুটো ঘটনা ঘটল। রাস্তা ধরে একটা মালবোঝাই ভ্যানরিকশা আসছিল, তার চালক ছেলেটা লাফ মেরে রিকশা থেকে নেমে, আর দোকানের ভেতর থেকে দোকানদার, দু–জনে একসঙ্গে “ডাক্তারবাবু…” বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেল নীলের পায়ের ওপর।
নীল, খুব গা না করে, “আরে, আরে… ধ্যাত্, ওঠো দেখি…” বলে সরে গিয়ে দুজনকেই ধরে তুলল। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলল, “অ্যাপেনডিক্স ছিল, না?” তারপরে ভ্যানরিকশা চালককে বলল, “পা ঠিক আছে?” ঘাড় নেড়ে লুঙ্গি তুলে হাঁটুর নিচের লম্বা কাটা দাগটা দেখাল ছেলেটা। বলল, “এক্কেরে। শুদু ভিজে দিনে একটু টাটায়। সেঁক দিলি কমি যায়।”
“ঠিক আছে, সেঁক দিবি। আর সাবধানে চলাফেরা করবি। মনে রাখবি ভেতরে এখনও স্টেনলেস স্টিল রয়েছে। আর একটা ভাঙলে আমার কাছেও আসতে পারবি না। আমি আর বেলডাঙায় নেই।” তারপরে দোকানদারের দিকে চেয়ে বলল, “তোমার পেট ঠিক আছে?”
দোকানদার ততক্ষণে সসপ্যান মেজে জল বসিয়েছে। বেরিয়ে এসে বলল, “আপনি নতুন জেবন দেছেন, ডাক্তারবাবু। সে রাতে তো মরতেই বসেছিলাম।”
“থাক, থাক, আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। জীবন একটাই থাকে। নতুন টতুন দেওয়া যায় না,” বলে নীল বৈয়াম খুলে একটা বিস্কুট বের করে কামড় দিয়ে আরও দুটো বের করে আঁখি আর সপ্তকের হাতে দিল। ভ্যানরিকশাওয়ালা, “আসি ডাক্তারবাবু, সালাম,” বলে চলে গেল। সপ্তক মৃদুস্বরে আঁখিকে বললেন, “না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।” আঁখিও মৃদুস্বরে বলল, “নীলকে এ–সব জায়গায় অনেকেই চেনে। কারওর না কারওর নিজের এবং প্রায় সকলেরই বাড়ির লোকের কিছু না কিছু চিকিৎসা করেছে।”
দোকানদার একটা থালায় চারটে গেলাসে চা এনে নীলের সামনে ধরে বলল, “ডাক্তারবাবু, আপনি এখেনে?”
চায়ের কাপে ফুড়ুৎ করে একটা চুমুক দিয়ে নীল বলল, “আমরা যাব ফুলপুকুর পি–এইচ–সি। ওখানে যে ডাক্তারবাবু আছেন, উনি আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তেন। ওনার সঙ্গে দেখা করতে।”
দোকানদার অনেকক্ষণ ধরেই নীলের সঙ্গে দুজনকে দেখছিল। এবারে সপ্তকের দিকে আঙুল তুলে বলল, “এই বাবুই এয়েছিলেন না, সেই সেদিনকে?”
সপ্তক বললেন, “হ্যাঁ। এক রাত আমার এই গাড়িই দাঁড়িয়ে ছিল এখানে। অবশ্য ড্রাইভার এ ছিল না।”
দোকানদার নীলকে বলল, “ফুলপুকুরের ডাক্তারবাবু তো সেইদিন থেকেই নিখোঁজ।”
ওরা তিনজনে চমকে বলল, “মানে?” সপ্তক বললেন, “নিখোঁজ আবার কী?”
দোকানদার আবার নীলকে উদ্দেশ্য করেই বলল, “মানে কেউ তাঁরে আর দেখেনি। গাঁ শুদ্ধু লোক মনে করেছে, এই ডাক্তারবাবুই ওনাকে ফুসলে নে গেছেন। গাঁয়ে বড়ো মিটিং ডেকেছে প্রধান মানোয়ার আলি। এখনই হচ্ছে লাগছে। ফুলপুকুরের কেউ সকাল থেকে এদিক মাড়ায়নি। লোকে কী করবে, পুলিশে জানাবে, না কি আগে এই ডাক্তারবাবুর খোঁজ করবে, সেটাই আলোচ্য বিষয়।”
ওরা মুখ তাকাতাকি করল। সপ্তক বললেন, “আমি যখন গ্রাম থেকে বেরিয়েছি তখন প্রতিম হাসপাতালে। ভোর থেকে ছিল। চারটে লেবার কেস এসেছিল। তার মধ্যে সেকেন্ড জনের কী কমপ্লিকেশন ছিল। ওই কেসটা শেষ করে প্রতিম আমার সঙ্গে কোনও রকমে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার দৌড়েছিল হাসপাতালে। দুটো লেবার বাকি, আউটডোরে ভীড়। কোনও রকমে টা–টা বলেছিল।” বলে চা–ওয়ালার দিকে চেয়ে বললেন, “আমি তো এই দোকানে এসে বসেছিলাম – কতক্ষণ। ডাক্তারবাবু তো আমার সঙ্গে ছিলেন না।”
দোকানদার বলল, “গাঁয়ের লোকে যা ভাবছে… পরদিনই ডাক্তারবাবু চলে গেছেন কি না?”
নীল বলল, “তার মানে পরদিন থেকে ডাক্তারবাবু নিখোঁজ? এখনও পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি?”
ঘাড় নাড়ল দোকানদার। না।
নীল চায়ের গেলাসটা রেখে উঠে পড়ল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা নম্বর খুঁজে ডায়াল করল। সপ্তকরা একদিকের কথাই শুনতে পেলেন।
“হ্যালো… হ্যাঁ। আমিই বলছি… কী খবর? কেমন আছ?”
…
“আচ্ছা, বেশ। শোনো। একটু দরকারে ফোন করলাম। ফুলপুকুর প্রাইমারির ডাক্তারবাবু… ও তুমি জানো… না না, বন্ধু–টন্ধুর সঙ্গে কোথাও যাননি। ওটা বানানো গল্প। আমরা, মানে ফুলপুকুরের ডাক্তারবাবু, আমি, আর সেদিন যে ডাক্তার এসেছিলেন, সবাই একই ক্লাসে পড়তাম। আমরা আজ আবার এসে শুনছি ডাক্তারবাবু নেই।”
…
“উনিও এসেছেন। উনি কিছুই জানেন না। আমরা ফুলপুকুর যাব, কিন্তু এখানে ভ্যান নেই। সবাই নাকি গ্রামে মিটিং করছে। এই অবস্থায় গ্রামে না গেলেই নয়। কিন্তু লোকে ধরে নিয়েছে আমাদের বন্ধু ফুলপুকুরের ডাক্তারকে ফুসলে নিয়ে গেছে। ওনাকে নিয়ে গ্রামে ঢুকলে একটা সমস্যা হতে পারে। তুমি কি আসতে পারবে? কত দূরে আছ?”
…
“বেশ। তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি। মোড়েই আছি… তুমি এলে… ভালো কথা – আমরা তিনজন আছি কিন্তু…”
…
“দুটো জিপ হলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে।”
লাইন কেটে নীল বলল, “এখানকার থানার ইনস্পেক্টর অরিন। আমার সঙ্গে ভালো পরিচয়। দু–জিপ পুলিশ নিয়ে আসছে। কপাল ভালো কাছাকাছিই ছিল কী একটা সমস্যা সামলানোর জন্য। ততক্ষণ গাড়িতে বসি।”
যথা আজ্ঞা। আঁখি আর সপ্তক গাড়িতে বসলেন, নীল গাড়ির গায়ে হেলান দিয়েই সিগারেট ধরাল।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আধঘণ্টার মধ্যেই দুরের রাস্তায় ধুলোর ঝড় দেখা গেল, আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল। একজন অফিসার নেমে নীলকে বলল, “স্যার, সব ঠিক আছে?”
নীল বলল, “এখানে তো ঠিক আছে, কিন্তু ফুলপুকুর তো যেতে হবে।”
ততক্ষণে সপ্তক আর আঁখি গাড়ি থেকে নেমেছেন। অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল নীল। অরিন বলল, “তাহলে চলুন, আমার জিপে আসুন। যেতে যেতে শুনে নেব। অ্যাই…” বলে পেছনের জিপকে বললেন, “তোমরা পেছনে এসো।” আর সপ্তকদের ড্রাইভারকে বলল, “তুমি এখানেই থাকো – কোথাও যাবে না। ডাক্তারবাবুদের হঠাৎ ফিরতে হতে পারে…”
ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল ড্রাইভার কেবল ঘাড় নাড়ল।
রাস্তা কাঁচা। তবে চওড়া। কাদার মধ্যে ভ্যান রিকশা চলে চলে গভীর গর্ত শুকিয়ে খাদ। সে সব সামলে চলতে সময় নিল। যে পথ ভ্যানরিকশায় এক ঘণ্টা নিয়েছিল, গাড়িতেও অতটাই লাগল। পথে নিজের অভিজ্ঞতার সব কথাই বলতে হল পুলিশ অফিসারকে। শুনে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন, “বলেন কী মশাই! লিভিং টুগেদার উইথ আ গোস্ট? পুলিশে চাকরি করতে গিয়ে অনেক আশ্চর্য জিনিস জেনেছি, এমনটা এই প্রথম শুনলাম।”
ফুলপুকুর গ্রাম জনশূন্য। তবে গাড়ি ঢোকামাত্র কিছু বাচ্চা ছেলে দৌড় দিল গাড়ির আগে আগে।
অরিন বলল, “গ্রামশুদ্ধ লোক মিটিং করতে পারে, এমন জায়গা একমাত্র দুটো। ইদগা, আর পি–এইচ–সির মাঠ। বাচ্চাগুলোর পেছনে চলো। ওরা মিটিঙেই যাবে।”
বাচ্চাগুলো ওদের নিয়ে গেল হাসপাতালেরই মাঠে। মাঠে অজস্র লোক। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গ্রামের প্রধান মনোয়ার আলি। আসেপাশে এক–দুজনকে চিনলেন সপ্তক। প্রধানের ছেলেরা।
জিপ থামামাত্র দ্বিতীয় গাড়ি থেকে বন্দুকধারী পুলিশ নেমে ওদের ঘিরে ধরে নিয়ে গেল হাসপাতালের বারান্দায় বসা প্রধানের দিকে। গ্রামের লোক সপ্তককে চিনতে পেরে, “ওই, ওই যে সেই…” ধ্বনি দিতে শুরু করামাত্র অরিন হাতের রুল তুলে, “এই, চুপ, সবাই চুপ,” বলে হাঁক দিতে হট্টগোলটা বাড়তে পারল না। কিন্তু অনেকেই নীলকেও চিনতে পারল।
“ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন?” “ডাক্তারবাবু, এই যে, এই যে আমি…” ধ্বনিও পাওয়া গেল।
ওরা বারান্দায় পৌঁছন–মাত্র গ্রামপ্রধান বললেন, “এই যে আপনি এসে গেছেন? আপনার বন্ধু কোথায়?”
অরিন গলাটা কড়া করে বলল, “ওনারা পুলিশে কমপ্লেন করেছেন, ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা জানেন, ডাক্তারবাবু কোথায়?”
জানে না। কেউ জানে না। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, ডাক্তারবাবুকে শেষ দেখেছিল সাকিম। সপ্তক চলে যাবার পরদিনও আউটডোরে ভীড় ছিল। দুপুরবেলা ডাক্তারবাবু হঠাৎ সাকিমকে বলেন, “শরীরটা ভালো লাগছে না। একটু বাড়ি যাচ্ছি। পেশেন্টদের বল – দুপুরে এসে বাকি সব্বাইকে দেখে দেব।”
সবাই অবাক। ডাক্তারবাবু কখনও এমন বলেন না। শরীর খারাপ বলে কাজ করছেন না, এমনটা কেউ মনেই করতে পারেনি। সাকিম বলেছিল, “আমি সঙ্গে আসি, ডাক্তারবাবু?”
উনি মাথা নেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সাইকেল নেননি। ওই রাস্তা ধরে হেঁটে গেছিলেন। সাকিম একটু দূরে দূরে গিয়েছিল। যাতে ডাক্তারবাবু দেখতে না পান। বারণ করা সত্ত্বেও সঙ্গে যাচ্ছে, দেখলে রাগ করবেন।
তারপরে?
ডাক্তারবাবু দরজা খোলা রেখেই ঢুকে গেলেন, ফলে সাকিমও আর এগোতে পারল না।
কেন?
ডাক্তারবাবুর কড়া নির্দেশ। দরজা খোলা থাকলে কেউ বারান্দায় উঠবে না। অনেক দিন ধরেই এইরকম।
বেশ। তারপর?
গেটের কাছে একটা বসার জায়গা আছে, সাকিম সেখানে বসে ছিল সারা দুপুর। ডাক্তারবাবু বেরোননি। দুপুরের আউটডোরের জন্য ডাক্তারবাবুকে ডাকতেও গেছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু সাড়া দেননি। সাকিম পি–এইচ–সি–তে ফিরে সবাইকে জানিয়েছিল। সাকিম, রাশেদ, ভোলা, সবাই ডাকতে গেছিল। কেউ সাড়া পায়নি। ফার্মাসিস্ট ছুটিতে, তাই ওরা নার্স বুলাদিকে জিজ্ঞেস করেছিল কী করা? বুলাদি বলেছিল, কিছু করতে হবে না। ডাক্তারবাবু তো বাচ্চা নন, যখন ডিউটিতে আসার, ঠিকই আসবেন।”
অরিন নার্সের ইউনিফর্ম পরিহিতা মহিলার দিকে ফিরে বলেছিল, “আপনি নার্স? আপনার আক্কেলটা কেমন? লোকটা অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোল, অজ্ঞান হয়ে গেছেন কি না, সেটাও আপনার মাথায় এল না?”
নার্স এমনিতেই কেঁদেছিলেন। চোখ ফোলা। অরিনের বকুনি খেয়ে হাউহাউ করে কেঁদে বললেন, “স্যার আমাকে কী বকাই না বকেছিলেন – তখন আমি সদ্য জয়েন করেছি। একদিন এই নাসিররা কেউ ছিল না, কেস এসেছে বলে আমাকেই ডাকতে যেতে হয়েছিল। আমি তো জানি না। বাইরের দরজা খোলা দেখে ঢুকে গেছি। স্যার বলেছিলেন আর কোনও দিন হলে আমাকে চার্জশিট করে দেবেন।”
বিড়বিড় করে, “তাই বলে অসুস্থ লোকটার কেউ খোঁজ–ও নেবে না? বুদ্ধির ঢেঁকি!” বলে অরিন আবার ফিরল সাকিমের দিকে। “তারপরে কী হল? কখন কারওর খেয়াল হল যে লোকটার খোঁজ নিতে হবে?”
সাকিম, নাসির, রাশেদ, ফতিমা, আসুরা, ভোলা সবাইকে জিজ্ঞেস করে বোঝা গেল যে সারা সন্ধে, সারা রাত, ডাক্তারবাবুর ঘরে আলোর রোশনি দেখা যায়নি। ওরা অনেক রাত অবধি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেছিল যে কারওর যদি ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঢোকার অধিকার থাকে তবে সে কেবল গ্রামপ্রধানের। তাই পরদিন ভোরে গিয়ে প্রধানের বাড়িতে সব কথা বলে। তখনই প্রথমে প্রধানের ছেলেরা, পরে প্রধান স্বয়ং আসেন, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যায়নি। বাড়িতে সবই রয়েছে, ডাক্তারবাবুর বই খাতা, জামা–কাপড়, মায় জুতো–চটি পর্যন্ত। কিন্তু ডাক্তারবাবু নেই।
“জুতোও রয়েছে? ঠিক বলছ?”
সাকিম হাতজোড় করে বলল, “আঁজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ভুল হবে কী করে? ওনার তো দুটোই জুতো। মানে ওই হাসপাতালে আসার কাবলি, আর বাড়ির চটি। দুটোই রয়েছে। বাইরের ঘরে জুতো, শোবার ঘরে চটি। আর দু–জোড়া ছেঁড়া জুতো, পরতেন না। সে–ও রয়েছে…”
“বোঝাই যাচ্ছে…” বলে অরিন উঠে দাঁড়াল। বলল, “বাড়ি কি খোলা রয়েছে?”
খোলাই আছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তালাই নেই।
অরিন সঙ্গের পুলিশদের নির্দেশ দিল, “ক্রাউড ডিসপার্স করো। সবাই যে যার বাড়ি যাক। কিন্তু গাঁ ছেড়ে যেন না যায়।” প্রধানের দিকে চেয়ে বলল, “আপনারাও। এখানে আর থেকে লাভ নেই। এটা এখন পুলিশের তদন্ত। বাড়িতে যান, গ্রাম ছেড়ে যাবেন না।”
চারজন পুলিশের সঙ্গে অরিন আর ওরা তিনজন রওয়ানা দিলেন প্রতিমের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে অরিন বলল, “প্রধানটা মহা চালু।”
নীল বলল, “হতে পারে। কিন্তু ওর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?”
অরিন বাড়িটা দেখিয়ে বলল, “ওই যে, বাড়ি – ওটাই উদ্দেশ্য হতে পারে।”
সপ্তক বললেন, “কিন্তু ওরা কিন্তু প্রতিমকে আজীবন ওখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিল।”
অরিন বলল, “আপনাকে সে কথা কে বলেছিল? ওরা, না ডাক্তারবাবু?”
সপ্তক যুক্তিটা বুঝলেন। বললেন, “এ বাড়িতে প্রধানের মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বাড়িটা ওদের কাছে না–পাক। এখানে ওরা কেউ থাকতে রাজি নন। আর এ গ্রামের কেউ ওখানে থাকবে না। বাড়ি নিয়ে ওরা করতই বা কী?”
কথা বলতে বলতে ওরা বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। দরজাটা হুড়কো টেনে আটকানো। চারিদিকটা দেখে নিয়ে অরিন হুড়কো খুলে দরজা ঠেলে ঢুকল। বাইরের ঘরটা যেমন দেখেছিলেন প্রতিম তেমনই রয়েছে। হ্যারিসনটাও খোলা পড়ে আছে। দরজার পাশে প্রতিমের কাদামাখা স্ট্র্যাপ শু–টা। অরিন রুল দিয়ে পর্দা সরিয়ে বসার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। বলল, “বাপরে!”
অরিন দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে কেউই দেখতে পাচ্ছে না অরিনের কী দেখে চমক লেগেছে। অরিন ভেতরে ঢোকার পরে একে একে সবাই ঢুকলেন। যে ঘরটা কদিন আগে সপ্তক দেখে গেছেন, সেটাই। কিন্তু বাকিদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলেন সেদিন নিজের চেহারাটা কেমন হয়েছিল।
“এ তো লাক্সুরি। সাংঘাতিক ওপিউলেন্স!” পাশ থেকে আঁখির গলা পেলেন।
সপ্তকই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন – বসার ঘর, প্রতিমের ঘর, উনি নিজে যে ঘরে শুয়েছিলেন, খাবার ঘর, রান্নাঘর… পেছনের দরজা খুলে…
“ও, একটা ঘর দেখান’ হল না… তবে ওটা তালাবন্ধ।”
সপ্তকের কথায় অরিন বলল, “কী ঘর?”
সপ্তক বললেন, “প্রতিমের বেডরুমের পরে আর একটা ঘর আছে। আমার মনে ছিল না। ওদিকটা অন্ধকার। ওটা কী, কেন তালামারা, ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। এ বাড়ির সবটাই আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকছিল কি না?”
“কী কী অদ্ভুত জিনিস দেখেছেন, তার একটা লিস্ট মনে মনে তৈরি রাখবেন। পরে লিখে নেব। এবার বলুন তালাবন্ধ ঘর কোন দিকে।”
আবার ফিরলেন। প্রতিমের ঘরের দরজা পার করে করিডোরটা দিনেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সকলেরই মোবাইলে টর্চ জ্বলে উঠল। তালায় আলো ফেলে অরিন বলল, “ও বাবা! এ তালা কবে লাগানো হয়েছিল? খোলা হয়নি তো হাজার বছর। এ খোলা যাবে না। ভাঙতে হবে।”
পেছন থেকে কে বলল, “স্যার?”
একজন বয়স্ক সিপাই। অরিন বলল, “কী বলছেন?”
সিপাই এগিয়ে এসে বলল, “এই ঘরেই প্রধানের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। আমি এসেছিলাম। আমিই দড়ি কেটে বডি নামিয়েছিলাম।”
অরিন ভুরু কপালে তুলে বলল, “সেই জন্যই বন্ধ থাকে? তাহলে হয়ত সেই থেকেই বন্ধ। যাও, গিয়ে প্রধানের বাড়ি থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে এসো। ওরা যদি কেউ আসতে চায়…”
নীল অসহিষ্ণুর মতো বলল, “অরিন, চাবি দিয়ে এ তালা খুলবে না। তার চেয়ে এখনই ভেঙে দেখা ভালো।”
অরিন একটু চেয়ে থেকে বলল, “বেশ। তাহলে দেখা যাক, বাড়িতে, বা বাগানে কোনও কিছু আছে কি না, যা দিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙা যেতে পারে।”
এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে কোদালটা পেছনের জমিতে নীলই পেল। তালার ওপরে কয়েকবার ঠুকে সুবিধা করতে না পেরে হুড়কোর পেছনে ঢুকিয়ে চাড় দিতে হুড়কোটাই আলগা হয়ে এল। তারপরে ঠুকে ঠুকে সবটাই দরজা থেকে আলগা করতে সময় লাগল না বেশি। দরজাটা চেপে আটকে ছিল। অরিন ভারি বুটজুতো শুদ্ধু দড়াম করে লাথি মারতে ছিটকে খুলে গেল। ভেতর থেকে কতদিনের বদ্ধ হাওয়া বেরিয়ে এল দুর্গন্ধযুক্ত। সেই সঙ্গে ধুলো। আর সেই ঘরে…
“মাই গড…” অস্ফূটে বলল অরিন।
থাকতে না পেরে ওখান থেকে দৌড়ে চলে গেল আঁখি। পেছন ফিরে কোনও রকমে বমি আটকালেন সপ্তক।
পেছন থেকে বয়স্ক সিপাই বলল, “ঠিক ওখানেই ঝুলছিল প্রধানের মেয়ের লাশ…”
~এগারো~
সারাদিনের শেষে ক্লান্তদেহে ওদের গাড়িতে তুলে দিল অরিন। বলল, “কেসটা নিয়ে কী করব জানি না। আপনি বলছেন, ওটাই ডাক্তারবাবুর বডি?”
প্রায় পঞ্চাশতম বার যন্ত্রচালিতের মতো সপ্তক বললেন, “ওর হাতে প্রতিমের ঘড়ি। পরনের শার্ট প্যান্টের যতটুকু পচে ঝরে যায়নি, সেটাই ওই দু–দিন ও পরেছিল। ঘড়িটা আমি চিনি। সেদিনও ছিল ওর হাতে। এইচ–এম–টি–র দম দেওয়া ঘড়ি। কলেজের সময়কার। পেছনে ওর নাম লেখা আছে। সেটাও তো আপনি দেখেছেন। যে লিখছিল, প্রতিম লিখতে গিয়ে প্রীতম লিখতে শুরু করেছিল। পরে ঠিক করতে হয়। সেই হিজিবিজিটাও রয়েছে। পি–আর–আই–টি… লেখার পরে আই–কে এ করা, টি–র সঙ্গে মেলানো… ডেডবডির ডান হাঁটুতে মাংস নেই আর। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মালাইচাকি নেই। থার্ড ইয়ারে প্যাটেলেকটমি হয়েছিল। কলেজের মাঠে ফুটবল খেলছিল – নীলকেই ট্যাক্ল্ করতে গিয়ে…”
অসহিষ্ণু সুরে অরিন বলল, “সব বুঝলাম, স্যার। কিন্তু ডেডবডিটা তো আজকের না। অন্তত পাঁচ–সাত–দশ বছরের পুরোনো। ওটা যদি পোস্ট–মর্টেমে ডাক্তারবাবুর বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই এত বছর ধরে কে ফুলপুকুর পি–এইচ–সি–তে ডাক্তারি করল? এটা আপনি ডাক্তার হয়ে, বা আমি পুলিশ হয়ে এক্সপ্লেন করতে পারব?”
হঠাৎ সপ্তক বললেন, “এখানে ডি–এন–এ ম্যাচিং হয়? ইন্ডিয়াতে? আমাদের ওখানে তো রুটিন…”
অরিন বলল, “হয়। কিন্তু রুটিন না। তবে ম্যাচিং কার সঙ্গে হবে? ডাক্তারবাবুর তো কেউ নেই শুনেছি।”
সপ্তক বললেন, “এক দিদি আছে। যোগাযোগ রাখত না, তবে ঠিকানা আছে। বাইরের ঘরে, যে ঘরে আমরা প্রথম ঢুকলাম, সেখানে দরজার অন্য দিকে – জুতোর দিকে না, একটা র্যাক আছে। তার নিচের তাকে একটা বাক্সে দিদিকে লেখা প্রতিমের চিঠি আছে অনেকগুলো। দিদি খুলত না, ফেরত পাঠিয়ে দিত…” বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপরে বললেন, “ফরেনসিক যদি ঠিক করে অ্যাসার্টেন করতে পারে, দেখবেন ওই ডেডবডি ন’বছরের পুরোনো।”
“কী করে বলছিস?” জানতে চাইল আঁখি।
“ওই জুতোর বাক্সে আমার চিঠিও আছে। না–খোলা, খামশুদ্ধু। পড়া চিঠি হয়ত অন্য কোথাও পাবেন। কিন্তু প্রথম না–খোলা চিঠি ন’বছর আগেকার। তার পর থেকে আমার সব চিঠি, না–খোলা – ওই বাক্সেই আছে। দেখবেন তো, দিদিকে লেখা চিঠিও শেষ ন’বছর আগের কি না?”
পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছে অরিন বলল, “স্যার, দোহাই আপনার – আর কনফিউজ করবেন না। এই কেসের কী রিপোর্ট লিখব আমি, ভেবে পাচ্ছি না।”
সপ্তক বললেন, “আমার রিটার্ন টিকিট পরের সপ্তাহে, যদি আর কোনও ইমিডিয়েট কাজ থাকে, হয়ত আরও সপ্তাহখানেক ডিলে করতে পারব। জানাবেন।”
গাড়ি ছেড়ে দিল। অন্ধকার রাস্তায় হেডলাইটের আলোয় চলা, গাড়ির গতি কম। প্রায় বারো কিলোমিটার পরে চওড়া হাইওয়েতে উঠে ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়াতে পারল। ফেরার পথে নীল জোর করে সামনের সিটে বসেছিল। দরজা ভেঙে বহু প্রাচীন ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখার পর থেকে নীল সারাদিন প্রায় কোনও কথাই বলেনি। জোরাজুরি করলে বলেছে, “আই অ্যাম অলরাইট।”
এখন খানিকটা ঘুরে পেছনের সিটে সপ্তকের দিকে ফিরে বলল, “একটা কথা বলি, যদি হাসাহাসি না করিস…”
নীলের মৌনতায় সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল আঁখি। বলল, “না। বল…”
নীল বলল, “প্রতিম কবে, কখন হারিয়ে গেল?”
সপ্তক বললেন, “শুনলি তো। আমি যেদিন ফিরলাম, তার পরদিন। সময়টা তো ঠিক করে এস্টাব্লিশ করা গেল না। তবে সম্ভবত বারোটার কিছু আগে…”
“তখন তুই কী করছিলি?”
হাসলেন সপ্তক। বললেন, “আমিও ভেবেছি কথাটা। ওই সময় নাগাদই স্বস্ত্যয়নটা শেষ হয়েছিল।”
আঁখি বলল, “এদিকে স্বস্ত্যয়ন শেষ হল, আর ওদিকে প্রতিমের শরীর খারাপ, আর তার পরে ওর হদিস পাওয়া গেল না?”
তিনজনে আবার চুপ করে গেলেন। খানিকটা গিয়ে নীল বলল, “ওই সিট–পকেটের প্রসাদটা, যেটা তুই প্রতিমের জন্য নিয়ে এসেছিলি, ওটা কোথায়?”
সপ্তক বললেন, “এখানেই… আমি…”
নীল ড্রাইভারকে বলল, “সামনে মাতঙ্গীর ব্রিজ। ওপরে গাড়ি দাঁড়াতে দেবে না। তুমি ব্রিজে ওঠার আগে সাইড করবে, আমি ছুটে যাব, আর আসব। প্রসাদের বাক্সটা আমায় দে তো…”
গাড়ি দাঁড়ান–মাত্র নীল ছুটে গিয়ে বাক্স থেকে পেঁড়াটা নদীর জলে ফেলে আবার ছুটে এসে গাড়িতে উঠে বলল, “কবে দাহ হবে, কবে অস্থি যাবে নদীতে, আপাতত এটাই হোক।”
গাড়ি চলতে শুরু করল, আঁখি বলল, “তুই স্বস্ত্যয়নের জলের শিশিটা প্রধানের ছেলেকে দিলি?”
ওপর নিচে মাথা ঝাঁকালেন সপ্তক। বললেন, “তখন তো মনেই ছিল না। গাড়িতেই রয়ে গেছিল। থানায় বসে বসে মনে হল। প্রধানের ছেলেকে দিয়ে বললাম ব্যাপারটা কী। বললাম, তুমি নেবে তো নাও, নইলে ফেলে দেব। ও নিয়ে নিল। ওকে এ–ও বলেছি কোনও মৌলবী ডেকে ওদের মতে যা করার যেন করে নেয়। শবনমের কথাটা বলিনি অবশ্য।”
তিনজনেই আবার চুপ করলেন। গাড়ি ছুটে চলল শহরের দিকে।