পূর্বপ্রকাশিতের পর
একটি নতুন স্বাস্থ্যব্যস্থার অঙ্কুরোদ্গম – শতবর্ষ আগে
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের চূড়ামণি জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হেনরি সিজারিস্ট ১৯৩০-এর দশকে সদ্য গড়ে-ওঠা রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, রুশ ভাষা শিখেছিলেন। নিবিড়ভাবে সোভিয়েত স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে লিখলেন সোশ্যালাইজড মেডিসিন ইন দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৩৭)। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য – “পাঁচ হাজার বছর ধরে মেডিসিনের ইতিহাসের জগতে যা অর্জিত হয়েছে তাকে প্রথম যুগ বলা যায় – কিউরেটিভ (সারিয়ে তোলা) মেডিসিনের যুগ। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি নতুন যুগ শুরু হয়েছে – প্রিভেন্টিভ (প্রতিরোধী) মেডিসিনের যুগ।” (পৃঃ ১০৪) এই বইয়েই লিখলেন – “এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা যে সোভিয়েত সিস্টেমের সামাজিক ইন্সিউরেন্স পুঁজিবাদী দেশের যেকোন ইন্সিউরেন্সের চেয়ে অকল্পনীয়ভাবে উৎকৃষ্ট।” লিখলেন – “এটা সম্পূর্ণত নতুন একটি মেডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হচ্ছে এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা। এ হল সোশ্যালিস্ট মেডিসিন … এর জন্য কোন জাতীয়বাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী প্রোগ্রাম সফল করার তাগিদ নেই।” আরও জানালেন – “যে সব স্যানাটরিয়াম এবং হেলথ রিসর্টগুলো আগে কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন ধনীর সুযোগ হিসেবে ছিল সেগুলো সবকটাই সমস্ত মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।” এক অমোঘ সত্যি তিনি তুলে ধরেন – “কেবলমাত্র জনতার স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের বিবেচনায় রাখা হয় এবং এটা বাহ্যত স্পষ্ট যে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব নয় … সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম দেশ যে মেডিসিনকে আক্ষরিক অর্থে সামাজিক চেহারা দিয়েছে, প্রথম দেশ যে জনতার স্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছে।”
সিজারিস্টের বইয়ের ১০ বছর আগে প্রকাশিত আনা হেইনস-এর হেলথ ওয়ার্ক ইন সোভিয়েত রাশিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছিল – “সোভিয়েত মেডিসিনের লক্ষ্য – যে কারণে এটা ফলপ্রসূ – এটা শুধু আরোগ্যের জন্য নয়, অসুখ প্রতিরোধের জন্য। সবার জন্য ইতিবাচক স্বাস্থ্যের জন্ম দেওয়া।” (পৃ; ২২) আরও জানালেন যে যক্ষ্মা-আক্রান্ত সমস্ত নারী-পুরুষ প্রাথমিকভাবে “রাত্রিকালীন স্যানাটরিয়াম”-এর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের কাজের সময়ের বাইরে অন্য সময় কাটাতে পারে। এছাড়া রয়েছে “ফ্রি ডায়েট ডাইনিং রুম” যেখানে ডাক্তারেরা তাদের রোগীদের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত খাবারের জন্য পাঠাতে পারে। এসবের সম্মিলিত ফলে ১৯১৩-তে প্রতি ১০০ জনে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ২৭, ১৯২৩-এ তা হল ১৭। (পৃঃ ২)
রাশিয়ায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে আসার পরে প্রায় হুবহু একই কথা বললেন আরও দুই বিশেষজ্ঞ স্যার আর্থার নিউজহোম এবং জন অ্যাডামস কিংসবেরি তাঁদের রেড মেডিসিনঃ সোশ্যালাইজড হেলথ ইন সোভিয়েত রাশিয়া (১৯৩৮) গ্রন্থে – “বাস্তবিকই, সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ যে দেশের সীমান্তের মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশুর জন্য পরিপূর্ণ প্রিভেন্টিভ ও কিউরেটিভ মেডিসিনের সুযোগ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং কার্যকরী করছে।” (পৃঃ vii)
আমি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শুধুমাত্র ১৯১৭ থেকে ১৯৩৭ সময়কালের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রটিতে সীমাবদ্ধ থাকবো। সিজারিস্ট তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে রাশিয়ার চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে বলেছিলেন – “আমার মনে হয় নীচের ৪টি পয়েন্ট সোভিয়েত স্বাস্থ্যব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করবেঃ (১) মেডিক্যাল সার্ভিসের জন্য কোন খরচ নেই, ফ্রি এবং সবার জন্য লভ্য, (২) সমস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব পায় প্রিভেনশন বা রোগ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা, (৩) সমস্ত স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করে কেন্দ্রীয় সংস্থা – পিপল’স কমিশারিয়েটস অফ হেলথ, (৪) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয় অনেক বড়ো পরিধিতে ভাবা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষা একান্ত আবশ্যিক।”
প্রাক-বিপ্লব (১৯১৭ পূর্ববর্তী) রাশিয়ার স্বাস্থ্যের চিত্র
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে (এখানে ইউরোপ ধরে নিতে হবে) ১৮৪৮-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন (বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে) স্বাস্থ্যের জন্য একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। নতুনভাবে জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আইন-কানুন, সোশ্যাল মেডিসিন এবং এপিডেমিওলজির মতো স্বাস্থ্যের নতুন শাখা তৈরি হল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল মেডিসিনের দর্শনের জগতে – নতুন করে বিশিষ্টতা পেলো প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বা আগাম রোগ-প্রতিরোধের বিষয়। টমাস কুনের অনুসরণে বলা যায় মানুষের গণ আন্দোলন এবং স্বাস্থ্যের দাবীতে সোচ্চার হওয়া মেডিসিনের দর্শন ও ভাবনার জগতে একটি “প্যারাডাইম শিফট” ঘটালো – বেড সাইড মেডিসিনকে অতিক্রম মেডিসিন এলো জনসমাজে এবং জনস্বাস্থ্য একটি আলাদাভাবে চিহ্নিত অবস্থান হল।
এগুলো যখন ইউরোপের অগ্রণী দেশগুলোতে চলছে তখন জারের রাশিয়ায় এর কোন প্রভাবই প্রায় পড়েনি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু পদক্ষেপ ওখানে নেওয়া হয়েছিল – যেমন, “মেডিক্যাল স্যানিটারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন” তৈরি হয়েছিল ১৮২০ সালে, স্মল পক্সের জন্য শিশুদের বাধ্যতামূলক টীকাকরণ চালু হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, “রাশিয়ান ফার্মেসি সোসাইটি ফর মিউচ্যুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স” জন্ম নিল ১৮৯৫ সালে। হাওয়ার্ড লিখটার জারের রাশিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে “আতঙ্কজনক” বলেছেন। লিখটার তাঁর গ্রন্থ এ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ টু পলিসি অ্যনালিসিসঃ হেলথকেয়ার পলিসি ইন ফোর নেশনস (১৯৮০)-এ বলছেন – “রাশিয়ার এক সুবিশাল অংশে কোন ধরনের মেডিক্যাল ব্যবস্থাই চূড়ান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল।” সেসময়ে রাশিয়ার মানুষদের চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৯১ কোপেক যা বর্তমান হিসেবে প্রায় ৯৫ পয়সা। রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রতি ৫৬৬৫ জন মানুষের জন্য ১ জন ডাক্তার ছিল, এবং প্রতি ১০০০ জনের জন্য ১টি হাসপাতাল বেড ছিল। গ্রামাঞ্চলে ওষুধের দোকান প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ১৯১৪ থেকে ১৯২০-র মধ্যে যে সমস্ত ডাক্তারদের জোর করে মিলিটারিতে নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ১০,০০০ জন মারা যায়।
ভৌগলিকভাবে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ (৮০ লক্ষ কিলোমিটার) জুড়ে বিস্তৃত রাশিয়ার ভূখণ্ডে বাস করতো প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি মানুষ – ১২.৯% ভাগ মানুষ শহরাঞ্চলে, ৮৭% গ্রামাঞ্চলে। এদের সবার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বলশেভিক সরকার – সেসময়ের বিশ্বে (এখনও কি নয়?) যা অকল্পনীয়, অভাবিত এবং অভূতপূর্ব।
প্রসঙ্গত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে মস্কোর জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ থেকে কমে ৯০০,০০০ হয়ে যায়। পেত্রোগ্রাদে ২০ লক্ষ থেকে কমে ৬০০,০০০। ১৯১৩-র হিসেব বলছে নবজাত শিশুদের ৫০% অবৈধ এবং রাশিয়ার মানুষের সেসময়ে গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৩২ বছর। সমগ্র রাশিয়া জুড়ে স্বাস্থ্যের প্রধান সমস্যা ছিল – যৌন রোগ, টাইফাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, চোখের রোগ ট্র্যাকোমা, প্লেগ, স্মল পক্স, কলেরা এবং ম্যালেরিয়া। ১৯১৩-র আরেকটি হিসেব বলছে সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের ৪% মানুষ মদ্যপ ছিল। ১৯১৪ সালে সিফিলিস বা গনোরিয়ার মতো যৌন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। সেনাবাহিনীতে যারা কাজ করতো তাদের ১০% যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিল। ভ্লাদিমির রেশেৎনিকভ এবং অন্যান্যরা তাদের গবেষণাপত্র “দ্য হিস্টরি অফ পাব্লিক হেলথকেয়ার ইন রাশিয়া”-তে জানাচ্ছেন – “সমগ্র ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের স্যানিটারি অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপের মধ্যে একটি। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে ১,০০০,০০০-এর বেশি মানুষ টাইফাস মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছিল। ১৯১৫ সালে নথিভুক্ত মহামারিজনিত রোগীর সংখ্যা ৮০০,০০০। এর মধ্যে ১৭৮,০০০ জন টাইফয়েড এবং ৪৩,০০০ কলেরা রোগী। ১৯০৯-এ স্মল পক্সে মৃত মানুষের সংখ্যা ৩২,০০০। সবমিলিয়ে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ২৫-৩০ জন। গড় আয়ুষ্কাল ছিল মোটামুটি ৪০ বছর। প্রতিবছর যে ৬০,০০,০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করতো তাদের মধ্যে ২০,০০,০০০ মারা যেত বিভিন্ন অসুখে এবং অপুষ্টিতে। ১৯শ শতকের শেষে এবং ২০শ শতকের গোড়াতে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০ শিশুতে ২৫০ জন। ১৯১০-এ প্রতি ১০০০-এ গড় মৃত্যুর হার ফ্রান্সে ১৭.৭, গ্রেট ব্রিটেনে ১৩.৫, জার্মানিতে ১৬.২ এবং আমেরিকাতে ১৫.৯।। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরে সরকারি বিভিন্ন নীতি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখে পড়ে সরকার ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬-তে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ হেলথ তৈরি করে। সঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া হয় এটা সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের (মিনিস্ট্রি অফ হেলথ) আদিরূপ।”
১৯০৫ থেকে নারী ও শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ১৯১৪ সালে কম-উন্নত কারখানাগুলোতে ৭৫% শ্রমিক ছিল নারী ও শিশু।
চলবে



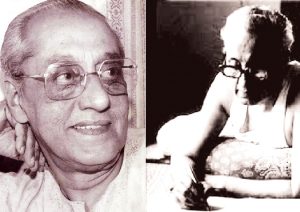
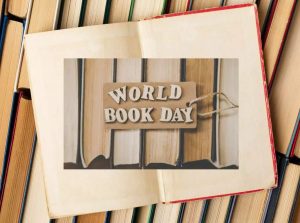
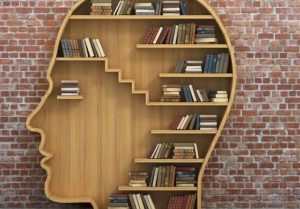








Wonderful sir
Very informative write up
your writing is appreciatable what knocks to everyone. well done keep it up.
খুবই ভালো লাগল। রচনাটি পড়ে অনেক অজানা বিষয় জানা গেল এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থিত হল যে ভারতবর্ষে রাশিয়ার মতো এই রকম পরিবেশ, এই রকম ব্যবস্থা কি কোনোদিন আসবে?
. very nice writing. well done.
keep it up.
চমৎকার।
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাক বিপ্লব স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিত্রটি পরিষ্কার করে বর্ণিত হয়েছে।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ধরণের চিত্র বর্তমান বিশ্বের বেশ কিছু দেশে আজও বর্তমান কিছু আধুনিক মুখোস পরে।
পরের পর্বর জন্য রইলাম।
ধন্যবাদ ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য।
Khub bhalo lekha. Eye opener
Enjoying reading.
অনেক নতুন বিষয় জানলাম। খুব ভালো লেখা।