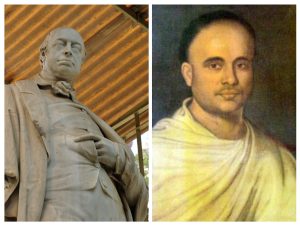মেডিক্যাল কলেজ ভাঙা হবে। কানাঘুষোও শোনা যাচ্ছে গোটা এম.সি.এইচ. বিল্ডিং–টাই ভেঙে নতুন মডার্ন বাড়ি তৈরি হবে, কুড়ি তলা। ছাত্র–ডাক্তার মহলে অসন্তোষ। কিন্তু কি হবে তা তো আর কেউ জানে না, তাই কেউ কিছু বলছে না। এস. এফ. আই. মেম্বাররা, একটা সবজান্তা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে : আমরা সব জানি। কী হয়েছে? পুরোনো জিনিস ভাঙা তো হবেই, না হলে নতুন আসবে কোত্থেকে? অঙ্কন একদিন বলল, “এম. সি. এইচ. ভাঙবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হবে, দেখে নিস।” ওকে বললাম, “তা তো বলবিই। তোদের ওই ওঁচা পার্টি হেরিটেজ মানে জানে না। তোদের যেমন কোনও হেরিটেজ নেই, তেমনি তোরা হেরিটেজকে সম্মান করতে জানিস না। যা মনে হবে তা–ই ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও করবি। আর যদি দেখিস জনমত উল্টোদিকে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিবি… ওরে, চললি কোথায়, ভস্মীভূত মানেটা জেনে যা…”
অঙ্কনের বাঙলা শেখার কোনও আগ্রহ নেই, চলে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অজিতের সঙ্গে গেছি ওয়ার্ড রাউণ্ডে। সেই বিশাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মন খারাপ লাগছে। যদিও জানি এই সবটাই আজকের দিনের নিরিখে জায়গার প্রচণ্ড অপচয় – এক একটা ফ্লোরে আজকের হিসেবে আড়াইটে থেকে তিনটে ফ্লোর হবে, ছাদই তিরিশ ফুটের ওপরে উঁচু।
একতলা দোতলা শেষ করে গেছি রুফটপ ওয়ার্ডে। স্থানাভাবের জন্য ছাদের ওপরে কোনওরকমে ইঁটের দেওয়াল, অ্যাসবেসটসের ছাদ। ফলস–সিলিং এত নিচু যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। গরমকালে এখানে রোগি সারার বদলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে না কেন, কে জানে। অজিতকে বললাম, “এই রকম ওয়ার্ডে মানুষ থাকতে পারে? নতুন হলে ভালোই হবে, বল?”
অজিত পেশেন্ট ফাইলে কী লিখতে লিখতে আড়চোখে চেয়ে বলল, “হঠাৎ? এস.এফ.আই–য়ে নাম লিখলি নাকি?”
বললাম ওকে, অঙ্কন কী বলেছে।
অজিতের হাত থেকে কলমটা প্রায় পড়ে গেল। “তাহলে সত্যিই ভাঙছে? তা না হলে অঙ্কন এ কথা বলল কেন?”
আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তাই সারা সন্ধ্যা কাজে মন দিতে পারছিলাম না।
রুফটপ ওয়ার্ডে কাজ শেষ হওয়া মানে দিনের কাজ শেষ। সাধারণত রাস্তা পেরিয়ে কুমার্স ক্যান্টিনে গিয়ে চা খাওয়া হয় একটা। আজ আর ভালো লাগছে না। অজিত আর আমি বেরোতে গিয়ে হঠাৎ অজিতের কী মনে হল, বলল, “দাড়ি, মেডিক্যাল কলেজের তিনকোনা ছাদটার ওপরে উঠেছিস কখনও?”
কখনও উঠিনি। বললাম, “চ, এই দিক দিয়ে আয়।”
দুজনে গিয়ে দাঁড়ালাম মেডিক্যাল কলেজ বিল্ডিং–এর তিনকোনা ছাদের ওপরে। যদিও তিনতলা বাড়ি, কিন্তু প্রায় ছ’সাত তলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। নিচে ছোটো ছোটো মানুষ। ওই যে অঙ্কন, ওই যে অংশুমান যাচ্ছে। সঞ্জয় এদিক দিয়ে যাচ্ছে কেন? রথিন–সর্বাণীর কাজ শেষ – দু’জনে সিনেমা চলল বোধহয়।
একটু অপেক্ষা করে মনে হল, আরে, আজ–বাদে–কাল এই বাড়িটা থাকবে কি না, জানাই নেই, আজ আমরা তার সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি, এই কথাটা লোকজনকে না জানালে কি চলবে? ব্যস, যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ, ওখান থেকে দাঁড়িয়েই আমি আর অজিত হাঁক পাড়তে লেগেছি : “অ্যাই সুমন্ত্র। ওরে হতভাগা বিশু! এসপি, আসবি নাকি? নভ্রতন, কুমার্স ক্যান্টিন যাচ্ছিস? না? কলেজ সুইটস? আমাদের জন্য দু প্লেট রসমালাই অর্ডার কর। আসছি।”
লোকেও তাদের চলার পথে দাঁড়িয়ে আমাদের পাগলামি দেখে হাসাহাসি করছে, কেউ কেউ আমাদের নানারকম জ্ঞানও দিচ্ছে। হঠাৎ ওখান দিয়ে যাচ্ছে ফ্যাটি–দা (ফ্যাটি–দাকে প্রথম দেখে বলেছিলাম, “ওর নাম ফ্যাটি যারা দিয়েছে তাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।” তাই শুনে ফ্যাটি–দার কে এক বন্ধু বলেছিল, “তুই তো সেই সময়ে দেখিসনি, তাই বলছিস।” যাই হোক, বলার বিষয় যেটা সেটা হল যে ফ্যাটি–দা রোগা না হলেও নামের সঙ্গে কোনও মিলই নেই)।
ফ্যাটি–দা আমাদের ওইরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খানিকক্ষণ চুপ করে কোমরে হাত দিয়ে ওপরে তাকিয়ে রইল। তারপর হেঁটে চলে গেল হস্টেলের দিকে।
পরে যখন যথেষ্ট মন ভালো হয়েছে, কুমার্স–এ চা খেয়ে হস্টেলে ফিরেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজা খুলতে যাব, ফ্যাটি–দা এসে ধরেছে।
“বলি ব্যাপারটা কী? সাহস খুব? ওই ভাঙা বাড়ি, তার মাথায় চড়েছ। সবসুদ্ধু যদি পড়ত, কী হত?”
দরজা খোলা স্থগিত রেখে বললাম, “কী আর হত, দাদা, ভেতরে থাকলে যা হত তার থেকে হয়ত ভালই হত। আর বিপদ তো তোমাদের বেশি হত। ভেঙে পড়লে তোমাদের মাথায় পড়ত, আমাদের মাথায় তো আর পড়ত না, বাড়ি তো আমাদের পায়ের তলায়।”
ফ্যাটি–দা খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।
খানিক পরেই নির্মল এসেছে আমার ঘরে। “কীরে? ফ্যাটি–দাকে কি বলেছিলি?”
আমি ঘাবড়ে গেলাম। “কেন? রেগে গেছে নাকি?”
“না না, রাগবে কেন? আমার সঙ্গে দেখা হতে বলে গেল, দাড়িকে বেশ বোকা–সোকা ভাবতাম, দেখলাম ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।”