“সিস্টেম – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক সিস্টেম – আমার এবং বাকিদের মাঝখানে মাথা গলায়। “অপর” যদি বঞ্চিত হয়, সেই বঞ্চনার কারণ “সিস্টেম” – সে সিস্টেমে আমি অংশগ্রহণ করি, কেননা আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে – যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করি না, কেননা সিস্টেম যেহেতু, অতএব এ নিশ্চিত অপরিবর্তনীয়। একদিকে এই সিস্টেমের কদর্যতা, আরেকদিকে সেই একই সিস্টেমে আমার অংশগ্রহণ – দুটোকে একইসাথে স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে।”
বার্নেট বাইস্ট্যান্ডার্সের “কনশায়েন্স অ্যান্ড কমপ্লিসিটি ডিউরিং দ্য হলোকস্ট” বইয়ে উপরের অংশটুকু পাবেন (তর্জমা আমার)। নাৎসী জার্মানী, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, হলোকস্ট এই প্রসঙ্গে কথাগুলো বলা।
কিন্তু, একটু ভেবে দেখলে, এই কথাটা কি আরো বৃহত্তর প্রেক্ষিতেও একইভাবে সত্যি নয়?
আমরা মেনে নিয়েছি “সিস্টেম”-কে – যে সিস্টেমে সমাজের পাঁচ শতাংশের হাতে থাকতে পারছে পঁচানব্বই শতাংশ সম্পদ, যেটা আমাদের কাছে অন্যায্য বা আশ্চর্য বলে বোধ হচ্ছে না – এবং মেনে নিয়েছি উন্নয়নের এমন মডেল, যাতে এই পরিস্থিতির উন্নয়নের শেষে দুই শতাংশের হাতে আটানব্বই শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হতে পারবে – আশা রেখেছি, উপরের দুই শতাংশ প্রভূত সম্পদশালী হয়ে উঠলে সে বিত্ত চুঁইয়ে আসবে নীচের আটানব্বই শতাংশের ঘরেও।
স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও তা-ই। আমরা “সিস্টেম” বলে মেনে নিয়েছি এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে চিকিৎসা কিনে নিতে হয় – যার যেমন টাকা, সে তেমন মানের চিকিৎসা কিনতে পারবে – এবং, যিনি কপর্দকহীন, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ মানুষ, তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা হবে না। এই নিয়ম, বা এই ব্যবস্থাকে আমাদের আর অদ্ভুত বা অন্যায় বলে মনে হয় না – উল্টে একেই প্রায় প্রকৃতির নিয়মের সমতুল ও অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা এসেছে – এমনকি চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের মধ্যেও।
অতএব, চিকিৎসকরা, যাঁরা কিনা এই সিস্টেমের কদর্যতা সবচেয়ে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করছেন – অথবা আমজনতার অধিকাংশ, যাঁরা এই সিস্টেমের সরাসরি শিকার – উভয়পক্ষই এই সিস্টেমকে অনিবার্য, প্রায় ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। বাড়তি সমস্যা, এই “সিস্টেম” খুব সচেতনভাবেই উভয়পক্ষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে এবং দুই পক্ষকে যুযুধান প্রতিপক্ষ হিসেবে ময়দানে দাঁড় করাচ্ছে। দোষারোপ ও গালিগালাজের ঝাপসা বাস্তব পার হয়ে “সিস্টেম”-টা বদলানোর কথা কেউই ভাবছেন না।
অথচ, এই সিস্টেম নিছক মনুষ্যসৃষ্ট – সুতরাং পরিবর্তনীয়। বিশেষত, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিশ্বাস রাখলে, এ “সিস্টেম” অপরিবর্তনীয়, এমন ভাবার তো কোনো কারণই নেই – উল্টে, যে “সিস্টেম” সমাজের গরিষ্ঠ অংশের স্বার্থের পরিপন্থী, সেই সিস্টেম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় টিকিয়ে রাখতে পারা-ই তো বিস্ময়কর।
আমরা সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মের বা ন্যাচারাল সিস্টেমের বশ। অর্থাৎ, বয়স বাড়লে কিছু অসুখবিসুখ অনিবার্য। সাধারণ সংক্রামক অসুখে মৃত্যুর সংখ্যা কমে গেলে মৃত্যুর মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায় অসংক্রামক ব্যাধি। এ নিয়ম বদলে ফেলা মোটামুটি অসম্ভব।
আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে রোগব্যাধির ধরণে বদল এসেছে। জীবনযাত্রার সাথে যুক্ত অসুখের সংখ্যা বেড়েছে। জীবনযাপনকে খানিকটা বদলে অসুখের এই ধাঁচটার কিছু পরিবর্তন সম্ভব হলেও পুরোপুরি বদলে দেওয়া হয়ত অসম্ভব। একে প্রাকৃতিক সিস্টেম ও নাগরিক সভ্যতার বিকাশের অঙ্গ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
কিন্তু, এর বাইরে রয়ে গিয়েছে মানুষের তৈরী এই আর্থসামাজিক সিস্টেম। এমন “সিস্টেম”, যেখানে, অনেক অসুখবিসুখের প্রধান কারণ আর্থিক অসাম্য, কাজ হারানো, খেতে না পাওয়া, সময়ে চিকিৎসা না পাওয়া। সমস্যা, আগেই যেকথা বললাম, এই সিস্টেমটিকেও প্রাকৃতিক সিস্টেমের মতো স্বাভাবিক বলে মেনে নিলে বা মেনে নেওয়ানো গেলে অসুখ-বিসুখের এই বড় কারণগুলো নজরের বাইরে রয়ে যায়। এবং চিকিৎসকের দায় যে অসুখের চিকিৎসার পাশাপাশি এই আর্থসামাজিক বিষয়গুলো নিয়েও সোচ্চার হওয়া, এই দায় ভুলিয়ে দেওয়া যায়।
আমরা জানি, “সিস্টেম” নিজের মতো করে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়েপিটে নেয়। প্রয়োজনমতো ইতিহাসের পাঠ বদলে দেওয়ার কথা তো সকলেরই জানা আছে। মেডিকেল শিক্ষাও তেমন রদবদল প্রকল্পের বাইরে নয়। অতএব, অসুখ-বিসুখের কারণ হিসেবে আর্থসামাজিক সমস্যাগুলোকে ভাবার প্রবণতা নবপ্রজন্মের চিকিৎসকদের মধ্যে বেশ কম – কেননা, তাঁদের পাঠক্রম থেকে এই ধরনের ভাবনাগুলো ক্রমেই কমিয়ে আনা হয়েছে – এবং দেশকালনিরপেক্ষ একটি আপাত-সর্বজনীন মেডিকেল কারিকুলাম জারি হয়েছে। “সর্বজনীন” শব্দটি এক্ষেত্রে ইদানিংকালের ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মতো – আদতে কর্মকর্তাদের বাইরে বাকি সর্বজনের অংশগ্রহণ ওই দর্শক হিসেবেই। অর্থাৎ, দেশকালের ভেদাভেদ ভুলিয়ে এই সর্বজনীন মেডিকেল শিক্ষা ও তার প্রয়োগের সুফল পান শুধুমাত্র আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষেরা – বাকিদের জন্যে, ওই, চুঁইয়ে আসার আশা।
সাধারণ একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন ধরুন, ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যে কেমোথেরাপি – প্রথম বিশ্বের অনুসরণে এখানেও ডে-কেয়ারেই দেওয়া হয়ে থাকে – কেননা, তেমনটাই “নিয়ম”। প্রথম বিশ্বের স্বচ্ছল নাগরিক – যাঁর আবাস থেকে ডে-কেয়ারের দূরত্ব হয়ত আধঘন্টার – এবং তৃতীয় বিশ্বের কপর্দকহীন অপুষ্টিতে ভোগা হতদরিদ্র, যিনি একঘণ্টা হেঁটে বা সাইকেলভ্যানে চড়ে রেলস্টেশনে পৌঁছে আড়াই কি তিন ঘণ্টার রেলযাত্রার শেষে কেমোথেরাপি নিতে হাজির হতে পারলেন, এবং ফিরবেনও একই পথে ওই একই দিনে – ডাক্তারির পাঠ শেখাচ্ছে, নিয়ম সকলের জন্যে এক – এবং এটাই সিস্টেম।
বিষয়টা এমন নয়, যে, চাইলেই আমরা সব সমস্যার নিরসন করে ফেলতে পারি। যেমন ধরুম, কেমোথেরাপি যাঁরা নিচ্ছেন, চাইলেও তাঁদের সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করে রাখা সম্ভব নয়। যেদেশে নাগরিকপিছু হাসপাতালে বেডের অনুপাত এতখানি কম, সেদেশে এমন করে ভাবতে চাইলেও কিছু করে ওঠা মুশকিল। কিন্তু, এই সমস্যাটা তো আলোচনায় আসা জরুরী। অথচ, হপ্তায় হপ্তায় প্রায়শই ক্যানসার-চিকিৎসার নিত্যনতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের যে আদানপ্রদান চলতে থাকে পাঁচতারা অডিটোরিয়ামে, ক্যানসারের আধুনিক চিকিৎসার খুঁটিনাটি নিয়ে এত কথা হয় – সেখানে কদাপি এই যে ডে-কেয়ার কেমোথেরাপি সিস্টেম, প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থার যাথার্থ্য নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। আসলে, আলোচনা তো দূর – সিস্টেমের এমন অনির্বচনীয় গুণ, এই কথাগুলো নিয়েও যে ভাবা যেতে পারে, এই চিন্তাটা মাথাতেই আসতে পারে না।
ঠিক যেমন করে এই শিক্ষাব্যবস্থার উজ্জ্বল কিছু ফসল পাঁচতারা হাসপাতালে “আন্তর্জাতিক মান”-এর চিকিৎসা দেওয়ার মুহূর্তে ভাবতে ভুলে যান – তাঁদের চিকিৎসা আন্তর্জাতিক হোক বা না হোক, দেশনিরপেক্ষ তো বটেই – কেননা, সে চিকিৎসা বা চিকিৎসাভাবনা দেশের বৃহত্তর অংশের বাস্তবতা থেকে বহুদূরে। তাঁদের ভাবনাতে সচরাচর এই প্রশ্ন আসতে পারে না, তাঁদের হাসপাতালের দরজা ঠেলে যাঁরা আসছেন তাঁরা দেশের কত শতাংশের প্রতিনিধি। এবং এই দেশটির যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সুদূর স্বপ্নেও তাঁদের চৌকাঠে পা রাখার কথা ভাবতে পারে না – কেন পারেন না? হতদরিদ্র কোনো পরিবারের সন্তান হয়ত এমন হাসপাতালের উন্নত পরিকাঠামোর সুযোগ পেলে বেঁচে যেতে পারত – কিন্তু, ওরকম ভাবার পথ সে হতভাগ্যদের নেই। কেন নেই? কেন থাকবে না??
কর্পোরেট হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসা করেন, তাঁদের মনে এসব প্রশ্ন হয়ত আসে – এলেও স্থায়ী হতে পারে না – আসে, এবং হারিয়ে যায়। কেননা, তাঁদের হাসপাতালের কাচের দরজা ঠেলে যাঁরা ঢুকতে পারেন না, তাঁরা নেহাতই “অপর” – বহুদূরের এবং অদৃশ্য “অপর”। কেননা, কখনও কখনও এই ব্যবস্থা স্বস্তিকর বোধ না হলেও, এই চিকিৎসকরা জানেন ও মানেন, এটাই সিস্টেম। এবং “সিস্টেম” অপরিবর্তনীয়।
এতদূর এসে শুরুর কথাগুলো আরো একবার পড়ে নেওয়া যাক।
“সিস্টেম – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সিস্টেম – আমার এবং বাকিদের মাঝখানে মাথা গলায়। “অপর” যদি বঞ্চিত হয়, সেই বঞ্চনার কারণ “সিস্টেম” – সে সিস্টেমে আমি অংশগ্রহণ করি, কেননা আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে – যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করি না, কেননা সিস্টেম যেহেতু, অতএব এ নিশ্চিত অপরিবর্তনীয়। একদিকে এই সিস্টেমের কদর্যতা, আরেকদিকে সেই একই সিস্টেমে আমার অংশগ্রহণ – দুটোকে একইসাথে স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে।”
সুতরাং, কর্পোরেট হাসপাতালের তকতকে ওপিডিতে বসে ঝকঝকে ডাক্তারবাবুর মনের গভীরে যদি কখনও প্রশ্ন জাগে, যে, তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োগের সুবিধে কেন পেতে পারবেন না দেশের বেশীর ভাগ মানুষ – এমনকি, তিনি যাঁদের চিকিৎসা করছেন, তাঁদের তুলনায় যাঁরা তাঁর সামনে পৌঁছানোর সুযোগ পেলেন না, তাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ত বেশী বই কম না – যদি কখনও মনে আসে পাঁচতারা হাসপাতালের বিল নিয়ে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন, যেমন একই পরীক্ষার মূল্য বেড বা কেবিন অনুসারে বেশী-কম হবে কেন – চিকিৎসক আর রোগীর মাঝে এমন করে মাথা উঁচিয়ে থাকে “সিস্টেম”, যে, চিকিৎসক শুধু সেটিই দেখতে পান – অর্থাৎ তিনি দেখতে শিখে যান, এই-ই “সিস্টেম” এবং সিস্টেম নিয়ে বেশী প্রশ্ন করে বিশেষ লাভ নেই – আর সিস্টেমে নিজের ভূমিকা নিয়ে প্রথম প্রথম কিছু অস্বস্তি থাকলেও ওটুকু কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না।
উল্টোদিকে, রোগীপক্ষ তথা সাধারণ নাগরিকের মুশকিল এই, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সিস্টেমের শিকার হচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না নাগরিক থেকে পেশেন্ট বা পেশেন্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, ততোক্ষণ অব্দি এই “সিস্টেম”-কে মেনে নেওয়া নিয়ে আপত্তির কিছু দেখতে পান না। কিন্তু, তিনি-ই আবার যখন প্রত্যক্ষত সিস্টেম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তখন আর “সিস্টেম” নয়, দেখতে থাকেন চিকিৎসকেরই মুখ – ক্ষোভ রাগ ঘৃণার লক্ষ্য হন সেই চিকিৎসক-ই।
নাৎসি আমলে একজন কর্মচারীর জবানবন্দী পড়ছিলাম। তাঁর কাজ ছিল, ইহুদি-ভরা ট্রেনগুলোকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর কাছে এই কাজ অনুচিত মনে হয় নি, কেননা, এটাই ছিল “সিস্টেম” এবং কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে সেই ইহুদিদের কী পরিণতি হত, সে নিয়ে তাঁর ভাবার কথা নয়, এবং সে বিষয়ে তাঁর নাকি কোনো দায়ই নেই।
মানেন এই যুক্তি?
“সিস্টেম” তো আকাশ থেকে পড়ে না। এমন অনেক টুকরো অংশ মিলে তবেই খাড়া হয় সিস্টেম – নাৎসি আমলের ওই কর্মচারীর মতো নাটবল্টু হয়ে সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখি আমরা সকলেই।
চিকিৎসা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে, এই সিস্টেমকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন চিকিৎসাকে ক্রেতা সুরক্ষা বিধির আওতায় এনে – এবং, সে নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে থেকে অল্পবিস্তর বিরোধিতা এলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে সেরকম কোনো প্রতিবাদ আসেনি। চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেও যে বিরোধিতা এসেছিল, তার মধ্যে বড় যুক্তিটি ছিল চিকিৎসার মতো পেশার পক্ষে এমন আইনের প্রয়োগ অবমাননাকর। চিকিৎসা যে ক্রয়যোগ্য পণ্য হতেই পারে না, এমন কথা জোরগলায় বলে ওঠার লোক বেশ কম। কিন্তু, সরকারবাহাদুর ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায় এনে স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে বাজারের আর পাঁচটা মালের সাথে সমান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দিলেও চিকিৎসা যে ক্রয়যোগ্য পণ্য, এ ধারণা চালু হতে শুরু করেছিল তার আগেই, সরকারি সিদ্ধান্ত স্রেফ সীলমোহর মাত্র। যেমন কড়ি ফেলা হবে, তেমন চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে, এমত ভাবনা “সিস্টেম”-এ পরিণত হতে শুরু করেছিল আগে থেকেই – চিকিৎসক বা সাধারণ মানুষ, এই ভাবনায়, মূলগতভাবে, কেউই সেভাবে আপত্তি করেন নি।
এখনও লড়াই প্রতিবাদ আপত্তি যেটুকু জারি আছে, সে ওই সিস্টেমকে শিরোধার্য করেই – অর্থাৎ, বিল বেঁধে দেওয়া যায় কি যায় না, প্যাকেজ অতিক্রম করে আরো অর্থ আদায় করা অনুচিত কিনা, সরকার গরীব মানুষের চিকিৎসার বিল মেটাবেন কি মেটাবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চিকিৎসাব্যবস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁরা কথা বলছেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই এই সিস্টেমের মধ্যে থেকেই যুক্তি সাজিয়ে চলেছেন।
চিকিৎসকেরা – যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া তো দূর, কোনো স্বাস্থ্যপরিষেবাই সম্ভব নয় – তাঁদের একাংশ “সিস্টেম”-এর সক্রিয় সমর্থক। কিন্তু, আরো একটা বড় অংশ এই “সিস্টেম”-কে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও, এমনকি “সিস্টেম”-টি মূলগতভাবেই অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও শেষমেশ সিস্টেমটিকে মেনে নিতে শুরু করেছেন – বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, কোয়ালিটি হেলথকেয়ার সস্তায় দেওয়া মুশকিল, বিনেপয়সায় দেওয়া তো অসম্ভব – কোয়ালিটি চাইলে ট্যাঁকের জোর মাস্ট।
অথচ, এই চিকিৎসকদেরই যখন টেবিলের উল্টোপারে বসতে হয় – অর্থাৎ যখন তিনি নিজে বা তাঁর প্রিয়জন অসুস্থ হন – চিকিৎসক থেকে পেশেন্ট বা পেশেন্ট পার্টিতে রূপান্তরিত মানুষটি তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের আধার সিস্টেমটির আসল চেহারাটা দেখার সুযোগ পান – এবং, সে অভিজ্ঞতা, প্রায়শই, সুখকর নয়। কিন্তু, যেহেতু এমন পরিস্থিতি খুব নিয়মিত ঘটতে থাকে না, ব্যক্তিচিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোধোদয়ের ঘটনাগুলো “সিস্টেম”-এর মূল ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না।
একইভাবে, অন্যান্য পেশার মানুষের ক্ষেত্রেও, মোটা মাইনে ও বেসরকারি এফিসিয়েন্সির স্বাচ্ছন্দ্যের নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বেসরকারিকরণই উৎকর্ষের একমাত্র পথ বলে অনুভূত হয়। ছিটকে পড়ার আঘাতের পরে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে গলা চড়ালেও, যেহেতু একইসাথে অনেকে ছিটকে পড়ছেন না এবং যেহেতু একজন ছিটকে পড়ার অর্থ আরেকজনের সামনে সুযোগ, সম্মিলিত গলা চড়ানো সিস্টেমটিকে বদলে ফেলার মতো ক্রিটিকাল মাস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও “সিস্টেম”-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধে না ঠিক অনুরূপ কারণেই।
অথচ, এই প্রতিটা মেনে নেওয়া, প্রতিটা প্রতিবাদবাদহীন সম্মতি সিস্টেমকে মজবুত করতে থাকে – প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষে।
মুশকিল এই, নিজের গায়ে আঁচ আসা অব্দি সবই মেনে নেওয়ার অভ্যেস থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়।
অতএব, ধন্দে থাকি, কীসের আশায় থাকব? একইসাথে অনেক মানুষ ঘোর বিপদে পড়ুন, এমন পরিস্থিতির? যাতে তাঁরা সম্মিলিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হন এবং প্রতিবাদ যাতে ক্রিটিকাল মাস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়? নাকি, আকস্মিক সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এমন আশ্চর্য ভোরের??

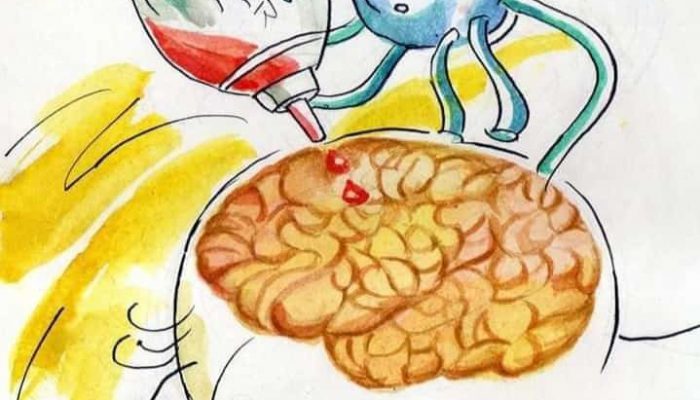












বিবাবু ঐ অবিবাহিতা গরীব মেয়েটি তোমার হাসপাতালে গেছে । কেমো নিচ্ছে । অশিক্ষা হেতু তোমাকে খুঁজে পায়নি । গরীব তো তাই বেশী খোঁজ করতে সাহস পায় নি । ওর মা মরা বোনপো আমার কাছে এসে কাঁদছিলো । এই মাসিই মানুষ করেছে তো ! যাই হোক গরীব মানুষ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ দেখে ঘাবড়ে গেছে । তোমার সঙ্গে দেখা করেনি বলে রাগ করো না । অশিক্ষিত মাসে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন এরা তো বোকা হয় – ভয় পায়- দলে দলে মরে ।
দাদা, তোমার কথাটা খুব সম্ভবত ঠিক নয়। আরেকবার খোঁজ নিও।
আমার হাসপাতালে আমাদের সপ্তাহে দুদিন ওপিডি – দুদিনই আমি বসি এবং কেমো-র তারিখ আমিই দিই। এর মধ্যে কোনো আশ্চর্য মহত্ত্বের ব্যাপার নেই – স্রেফ লোকবলের অভাবের কারণেই। অতএব, আমার সাথে একেবারে দেখা না হয়ে কেমো পাচ্ছে আমাদের বিভাগে, খুবই আশ্চর্য হবো এমন হলে।
আর, অন্য বিভাগে কেমো হলেও অ্যাডভাউস আমরাই দিই। কাজেই, তোমার ইনফরমেশন একবার যাচাই করে নিও।
সচরাচর ধনী লোকের চিকিৎসার সুযোগ পাই না। গরীব এবং অতি গরীব – পেশেন্ট প্রোফাইল এর মধ্যেই থাকে। তোমার চেয়ে কমদিনের অভিজ্ঞতা – তবু বলি, অনেকে বোকাসোকা অবশ্যই, কিন্তু অতিচালাকের সংখ্যাও কম কিছু নয়। এবং মৃত্যুহারে এই দুইপক্ষের মধ্যে ফারাক নেই।
সিস্টেম কে অস্বীকার বা পাল্টাতে গেলে তো একটা ঐ তোমার ভাষায় “ক্রিটিক্যাল মাস” এর প্রয়োজন। তা সেটা সেই “লাও তো বটে কিন্তু আনে কে” এইরকম একটা অবিচ্ছেদ্য চক্র তৈরী করে কি লাভ? তার বদলে, চলো পাল্টাই (সিস্টেম নয়, নিজেকে এবং অপরকেও)।
ঠিক কথা।
কিন্তু, সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথাগুলো ওঠা তো জরুরী। এবং সম্মিলিতভাবে ওঠা জরুরী।
শুধুই একক প্রয়াস জারি থাকলে সিস্টেমের তাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে সময় লাগে না। বেসরকারি ও সরকারি উভয় স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোতেই এমনটা দেখছি।
গড়পড়তা লেখার বাইরের বৃত্তে ভাবানোর মতো লেখা। সিস্টেম, আমার এবং আরও অনেকের বিচারে, স্বয়ম্ভূ নয়। একে টিঁকে থাকার জন্য, অর্থবহ হবার জন্য প্রতিমুহূর্তে মান্যতা এবং গ্রাহ্যতা উৎপাদন করে যেতে হয়। আমরা সবাই এই গ্রাহ্যতা দিই। যারা দেয়না তারা অ-নাগরিক। রাষ্ট্র ০ এবং ১ এই দুই integer-এ আমাদের বিচার করে।
যারা ভাবতে পারি তাদের আরও গভীরে ভাবতে হবে। রাষ্ট্র প্রতিমুহূর্তে অতিরাষ্ট্র হয়ে উঠছে। এর সিস্টেমও সেভাবে বদলাচ্ছে।
আরেকটা কথা। আমরা স্বাস্থ্য নিয়ে কথা প্রায় বলিই না, বলি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। ক্যান্সারের চিকিৎসাও স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যেই পরে। ক্যান্সার প্রথম “আধুনিকতার অসুখ” – হাই-টেক কর্পোরেট ডিজিজ। পরে প্রায় সব অসুখই জুড়েছে। যেগুলোকে ধরা যায়নি সেগুলো “tropical neglected diseases”.
আমাদের আবার আলমা-আটা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা জোর গলায় বলতে হবে।
একদম ঠিক কথা, জয়ন্তদা।
❤❤
খুব ভালো লেখা। মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।
জামালদা,
ধন্যবাদ।
কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা রইল।
❤❤
ভালো লাগলো। বেসিক জায়গাটা এড়িয়ে যাওয়া হয় নি, বরং, বেসিক জায়গাতেই প্রশ্নটা তুলেছ। এই একই প্রশ্ন স্বাস্থ্যের মতো, শিক্ষাতেও প্রযোজ্য।
আশ্চর্য এই যে, একটা সময়ে ভাবতে পারিনি(বা চাইনি), যে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাও পণ্য হতে পারে। এখন মনে হয় যে এই দিনগত বেঁচে থাকার সব কিছুই, হয়ত বা, যে যার মতন করে ক্রয় করেছে। আছে আর নেই এর ফারাক প্রকট হয়ে উঠেছে।
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়টি যেহেতু সবচেয়ে জরুরি একটা ক্ষেত্র, আবশ্যিক একটা জায়গা, সেখানে সত্যিই সিস্টেম বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাই চলতে পারে না, অন্তত আজকের পরিপ্রেক্ষিতে।
নানান কার্যগতিকে আপনার লেখার সঙ্গে অনেকদিন দেখা করা হয়ে ওঠেনি।
আপনার প্রায় সব লেখাতেই সমাজ-সচেতনতার কথা থাকে। পড়তে ভালো লাগে, ভাবতে ভালো লাগে কেউ অন্তত ভাবছেন। আমি অধিকাংশতই সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে নিজেকে রাখি; তার বাইরে যাওয়ার নানান ধরণের মুরোদের ঘাটতি আছে। বাধ্য হয়েই যাই, ফিরে এসে আর যাতে না যেতে হয়, অদৃষ্টের কাছে আবেদন জানাই। প্রার্থনা করার ফল আর জোর কোনোটাতেই ভরসা রাখার বয়স নেই আর।
লেখাটা শেষ করেছেন যেখানে, সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ এই যে আম-জনতা, অন্তত ভারতের , কখনই দায়ে পড়েও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি নানান কারণে। গান্ধির মতো তালেবর কোনো কোনো নেতা কিছু সময়ের জন্য হয়তো কিছু মানুষের আড় ভাঙাতে পেরেছে। এ দেশের এমন সংস্কৃতি মোটামুটি জেনেটিক-প্রায়। জেনেটিক রোগ কোন চিকিৎসায় সারে কে জানে।
ভরসা ওই গান্ধির মতো কোনো নেতা। সেটি মেডিকেল বিষয়ের হলে কোনো ডাক্তারবাবুর পক্ষেই সহজতর হয়। ডাক্তাররা যে নিজেদের দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে তুলতে পেরেছে তার পেছনে সমাজের মেধাতন্ত্রকে অমোঘ বলে ভেবে নেওয়ার অনিবার্যতা আছে বোধহয়। এই কিছুদিন আগেই আপনার লিঙ্কেই এক নবীন ডাক্তারবাবু সম্ভবত নচিকেতার কোনো গানের প্রতিবাদে একটি গান করে সমর্থন ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাতে ডাক্তারদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পেছনে তাঁদের মেধার জোরটিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ডারউইনিজমের উত্তর কী, কে জানে।
যদি ডাক্তারদের বিশেষ মেধাবী শ্রেণি, এবং সেই সুবাদে মেধাতন্ত্রের জয়ের পক্ষে সওয়াল করতে দেখা যায়, তবে সেই মেধার কাছেই একটি বিনীত অনুরোধ- মেধাহীন মানুষদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিনত করার এই দাবিটিতে প্রথম শ্রেণির মানুষরা সুরক্ষিত তো?
মেধাবী মানুষ হিসেবেই তো ডাক্তারদের এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ বেশি। ভুটানের রাজাই তো রাজতন্ত্রে সংস্কার আনার জন্য জনসচেতনতার অন্যতম পুরোধা।
এই ধরুণ আপনি একজন ডাক্তার বলেই তো এই লেখাটির সুযোগ পাচ্ছেন। আপনি একজন ডাক্তার বলেই আমি আপনার লেখাটিকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি। আপনি একজন ডাক্তার বলেই তো প্রশাসনে সিস্টেমের বিরুদ্ধে তদ্বির করার জন্য আম-জনতার চেয়ে বেশি এগিয়ে আছেন। আপনি এগিয়ে আছেন বলেই তো এরকম ভাবতে পারছেন।
সিস্টেম বদলানো দীর্ঘস্থায়ী বিবর্তনের পথ হয়তো। বিপ্লব কোনো দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে বলে মনে হয় না। সিস্টেম বদলানো পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এটুকু কথা অন্তত ছড়াক- রোগীরা ডাক্তারদের থেকে মেধায় ততটা ন্যুন না হতেও পারে যাতে তাঁকে প্রথমেই একটি সাবস্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট হিসেবে দেখা যায়, হিউমিলিয়েট করা যায়। যাতে তিনি শারীরিক রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার পথে মানসিক রোগীতে রূপান্তরিত না হন।
খুব সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ। সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই বোধ সমগ্র সমাজে সঞ্চালিত হওয়া নিতান্ত জরুরী। সেখানে চিকিৎসকের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত তার হয় নি। তোমার লেখার প্রতিটি শব্দ আসলে নিজের পিঠেই চাবুক মারে। আমরা যারা প্রান্তিক চিকিৎসক তারা প্রতিদিন এই সিস্টেমের শিকার মানুষগুলোকে দেখতে পাই। বাড়ি ফিরে চুপ করেই থাকি। সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই শ্লোগান সৎভাবে আবার উঠে আসুক।
ভালো লেখা। আমরা আর কবে যে বুঝবো। আপনার লেখার জন্য আবার অপেক্ষা তে রইলাম। আপনার ফোন নাম্বার পেলে অনেক লোক এর পাশে থাকতে পারতাম। আমি এই সাইটের নিয়মিত পাঠক।
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লেখা । ” সিস্টেম ” বানানোর পেছনে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুনাফালাভের চক্রান্ত তো থাকেই । মানুষ জেনে উপায়ন্তর না থাকায় অথবা কিছু না বুঝে তাকে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তি মানুষ যদি আরো বেশী করে সচেতন হয়–তাহলে বদলানো যেত । কিন্তু আমাদের দেশে জন জাগরণের কোনো আশা নেই ।
জয়ন্তদা যা বললেন , একমত–প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দাবী আরো জোরালো করতে হবে
কথাগুলো ওঠা অবশ্যই জরুরি, আর সেটাই মনে হয় ক্রিটিক্যাল মাস তৈরির একটা পূর্বশর্ত। আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হলাম ‘চিকিৎসা যে ক্রয়যোগ্য পণ্য হতেই পারে না’ এই কথাটা পড়ে। এভাবে তো ভাবিনি! বরং ক্রেতা সুরক্ষার ব্যাপারটা ঘটায় মনে মনে খুশিই হয়েছি, কারণ আমারও অনেকের মত ডাক্তারি গাফিলতির অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তোমার লেখাটা পড়ে এই কথাটা মাথায় থাকবে। পড়ানোর জন্য ধন্যবাদ!
These are actually great ideas in concerning blogging.