তিন দিনের জ্বর আর সর্দি কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল রজত। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ICU তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মাত্র তিনদিনের জ্বর যে আসলে এরকম ভয়াবহ নিউমোনিয়া হয়ে বাসা বেঁধেছে শরীরে, এ যেন নিজের ই বিশ্বাস হচ্ছিল না রজতের। তার বয়েস মাত্র পঁয়ত্রিশ। একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করে। নিয়মিত শরীরচর্চা করে সে। না আছে সুগার, না আছে প্রেসার। হ্যাঁ, একটু আধটু স্মোক করে সে। কিন্তু তার জন্য কোনদিন আজ অবধি অসুবিধে হয়নি। ICU তে ঢোকার অল্পক্ষণের মধ্যেই, ডিউটি রত ডাক্তারটি রজতের বাবা মা কে জানালেন, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বিপদ সীমার নীচে চলে যাচ্ছে। ভেন্টিলেশনের দরকার পড়বে। প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলেন রজতের বাবা। আজ অবধি যত চেনাজানা মানুষ কে ভেন্টিলেশনে যেতে দেখেছেন, কাউকে উনি বেঁচে ফিরতে দেখেন নি। আতঙ্কিত স্বরে তিনি তরুণ ডাক্তার টিকে আঁকড়ে ধরলেন প্রায় “- কিন্তু ডক্টর, ভেন্টিলেশনে গেলে তো আর বাঁচবে না! কি এমন রোগ হল, যাতে এত খারাপ হয়ে গেল শরীর !”
…..
উপরের ঘটনা টি কাল্পনিক কিন্তু ভীষণ রকমের সত্যি। ভেন্টিলেটর নামটি শুনলেই বুকের মধ্যে কাঁপন ধরে। অজানা ভয় চেপে বসে বুকের মধ্যে। তার সাথে অভিশাপের মত লাগে প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা। আর সেইসঙ্গে দুর্বোধ্য মেডিকেল সায়েন্সের কথাবার্তা। তারপর থাকে সইসাবুদ। কনসেন্ট দেবার বা না দেবার দ্বিধা দ্বন্দ্ব। এবং সর্বোপরি, আকাশছোঁয়া বিলের বোঝা। কারণ এ যেন চক্রব্যূহ। একবার ঢুকলে বেরনো দুঃসাধ্য।
…..
চেষ্টা করি ভেন্টিলেশন সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞান এখানে তুলে ধরতে।
১. ভেন্টিলেশন আসলে কি এবং কেন?
২. “রুগী ভেন্টিলেশনের একবার গেলে আর বেঁচে ফেরে না ” – এই ধারণা তে কত টা সত্যি, কত টা মিথ?
৩. ভেন্টিলেশনের কনসেন্ট নিয়ে ডাক্তার রা এত চাপাচাপি করেন কেন?
৪.ভেন্টিলেশন থেকে বের হতে এত সময় লাগে কেন, ভেন্টিলেটরে দেবার প্রক্রিয়া তো কয়েক মিনিটেই হয়ে যায়?
৫. ভেন্টিলেশনে দিলে এত খরচ কেন হয়?
৬. “ভেন্টিলেশন খুলে দিন” বললেও ডাক্তার রা খুলতে চান না কেন?
৭. “ব্রেন ডেড” রুগীকে জোর করে ভেন্টিলেশনে রেখে হাসপাতাল গুলি বিল বাড়ায়। এই ধারণা কত টা সত্যি?
আজকে শুরু করি প্রথম প্রশ্ন দিয়ে। একটু জানি ইতিহাস।
ভেন্টিলেশন আসলে কি এবং কেন?
…….
ভেন্টিলেটর হল একটি যন্ত্র যা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস নিতে ও ছাড়তে সাহায্য করে ।
এই কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ভেন্টিলেশন।
এ যন্ত্র তৈরি হবার পিছনে অসংখ্য মানুষের নিরলস বিজ্ঞানসাধনা ও চর্চা জড়িয়ে রয়েছে। আর এখনো এই যন্ত্রকে উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রক্রিয়া নিরন্তর চলছে।
অন্যান্য প্রাণীর মত, বাতাসই যে মানুষেরও বেঁচে থাকার জন্য সবথেকে বেশি দরকারি, আর সেই বাতাস আসলে শরীরে ঢুকছে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে, এ কথা প্রথম বলেন গ্যালেন নামে এক গ্রীক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক, সেই দ্বিতীয় শতকে৷ ফুসফুস কে কাজ করাতে গেলে যে বুকের খাঁচার মাংসপেশী গুলোর জোর দরকার, মানবজাতির এইসব বুঝতে বুঝতে মধ্যযুগ টুগ পার করে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি হয়ে গেল।শেষে ব্রাসেলসের বিজ্ঞানী আন্দ্রে ভেসালিয়াস, ইতালির পাদুয়ায় এনাটমির শিক্ষক থাকাকালীন ১৫৪৩ সালে প্রথম তাঁর লেখায় উল্লেখ করলেন যে কৃত্রিম উপায়ে বাইরে থেকে শ্বাস দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে। উনিও গ্যালেনের থিওরির ওপরেই ভাবনা চিন্তা করছিলেন। অবাক কান্ড তখন ও ওঁরা জানেন না বাতাসে অক্সিজেন নামেও একটি উপাদান আছে।অথচ ভেসালিয়াস আন্দাজ করেছিলেন শ্বাসের নালীতে ফুটো করে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ কেউ পাত্তা দেয়নি তখন তাঁকে। তাছাড়া শব ব্যবচ্ছেদ এর জন্য চার্চের রোষের মুখেও পড়লেন তিনি।
এরপর এলেন “কোষ” আবিষ্কর্তা রবার্ট হুক। ১৬৬৭ সালে, ফুসফুসে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন আর হৃদপিণ্ডে র সংকোচন হয় বলেই প্রাণী রা বেঁচে থাকতে পারে, একটি কুকুরের ওপরে একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। তখনো, অক্সিজেন নামে গ্যাসটির কথা জানে না কেউ। অক্সিজেন আবিষ্কার হল আরো একশ বছর পার করে ১৭৭৪ সালে জোসেফ প্রিস্টলি আর উইলিয়াল স্কিল এর এক ই সময় করা কিন্তু দুটি পৃথক এক্সপেরিমেন্ট-এ। আর ঠিক এর পরে পরে ল্যাভয়সিয়ার প্রমাণ করলেন এই অক্সিজেনই মানুষের বেঁচে থাকার সবথেকে জরুরি উপাদান।
এইবার শুরু হল বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস আর স্তিমিত হয়ে যাওয়া হৃদস্পন্দনকে পুনরায় চালু করার লড়াই। টোস্যাক বললেন মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেবার কথা, যে প্রক্রিয়া এখনো ব্যবহার হয়ে আসছে। ল্যাভয়সিয়ারের থিওরির প্রায় একশ বছর পর ১৮৬৪ সালে আল্ফ্রেড জোন্স তৈরি করলেন এক “রেস্পিরেটর”। আজকের ভেন্টিলেটর-এর প্রপিতামহ। সে এক কান্ড। লোহার বাক্সের মধ্যে মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সের ভেতরের বাতাস টেনে বের করে ভেতরের চাপ কমিয়ে দাও। তাতে মানুষটির ফুসফুসের ভেতরের চাপে ফুসফুস সম্প্রসারিত হবে। হাওয়া ঢুকবে। তারপর আবার বাতাস ঢুকিয়ে বাক্সের ভেতরে চাপ বাড়াও, সেই চাপে ফুসফুস থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবে।
আল্ফ্রেড জোন্সের এই যন্ত্রকে আর একটু উন্নত করে, বোস্টনে, পোলিও রোগাক্রান্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসায় লাগালেন ড্রিঙ্কার আর শ’। ১৯২৯ সাল। তাঁদের যন্ত্রকে বলা হতে লাগলো “আয়রন লাং”। মহামারীর সময়, বেশি সংখ্যক শিশুর চিকিৎসার জন্য প্রথমে পিটার লর্ড ও তারপর জেমস উইলসন বোস্টনের শিশু হাসপাতালে তৈরি করে ফেললেন “ভেন্টিলেটর রুম”। পুরো একটা ঘরের বাতাসের চাপ বাড়ানো-কমানোর জন্য ইয়া বড় বড় পিস্টন বসিয়ে।
চলে এল ১৯৫১ সাল। কোপেনহেগেন শহরে পোলিওর মহামারী। গড়ে ৫০ জন শিশু আক্রান্ত হচ্ছে রোজ। ৮০% এর বেশি শিশু মারা যাচ্ছে। প্রথমে ভাবা হচ্ছিল কিডনি বিকল হয়ে তাদের এই অবস্থা। শেষে বোর্ন ইবসেন নামে এক এনাস্থেসিওলজিস্ট প্রথম ধারণা দিলেন পোলিও তে “রেস্পিরেটরি ফেলিওর” এর। পক্ষাঘাত হয়ে, শ্বাস নেবার কাজে ব্যবহৃত মাংসপেশী ব্যবহার না করতে পারার জন্য ধীরে ধীরে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে শিশুরা। ইবসেন ফিরে গেলেন সেই ভেসালিয়াসের থিওরিতে। গলায় শ্বাসনালীতে ফুটো করে ঢুকিয়ে দিলেন টিউব। তাতে জুড়ে দিলেন পাম্প বেলুন। কিন্তু পাম্প করার মত উন্নত যন্ত্র ও তো তখনো তৈরি হয় নি! শেষে কোপেনহেগেন জুড়ে বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য, ১৫০০ জন ছাত্র হাতে হাতে রিলে করে পাম্প করা শুরু করল।সব মিলিয়ে ১৬৫০০০ ঘন্টা তারা পাম্প করেছে নিরলস। মন্ত্রের মত কাজ হল। মৃত্যুর হার নেমে এল ৮০ % থেকে ৪০% এ। এত গুলি বাচ্চার চিকিৎসার জন্য তাদের একত্রে একটি ওয়ার্ডে ভর্তি করে প্রবল যত্ন শুরু হল। যাতে এই বাচ্চা গুলি থেকে অন্যদের সংক্রমণ না ছড়ায়। সেই হল প্রথম “ইন্টেন্সিভ কেয়ার”। এক এনাস্থেসিওলজিস্টের হাত ধরেই আই সি ইউ-র ভাবধারার সূত্রপাত।
ভেন্টিলেশনের মূল কার্যপ্রণালী বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল যুগান্তর। এতদিন তৈরি করা হচ্ছিল দেহের বাইরে নেগেটিভ প্রেশার।পরোক্ষ ভাবে। এবার, ভেন্টিলেশন হবে ফুসফুসের ভিতরে সরাসরি,প্রত্যক্ষভাবে অক্সিজেন ঢুকিয়ে, পজিটিভ প্রেশার দিয়ে। সুতরাং, নতুন জানলা খুলে গেল। এখন এই যন্ত্র শুধু মাংসপেশীর কাজ টুকুই করবে না, ফুসফুসের গ্যাস আদানপ্রদানের কাজেও সহায়তা করবে। রক্তে গ্যাসের লেভেল দেখে ঠিক করে নেওয়া যাবে কার কত অক্সিজেন চাই। শুধু তাই না, শরীরে অতিরিক্ত জমে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড কে বের করার জন্যও সাহায্য করবে। গত সত্তর বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানী রা গবেষণা করে বের করে চলেছেন নতুন, উন্নত ভেন্টিলেটর। এখন এসে গিয়েছে NAVA,যেখানে রোগীর শ্বাস নেবার ক্ষমতা, স্নায়ু ও মাংসপেশি র কাজের ধরণ দেখে বুঝে নেবে যন্ত্র, ঠিক মেপে শ্বাস নিতে সাহায্য করবে,সুস্থ অবস্থায় যেমন আমরা টের ই পাই না যে, শ্বাস নিচ্ছি।
ভেন্টিলেটরকে তৈরি করা হয়েছে মানুষকে সাহায্য করার কথা ভেবে। কিন্তু এই এত যন্ত্রপাতি, কলকব্জার ব্যবহারে কিছুই কি ক্ষতি নেই?
আছে।
– ফুসফুসের কোষ ও কলায় অভ্যন্তরীণ ক্ষতি। ভেন্টিলেটরের বাতাসের চাপ থেকে।
– রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ ফুস্ফুস, যেমন টিবি বা সি ও পিডি র মত অসুখে লাংসের পর্দা ফেটে যাওয়া।
-অক্সিজেন, যেমন বাঁচিয়ে রাখে তেমনি মাত্রাতিরিক্ত হলে ক্ষতিও করে।
-জীবাণু সংক্রমণ৷
এই সমস্ত কিছুও মানুষের ই ভেবে চিন্তে বার করা।এই নিয়েও চিন্তা জারী থাকবে যে কিভাবে এই জটিলতা গুলো কে কাটিয়ে আরো উন্নত মানের যন্ত্র তৈরি করা যায়।
এবার দেখা যাক, প্রধাণতঃ কোন ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা ভেন্টিলেশনের কথা বলেন।
তা হল, সেই ইবসেন সাহেবের তত্ত্ব অনুযায়ী, শ্বাসের বিকলতা বা “রেস্পিরেটরি ফেলিওর”।
দু ধরণের হয় এটি৷
টাইপ 1ঃ মূলত অক্সিজেনের অভাব।
টাইপ 2ঃ মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়া।
টাইপ ওয়ান, অক্সিজেনের অভাব প্রধানত যে যে ক্ষেত্রে দেখা যায় –
- হার্ট ফেলিওর
- নিউমোনিয়া
- ট্রমা বা আঘাতজনিত কারণ
- একিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম
- এম্বলিজম
- একিউট ইন্টারস্টিসিয়াল নিউমোনাইটিস
- ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ
- এস্থমা
- ব্লাড ট্রান্সফিউশন এর পর
- সেপ্টিক শক
টাইপ টু, কার্বণ ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়া যে ক্ষেত্রে দেখা যায় –
- ব্রেন স্ট্রোক
- মোটর নিউরোন ডিজিজ
- পোলিও
- গুলেন-বেরি সিন্ড্রোম
- মায়েস্থেনিয়া গ্রেভিস
- কীটনাশকের বিষক্রিয়া
- টক্সিন – সর্প দংশন, জেলিফিস,মাছ, টিক
- বটুলিজম
- ঘুমের ওষুধের ওভারডোজ
- সি ও পি ডি
- সিস্টিক ফাইব্রোসিস
এই সমস্ত ক্ষেত্রে, ভেন্টিলেটরের কাজ অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের অপসারণ । কাজেই ভেন্টিলেটর নিজে কোন ওষুধ নয়। এটি চিকিৎসার একটি সহায়ক পদ্ধতি। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম। বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরী উপাদান টিকে শরীরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করা।
আর ক্ষতিকারক গ্যাস টিকে বের করে দেওয়া।
কিন্তু এত কিছুর পরেও ভেন্টিলেশনে দেওয়া রুগীদের সবাই কে তো বাঁচানো যায় না। কেন যায় না? কিসের ওপর নির্ভর করে ভেন্টিলেশনে দেওয়া রুগীর ভালো হওয়া? সত্যি ই কি ভেন্টিলেশনে দেওয়া মানে জীবনের শেষ অবস্থা? এই নিয়ে লিখব পরের কিস্তিতে।






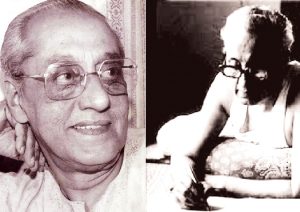
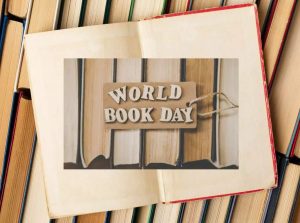
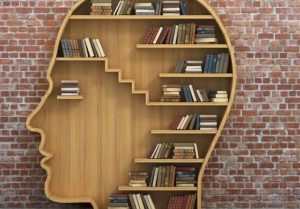








পুরো টা জানার খুব ইচ্ছা থাকল,
আর্থিক কারণ মুখ্য হলেও দিলে আর ফিরবে ধরে নিয়ে বাবার শেষ সময়ে পিছিয়ে এসেছি।
অন্যদের ক্ষেত্রে যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি
পুরোটা জানতে চাই।
ধন্যবাদ। চেষ্টা করব সহজ ভাবে বোঝানোর।
পরের অংশের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।
খুব সহজে বোঝাতে পারলে মানুষের অনেক ভুল ধারণা কেটে জাবে…..thank you.
অপেক্ষায় আছি
অনেক ভুল ধারণা আছে। পুরোটা জানার অপেক্ষায় রইলাম
জানার অপেক্ষায় রইলাম ।
খুব ভালো লেখা। পুরোটা পড়তে চাই ।
মানুষ কে সচেতন করার জন্য ধন্যবাদ