সম্পাদকের কাছ থেকে ফোনটা বেশ কড়া করেই এসেছিল – “খুব অন্যায় হয়েছে তোমার। ডাক্তারদের লকডাউনের অভিজ্ঞতা ডাক্তারদের পোর্টালেই আগে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে সার্জনদের অভিজ্ঞতা তো ভীষণই ইম্পর্ট্যান্ট।” তারপর একটু থেমে আদেশ আসে “লেখাটা রিরাইট করো। আরো ‘গভীরে যাও’। সার্জনরা কি অসুবিধায় পড়ছে সেটা সবাই জানবে না?”
সুতরাং সার্জনদের দৈনন্দিন কাজের মতোই যোগবিয়োগ শুরু করে দিই। একেবারে গোড়া থেকে।
যেকোনো পুরনো হয়ে যাওয়া স্বামীই জানে স্ত্রী মিষ্টি করে কোনো কথা বলছে মানে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। সেরকমই মিষ্টি সুরে লকডাউনের তিন-চার দিনের মাথায় স্ত্রী আমাকে জানায় যে আমার ভায়রাভাই ওর দিদির রান্না করে দিচ্ছে। “তুমি দু’বেলা করে অন্তত একটু বাসনকোসন মেজে দাওনা গো!”
আমি আঁতকে উঠি। আমাদের কাজের মাসির বাড়ি আমাদের ফ্ল্যাটের পাশেই। একেবারে হাত বাড়ালেই বন্ধু। সে তো রোজ কাজে আসছে। সুতরাং আলাদা করে আমার বাসন মাজার কোনো কারণ নেই। তার ওপর চিকিৎসক বলে লকডাউনে আমার তো ঘরে বসে থাকারও উপায় নেই। হাসপাতাল থেকে কড়া নির্দেশ আছে, এই সময় কাজে ডুব মারা নৈব নৈব চ। সুতরাং অন্যান্য স্বামীদের মতো ওভারটাইম করার প্রশ্ন আসছে কেন। আমি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেও অর্ধাঙ্গিনী বুঝতে নারাজ। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে তার বান্ধবীরা প্রতিনিয়ত জানিয়ে যাচ্ছে যে তারা কতো গৃহকর্মনিপুণ স্বামী পেয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আমার ভায়রাভাই তার রান্না করার ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে বসে আছে।স্বভাবতই আমার স্ত্রীর হিংসায় নীল হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।
এমনিতেই হাসপাতালে ডিউটি করি বলে পাড়ায় এবং ফ্ল্যাটে কিছুটা ব্রাত্য হয়ে আছি। পাড়াপ্রতিবেশিদের বধ্যমূল ধারণা আমি ফেরার সময় আমার স্টেথোস্কোপ রাখার ব্যাগে করে একব্যাগ করোনা নিয়ে ফিরি।
পড়শীদের সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। কিন্তু লকডাউনে আমার অবস্থা শোলের গব্বর সিংয়ের মতো হয়ে গেছে। একেবারে ভিলেন। না ঘুমোলে বাচ্চাদের মায়েরা বলে – “শো যা, নেহি তো ডাক্তারবাবু আ যায়েগা।” কারো সাথে আচমকা রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংয়ের মাত্রাটা একমিটার থেকে বাড়িয়ে দুমিটার করে নেয়। মাস্কের ওপরে হাত চাপা দিয়ে দু’একটা কথা বলে পড়িমরি করে পালিয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকেও নিস্তার নেই। স্নান না করে প্রায় ঘরে নিঃশ্বাস শুদ্ধু ফেলা যাবেনা। এবং যতবার হাসপাতাল থেকে ফিরবো ততবারই স্নান মাস্ট । সাধারণত দিনে দুবার করে হাসপাতাল যেতে হয়। দুবার স্নান তবু মেনে নিচ্ছিলাম। অ্যাডমিশন ডের দিন রাত্রি দুটোর সময় বাড়ি ফিরে দেখি গৃহিণী গামছা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার আগে আমার চারবার স্নান সারা হয়ে গেছে সেদিন । আমার প্রায় হাতেপায়ে ধরার অবস্থা – এবার স্নান করলে করোনায় না মরে নিউমোনিয়ায় মারা যাবো। আর আমিতো সার্জারির ডাক্তার, সংক্রামক রোগী থাকা ওয়ার্ডে আমাদের খুব প্রয়োজন ছাড়া যেতে হয়না। সারা গায় স্যানিটাইজার মেখে ছাড়া পেয়েছিলাম সেদিন।
লকডাউনের সময় একটু বেলা করে রাউন্ড দিই। সবকিছু চলছে বেশ ঢিমেতালে। এমারজেন্সি অপারেশন ছাড়া অহেতুক অপারেশনের ঝুঁকি কেউ নিচ্ছেনা। কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে না ঢুকলে সার্জনদের হজম-টজমের গোলমাল দেখা দেয়। সুতরাং দূরত্ব বজায় রেখে তিন-চারজন আড্ডাবাজ ডাক্তার ওটিতে ঠিকই উপস্থিত হচ্ছে। মাস্কের আড়াল থেকে অধুনা ভাইরাল হয়ে যাওয়া সেই বিখ্যাত ডায়ালগটাও দিয়ে বসছে “আমরা কি চা খাবো না?” সিস্টার দিদিরা মায়ের জাত, রাগ করলেও ফ্লাস্ক থেকে ঠিক চা ঢেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আড্ডার বিষয় অধিকাংশ সময়ই করোনা ভাইরাস। আসলে ডাক্তারদের সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপগুলোয় এখন হুট টপিক করোনা ভাইরাসের স্বভাবচরিত্র। আর এরকম চরিত্রহীন জীবাণুর মুখোমুখি এই প্রজন্মের ডাক্তাররা হয়নি। মহিষাসুরের মতো মুহুর্মুহু রূপ বদল করতে ওস্তাদ কোভিড১৯। ব্যাটাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছেনা। এ যেন “নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।/ ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।” অস্ত্র দিয়ে একে বিনাশ করা যায়না, আগুন পোড়াতে পারেনা, জল ভেজাতে পারেনা আর বায়ু শোকাতেও পারেনা। গীতার আত্মার ডেফিনেশনের মতো অবিনশ্বর হয়ে বসে আছে করোনা ভাইরাস। সেই আড্ডায় সত্য-মিথ্যা পোস্টগুলোর কাটাছেঁড়া হয়।
আর দিনরাত মিটিং তো লেগেই আছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যভবনের সাথে মিটিংগুলোর পরিবেশ ভূতের গল্পের মতো গা ছমছমে। অন্ধকার ঘর। এদিক-ওদিক করে খান দশেক ডাক্তার মুখোশ পরে বসে আছে। জুমের মাধ্যমে সাদা দেওয়ালে স্বাস্থ্যভবনের বড়কর্তাদের মুখ। অন্ধকারে ঘুমিয়ে নেবারও উপায় নেই। কলকাতার স্ক্রিনেও যে এককোণে ছোট্ট করে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে। নতুন নতুন নির্দেশ আসছে। নির্দেশের পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হচ্ছে। তারপরে আবার জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক অন্য সমস্ত ডাক্তারদের নিয়ে বসছে। জেলা প্রশাসনের তরফে উপস্থিত থাকছেন বিভিন্ন আধিকারিক। আসলে লড়াইটা যে মানুষের সাথে মৃত্যুর। সব মানুষ সত্যিই এককাট্টা হয়ে লড়তে চাইছেন। এরমধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেগুলোর মোকাবিলা করার কথাও ভাবতে হয়।
এরমধ্যে কোভিড১৯ চিকিৎসা হওয়ার হাসপাতালগুলো দুভাগে ভাগ হয়েছে। যারা ভীষণরকম শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, কিন্তু এখনো রিপোর্ট আসেনি – তাদের লেভেল ওয়ান ও টু হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। গালভরা একটা নামও দেওয়া হয়েছে – সারি হাসপাতাল। সারি অর্থাৎ সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস। তো একদিন পালে বাঘ পড়লো। সারি হাসপাতাল থেকে সার্জনের ডাক পড়লো। অন-ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের সন্দেহ পেপটিক পারফোরেশন বা নাড়ি ফুটো হয়েছে।
জয়পুর এস এম এস হাসপাতালের সার্জনদের কাছ থেকে একটা খবর আসছিল – পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড নাকি ভয়ংকর রকম সংক্রামক কোভিড১৯এর ক্ষেত্রে। ভীষণরকম সাবধানতা অবলম্বন করে গেলাম সেখানে। আমার পোশাক দেখলে নাসার মহাকাশযান আমার জন্য দরজা খুলে দেবে।
যাহোক, দেখা গেলো রোগীর পেপটিক পারফোরেশন হয়নি। আর হ্যাঁ – জয়পুরের সেই রোগীটিকে সবরকম সুরক্ষা নিয়ে যাঁরা অপারেশন করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের করোনা সংক্রমণ হয়েছে। একমাত্র এমারজেন্সিতে যে ডাক্তার তাঁকে দেখেছিলেন তাঁর কিছু হয়নি। তিনি যে অপারেশনের ঘরে ঢোকেননি। একটুর জন্য বেঁচে গেছি।
আমরা ভয় পেলেও বেপরোয়া কিছু মানুষ পথে বেরোচ্ছে। সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয়। কারণ সার্জারি ডিপার্টমেন্টের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন দশ-পনেরোটা করে অ্যাক্সিডেন্টের রোগী আসছে। তাদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জনের অবস্থা বেশ খারাপ থাকছে। খুব খারাপ রোগীদের (যাদের মস্তিষ্কে বা ফুসফুসে ইঞ্জুরি থাকছে) বড়ো জায়গায় পাঠানো যাচ্ছে না। কি করে যাবে, সেখানে গিয়ে আদৌ বেড পাবে কিনা, বেড পেলেও ডাক্তার পাবে কিনা – এসব বেয়াড়া প্রশ্নগুলো রয়েই যাচ্ছে। আবার রেখে দিয়ে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করলেও অন্যরকম দুর্ভাবনা থাকছে। পরে যদি প্রশ্ন ওঠে নিউরোসার্জারি বা কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি করার পরিকাঠামো নেই জেনেও কেন আপনি জেলা হাসপাতালে রোগীকে রেখে দিলেন এবং মৃত্যুর কারণ হলেন- সেই প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবো না। ডাক্তারদের এখন বিশাল একটা ভয়ের জায়গা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা। তাই মধ্যপন্থা নিয়ে রোগীর আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে রোগীর অবস্থা খারাপ। তার সাথে রেফারও লেখা থাকছে। নিজেদের মতো করে চিকিৎসা কিন্তু বন্ধ হচ্ছেনা।
লকডাউনে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। পারিবারিক মারপিট যেন এই অস্থির সময়ে পছন্দের পাসটাইম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আক্রমণের শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা। কর্মহীনতা কি নৃশংসতা বাড়িয়ে দেয়? লকডাউন তখন দিন দশেক গড়িয়েছে। ভোররাতের দিকে একজন রোগিণী এলো। সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন। মাথার ওপর থেকে একটি ক্ষত নেমে এসেছে কপাল পর্যন্ত। গভীরতা ছুঁয়েছে খুলির হাড় পর্যন্ত। তার বীরপুঙ্গব স্বামী মারধর করেছে। সেলাই দিতে দিতে নিস্তেজ হয়ে আসা মহিলাকে পরামর্শ দিই নিজের বাবা-মার কাছে পালিয়ে যাওয়ার। গরীব বাবা-মার বোঝা হতে চায় না মহিলা। আর পালিয়েই বা যাবে কোথায়? চতুর্দিকে সমাজের দেওয়াল আছে না? দেওয়ালে তো পিঠ ঠেকে যাবেই। একজন অসহায় নারী কতো দূর দৌড়ে পালাতে পারে? আমাদের সমাজে নারীর কাছে পৃথিবীটা বড়ো ছোটো।
বিকেলের দিকে কোনো কাজ থাকে না। ব্যালকনি দিয়ে দেখি আকাশে রঙবেরঙের ঘুড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে। একদিন কেটে যাওয়া একটা ঘুড়ি হাতে এলো। ছেলেমেয়ে ভীষণ উত্তেজিত। “বাবা, ঘুড়ি ওড়াতে পারো?”
আমাদের ছেলেবেলাটা অন্যরকম ছিল। পড়াশোনা নিয়ে ইঁদুর দৌড় ছিল না। ছুটির দুপুরে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল, বিকেলবেলায় খেলার মাঠ ছিল, রাতে ঠাকুমার কোলের ভেতর সেঁধিয়ে ভূতের গল্প ছিল। আমাদের ‘ছিল’র তালিকাটা বেশ লম্বা। ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফ্ল্যাটের ছাদে চলে গেলাম। প্রথমদিকে না পারলেও কিছুক্ষণের চেষ্টায় ঘুড়ি আকাশে উড়লো। চতুর্দিকে “পেটকাটি চাঁদিয়াল মোমবাতি বগ্গা/ আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা।” বেশিক্ষণ আকাশে থাকা হলোনা, একটা ঢাউস ঘুড়ি আমারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেলে মেয়ে দুইপাশে লাফাচ্ছে।
“বাবা, তুমি বাঁদিক থেকে ডানদিকে টানো” – মেয়ে বলে ওঠে।
ছেলে বলে “না, তুমি ওপর থেকে নিচে নামাও।” দুই সন্তানের পরামর্শের মাঝে আমার ঘুড়ি কেটে যায়।
কেটে যাওয়া ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে মেয়ে জিজ্ঞেস করে “ঘুড়িটা কোথায় যাচ্ছে বাবা?”
মনশ্চক্ষে দেখতে পাই কবীর সুমনের গানের সেই ছেলেটা ঘুড়িটা ধরতে ছুটছে। এই লকডাউনের বাজারে তাকে যে আর রিকশা চালাতে হচ্ছেনা।
আমি চুপিচুপি মেয়েকে বলি যে আমার ছোটবেলার কাছে ঘুড়িটা পালিয়ে যাচ্ছে।




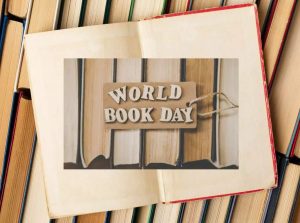
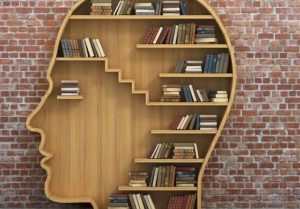









কি দারুণ।
গল্পটা প্রথম পড়ি আনন্দবাজার পত্রিকায় তার পর থেকে কত বার যে পড়েছি হিসাব নেই।।আমার মন খারাপ হলে ই গল্প টা পড়ি,খুব ভালো লাগে।।
অসাধারণ হয়েছে Sir । আপনার লেখা এখনো পর্যন্ত সব থেকে আমার প্রিয় গল্প এটা।❤