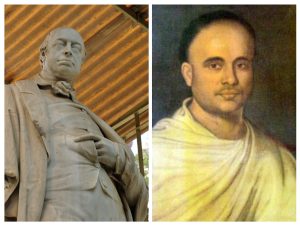আমি, মা আর বাবাকে নিয়ে যে ছোট্ট ত্রিভুজ ছিলো নিকটজনের ভিড়ে সেটা ভর্তি হয়ে উপচিয়ে গেলো। নিজেদের মধ্যের ভালবাসা ছড়িয়ে গেলো বহুজনের মাঝে। ভীড়ের মাঝে আর যাই হোক প্রেমের গান হয় না, গতিকৃষ্ণ নাগের হার্মোনিয়াম অনাদরে পড়ে রইলো-গান আর আসে না। অমল আর গায়ত্রীর সেই জীবনানন্দ পাঠ, রান্না টেস্ট করে দেখা, হাঁটতে হাঁটতে দারকেশ্বর নদের পাড়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। তার বদলে আমার স্মৃতিপটে একটা আনন্দময়, উজ্জ্বল শৈশবের ছবি অবশ্য স্মৃতির পটে আঁকা রইলো।
তিনটে ঘরের একটা ঘরে ঠাকুমা, একটায় অন্য অতিথি-তখন সন্তান হতে, চিকিৎসার জন্য- অনেকেই বাঁকুড়ায় আমার মা বাবার কাছে এসে থাকতো, আমার কাকিমারাও সন্তান প্রসবের জন্য মায়ের কাছে আসতো। মা তখন সবাইকার গুরুজন স্থানীয় হয়ে উঠেছিল।
একটা ছিলো বসার ঘর; বেতের সোফাসেট (সেজকাকার দেওয়া) আর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পরিবার।একটা পাঁচিল দেওয়া উঠোন ছিলো।সঙ্গে ছিলো একটা কয়লা রাখার ঘর। হঠাৎ মানসিক অসুখে ভুগে সমুকাকা তখন এসে ঐ ঘরে থাকতো। ইঞ্জিনিয়ার কাকা-নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। আমি হাঁ করে বসে সেই কারিগরি দেখতাম। কিন্তু কোনোদিন দু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখিনি এতো মানুষের খাবার কোথা থেকে আসছে। অবশ্য রাতে পড়ার পর রান্না ঘরে বসে উনুন ধরানো, উনুনে কয়লা দেওয়া, রান্না করা মা’কে দেখতাম। ডাল সাঁৎলাচ্ছে, বেগুন পোড়া করছে। কে বলবে এই মেয়েটা একটা ডাক্তার-নিপাট গৃহবধূ নয়?
তখন মামার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কেবল চিঠিতে। মালয়েশিয়া থেকে অন্য রকম ইনল্যান্ডে চিঠি আসতো-“স্নেহের বুচু, আশা করি তোমরা সবাই…..”,দোদোর চিঠি আসতো “স্নেহের বুচু….”
নকশাল আন্দোলনের পর বাঁকুড়ার পাট চুকলো। এসে পৌঁছলাম কল্যাণীতে। খোলা মাঠ, হুহু হাওয়া, দূর থেকে আসা বৃষ্টি-যতদূর চোখ যায়-ওপারে গাছপালা ঝাপসা হয়ে আসা বৃষ্টি-এখানেই আমি প্রথম সত্যিকারের স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম-নিয়মমাফিক। স্কুলটা ভালো লেগে গেল, শহরটাও। এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল। বন্ধুও জুটলো অনেক।প্রথমে মা বাবার টিবি হাসপাতালে চাকরি। বিরাট কোয়ার্টার। মিলিটারি ব্যারাক থেকে কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। তারপর জেএনএম হাসপাতালে। এবার মামাবাড়ির সবাই আসতে আরম্ভ করলো। লিলি, রিণি, বাপ্পু ছোট্টু, বাচ্চু। বাবার দিকের আত্মীয়রাও আসতো। সুজিত, অপু, বড়পিসি, দাদা। এখানেই এক কাকিমার সন্তান প্রথম কয়েক মাস ছিলো-নাকি জন্মেছিলো?
স্মৃতি সব সময় কাজ করে না। যাওয়া আসা দু তরফেই চলছিল-আমরাও যেতাম। বেশ একটা একান্নবর্তী পরিবারের আমেজ আবার ফিরে এলো। এরপর আমার জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো ভাইরা পড়াশোনার জন্য কল্যাণী এসে থাকলো। এখানের স্কুলে পড়া, পাস করে কলেজ-সব কিছুতেই মা বাবা জড়িয়ে আছে।
মায়ের ভূমিকাটা ছিলো ফুটবল দলের মিডফিল্ডারের মতো-ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। কেউ টের পেতো না-কখন সব কিছু ঠিকঠাক জুটে যেতো-খাবার থেকে জামাকাপড় সব। গোল করার ক্রেডিট তো মিডফিল্ডার পায় না, মা’ও পায় নি। কখনও কোনও গন্ডগোল হয়নি, সব বিপদ নিঁখুত ট্যাকল করে সামলে দিতো। আর বাবা বড়ো বড়ো কাজগুলো করতো-কল্যাণীতে ঠিক সময়ে জমির জন্য লটারিতে নাম দেওয়া, ভাইঝির বিয়ের ব্যবস্থা-ছেলের পড়া-সবই কিন্তু চমৎকার একটা ছন্দবদ্ধ পদ্ধতিতে সব চলতো।
সময় চলে গেল বহু বহু, কবে যেন কল্যাণীতে বাড়ি হলো, কবে যেন ওদের ছোট্ট তপ্পি বড়ো হয়ে গেল। মা বধূবরণ করলো। আমি তখন সংসার, সন্তান, ডাক্তারিতে বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভুলেই গেলাম কল্যাণীতে মাধবীকুঞ্জ সমেত ছোট্ট বাড়িটার কথা। ভুলে গেলাম একটা বুড়ি পথ চেয়ে বসে আছে, আর একঝাঁক ঝগড়াটে ছাতারে এসে ফরসা, ছোটোখাটো বুড়ির হাত থেকে খাবার খেতে খেতে চিৎকারে বাড়ি,বাগান মাত করে দিচ্ছে।
শুধু ফোন করে খোঁজ নেওয়া শুধু ছুটি কাটাতে যাওয়া। আমার মেয়েটা ছোটবেলায় আমার মায়ের ন্যাওটা ছিলো আর ছেলেটা মানে ওদের নাতিটা দুজনেরই ভক্ত-সে একা একা কল্যাণীতে গিয়ে দুজন বুড়োবুড়ির কাছে থেকে যেতো।
সময় বয়ে গেলো। আমিও প্রৌঢ় হলাম। জরার সঙ্গে ব্যাধি এসে জুটলো। হৃদযন্ত্রে গোলমাল।
(পরবর্তী পর্বে সমাপ্য)
ক্রমশ