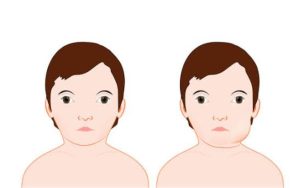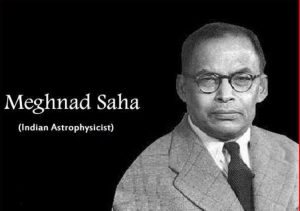পূর্বপ্রকাশিতের পর
ডা. মোসেস ব্যারনের প্রবন্ধ পড়ে, নিজের ছকা পরিকল্পনায় যথেষ্টই আস্থাশীল ছিলেন বান্টিঙ। তাই সেইদিন সকালেই ছুটলেন বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ডা. মিলারের কাছে। মিলারকে তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা জানালেন বান্টিঙ। বললেন, কুকুরের প্যানক্রিয়াসের নালি বেঁধে, আইলেটস থেকে নির্যাস সংগ্রহ করতে চান তিনি। এ বিষয়ে মিলারের মতামত ও সাহায্য চান তিনি। মিলার জানান, বান্টিঙের পরিকল্পনা ভালোই, কিন্তু জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মতো পরিকাঠামো নেই তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে এই ব্যাপারে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জন জেমস রিচার্ডস ম্যাক্লাউডের [১০] সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বান্টিঙ। ডা. ম্যাক্লাউড শুধুমাত্র দেশের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকই নন, এই মুহূর্তে তিনি পৃথিবীর অন্যতম সেরা কার্বোহাইড্রেট বিশেষজ্ঞও বটেন। তাছাড়া প্রাদেশিক রাজধানী ও দেশের সব চাইতে জনবহুল শহর হওয়ার সুবাদে টরন্টো শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও অনেক বেশি। ফলে ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে যোগাযোগ করাটাই বান্টিঙের পক্ষে শ্রেয় হবে বলে মনে করেন ডা. মিলার।
বান্টিঙের দু’চোখে তখন প্যানক্রিয়াস নির্যাসের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের জন্য সাত সমুদ্র পাড়ি দিতেও রাজি আছেন তিনি। যাবেন তিনি, ডা. মিলারের পরামর্শ মতো টরন্টো যাবেন তিনি। দেখা করবেন ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে। সবিস্তারে বলবেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। ডা. ম্যাক্লাউডের সাহায্য যে বড় প্রয়োজন আজ তাঁর।
সেই মতো, ৮ই নভেম্বর ১৯২০ সালে বান্টিঙ উপস্থিত হলেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোজা গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে। কুকুরের প্যানক্রিয়াস নালি বেঁধে, আইলেটস থেকে নির্যাস নিষ্কাশনের পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন ম্যাক্লাউডকে। ম্যাক্লাউডের সাথে কথা বলতে বলতে, সৃষ্টির আনন্দে ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করতে শুরু করেছেন বান্টিঙ। বুকটা কেমন যেন দুরুদুরু করছে তাঁর। উত্তেজনার বশে সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। সব কথা যেন গুছিয়ে বলতেই পারছেন না তিনি। ম্যাক্লাউড কিন্তু শান্ত ভাবেই শুনলেন বান্টিঙের পরিকল্পনার কথা। বান্টিঙের প্রস্তাবে বড় একটা হেলদোল নেই তাঁর। সব শুনে ঠান্ডা গলায় তিনি জানালেন, এই পরীক্ষা অবান্তর এবং খুবই খরচ সাপেক্ষ। আরো উন্নত পরিকাঠামো এবং যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনেক অভিজ্ঞ গবেষক ইতিমধ্যেই এই নির্যাস নিষ্কাশনের চেষ্টা করেছেন এবং করছেনও। কিন্তু তাঁদের কেউই এখনও পর্যন্ত সফল হন নি। এই জাতীয় পরীক্ষা থেকে ইতিবাচক ফলের আশা খুবই কম। এতদসত্ত্বেও, বান্টিঙ যদি এই পরীক্ষা করতে চান, তবে সেটা নেহাৎই তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার।
বান্টিঙের কথাবার্তা শুনে, অভিজ্ঞ ডা. ম্যাক্লাউডের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি যে পেশায় শল্যবিদ হলেও গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ বান্টিঙ। তাছাড়া এই জাতীয় পরীক্ষার হালফিলের কোনো খবরাখবরও রাখেন না তিনি। বান্টিঙের প্রস্তাব তাই নিতান্তই অপরিকল্পিত এক ব্যক্তিগত বাসনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি ডা. ম্যাক্লাউডের।
| জন জেমস রিচার্ড ম্যাক্লাউড |
ম্যাক্লাউডের কাছ থেকে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন বান্টিঙ। ম্যাক্লাউডের কথাবার্তায় বেশ হতাশ তিনি। বান্টিঙ বুঝে গেছেন যে তাঁর পরীক্ষায় বিশেষ সম্মতি নেই ম্যাক্লাউডের। ম্যাক্লাউড সম্পর্কে বুঝি মনে মনে একরাশ অভিমান পুঞ্জিভূত হয়ে উঠল তাঁর। আমার দায়িত্বে আমি পরীক্ষা করবো, তাতে ওনার অতো ব্যাগড়া দেওয়ার কী আছে? উনি তো শুধু ওনার গবেষণাগারটা ব্যবহারের অনুমতি দেবেন, তাতে এত সমস্যার কী আছে? আর হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় কুকুর আর সরঞ্জামের ব্যবস্থাও করে দিতে হতো তাঁকে। এতে কী এমন অসুবিধা হতো তাঁর? ম্যাক্লাউডের কথাবার্তায় বেজায় অখুশি হয়েছেন বান্টিঙ। এখন কী হবে তাঁর প্যানক্রিয়াস নির্যাস নিষ্কাশন পরিকল্পনার? মিলার তো কোনো আশাই দেন নি, ম্যাক্লাউডও নিরাশ করলেন। তাহলে তো তাঁর সমস্ত পরিকল্পনারই একেবারে দফারফা। জন্মের আগেই মৃত্যু ঘটবে তাঁর স্বপ্নের? দুঃখে অভিমানে হতাশায় মানসিক ভাবে বেশ খানিকটা ভেঙ্গে হয়ে পড়লেন বান্টিঙ। এখন ঠিক কী করবেন তা কিছুই বুঝে উঠতে উঠতে পারছেন না তিনি। হঠাৎ করে পৃথিবীর সব পথই যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর কাছে। দু’চোখ ভরা আশার আলো নিয়ে টরন্টোয় এসেছিলেন তিনি। আর আজ দু’চোখ ভরা ব্যর্থতার আঁধার নিয়ে লন্ডনে ফিরলেন।
ঠিক এমন সময়ে, একটা খনিজ তেল কোম্পানিতে মেডিক্যাল অফিসারের পদে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব এলো বান্টিঙের কাছে। উত্তর কানাডার বরফাচ্ছাদিত প্রায় জনহীন প্রান্তরে খনিজ তেলের সন্ধানে যাচ্ছে কোম্পানিটা। চিকিৎসক হিসেবে তাঁদের সাথে সেখানে যেতে হবে তাঁকে। অভিমান আর ব্যর্থতা আজ বাসা বেঁধেছ তাঁর বুকে। এই ব্যর্থতার আবহ থেকে মুক্তি চান বান্টিঙ। চলে যেতে চান তিনি, দূরে, অনেক দূরে, অজানা কোনো শহরে চলে যেতে চান তিনি। যেখানে কেউ তাঁকে চিনবেন না, তিনিও কাউকে চিনবেন না। ভুলে যেতে চান লন্ডন আর টরন্টোর পরিবেশ। ঠিক করলেন, তেল কোম্পানির কাজটা গ্রহণ করবেন তিনি। চলে যাবেন ভিন রাজ্যে। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে লন্ডন শহরে পসার তো ভালোই জমেছে তাঁর। সদ্য একটা গাড়িও কিনেছেন বান্টিঙ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটাও ভালোই চলছে। এমতাবস্থায় এই সব ছেড়ে চলে যাওয়াটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। লন্ডনে এখন তাঁর যা আয়, তাতে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যাবে তাঁর। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কিন্তু ঠিক হবে না। কেন জানি না, বন্ধুদের পরামর্শ মনে ধরল বান্টিঙের। মাথাটাও কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে এখন তাঁর। তেল কোম্পানীর চাকরির প্রস্তাবটা শেষ পর্যন্ত বাতিলই করলেন বান্টিঙ।
এলো নতুন বছর, ১৯২১ সাল। দেখতে দেখতে আরো তিন চার মাস অতিক্রান্তও হয়ে গেলো। বান্টিঙ কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেন না প্যানক্রিয়াস থেকে নির্যাস নিষ্কাশনের পরিকল্পনার কথা। এতদিনে অন্তত কয়েক শ’বার তাঁর পরিকল্পনার কথা ভেবে দেখেছেন তিনি। নাহ্, কোনো ভুল ভাবছেন না তিনি। কুকুরের প্যানক্রিয়াস বাঁধার পরিকল্পনায় কোনো ভুল নেই তাঁর। এভাবেই সাফল্য আসবে বলে তাঁর ধারণা। তাছাড়া, তিনি একজন শল্যবিদ। সুতরাং, কুকুরের প্যানক্রিয়াস নালি সুচারু ভাবেই বাঁধতে পারবেন তিনি। নালি বাঁধার কিছুদিন পর, প্যানক্রিয়াসটা কেটে নিলেই তো কেল্লা ফতে। আইলেটস থেকে নির্যাস নিষ্কাশন হবেই। আর তা দিয়ে প্রস্তুত করা যাবে ডায়াবিটিসের ইঞ্জেকশন। নিজের পরিকল্পনা একেবারে ছবির মতো ভাসছে তাঁর চোখের সামনে। পারবেন, আইলেটস থেকে নির্যাস নিষ্কাশন করতে ঠিক পারবেন তিনি।
সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একদিন ঠিক করলেন, আচ্ছা, আর একবার ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে দেখা করলে কেমন হয়? আর একবার তাঁর পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে তো বলা যেতেই পারে তাঁকে। দেখাই যাক না এবার কী বলেন ডা. ম্যাক্লাউড। যদি রাজি করানো যায় উনাকে। আশায় বুক বাঁধলেন বান্টিঙ। ঠিক করলেন আবার যাবেন তিনি টরন্টোয়, আবার দেখা করবেন ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে। সেই মতো, ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে, আবার টরন্টো শহরে উপস্থিত হলেন বান্টিঙ। আবার দেখা করলেন ডা. ম্যাক্লাউডের সাথে। আবার তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন ম্যাক্লাউডকে। বান্টিঙের সমস্ত পরিকল্পনার কথা স্মরণেই আছে ম্যাক্লাউডের। সব দিক বিবেচনা করে ম্যাক্লাউড বললেন, আপনি যদি নিতান্তই এই পরীক্ষা করতে চান, তাহলে তা করতে পারেন, তবে তা করতে হবে আপনার নিজের খরচায়। নিজের খরচা-পাতি দিয়ে এই গবেষণা চালাতে হবে আপনাকে। আপনাকে কোনো রকম অর্থ সাহায্য করতে পারবো না আমরা। তবে হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আর পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ও প্রয়োজনীয় কুকুরের বন্দোবস্তও করে দেওয়া যাবে। সর্বোপরি, এই গবেষণার কাজে সহযোগিতার জন্য আমার এক ছাত্রকেও জুড়ে দেবো ক্ষণ আপনার সাথে। তবে সময় কিন্তু ঠিক দু’মাস। এই দু’মাসের মধ্যেই যা করার করতে হবে আপনাকে। দু’মাসের মধ্যে যদি কিছু প্রমাণ করা যায় তো ভালো, আর এই দু’মাসের মধ্যে যদি কিছু প্রমাণ করা না যায়, তাহলে এই গবেষণা চালু রাখা আর সম্ভবপর নয় আমাদের পক্ষে, সেখানেই ইতি টানতে হবে আপনাকে।
দু’মাস! বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন বান্টিঙ। এই রকম ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে কোনো গবেষণা হয় নাকি? মনে মনে দ্রুত ভেবে চলেছেন বান্টিঙ, দু’মাসে পরীক্ষা করতে গেলে তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে ল্যাবেই পড়ে থাকতে হবে আমাকে! তাহলে আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কী হবে? টাকার জোগানই হবে কী ভাবে? চিন্তিত বান্টিঙ বললেন, ‘আমি তো ভেবেছিলাম সপ্তাহান্তে, শনি-রবিবারে ছুটিতে এসে গবেষণা করবো এখানে আর বাকি দিনগুলো লন্ডনে প্র্যাকটিস করবো’।
‘না, না, না, তা সম্ভব নয়’, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ম্যাক্লাউড। ‘এত দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালানো সম্ভব নয়। এখন যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনি নিন’।
বান্টিঙ পড়লেন মহাসমস্যায়। তিনি বুঝতে পারছেন, তলিয়ে ভাবনা চিন্তা করার পরিস্থিতি নয় এটা। কথায় কথায় না আবার বেঁকে বসেন ম্যাক্লাউড! ম্যাক্লাউড যে গবেষণা করার সুযোগটা করে দিচ্ছেন এটাই অনেক। যেটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে তা হাত ছাড়া করতে মোটেও রাজি নন তিনি। তাই আর বেশি কথা বাড়ালেন না বান্টিঙ। তড়িঘড়ি করে জানিয়ে দিলেন, রাজি, দুমাস সময়ের শর্তে রাজি তিনি। লন্ডনের চেম্বার বাজি রেখে ম্যাক্লাউডের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন বান্টিঙ। ম্যাক্লাউডও জানালেন, বেশ, তাহলে চলে আসুন, কাজ শুরু করে দিন। করমর্দন করে সেদিনের সেদিনের মতো বিদায় নিলেন বান্টিঙ। তবে কপালে তখন গভীর চিন্তার ভাঁজ তাঁর। অথচ বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঢিপ ঢিপ করছে অজানা এক উত্তেজনায়। ম্যাক্লাউড যে শেষ পর্যন্ত রাজি হবেন এটা ভাবতেই পারেন নি তিনি। উফফ, কী যে আনন্দ হচ্ছে তাঁর আজকে, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবেন না তিনি। তাঁর স্বপ্ন সফল হবার প্রাথমিক ধাক্কাটা সরে গেছে। এখন শুধু হাতেকলমে পরীক্ষা করাটাই বাকি। আর পরীক্ষায় ঠিক সফল হবেনই তিনি। এটুকু আত্মবিশ্বাস আছে তাঁর মনে। পরক্ষণেই একটা দুশ্চিন্তা ছেয়ে ফেলছে তাঁকে। টাকা? টাকা পাবেন কোথা থেকে? টরন্টোয় বসে টানা দু’মাস গবেষণা করলে লন্ডনের চেম্বারের কী হবে? আয় কী হবে তাঁর? উল্টে ম্যাক্লাউড তো জানিয়েই দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোনো রকমের অর্থ সাহায্য পাবেন না তিনি! এদিকে আবার কিছুদিন আগেই সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে একটা গাড়ি কিনেছেন বান্টিঙ। বাজারে অনেকটা দেনা রয়েছে এখনও তাঁর। এই মহূর্তে যে ক’টা টাকা আছে তাঁর হাতে, তা দিয়ে চলবে দু’মাস?
চলবে মানে? আলবৎ চলবে। চালাতেই হবে। যে করেই হোক, দাঁতে দাঁত চেপে কাটাতে হবে দু’টো মাস। এটা তাঁর জীবনপণ সংগ্রাম। প্যানক্রিয়াস থেকে প্রস্তুত করতেই হবে প্রয়োজনীয় নির্যাস। তবে লন্ডনের প্র্যাকটিস একেবারে বন্ধ করবেন না বলেই ভাবছেন তিনি। স্থানীয় সবাইকে জানিয়ে দেবেন, দু’মাসের জন্য ছুটি নিচ্ছেন তিনি। দু’মাস পর আবার চেম্বার চালু করবেন তিনি। সেই মতো দু’মাসের জন্য লন্ডনের চেম্বার বন্ধ রাখার নোটিস ঝোলালেন তিনি। ১৪ই মে ১৯২১, লন্ডনের প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিরতি নিয়ে টরন্টোগামী ট্রেনে চেপে বসলেন বান্টিঙ। এবার যেন আর টরন্টো যাচ্ছেন না তিনি, যাচ্ছেন স্বপ্নের এক দেশে। দুচোখ ভরা জেদ আর এক রাশ স্বপ্ন নিয়ে লন্ডন ছেড়ে টরন্টো অভিমুখে রওনা দিলেন বান্টিঙ। যদিও এরপর আর কোনোদিনও তাঁকে লন্ডন ফিরতে হয় নি প্র্যাকটিস করার জন্য।
(চলবে)
[১০] উত্তর স্কটল্যান্ডের ক্লুনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জন জেমস রিচার্ড ম্যাক্লাউড (১৮৭৬-১৯৩৫)। ১৮৯৮ সালে এবাডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেরিশাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে, ১৮৯৯ সালে ইংলন্ডের লন্ডন হাসপাতালে ‘ডেমনস্ট্রেটর’ পদে যোগ দেন। ১৯০৩ সালে ইউএসএর ক্লিভল্যান্ড শহরের ‘ওয়েস্টার্ন রিসার্ভ ইউনিভার্সিটি’তে ফিজিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি। এই সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। ১১টা পাঠ্যপুস্তকও (কয়েকটা যুগ্মভাবে) রচনা করেন ম্যাক্লাউড। এই পুস্তকগুলোর অধিকাংশই দারুণ সাফল্য লাভ করে। ১৯১৮ সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন ম্যাক্লাউড। ১৯২৮ সালে এবাডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রিজিয়াস চেয়ার’এ যোগ দেবার ডাক পেলে দেশে ফিরে যান ম্যাক্লাউড।