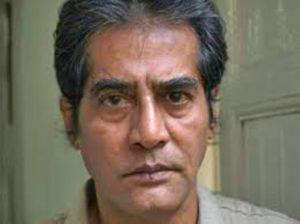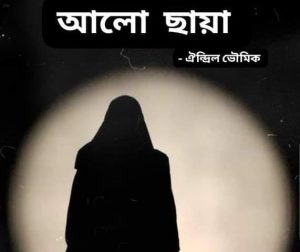আমরা যখন ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছি, বেশি নয়, বছর তিরিশেক আগের ঘটনা, তখনও বিখ্যাত মানুষেরা চিকিৎসা পেতেন সরকারি হাসপাতালে। উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র থেকে শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবাই চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতেন সরকারি হাসপাতালে। মন্ত্রী-সান্ত্রীরাও তা-ই। এমনকী বিনয় চৌধুরীর মতো বড়োমাপের নেতামন্ত্রীও। আর এখন? তথাকথিত সেলিব্রিটিদের কথা না হয় বাদই রাখছি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, তেমন হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের কথা তো ছেড়েই দিন, পাড়ার পঞ্চায়েত-প্রধান অবধি—নেহাত থানাপুলিশ জেলহাজত থেকে বাঁচার তাড়না না থাকলে—সরকারি হাসপাতালমুখো হয় না। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর বাদে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঠিক কেমন দাঁড়িয়েছে, তার আঁচ পেতে উপরের কথাগুলো খুব একটা কাজে আসবে এমন নয়—কিন্তু কথাগুলো একেবারে অপ্রাসঙ্গিকও নয়।
পঁচাত্তর বছরের আলোচনা প্রসঙ্গে স্রেফ শেষ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখাটা শুরু করলাম, কিন্তু বদলটা এমন করে ধরার চেষ্টাও, সম্ভবত, অন্যায্য নয়। কেননা, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে বাঁকবদল আমরা দেখছি— যেখানে কিছু চমকপ্রদ উন্নতির ঠিক পাশেই আমরা দেখছি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, শহুরে এলাকায় বাড়ির পাশে একাধিক ঝাঁ-চকচকে হাসপাতালের বিপরীতে প্রত্যন্ত এলাকায়, এমনকী অনেক তথাকথিত শহুরে অঞ্চলেও ন্যূনতম স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোর অভাব—যেখানে আমরা জানতে পারছি, এদেশে প্রতিদিন নাকি লক্ষাধিক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাচ্ছেন স্রেফ চিকিৎসার খরচ বহন না করতে পেরে, অথচ এই দেশেরই অনেক চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান প্রায়োগিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। একদিকে যদি দেখি বিলেত-ফেরত চিকিৎসকরা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে সময় নিয়ে রোগী দেখতে পারছেন, এমনকী রোগী আসার জন্য অপেক্ষা করছেন, আরেকদিকে ভিড়ে-ঠাসা সরকারি ওপিডি-তে একজন ডাক্তার কয়েক ঘণ্টায় পাঁচ-সাত-শো রোগী দেখতে বাধ্য হচ্ছেন, আরও একদিকে রোগীদের সামনে ডাক্তার বলতে হাতুড়ে ছাড়া অপশন নেই—আলোছায়ার এই আশ্চর্য সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে এই শেষের তিরিশ বছরেই। কেননা, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা যে একটা পয়সা দিয়ে কেনার বস্তু হতে পারে, এমন উদ্ভাবনী চিন্তা স্বাধীনতার ঠিক পরেই শুরুর কয়েক দশকে সম্ভব হয়নি। বা চিন্তাটা অনেকের পেটে পেটে থাকলেও, বুক বাজিয়ে প্রকাশ্যে বলে বসা সম্ভব হয়নি।
অতএব, স্বাধীনতার পঁচাত্তর থুড়ি ছিয়াত্তর বছর বাদে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে বসলে ধন্দে পড়তে হয়—ঠিক কোন স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা লিখব? কেননা, দেশে তো সমান্তরালভাবে দুটো স্বাস্থ্যব্যবস্থা চলছে। একটি বড়োলোকদের জন্যে, আরেকটা গরিবদের জন্য। চমকপ্রদ উন্নতি যদি প্রথমটির ধর্ম হয়—খরচা, চিকিৎসার পেছনে ব্যয় এবং চিকিৎসা-পরিকাঠামো, চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত আনুষঙ্গিক স্বাচ্ছন্দ্য দুই দিক থেকেই চমকপ্রদ উন্নতি, যে ব্যবস্থাটি মূলত বেসরকার—তাহলে দ্বিতীয়টি, মূলত সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, তার ইতিহাস লাগাতার অবহেলার, উত্তরোত্তর প্রান্তিক হতে হতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার।
আমারই এক অগ্রজপ্রতিম শিক্ষককে তাঁর কিশোর পুত্র বলেছিল—বাবা, জানো তো, বন্ধুরা বলছিল, যে সব রোগীর আর কোথাও যাওয়ার সামর্থ্য নেই, শুধু তারাই সরকারি হাসপাতালে যায়। আর যেসব ডাক্তাররা আর কোথাও চান্স পায় না, শুধু তারাই সরকারি হাসপাতালে চাকরি করে। মর্মাহত চিকিৎসক-শিক্ষক, তার পর থেকে, কোন হাসপাতালে চাকরি করেন, অপরিচিত কেউ এমন প্রশ্ন করলে, উত্তরে পারতপক্ষে সরকারি হাসপাতালের নাম করতে চান না। অতএব, স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের মাথায়, দেশের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল এমনই যে সেখানে চিকিৎসা করানো তো দূর, সেখানে চিকিৎসা বা চাকরি করাটাও আর সম্মানের নয়। আবার পাঁচতারা হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসা করেন, চিকিৎসার মাত্রাছাড়া খরচা নিয়ে কথাবার্তা উঠলেই তাঁরা অবলীলাক্রমে বলে বসেন, বিনেপয়সায় চিকিৎসা করানোর জন্য সরকারি হাসপাতাল তো আছেই, রেস্তোরাঁয় খাবার সময় খাবারের দাম কেন বেশি বা সেখানে সুস্বাদু খাবার কেন বিনেপয়সায় পাওয়া যাবে না, এমন অভিযোগ করার মানে কী! বেশি দাম জেনেইবা, বেশি দাম জেনেও তো খেতে এসেছেন!! অর্থাৎ, এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, এই চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থারই ফসল কিছু চিকিৎসক রেস্তোরাঁয় খাওয়ার মতো বিলাসী শখের সঙ্গে চিকিৎসার মতো একটা আবশ্যিকতাকে এক করে ভাবতে পারেন। শুধু ভাবতে পারেন, তা-ই নয়—বিন্দুমাত্র চক্ষুলজ্জা বা সংকোচ ছাড়া সে কথা বাজারে বলে বসতেও পারেন। এমন পরিস্থিতি সামান্য এক কি দুই দশক আগেও সম্ভব ছিল কি? স্বাধীনতার পর একখানা আস্ত শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করার শেষে এও এক অর্জন বই কী!
কিন্তু স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর ও ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা, এমন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনাটা বড্ড ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর আড্ডার মতো দাঁড়াচ্ছে। কথাগুলো একটু হলেও গুছিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক।
২০১৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেন—Universal Health Coverage— Everyone, Everywhere। বাংলায় বলতে গেলে, সবার জন্য, সর্বত্রগামী স্বাস্থ্যব্যবস্থা। এই লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করার জন্য আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ বলতে, স্বাস্থ্যব্যবস্থাটিকে কীভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব, সেই ভাবনা। ঠিক কেমন করে সাজালে স্বাস্থ্যপরিষেবা সবার নাগালের মধ্যে পৌঁছাতে পারা সম্ভব হবে, চ্যালেঞ্জ বলতে এটাই। সাজিয়ে লিখতে গেলে ইংরেজি আদ্যক্ষর A-যুক্ত কয়েকটা শব্দ দিয়ে সমস্যাগুলো ধরা যেতে পারে—
১. Awareness বা সচেতনতা ও তার অভাব—স্বাস্থ্য বলতে যে শুধুই চিকিৎসা নয়, এই সচেতনতাটুকু থাকলেই অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া যায়। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, দুই স্তরেই সচেতনতা জরুরি। শিক্ষার সঙ্গে এই সচেতনতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, কাজেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে উত্তরোত্তর অবহেলার সঙ্গে স্বাস্থ্য-অসচেতনতা যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। ব্যক্তিগত স্তরে অসচেতনতার কারণে সহজে নিরাময়যোগ্য অসুখও জটিল আকার ধারণ করে। আবার সামাজিক স্তরে এই অসচেতনতার কারণে জনস্বাস্থ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যে অবহেলাকে ঢাকতে সরকার ‘সুপার-স্পেশালিটি’ হাসপাতালের নামে মস্ত বড়ো বিল্ডিং খাড়া করলে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হওয়ার বদলে খুশি হয়ে থাকেন, বাড়ির পাশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উন্নত হওয়ার বদলে সরকারি বিমার সাহায্যে পাঁচতারা হাসপাতালে চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারেন।
২. Access—স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে এই অ্যাক্সেস-এর অর্থ, পরিষেবা গ্রহণ করতে পারার সুযোগ ও অধিকার। শব্দটির একটা কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ করা যেতে পারে—নাগাল। কিন্তু আপাতত আমরা ইংরেজি শব্দটিই ব্যবহার করব। এই অ্যাক্সেস-এর সমস্যা অনেকভাবে ঘটতে পারে। ভৌগোলিক অ্যাক্সেস-এর মানদণ্ড হিসেবে বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রের পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এমনটাই বলা হয়েছে। কিন্তু ২০১২ সালে এক সমীক্ষায় প্রকাশ, এই হিসেব মানলে এদেশে মাত্র সাঁইত্রিশ শতাংশ মানুষের কাছে বেডসহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যাক্সেস আছে, শুধু বহির্বিভাগভিত্তিক পরিষেবার হিসেব করলে আটষট্টি শতাংশ মানুষের কাছে সেই অ্যাক্সেস আছে। এ তো গেল ভৌগোলিক অর্থে অ্যাক্সেস-এর প্রশ্ন। সামাজিক বা অর্থনৈতিক অ্যাক্সেস-এর সংকটও কিছু কম নয়। বস্তির লাগোয়া জমিতে পাঁচতারা হাসপাতাল গজিয়ে উঠলে তাতে যে নো-এন্ট্রি বোর্ড না ঝোলানো থাকলেও বস্তির গরিবগুরবোদের অ্যাক্সেস থাকবে না, সেটা তো অপ্রত্যাশিত নয়।
৩. Absence of manpower—যাকে আমরা মোটামুটিভাবে ডাক্তারের অভাব হিসেবে ভাবতে শিখেছি। ২০১১ সালের তথ্য অনুসারে দেশে প্রতি দশ হাজার জন্য মানুষের জন্য কুড়িজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে একত্রিশ শতাংশ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক (চলতি ভাষায়, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার), নয় শতাংশ আয়ুশ চিকিৎসক, নার্স (প্রশিক্ষিত ও আংশিক প্রশিক্ষিত ধরে) তিরিশ শতাংশ, ফার্মাসিস্ট প্রভৃতি পেশার মানুষজন এগারো শতাংশ এবং অন্যান্য স্তরের কর্মী নয় শতাংশ। অর্থাৎ, আয়ুশ চিকিৎসকদের ধরলে, দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশই চিকিৎসক। অথচ, হিসেবটা অন্যরকম হওয়ার কথা। কেননা স্বাস্থ্যপরিষেবায় চিকিৎসকরা আপাতদৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও সামগ্রিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাকি স্তরের কর্মীরা অপরিহার্য। তদুপরি, স্বাস্থ্যকর্মীদের এই বিন্যাস সুষম নয়। শহরাঞ্চলে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম নয়,সম্ভবত বেশিই—এদিকে ভারত সরকার ২০১৫ সালে জানিয়েছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর সাতাশ শতাংশেই ডাক্তার নেই। সরকারি চাকরিতে ঢোকার ব্যাপারেও ডাক্তারদের মধ্যে আগ্রহ কম, প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়ার ব্যাপারে তো রীতিমতো অনীহা। নার্সদের ক্ষেত্রেও, সরকারি হিসেবেই, সরকার অনুমোদিত পদের অন্তত দশ শতাংশ শূন্য। এরই উলটোপিঠে আমরা যদি বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দিকে তাকাই, সেখানে শূন্যপদ তো নেইই, উলটে একটি শূন্যপদে ঢোকার জন্য ডাক্তারদের মধ্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই লেখার শুরুতে আমার অগ্রজ শিক্ষকের গল্পটা মনে করলে এমন বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা পাওয়াটা কঠিন নয়। অতএব, পাড়ায় পাড়ায় মেডিক্যাল কলেজ খুলে পাশ-করা ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন আশা কম।
৪. Affordability বা চিকিৎসার খরচ—সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসার খরচ নামমাত্র, এই রাজ্যে তো পুরোপুরি বিনেপয়সায় চিকিৎসা হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসক ও আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যকর্মী রোগীর সংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল, শহর থেকে দূরে গেলে এই অপ্রতুলতা ভয়াবহ—আবার বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীর অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু সেখানে চিকিৎসার খরচ লাগামছাড়া। এই বৈপরীত্যের সমাধান কোথায়? চিকিৎসার মান বা চিকিৎসা-পরিকাঠামোর মানের সঙ্গে সাযুজ্যহীনভাবেই, খানিকটা অন্যায্যভাবেই, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্মান হারিয়েছে। সরকারি হাসপাতালে যাঁরা আসেন, তাঁদের বেশিরভাগই আসেন বাধ্য হয়ে—অসুস্থতাজনিত বাধ্যতা নয়, অন্যত্র চিকিৎসা করাতে না পারার অসামর্থ্যজনিত বাধ্যতা, পারলে তাঁরা ধারদেনা করেও বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। অতএব, দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খরচের পঁচাত্তর শতাংশ আসে রোগীপরিজনের পকেট থেকে এবং প্রতি বছর, প্রতিদিনই অজস্র মানুষ সেই খরচ সামলাতে না পেরে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তে পরিণত হচ্ছেন, নিম্নবিত্ত থেকে পরিণত হচ্ছেন হতদরিদ্র কপর্দকশূন্যয়। সরকারবাহাদুর স্বাস্থ্যখাতে খরচ করেন জিডিপি-র দুই শতাংশেরও কম—পরিস্থিতি বদলাতে হলে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়ানো উচিত বর্তমান ব্যয়ের অন্তত দুই থেকে তিনগুণ (কথাটা অবাস্তব কিছু দাবি নয়, ওই ব্যয় পৃথিবীর সব উন্নত বা আধা-উন্নত দেশই করে থাকেন)— কিন্তু সরকারের তরফে তেমন কোনো সদিচ্ছে চোখে পড়ছে না। ব্যয় যেটুকু হয়, তারও অধিকাংশ চলে যায় হাইটেক হেলথকেয়ারে, যার অধিকাংশই শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ইদানীং তো পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে চলেছে, কেননা সরকারি স্বাস্থ্যবিমার কল্যাণে এই সীমিত পরিমাণ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের বড়ো অংশ সরকারি স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর উন্নতির বদলে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ভরতুকিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। মুশকিল হল, সার্বিক অসচেতনতার কারণে, এই অব্যবস্থা নিয়ে আমজনতারও বিশেষ হেলদোল নেই—সরকারি স্বাস্থ্যবিমা যে ধীরে ধীরে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাটিকেই ফোঁপড়া করে ফেলবে, তেমন ভাবনা নেই—বরং সরকারি টাকায় ঝাঁ-চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পেরে সবাই খুশি, যে খুশি ভোটবাক্সে প্রতিফলিতও হচ্ছে।
৫. Accountability বাদায়িত্ব নেওয়া— না, এই পয়েন্টের বিশদে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সামগ্রিক এই অব্যবস্থার দায় কার? আপাতত জনগণের চোখে ডাক্তারই প্রায় শ্রেণীশত্রু। কিন্তু সামগ্রিক এই অপ্রতুলতার পেছনে কারা? বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও লাগামছাড়া ব্যয়ের পেছনে আসলে কারা?সামনে উপস্থিত ডাক্তারবাবুর উপরই গায়ের ঝাল মিটিয়ে জনসাধারণ খুশি। অতএব, দায়ের অনুসন্ধানের আশা, আপাতত, মরীচিকা মাত্র।
কিন্তু ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমরা এসে পৌঁছোলাম কোন পথে?
ঠিকঠাক কল্যাণকামী রাষ্ট্র—ওয়েলফেয়ার স্টেট—হই বা না হই, আমাদের দেশটি রাষ্ট্র-পরিচালনার দিক থেকে রীতিমতো দাপুটে রাষ্ট্র। নাগরিকের ঠিক কী করা উচিত বা অনুচিত, সে বিষয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র সদাই বিচলিত। এতদসত্ত্বেও, বিস্ময়কর, আমাদের এই রাষ্ট্র কখনোই স্বাধীনতার পরের এই পঁচাত্তর, থুড়ি ছিয়াত্তর বছরের ইতিহাস সাক্ষী। স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয় হিসেবে ভাবেননি। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুই সরকারেরই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।আলগাভাবে দেখতে হলে, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যপ্রকল্পের দায় কেন্দ্রের এবং ব্যক্তিমানুষের অসুস্থতার মুহূর্তে চিকিৎসাবিষয়ক পরিকাঠামো ইত্যাদির ভার রাজ্যের হাতে, বিভাজন মোটামুটি এরকম। কিন্তু প্রতিরোধমূলক প্রকল্প যদি কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথভাবে পালন করতেন, তাহলে কি বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন ফারাক চোখে পড়ত? আবার ব্যক্তিমানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তো রাজ্য থেকে রাজ্যে বিভিন্ন চিত্র ধরা পড়ে। কোথাও হয়তো সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত, আবার কোথাও হয়তো বেসরকারি হাসপাতালেরই দাপট, সরকারি ব্যবস্থাটা কোনোক্রমে টিমটিম করে জ্বলছে।
অথচ, স্বাধীনতার ঠিক আগেপ্রাক-মুহূর্তই বলা যায়–স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিষয়ে আমাদের দেশেই এমন একটি রিপোর্ট পেশ হয়েছিল, যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সুদূরপ্রসারী ভাবনা এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সেই রিপোর্টের অন্তত মূল কথাগুলোও যদি মানা হত, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আজ এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারত না।
স্বাধীনতার আগে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় চিকিৎসাব্যবস্থার কথা বলতে হলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এক, নাগরিকের চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই, এমন ভাবনা (যদিও, ঔপনিবেশিক প্রভুর চোখে ভারতীয়রা সবক্ষেত্রে ‘নাগরিক’ ছিলেন না)। দুই, স্বাস্থ্যপরিষেবা যাঁদের জন্য খোলা ছিল, সেই পরিষেবা বিনামূল্যে মিলত (যদিও, আবারও মনে করাই, সেই পরিষেবা গ্রহণ করা সুযোগ সর্বত্র সবাই পেতেন না)। তিন, চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলো, বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, শহরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দেশের বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাগুলো খানিকটা খাটে বই কী! নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, এই কথাটা বড়োবাবুরা ভুলে মেরে দিয়েছেন, সেটা আলাদা প্রশ্ন—বড়ো বড়ো লোকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাঁচতারা হাসপাতালে দেশ ভরে গিয়েছে, পরিষেবা সেখানে বিনামূল্যে মেলে না, কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সরকারি স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে ‘বিনামূল্যে’ চিকিৎসা দেওয়ার দায়বদ্ধতা সরকার, অন্তত প্রকাশ্যে, এড়িয়ে যেতে পারছেন না।আর গ্রাম ও শহরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রবহমান ফারাকের প্রমাণ তো এই সদ্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যখন সরকার গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য তিন বছরের ডিপ্লোমা পাশ ‘ডাক্তার’ তৈরির কথা ভাবতে শুরু করেছেন।
প্রাচীনকালের কথা বাদ দিলে (যেমন অশোকের শাসনকাল) উপনিবেশ-পূর্ব ভারতবর্ষে সরকারি উদ্যোগে রীতিমতো সংগঠিত কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু স্থানীয় স্তরে স্থানীয় চিকিৎসকরা ছিলেন, অসুস্থ মানুষ চিকিৎসা পেতেন। শুরুতে ছিল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা—দশম শতকের পর আয়ুর্বেদের অগ্রগতি থেমে যায়। ইউনানি-র শুরু তারপর।সাহেবি ‘আধুনিক চিকিৎসা’ আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙেচুরে যায়, বা ভেঙেচুরে দেওয়া হয়, এমনও বলা যায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুরা চিকিৎসাব্যবস্থার যে বন্দোবস্ত করেছিলেন, তা মূলত তাঁদের নিজেদের জন্যই। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেত তেমন অসুখই, যেগুলো কিনা এদেশের জলহাওয়ায় অনভ্যস্ত সাহেবদের চোখে বড়ো সমস্যা ছিল। কচিৎ-কদাচিৎ দেশীয় লোকজনও চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে বড়োবাবুদের বিশেষ ভাবনা ছিল না, থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে। উনবিংশ শতকের শেষের দিলে গ্রাম না হলেও মফস্সল এলাকায় দেশীয় মানুষজনের চিকিৎসার জন্য কিছু হাসপাতাল তৈরি হয় বটে, তবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় খানিকটা বদল আসে এদেশে রকফেলার ফাউন্ডেশনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে—১৯২০ সাল নাগাদ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি দিয়ে শুরু, পরবর্তীকালে রকফেলার ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম ছড়ায় অন্তত চারটি প্রদেশে। কিন্তু তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড সীমিত থাকে রোগ-প্রতিরোধমূলক উদ্যোগেই (প্রিভেনটিভ কেয়ার)—চিকিৎসা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। লক্ষ করলে দেখবেন, আজ, এই এত বছর বাদেও, গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও রোগ-প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যপ্রকল্পগুলো যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়, সে তুলনায় গ্রামের মানুষের চিকিৎসা-ব্যবস্থা বিষয়ক সরকারি উদ্যোগ খুবই সীমিত (ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই, জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা, এ প্রশ্নই নেই, বরং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যে গুরুত্বই প্রাথমিক শর্ত। অসুস্থ মানুষটির উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত অত্যন্ত জরুরি অবশ্যই, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা সামগ্রিকভাবে একটি রাজ্য ও দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বই সর্বাধিক।
এমতাবস্থায়, ঔপনিবেশিক শাসনকালের একেবারে শেষ পর্বে, ১৯৪৩ সালে, স্যার জোসেফ ভোর-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় হেলথ সার্ভে অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি (আমাদের ডা. বিধানচন্দ্র রায়ও সেই কমিটির সদস্য ছিলেন)— ১৯৪৬ সালে সেই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে, পরবর্তীকালে যে রিপোর্ট ভোর কমিটি রিপোর্ট নামে বহুলপরিচিত।
ভোর কমিটির রিপোর্টে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল—
স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমন হবে, যার মধ্যে রোগপ্রতিরোধী ভাবনা এবং ব্যক্তিমানুষের অসুস্থতার চিকিৎসা, দুইই থাকবে। সঙ্গে থাকবে স্বাস্থ্যকর অভ্যেস গড়ে তোলার উদ্যোগও।
পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে মানুষের কাছাকাছি অঞ্চলে, যাতে যাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা, সেই মানুষজন সেই ব্যবস্থার সর্বাধিক সুফল পেতে পারেন।
সাধারণ মানুষ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মধ্যে দিয়েই কার্যকরী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।
চিকিৎসা-পেশার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষ ও আনুষঙ্গিক পেশার মানুষ—স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুধরনের মানুষকেই প্রয়োজন। এই সবধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব জরুরি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিচালনা বা বদলের ব্যাপারে এঁরা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, সেটা দেখা জরুরি।
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে, সেখানে একক ব্যক্তিচিকিৎসকের চাইতে চিকিৎসক-টেকনিশয়ান-স্বাস্থ্যকর্মী সবার সম্মিলিত উদ্যোগ অধিকতর কার্যকরী।
সমাজের কিছু অংশের মানুষ—গর্ভবতী মা, শিশু, মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া, তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।
কেবলমাত্র টাকাপয়সার অভাবের জন্য কেউ যাতে স্বাস্থ্যপরিষেবা বা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।
বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে (কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে) প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ পান, তার খেয়াল রাখতে হবে।
ভোর কমিটি সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক কী কী সুপারিশ করেছিল, সেই তালিকা জানার চাইতে লক্ষ্য হিসেবে কী কী চিহ্নিত করতে পেরেছিল, সেটা মনে রাখা জরুরি। গ্রাম-শহরের স্বাস্থ্যের বিভাজন অনুধাবন করেই কমিটির সুপারিশ ছিল, আমজনতার যত কাছাকাছি সম্ভব, সেখানে স্বাস্থ্যপরিষেবার বন্দোবস্ত করা। শুধু রোগপ্রতিরোধী পরিষেবা নয়, চিকিৎসা-পরিষেবাও—এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে তাঁরা সাজাতে চেয়েছিলেন জেলাভিত্তিক ইউনিটের মাধ্যমে। জেলার মধ্যেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকবে প্রাইমারি ইউনিট, তার উপরের ধাপে সেকেন্ডারি এবং জেলার হেডকোয়ার্টারে থাকবে টার্শিয়ারি ইউনিট। প্রতিটি জেলাতেই যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে—যেখানে রোগপ্রতিরোধ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যেস গঠনে উদ্যোগ (হেলথ প্রোমোশন), সবই হবে।
ভোর কমিটির সুপারিশ ছিল, প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য থাকতে হবে ন্যূনতম পাঁচ-শো সাতষট্টি হাসপাতাল-বেড (সেসময় ভারতে ছিল চব্বিশটি এবং ইংল্যান্ডে ছিল সাত-শো চব্বিশটি), থাকতে হবে কমপক্ষে ৬২.৩ জন ডাক্তার (তৎকালীন ভারত ও ইংল্যান্ডে ছিল যথাক্রমে ১৫.৮৭ এবং ১০০) ও ১৫০.৮ জন নার্স (ভারত ও ইংল্যান্ডে ছিল যথাক্রমে ২.৩২ এবং ৩৩৩)। ব্র্যাকেটের সংখ্যাগুলো থেকেই স্পষ্ট, স্বাধীনতার ঠিক প্রাকমুহূর্তে, ভারত এবং ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর মধ্যেকার আসমান-জমিন ফারাকটুকু—যে ফারাক, একমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সঠিক পরিকল্পনার দৃঢ়চেতা প্রয়োগের মাধ্যমেই কমিয়ে আনা সম্ভবপর ছিল, দুর্ভাগ্য আমাদের, তেমন পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক উদ্যোগ সেভাবে দেখা যায়নি।
কমিটির আরও বিভিন্ন সুপারিশ বা তার বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টার্শয়ারি-তে ভেঙে পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ভোর কমিটির সুপারিশের আদলেই ঘটেছে বটে, কিন্তু কমিটি দ্বারা ঘোষিত যে লক্ষ্যের কথা বললাম, ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সেই মহতী লক্ষ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, নিশ্চিত।
ভোর কমিটি তো স্বাধীনতার ঠিক আগের ব্যাপার, কিন্তু তার পর? স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বলা হয়েছিল, প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জারি আছে, লক্ষ্য হবে সেই কাঠামোটিকেই আস্তে আস্তে বদলানো, যেখানে সীমিত কয়েকজনের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না— সম্পদের যথাসম্ভব সুষম বণ্টন সম্ভবপর হবে এবং বয়স্ক অসুস্থ দুর্বলদের জীবনযাপন সুরক্ষিত থাকবে। আজ এই এত বছর বাদে, কথাগুলো ফিরে পড়ে দেখতে চাইলে, হতাশা নাকি আমোদ, কোনটি সঠিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, সে নিয়েই ধন্দে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে, ভোর কমিটির সুপারিশের দু-চারখানা ইতিউতি প্রয়োগ হলেও কার্যক্ষেত্রে তার মূল স্পিরিটটুকু যে ভুলে যাওয়া হবে, এ তো অপ্রত্যাশিত নয়!
কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থা তো বৃহত্তর আর্থসামাজিক পরিকাঠামো বা পরিকল্পনার বাইরের কোনো বিষয় নয়৷ স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাইরে গিয়ে যদি দেখি, প্রথম কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে তথাকথিত ‘সমাজতান্ত্রিক’ ভাবনার কথা বলা হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের শেষে বিধ্বস্ত একটি দেশের আধুনিক পুনর্গঠনের জন্য যে ভারি শিল্পের বিকাশ জরুরি ছিল, তা গড়ে তোলার মতো পুঁজি দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে তেমনভাবে ছিল না। কাজেই, ভারী শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল নব্য-স্বাধীন রাষ্ট্রকেই—এমন শিল্প, যা নিজে ততখানি লাভজনক না হলেও কাঁচামাল জোগাতে সক্ষম হবে অনুসারী শিল্পকে, যে অনুসারী শিল্প অপেক্ষাকৃত কম পুঁজিতে গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং লাভজনকও হবে। অতএব, সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্প গড়ে উঠল বটে, সেই শিল্পের হাত ধরে দেশীয় পুঁজিরও বিকাশ ঘটল—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর দেশীয় পুঁজিপতিদের শিল্পস্থাপনের জন্য পুঁজির জোগানও সহজ হয়ে গেল। কিন্তু সেই পুঁজির বিকাশ সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রে দেশের নাগরিকদের দশ শতাংশেরও কর্মসংস্থান ঘটাতে পারল না। এক অর্থে, সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি পুঁজির বিকাশ ও প্রসার ঘটাল, কিন্তু সেই পুঁজির বিকাশের সুফল কোনোভাবেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে পৌঁছাতে পারল না। অথচ, সরকারি অর্থের সিংহভাগ বেরিয়ে যেতে থাকল সেই পুঁজির বিকাশের উপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার অগ্রগতি যতখানি হওয়ার কথা ছিল, তার ধারে-কাছেও না পৌঁছাতে পারার পেছনে এই কথাটুকু মনে রাখা জরুরি বই কী!
কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিত নিয়ে এত কথা বলতে বলতে এই সার সত্যটুকু ভুলে যাওয়া চলে না, যে, স্বাধীনতার পরের এই পঁচাত্তর, থুড়ি ছিয়াত্তর, বছর গড়িয়ে গেল—এত বছরের মধ্যে, কখনো কোনো সরকারই দেশের মানুষের স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার হিসেবে দেখেননি। প্রাক-স্বাধীনতা ভোর কমিটির চিন্তাভাবনা খানিকটা ব্যতিক্রমী। পরবর্তীকালেও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে নিয়ে বিস্তর ভাবনাচিন্তা হয়েছে, কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও এসেছে। একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যের কথা উঠেছে। টুকরো টুকরো করে ভোর কমিটির কিছু কিছু ভাবনার গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে, ভুলেও যাওয়া হয়েছে, সামগ্রিকভাবে কমিটির বক্তব্যগুলো একলপ্তে কার্যকরী করার কথা সেভাবে ভাবা হয়নি। সবচাইতে বড়ো কথা, স্বাধীনতার পরের পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশের কোনো সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি, অন্তত ঘোষিত এবং লিখিত স্বাস্থ্যনীতি, সেটুকুই লিখে ওঠা যায়নি—দেশের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন হয় ১৯৮৩ সালে। এ থেকেই আঁচ করা যায়, দেশের কর্তাদের চোখে স্বাস্থ্যব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু! এবং সেই শুরুর দিন থেকে চলতে থাকা অনীহার আরেক প্রমাণ, দেশে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেশের আয়ের এক শতাংশের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে চলেছে, সেই স্বাধীনতার পর থেকেই (শুরুতে অবশ্য পরিমাণটা এক শতাংশেরও কম ছিল) হাজার ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পরেও তা দুই-আড়াই শতাংশে পৌঁছাতে পারেনি, যদিও সবার সামর্থ্যের মধ্যে একখানা মজবুত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে সেই প্রতিশ্রুত আড়াই শতাংশও যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন নিদেনপক্ষে পাঁচ শতাংশ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে মোট ব্যয়, এদেশে তার মাত্র পনেরো শতাংশ খরচ সরকার করে থাকেন। প্রথম বিশ্বে সরকারের তরফে ব্যয় সত্তর শতাংশ—আমরা গরিব দেশে, এই যুক্তি দেবার আগেই বলে রাখি, বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চল যে সাব-সাহারান আফ্রিকা, সেখানকার দেশগুলোতেও এই ব্যয় চল্লিশ শতাংশ। অতএব, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পার করার পরে, ২০০২ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত চিঠিচাপাটিতে সরকার স্বীকার করছেন—স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যাবতীয় সূচকে দেশ রীতিমতো পিছিয়ে, রাজ্য থেকে রাজ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসূচকের ফারাক প্রচুর, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল সর্বত্র বেশ দুশ্চিন্তার বিষয় এবং সেই স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া যায়নি, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর মানুষের কাছ অবধি নিয়ে যাওয়া যায়নি—সেই ‘স্বীকারোক্তি’-র পর দুই দশক পার হয়ে গেলেও পরিস্থিতি বদলেছে কি?
স্বাধীনতার পরের প্রথম দু-টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের যে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, তাতে বিশেষ বদল ঘটানোর চেষ্টা হয়নি। স্বাধীনতার আগেও যেমন, স্বাধীনতার পরেও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ সীমাবদ্ধ ছিল শহরাঞ্চলে। ‘কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’-এর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বন্দোবস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু ভোর কমিটির সুপারিশের ধারে-কাছে যাওয়ার চেষ্টা হয়নি। সাহেবসুবোরা যেমন করে জীবাণুবাহিত অসুখবিসুখে সন্ত্রস্ত থাকতেন, ঠিক তেমনই শুরুতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে। জোর দেওয়া হল টিবি প্রতিরোধেও, বিশেষত টিকার মাধ্যমে। যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনকালে সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য-চিকিৎসার প্রতি নিদারুণ অবহেলাই নিয়ম ছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিস্তর খামতি সত্ত্বেও, চমকপ্রদ উন্নতি দেখা গেল। শিশুমৃত্যুর হার কমে এল, গড় আয় বাড়ল অনেকখানিই। কিন্তু দু-খানা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, পর্যালোচনা করতে বসে, মুদালিয়র কমিটি স্পষ্টভাবে বললেন, বিভিন্ন সূচকে চমকপ্রদ উন্নতির পরেও গ্রামের স্বাস্থ্য-চিকিৎসার পরিস্থিতি বেশ খারাপ, প্রায় পরাধীন কালের মতোই। কিন্তু, আমরা এই প্রবন্ধের পরিসরে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে গঠিত একের পর এক কমিটি এবং তাদের বিভিন্ন সুপারিশের তালিকা করতে বসিনি। কেননা, দু-টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মুদালিয়র কমিটির এহেন পর্যবেক্ষণের পরও আমরা দেখব, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুহূর্তে সরকার অনুভব করছেন, দেশের স্বাস্থ্যপরিস্থিতির যেটুকু উন্নতি, তার প্রায় পুরোটাই ঘটেছে শহরাঞ্চলে এবং সেই উন্নতি ঘটতে পেরেছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি অবহেলার মূল্যে—অর্থাৎ, ভাবনাচিন্তা স্বীকারোক্তি ইত্যাদি প্রভৃতির পরেও হাল বদলায় না। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখেই ভাবা হবে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর কথা (মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম)। আবার এর কিছুদিনের মধ্যেই জরুরি অবস্থার সুযোগে, জনসংখ্যাকেই দেশের যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ ভেবে ঘোষিত হবে কুখ্যাত জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, যেখানে জোর করে বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচী গৃহীত হবে।যদিও তার ঠিক আগেই, বুখারেস্টে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সম্মেলনে সরকার বলে আসবেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সামাজিক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, প্রতি পর্বেই, এদেশের সরকার স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ভুলটা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এমন নয়—ব্যর্থতা বলতে, সেই ভুল চিহ্নিত করার পরেও ভুল শুধরে সঠিক পথটা গ্রহণ করতে পারেননি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ই আমাদের দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার “২০০০ সালের মধ্যেই সকলের জন্য স্বাস্থ্য” সনদে সই করে আসবেন—পরিকল্পনার মধ্যে সমাজমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা বলবেন, গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য-চিকিৎসার হাল ফেরানোর জন্য সেই পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ এগোনোর কথা বলবেন।কিন্তু, অর্থবরাদ্দের ব্যাপারে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা হবে না, মুখে অনেক সদিচ্ছার কথা বলা হলেও বাস্তব পরিস্থিতির বিশেষ বদল হবে না।
এতশত সমালোচনার মধ্যেও স্বীকার করি, সেসময়—অর্থাৎ স্বাধীনতার পরের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে, স্বাস্থ্যপরিকল্পনার মধ্যে অন্তত এমন বেশ কিছু কথা উঠে আসত, যা সদর্থক তো বটেই, যার পেছনে ভাবনাগুলোও সুদূরপ্রসারী। ১৯৮৩ সালে, স্বাধীন দেশের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন হল যখন, তখন স্বীকার করা হয়েছিল পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ এড়িয়ে দেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝে মেডিক্যাল শিক্ষার সিলেবাস তৈরির গুরুত্বের কথা৷ বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সারিয়ে-তোলার চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেওয়ার যে পশ্চিমা চিকিৎসাবিজ্ঞানানুসারী প্রবণতা, তাকে অতিক্রম করে রোগব্যাধি নিবারণ ও স্বাস্থ্যভ্যাস গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়ে এসেছে আগাগোড়া—বলা হয়েছে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সমাজের সব অংশকে অংশীদার করে তোলার কথা। কার্যক্ষেত্রে এসবের অনেক কিছুই কঠোর সমালোচকরা বলবেন, এসবের কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি, একথা অনস্বীকার্য, তবু ভাবনাগুলো যে সদর্থক ছিল, সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দু-টি সমস্যা বারবারই দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়ন-সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে—তার প্রথমটি যদি হয় অর্থসংকট, তাহলে দ্বিতীয়টি প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও আনুষঙ্গিক জটিলতা।
আবারও বলি, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার পেছনে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ সেই স্বাধীনতার সময় থেকে শুরু করে জিডিপির এক শতাংশের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে। শুরুতে যদি ০.৮-০.৯ শতাংশ হয়, তো পরের দিকে ১.২-১.৫ শতাংশ। এই পরিমাণ বরাদ্দ, বলাই বাহুল্য, এমনকী একখানা মাঝারি মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। তদুপরি লাল ফিতের ফাঁসের জটিলতায়, এই অর্থটুকুনিরও, সবসময়, সদ্ব্যবহার হয়নি। এবং তার পর, এই বরাদ্দর অধিকাংশই খরচা হয়েছে নিরাময়-মুখী চিকিৎসাব্যবস্থার পেছনে—এবং শহরাঞ্চলের হাসপাতালের পেছনে। নিবারণ-মুখী (প্রিভেন্টিভ) চিকিৎসাব্যবস্থার পেছনে খরচ হয়েছে যৎসামান্য। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব বারবার স্বীকার করার পরও, সেই খাতে আনুপাতিক ব্যয় বা কার্যকরী ব্যয় ক্রমশ কমে এসেছে।
জনস্বাস্থ্য, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, নিবারণ-মুখী স্বাস্থ্য—এককথায় যেকোনো দেশের স্বাস্থ্যসূচক ইত্যাদি নির্ভর করে যে পরিকাঠামোর উপর, স্বাস্থ্যব্যবস্থার এই প্রতিটি বুনিয়াদি অংশে কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বের হ্রাস, বিশেষ করে, ঘটেছে গত তিন দশকে। আর্থিক উদারীকরণ দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রেও বড়োসড়ো বদল এনেছে। সে প্রসঙ্গ দিয়েই এই লেখা শুরু করেছি। স্বাধীনতার পর শুরুর চার-পাঁচ দশক সকলের জন্য স্বাস্থ্যের কথা বলা হতো, স্লোগান পরে এলেও ভাবনাগুলো সবাইকে নিয়ে চলার মতোই হত, অন্তত মুখে অন্যরকম কিছু বলা হত না। কিন্তু শেষের তিন দশকে পরিকল্পনার সারাংশ বলতে, সমাজের সীমিত কিছু অংশের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসাব্যবস্থা বহাল রেখে নীচুতলার মানুষের জন্য কাজ-চালানো বন্দোবস্ত। আসলে, স্বাস্থ্য বা হেলথ ততদিনে হেলথকেয়ার। স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমন দাঁড়াল, যেখানে স্বাস্থ্য আর অধিকার নয়—কমোডিটি, অর্থাৎ কিনে নেওয়ার মতো পণ্য মাত্র, যে যার সামর্থ্য অনুসারে কিনবেন।
তা বলে কি পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে, যেখানে সরকার বা সরকারি দল বা এমনকী বিরোধী দল, কেউই গরিবের স্বাস্থ্যের কথা ভাবছেন না? অন্তত ভাবার কথা মুখেও বলছেন না? বালাই ষাট! গণতন্ত্রের দেশে অমন বললে চলে!! মুখে সবসময়ই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা নিয়ে সকলেই চিন্তিত। আপাতত মাঝের সময়টুকু ডিঙিয়ে আমরা একেবারে সাম্প্রতিক উদাহরণে চলে আসব। অর্থাৎ শেষ যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত হয়েছে, সেখানে। ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। যেমন আশা করা হয়, ঠিক তেমন সুরেই সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে জোর দিতে চেয়েছেন। স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের সত্তর শতাংশই প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচা করা দরকার, এমন কথাও বলেছেন। এর চাইতে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে! কিন্তু, স্বাস্থ্যনীতিটি যদি আরেকটু খুঁটিয়ে পড়ি?
এই স্বাস্থ্যনীতিতে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বাদে বাকি সব—অর্থাৎ গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা, পরিভাষায় টার্শিয়ারি কেয়ার—সেই সব ক্ষেত্রেই, সরকার একেবারে খাতায়কলমে সিদ্ধান্ত নিলেন, বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনমতো চিকিৎসা কিনে নেওয়া হবে। না, সবসময় কিনে নেওয়া হবে এমন নয়, সরকারি ব্যবস্থায় সম্ভব না হলে তখনই কিনে নেওয়া হবে, এবং পরবর্তীতে যাতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সেই চিকিৎসা সম্ভব হয়, তেমন পরিকল্পনাও করা হবে। সুতরাং, বন্দোবস্তটি আপাতত প্রয়োজন মেটানোর জন্য। কিন্তু প্রশ্ন রয়েই যায়, বরাদ্দের সত্তর শতাংশ যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় হয়, তাহলে গুরুতর অসুখের চিকিৎসার জন্য পড়ে থাকে তিরিশ শতাংশ—এবং সেই চিকিৎসা কেনা হবে ব্যয়বহুল বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে। সরকারি পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কতটুকু পড়ে থাকবে? মানে, কোন অলৌকিক পথে সরকার আপাতত কিনে নেওয়ার পরিস্থিতি থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন?
নতুন স্বাস্থ্যনীতিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপির আড়াই শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। যেটা ২০১৭ সাল, যখন নীতি প্রণয়ন হচ্ছে, তখনকার বরাদ্দের দ্বিগুণ। কিন্তু ভেঙেচুরে যাওয়া একটি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড়োসড়ো কিছু মেরামতি আড়াই শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে হওয়া মুশকিল। তদুপরি, আপাতত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পৌঁছে গেলাম, আড়াই শতাংশের সম্ভাবনাও তেমন চোখে পড়ছে না। এদিকে ওই একই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে রাজ্য সরকারগুলোর কাছে দাবি করা হয়েছে, তাঁরা যেন ২০২০ সালের মধ্যেই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে অন্তত আট শতাংশ করেন—অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার নিজেদের জন্য আট বছরে বরাদ্দ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করলেও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করলেন তিন বছরে বরাদ্দ বাড়িয়ে দ্বিগুণেরও বেশি করার— এ তো আশ্চর্য আবদার!! স্বাভাবিকভাবেই, তেমন কিছু উন্নতি, নীতিপ্রণয়নের পরের ছয় বছরেও, দেখা যাচ্ছে না।
বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কিছু অদ্ভুত নীতি দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসাব্যয়ের বিল দু-ভাবে মেটানো যায়, একটিকে বলে ক্যাপিটেশন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি ফি-ফর-সার্ভিস পদ্ধতি। প্রথমটিতে একজন মানুষ বা একটি পরিবারের বছরে (বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিকিৎসাব্যয় হিসেব করে অর্থবরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়টিতে, চিকিৎসা অনুসারে বিল মেটানো হয়। অর্থাৎ, প্রথমটিতে যদি যত কম চিকিৎসা করে খরচা বাঁচানোর চেষ্টার সম্ভাবনা থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে বেশি চিকিৎসার (যেমন, অকারণে পরীক্ষানিরীক্ষা, প্রয়োজনের চাইতে বেশিদিন হাসপাতালে ভর্তি রাখা ইত্যাদি) প্রবণতা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা। খুবই আশ্চর্যের কথা, স্বাস্থ্যনীতিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্যাপিটেশন পদ্ধতি অনুসৃত হলেও টার্শিয়ারি কেয়ারের জন্য ফি-ফর-সার্ভিস পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। অথচ, ব্যয়বহুল টার্শিয়ারি কেয়ারের জন্য ক্যাপিটেশন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারত। সেক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রের তরফে রোগীর গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে চিকিৎসার জরুরি অংশটুকু সমাধা হওয়ামাত্র রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ফেরত পাঠানোর আগ্রহ থাকত,কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় অধিক চিকিৎসা ও চিকিৎসাব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্যাপিটেশন পদ্ধতির কারণে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সামান্য সুযোগেই রোগীকে টার্শিয়ারি কেয়ারে রেফার করে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা।
অর্থাৎ, সরকারি স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমেই সরকারি অর্থ (যা কিনা জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ) কেমন করে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুষ্ট করতে পারে, তার এত চমৎকার উদাহরণ দ্বিতীয়টি পাওয়া মুশকিল। বিবিধ সরকারি স্বাস্থ্যবিমা মডেল এই কাজটিই অত্যন্ত কার্যকরীভাবে করে চলেছে—সরকারি টাকা ঘুরপথে বেসরকারি হাতে পৌঁছে দেওয়া।
এমতাবস্থায়, স্বাধীনতার পঁচাত্তর থুড়ি ছিয়াত্তর বছর বাদে, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বলতে—একদিকে ধুঁকতে থাকা সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যা কিনা উত্তরোত্তর ক্ষয়িষ্ণু, এবং দেশের মানুষের অধিকাংশের চিকিৎসা সেখানেই হয়। আরেকদিকে ক্রমশ ফুলেফেঁপে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বমানের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেখানে দেশের উপরের তলার বড়োজোর পাঁচ কি দশ শতাংশের চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। দেশের অধিকাংশ মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রথম স্বাস্থ্যব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু পরিষেবা গ্রহণ করেন দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি থেকে। দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার সিলেবাস এমনভাবে লেখা হয়, যাতে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির জন্য সস্তায় কর্মীর জোগান নিশ্চিত থাকে, আর প্রথম ব্যবস্থাটির জন্য আয়ুশ পাঠক্রমের পর ব্রিজ কোর্স পড়িয়ে জগাখিচুড়ি বন্দোবস্ত জারি রাখা হয়।
উপনিবেশ-কালীন ভারতবর্ষে সবার জন্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ছিল না। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য চিকিৎসার পৃথক মাপকাঠি ছিল। ভারতীয়দের মধ্যেও ধনীরা, খানিকটা হলেও, সুচিকিৎসা পেতে পারতেন। স্বাধীনতার ঠিক আগেই ভোর কমিটি এই অসাম্য কোন পথে দূর করা সম্ভব, সে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। ভোর কমিটির সব কথা না শুনলেও পরের কয়েক দশকে ভাবনাচিন্তা তদনুসারী ছিল, যদিও একটা সুঠাম স্বাস্থ্যব্যবস্থার মতো কাঙ্ক্ষিত অর্থের জোগান কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গত কয়েকদশকে দেশের স্বাস্থ্যভাবনা, স্বাস্থ্যপরিষেবার অসাম্য দূর করার পরিবর্তে, সেই অসাম্যকে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর করে চলেছে। আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ যদি এই অসাম্যমুখী যাত্রার গতি রোধ করতে না পারে, তাহলে, হতদরিদ্রদের কথা তো ছেড়েই দিন, আমরা যারা এখনও আর্থসামাজিক শ্রেণী-অবস্থানের কারণে সুচিকিৎসার সুযোগ পাই, পরিস্থিতি তাদের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।