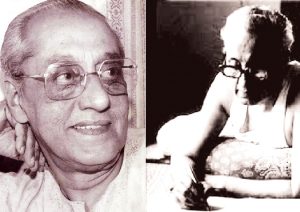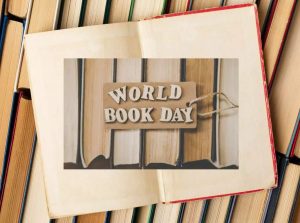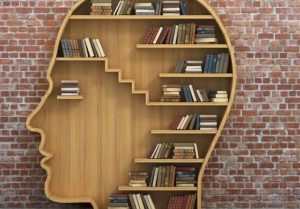অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের রাজ্য থেকে রোগীরা দক্ষিণ ভারতে চলে যায় কেন? এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। হতে পারে-
১. আমরা পশ্চিমবঙ্গে ভালো চিকিৎসা দিতে পারি না।
২. এখানে খরচ বেশী হয়।
৩. আমাদের ব্যবহার ভালো না।
৪. দক্ষিণ ভারতের হাসপাতালে এক ছাদের নীচে সব ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গাতে তা নেই।
৫. মানুষ আমাদের অবিশ্বাস করে।
জানি না। সত্যিই জানিনা। তবে কতগুলো ঘটনা জানি, যেগুলোতে আমি নিজে যুক্ত ছিলাম। শোনা গল্প নয়।
১
কয়েকদিন আগে কলকাতার এক ক্লিনিকে ঢাকা থেকে এক রোগিনী এসেছেন। তাঁর ঘাড়ের কাছে মেরুদন্ডে স্লিপ ডিস্ক আছে। হাতের জোর এবং সাড় অনেক কমে গেছে। সাত মাস যাবৎ ঢাকায় চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসা করছেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জেন যিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর। তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। কারণ তিনি কলকাতা সহ ভারতের অনেক শহরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বক্তৃতা এবং ট্রেনিং দিতে যান। তিনি শেষ পর্যন্ত সার্জারির বিধান দিয়েছেন।
কিন্তু ঢাকার বাঙালি রোগিনী সার্জারী করাতে চান না। তিনি কলকাতায় এসেছেন এই শুনে যে, এখানে আমরা নাকি যে রোগীর সার্জারির একান্ত প্রয়োজন তাকেও শুধুমাত্র কয়েকটা ট্যাবলেট-ক্যাপসুল খাইয়ে সুস্থ করে তোলার মত ম্যাজিক জানি। তিনি ঢাকার ডাক্তারদের সম্পর্কে অনেক খারাপ খারাপ কথা বললেনে, যা আমার একেবারে ভালো লাগল না। কলকাতার ডাক্তারদের সম্বন্ধে তাঁর অবাস্তব রকমের ভালো ধারণা। কিন্তু যেই আমি বললাম যে, সার্জারী ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তিনি মুখ চুন করে দক্ষিণ ভারতের দিকে রওনা হলেন।
২
আমাদের সহ্যশক্তি অতুলনীয়। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ সবে চালু হয়েছে। কলেজ ক্যান্টিন তখনো দূর অস্ত। কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছি। ঘরবাড়ি নেই। হোটেলে-মেসের ঘরে থাকি। আউটডোর শেষ করে বটতলাচকের আরতি হোটেলে ভাত খেতে যেতাম। হাসপাতালের অন্যান্য কর্মী এবং রোগীর পরিজনদেরও দুপুরের খাওয়ার জায়াগা ছিল ওটাই। সেই আরতি হোটেলের দেওয়ালে দেওয়ালে ডাঃ ডি কে লোধের পোষ্টারের মত দক্ষিণ ভারতের এক ধর্মীয় দাতব্য হাসপাতালের বিজ্ঞাপন সাঁটা থাকত। তাতে থাকত মেদিনীপুর এবং আপামর পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদের সম্বন্ধে বাছা বাছা বাক্য, কম খরচায় দক্ষিণের শহরে গিয়ে ম্যাজিকের মত সুস্থ হওয়ার হাতছানি এবং সর্বদুশ্চিন্তাহরণ কয়েকটা ফোন নম্বর।
৩
মেদিনীপুরের দিনগুলো পেরিয়ে অনেক বছর পরে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারী হাসপাতালে মেরুদণ্ডের চিকিৎসা করি। আউটডোরে রোগী দেখছি। দক্ষিণ ভারতীয় হাসপাতাল গ্রুপের চেন্নাই-এর হাসপাতালে কোমরে অপারেশন হওয়া আসানসোলের এক রোগী এসেছে সেলাই (ষ্টেপল) কাটাতে। তিনি সরাসরি আমার রোগী না হলেও, হাসপাতাল পরিচালকদের অনুরোধে এটা করে দিতে হবে। সেই রোগী বাইরে অপেক্ষা করছে। অন্য রোগী দেখছি। হঠাৎ শুনি বাইরে কোলাহল,উত্তপ্ত পরিবেশ। আমার সহকারীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, ‘আপনার দুই রোগীর মধ্যে ঝগড়া লেগেছে।’
ঘটনাচক্রে সেদিন আমার নিজের অপারেশন করা এক রোগীও ষ্টেপল খুলতে এসেছে। কাকতালীয় ভাবে এই দুই রোগীরই বয়স প্রায় সমান। দুজনেই পুরুষ। চেহারা একই রকম। দুজনেই সুগারের রোগী। কোমরের একেবারে একই জায়গায় সমস্যা ছিল দুজনের। একই অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের পরে দুজনেই খুব ভালো আছেন। ব্যথা উধাও।
প্রথমজনের বাড়ি আসানসোল। তিনি চেন্নাই থেকে অপারেশন করে এসেছেন। ষ্টেপল খোলার সময় তিনি বললেন, ‘আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।’
অভিযোগ! আমি তো এর অপারেশন করি নি! তাহলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিসের?
‘কি অভিযোগ?’
‘আপনারা কলকাতার ডাক্তাররা নিজেদের বিজ্ঞাপন করতে পারেন না? লোকের কত উপকার হত এতে!’
‘ডাক্তাররা নিজেরা নিজেদের বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। অন্ততঃ মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়ম তো তাই বলে। সুস্থ ও সন্তুষ্ট রোগীর মুখে মুখেই আমাদের প্রচার হয়।’
‘শুধু না জানার জন্য আর ওই চেন্নাইওয়ালাদের বিজ্ঞাপনে ভুলে দেড়গুণ খরচ করে চেন্নাই থেকে অপারেশন করে এলাম। অথচ এখানে কত কম খরচ হত!’
দেড়গুণ নয়। আমার সহকারী বিল দেখে জানালো, আমার অপারেশন করা রোগীর থেকে ওনার খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ বেশী।
৪
অল্প কয়েক বছর আগেকার কথা। সকাল সকাল এক পরিচিত ফিজিওথেরাপিষ্টের ফোন। ‘স্যার একটা অদ্ভুত কেস পাঠাচ্ছি। ‘—-‘ তে অপারেশন করা (দক্ষিণ ভারতের এক নামকরা ধর্মীয় দাতব্য হাসপাতালের নাম বলল)। কিন্তু অপারেশনের পরে উন্নতি তো হয়ই নি। বরং আরো খারাপ হয়েছে। এক্সরে দেখে আমার কেমন গন্ডগোল মনে হচ্ছে।’
কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার মোবাইল ফোনে এক্সরে চলে এল।
ফিজিওথেরাপিষ্ট বলল, ‘এক্সরে টা দেখেছেন স্যার? সমস্যা আছে না?’
‘আছে তো!’
‘আপনি এটা ঠিক করে দিতে পারবেন তো।’
‘পারব। পাঠিয়ে দাও।’
কিছুক্ষণ বাদে রোগী এল। অর্ধেক প্যারালাইসিস। অপারেশন হয়ে গেছে প্রায় দু-সপ্তাহ আগে। মেরুদণ্ডের দুই নম্বর লাম্বার হাড় ভাঙা। কিন্তু স্ক্রু-রড লাগানো আছে তিন নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর হাড়ে। ভাঙা দু নম্বর হাড় যেমন ছিল, তেমনই পড়ে আছে। রোগীকে ও রোগীর বাড়ির লোকজনদের এক্সরে দেখিয়ে বুঝিয়ে বললাম, ‘দেখুন, আগের অপারেশনে সমস্যা আছে। আপনার আর একবার অপারেশন করা প্রয়োজন। ভর্তি করুন, করে দেব। তবে প্যারালাইসিস পুরোপুরি ঠিক হবে কিনা বলতে পারব না।’
‘তা কি করে বলবেন? কলকাতায় এইসব জটিল অপারেশন হয় না কি! আবার ওখানেই নিয়ে যাব।’
ফিজিওথেরাপিষ্টের মুখে শুনলাম রোগীকে বিমানে চড়িয়ে আবার সেই দক্ষিণের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়েছে। রোগী স্থায়ী ভাবে প্যারালাইজড্ এবং খুশি।
৫
বছর পনের আগের কথা। আমি তখন দিল্লির এইমস্ হাসপাতালে মেরুদণ্ডের সার্জারির একটা ট্রেনিং নিতে গেছি। প্রফেসর অরবিন্দ জয়সোয়ালের আউটডোরে রোগী দেখছি। পাশের টেবিলে এক বাঙালি দম্পতি তাদের বছর পনেরোর কন্যা সন্তানকে প্রফেসর জয়সোয়ালকে দেখাতে নিয়ে এসেছে। জয়সোয়াল স্যারের আউটডোরে সরাসরি যাওয়া সহজ কথা নয়। কারণ একমাত্র খুব জটিল রোগীরা জুনিয়দের কড়া ছাঁকনি পেরিয়ে জয়সোয়াল স্যারের কাছে পৌঁছতে পারে। এইমস-এর হিসেব মতো এই রোগী তেমন জটিল কিছু নয়। খুব উঁচু স্তরে যোগাযোগ থাকলে অবশ্য আলাদা ব্যপার।
রোগীর পরিবার বেশ উচ্চবিত্ত এবং নিশ্চয়ই কোনো শক্ত খুঁটির জোর আছে। মেয়েটির স্কোলিওসিস অর্থাৎ পিঠ খুব বাঁকা। দেখে আমারই মনে হল অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই। জয়সোয়াল স্যারও তাই বললেন। রোগীর বাবা-মা স্বাভাবিক ভাবেই অপারেশনে রাজি নয়। তবে সেটা মেরুদন্ডের অপারেশনে বাড়তি ঝুঁকির কারণে নয়। তাদের এই অনীহার কারণ, অপারেশনের কারণে পিঠে লম্বা দাগের জন্য বিয়ের বাজারে মেয়ের দাম কমে যাবে। তারা কলকাতাতেও সম্ভাব্য সব ডাক্তারকে দেখিয়েছে। তারাও একই উপদেশ দিয়েছে এবং সেটা ওদের পছন্দ হয়নি। তাই এইমসে আগমন।
অনেকক্ষণ ধরে পোষা বেড়ালের মত জয়সোয়াল স্যারের হাতে পায়ে ধরে ঘ্যানঘ্যান করছিল ওরা। টিপিক্যাল বাঙালি হিন্দি এবং মাঝে মাঝে বাংলা শুনে পাশের টেবিল থেকে আমি খেয়াল রাখছিলাম। জানতাম জয়সোয়াল স্যার এবার বিরক্ত হবেন। তাই হল।
‘অপারেশন ছোড়কে দুসরা কোই অপশন নেহি হ্যায়।’
‘ব্যায়াম করনেসে স্ট্রেট নেহি হোগা? দেখিয়ে না।’
ডাঃ জয়সোয়াল বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, ‘তুমহারা কলকাত্তাকা পেশেন্টকো সামহালো।’
‘কলকাত্তাকা বাঙালি ডক্টর হ্যায়। আপ উনকো পাশ যাইয়ে। আচ্ছাসে সমঝায়েগা।”
‘আপনাদের মতো ভালো ডাক্তাররা কেন যে কলকাতায় ফিরে আসেন না! কলকাতার অবস্থা কত খারাপ ভাবতে পারবেন না।’ কলকাতার ডাক্তারদের সম্পর্কে বাছা বাছা কয়েকটা বিশেষণ প্রয়োগ করল সেই দম্পতি।
‘আমি তো মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পড়াই। এখানে এসেছি ট্রেনিং নিতে।’
যেই শুনল আমি পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তার, তাও আবার মেদিনীপুরে চাকরি করি- সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর বাঘে পরিণত হল। ‘আপনি’ থেকে সোজা ‘তুমি’,’গঙ্গারাম হাসপাতালে ভালো স্পাইন সার্জেন কে আছে বল তো?’
‘জানি না। খুঁজে নিন। আমার কাজ আছে।’
৬
অবশেষে একটা উল্টো ঘটনা বলি।
কর্পোরেট হাসপাতালে আমার আউটডোরে এক রোগী এল। তামিল যুবক। বাড়ি কোয়েম্বাটোরে। চাকরি করে কলকাতায়। সেক্টর ফাইভে। বেশ কিছুদিন হল কোমরে এবং পায়ে প্রচন্ড ব্যথা। পায়ের জোর কমে গেছে। স্লিপ ডিস্ক। অপারেশন লাগবে। অন্য সব চিকিৎসা করা হরেছে। সাফল্য আসে নি। সেদিনই ভর্তি হতে চায়। তার রেকর্ড ঘেঁটে দেখলাম, রোগী প্রথমে দেখিয়েছে কোয়েম্বাটোরের গঙ্গা হাসপাতালে। ওখানেও ওই একই – অপারেশন করতে বলেছে। কোয়েম্বাটোর অর্থোপেডিক্সে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল।
‘ওখানে অপারেশন করালেন না কেন?’
‘ওখানে তো সব কিছুতেই অপারেশন করতে বলে। তাই ওদের বিশ্বাস করতে পারিনি।’
ভর্তি হল, অপারেশন করলাম।
সেই হিন্দিতে একটা কথা আছে না, ‘ঘর কি মুরগী দাল বরাবর’।