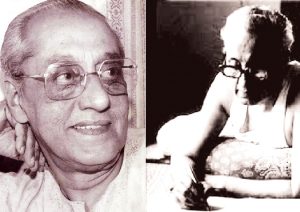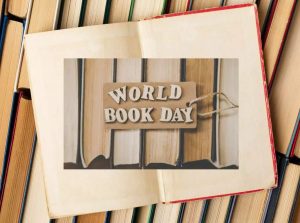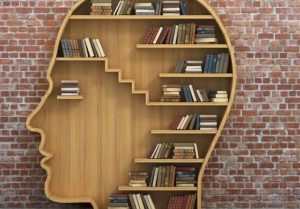সাত সকালে পেটে ব্যথার রোগী। সাথে পরিজনের পল্টন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সঙ্গে আসা গ্রামীন চিকিৎসক। রাত থেকেই “গ্যাসের” চোটে পেটে ব্যথা। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জম্পেশ খেয়ে দেয়ে পেট ফুলেছে। পুরোটাই ডান হাতের কম্ম ।গত দেড়দিন বাম হাত আর কাজেই লাগেনি স্যার। মিচকি হেসে গ্রামীণ চিকিৎসক আমার গুরুগম্ভীর মুখে কিছুটা লঘুত্ব লেপে দেওয়ার চেষ্টা করলেও “বাম হাত আর কাজেই লাগেনি” কথাটায় কপালের ভাঁজ গভীর হলো আমার।
বলেন কি? তার মানে পটি হয়নি?
যন্ত্রনাকাতর মুখখানা বার দুয়েক দুলিয়ে জামাইবাবাজি ফুলে যাওয়া পেটের আভরণ খুলে ঢাউস পেট খানা মেলে ধরলেন আমার সামনে।
সত্যিই মাত্রাতিরিক্ত গ্যাস ভরে দেওয়া বেলুনের মত আকৃতি। শক্ত। ফ্লুইড থ্রিল না থাকলেও পেট এক্কেবারে অ্যাসাইটিস রোগীর মত ফোলা।
গলা থেকে স্টেথোস্কোপ নামিয়ে পেটের দুই দিকে পেরিস্টালসিসের গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ শোনার আশায় উৎকর্ন হলাম। কিন্তু পরিজনেদের কথাবার্তায় বিশেষ কিছু কানে পৌঁছালো না। ঈশারায় ওঁদের চুপ করতে বলে পূনরায় স্টেথোস্কোপ রাখলাম পেটের ওপর। মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় বার দুয়েক সে আওয়াজ পেলেও তা মাত্রাতিরিক্তভাবে কম।
রোগীপরিজনের মাঝেই গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “পটি না হয় হয়নি, কিন্তু বাতকর্ম হয়েছে কি?”
আমার কথায় শ্বশুরবাড়ির পরিজনেদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আড়ালে মাথা নাড়িয়ে বললেন “না”।
চমকে উঠলাম। সামাজিক লজ্জার বাতাবরন ভেঙে আবারও জিজ্ঞেস করলাম- “একবারও হয়নি?”
জামাইবাবাজি প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
আমার কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো। ইন্টারকম ফোন ঘুরিয়ে হাসপাতালের এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে ফোন করলাম আমি। “স্ট্রেট এক্স-রে অ্যাবডোমেন ইন এরেক্ট পশ্চার – এটা এক্ষুনি করা যাবে?”
এক্স-রে টেকনিশিয়ান গৌতম বাবু সোৎসাহে বললেন, “কেন হবে না ডাক্তারবাবু? রোগীকে পাঠিয়ে দিন। এক্ষুনি করে প্লেট পাঠিয়ে দিচ্ছি।”
যাক! খানিক আশ্বস্ত হয়ে যেই না রোগীর দিকে ফিরেছি, দেখি রোগীর মুখে জল ঢালছেন গ্রামীণ চিকিৎসক।
আমি রে রে করে উঠলাম। জলের বোতল হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতেই সকলের বাঁকা চোখের শিকার হলাম আমি। জল খাওয়ানোর মত এক নিরীহ আয়োজনে আমার প্রচন্ড আপত্তির প্রকাশ সকলের বিরক্তি বাড়ালো। কিন্তু আমি যে রোগের কথা ভাবছি, তাতে যে মুখে কিচ্ছুটি দেওয়া যায়না। খাবার তো দূর অস্ত,জল,এমনকি মুখে খাবার ওষুধও নয়।
বলতে না বলতেই এক্স রে ডিপার্টমেন্ট থেকে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাক পড়লো। হাতে চ্যানেল করে প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করার পর স্যালাইন চালিয়ে স্ট্রেচারে শুইয়ে এক্স রে ডিপার্টমেন্ট গেলো রুগী।
আমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে গ্রামীণ চিকিৎসক মুখ ঝুঁকিয়ে আড়ালে জিজ্ঞেস করলেন “কি বুঝছেন স্যার?”
তখন সবেমাত্র এম.বি.বি.এস পাশ করে গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে জয়েন করেছি। সাধাসিধে আটপৌরে জীবন দর্শনে মারপ্যাঁচের প্রয়োজনীয়তা তখনও এক্কেবারেই না জানা।
গ্রামীণ চিকিৎসকের প্রশ্নের জবাবে কোনোকিছু রাখঢাক না রেখেই বিশ্লেষণ করলাম- “আমার মনে হয় ‘ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশান’। সহজ ভাষায় পেটের নাড়িভুঁড়ির মাঝে খাদ্যনালীর বাধা। মুখ দিয়ে যাইই খান না কেনো, এ রোগের কারনে পায়ুপথে অগ্রগতি বন্ধ।অর্থাৎ কিনা পেরিস্টালসিস নেই বললেই চলে। ফলতঃ পেট ফুলে বিপত্তি। পায়খানা বন্ধ। এমনকি বাতকর্ম টুকুও বন্ধ। এমতাবস্থায় মুখে কিছু খাওয়ালে তা আরও অবস্ট্রাকশান বাড়িয়ে সংকট বাড়িয়ে তুলবে।এক্ষেত্রে কিচ্ছুটি না করে হাসপাতালই একমাত্র রাস্তা।”
“তাহলে উপায়?” গোল গোল চোখে জিজ্ঞাসা করলেন গ্রামীণ চিকিৎসক।
“ঘোরতর অবস্ট্রাকশান হলে সার্জারী ছাড়া গতি নেই। ভলভিউলাস, ইন্টাসাসেপশান,আ্যাঢেশান,ক্রন’স ডিজিজ,ডাইভার্টিকুলাইটিস,বা কোনও ক্যান্সারের কারনে এ অবস্ট্রাকশান হলে আমাদের গ্রামীণ হাসপাতালে তা সম্ভব নয়। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে হতে পারে।”
এই “নিয়ে যাওয়ার” কথা হলেই রোগী পরিজনেরা হঠাৎ বেঁকে বসেন। চিকিৎসকের দক্ষতায়ও প্রশ্নচিহ্ন বসান। অধিকাংশ চিকিৎসক নিগ্রহের মূল কারনও এখান থেকেই জন্ম নেয়।
নব্য চিকিৎসক জীবনে এ সংকট আগে কখনও সম্যক অনুভব করিনি। কিন্তু রেফারের সম্ভাবনার উল্লেখ করতেই গ্রামীণ চিকিৎসক নম্রতার খোলস ছেড়ে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে বাকি পরিজনেদের ভিড়ে আস্ফালন শুরু করলেন।
ইতিমধ্যে এক্স-রে এলো। এয়ার-ফ্লুইড লেবেল দেখে বুঝলাম, যা ভেবেছি ঠিক তাই। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশান। তবে কি কারণে এ অবস্ট্রাকশান, এক্স-রে দেখে তা বোঝার মত অভিজ্ঞতা তখনও তৈরি হয়নি আমার।
বাকি প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন গুলো দেওয়া হলো। সবুজ রেফারাল কার্ড লিখে রোগী পরিজনেদের দিকে বাড়াতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রোগীর শাশুড়ী মা। “পারবেন না যদি, আগেই বলে দিতে পারতেন। খামোকা সময় নষ্ট করলেন কেন? সামান্য গ্যাসের চিকিৎসা করতে পারেন না। হাসপাতাল খুলে বসে আছেন কেন?”
গ্রামীণ হাসপাতালে এ হেন চিকিৎসার পরিকাঠামোর অভাবের যুক্তি সেদিন একদল পরিজনের অযৌক্তিক চিৎকারে মিলিয়ে গিয়েছিলো।
একপ্রস্ত তান্ডবের পরে হাসপাতাল ছাড়েন তাঁরা। চিকিৎসকের জীবনে রোগীর পরিজন কেন “পেসেন্ট পার্টী” হিসেবে পরিগনিত হয় তার কিছু ধারনা হয়েছিলো সেদিনই।
এরপর বাকি রোগীদের ভিড়ে কেটে গেছে প্রায় ঘন্টা ছয়েক।হঠাৎই অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে চার কাঁধে সেইই রোগীকে নিয়ে ঢুকলেন বেশ কয়েকটা নতুন মুখ।
“ডাক্তারবাবু, গ্রামীণ চিকিৎসক বলেছিলেন- পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ির অবস্ট্রাকশান হয়েছে বোধহয়। পায়ুপথে এনেমা দিয়ে পায়খানা করিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিন তিন খানা এনেমা দিয়েও কিচ্ছুটি হয়নি। বরং পেটব্যথা বেড়ে কাতর হয়েছেন উনি।সকলের পরামর্শে মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করার জন্য উদ্যত হই। তখন রাগের মাথায় আপনার দেওয়া রেফারাল কার্ডটি উনার শাশুড়ী মা ছিঁড়ে ফেলায় আপনার কাছে আবার ঐ কার্ড নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি স্যার।”
ডাক্তারবাবুদের রাগ পুষে রাখতে নেই। অভিমানের স্থানও হাসপাতালে নেই। নতুন মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে খসখস করে সবুজ কার্ড লিখে ব্যাথা কমানোর ইঞ্জেকশন পূনঃপ্রয়োগ করে মেডিক্যাল কলেজের সার্জারী বিভাগের বন্ধু চিকিৎসককে ফোন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ করে বিদায় দিলাম রোগীকে।
পরের দিন বন্ধু চিকিৎসকের ফোনে আশ্বস্ত হলাম।অপারেশান সাকসেসফুল। ইন্টাসাসেপশান ছিলো। প্রাণে বেঁচেছেন কোনোমতে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় মনে পড়লো- গ্রামীণ চিকিৎসকের সাথে আলোচনায় মুখে কিছু না দেবার কথা বললেও পায়ুপথে এনেমা দেওয়াও যে বিপজ্জনক সে বিষয়ে আলোচনা আর করা হয়ে ওঠেনি।