(পূর্ব প্রকাশিতর পরে)
আগের পর্বের পর এটা-ওটা কারণে লম্বা ফাঁক পড়ে গেল। আগের কথাগুলো মনে আছে কিনা, জানি না। একটু এই বিরতির সুযোগে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।
বিজ্ঞানের চর্চা বা বিজ্ঞানের গবেষণা এবং সামাজিক পরিসরে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা গবেষণালব্ধ তথ্যের গুরুত্ব নিরূপণ – দুটি রীতিমতো আলাদা বিষয়। আর দুইয়ের মধ্যে ফারাকও অনেক।
একটা উদাহরণ ধরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমাদের অনেক ক্রিয়াকলাপ বা আচার-ব্যবহারের পিছনে থাকে আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তি – এবং তার পিছনে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে আমাদের জিন তথা জেনেটিক গঠন। কিন্তু, মানুষকে বা মানুষের সামাজিক আচরণকে শুধু কিছু জৈবিক প্রবৃত্তির সমষ্টি হিসেবে দেখতে চাইলে সমস্যা হয়। কেননা, বেশ কিছু আচরণের ব্যাখ্যা মেলে না সহজে।
ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথা হল প্রজাতির সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই বেছে বেছে নির্বাচিত হবে, যেগুলো কিনা প্রজাতিকে বংশানুক্রমে এই বিশ্বে টিকে থাকতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ এত বছরের বিবর্তনের শেষে, আমাদের শরীরে তেমন জিন-ই বেশী করে থাকবে, যেটি কিনা আমাদের জিনকে বংশানুক্রমে প্রবাহিত করতে সাহায্য করবে – বংশবৃদ্ধি করতেও সুবিধে হবে, এবং নিজেদের ও পরবর্তী প্রজন্মের বেঁচে থাকতেও সুবিধে হবে। এই বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের সপক্ষে প্রমাণের অভাব নেই এবং এই তত্ত্ব মোটামুটিভাবে সর্বজনমান্য। সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই, যখন এই তত্ত্বকে সামাজিক তত্ত্ব হিসেবে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করার কথা ভাবা হয়, যা কিনা হয়েছিল নাৎসি জার্মানিতে।
কিন্তু এর সাথে, আরেকটি সমস্যাও দেখা দিচ্ছে প্রায়শই, যা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে চাইছি এখন।
যেহেতু তেমন জিনই নির্বাচিত হবে, যা কিনা প্রজাতিকে সবচেয়ে সফলভাবে টিকিয়ে রাখতে ও বংশবিস্তারে সাহায্য করবে – এর উল্টোপিঠেই একটি ধারণা জুড়ে দেওয়া হয়, জিনের ধর্মই নিজের স্বার্থরক্ষা – যেকোনো মূল্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখা ও পরবর্তী প্রজন্মে নিজেকে প্রবাহিত করা। কিন্তু, যেহেতু জিনের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা বা মন বা শরীর নেই, সেহেতু এই তত্ত্বের সাথে এমন ধারণা ওতপ্রোতভাবে জুড়ে যেতে থাকে, যে, জিন যদি স্বার্থপর হয়, তাহলে জিনের অধিকারী মানুষটিরও স্বাভাবিক প্রবণতা স্বার্থপরতা। অর্থাৎ, জিন মাত্রেই স্বার্থপর, অতএব মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর।
অথচ, স্রেফ একদল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মানুষ নিয়ে গঠিত সমাজের তুলনায় একদল পরার্থপর মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা-নির্ভর একটি সমাজে তো বেঁচে থাকা অনেক স্বস্তির ও সহজ – আরামেরও। তাহলে তেমন জিন কেন নির্বাচিত হবে না??
খুঁজেপেতে দেখা গেল, তথাকথিত সভ্য মনুষ্যসমাজে তো বটেই, ভদ্রতার শিক্ষাবিহীন প্রাণিসমাজেও এমন অনেক আচরণ রয়েছে, স্রেফ আত্মসর্বস্বতার তত্ত্ব দিয়ে যার হিসেব মেলানো মুশকিল। তাহলে?
বিজ্ঞানীরা আনলেন পারস্পরিক স্বার্থপর সহযোগিতার তত্ত্ব – এমন সহযোগিতা, যা কিনা বৃহত্তর অর্থে স্বার্থপরতাই – রেসিপ্রোকাল অলট্রুইজম। এই তত্ত্ব অনুসারে, একটি প্রজাতি এমন আচরণ করতে পারে, যাতে আপাতদৃষ্টিতে তার নিজের কোনো লাভ নেই – উল্টে আপাত ক্ষতির সম্ভাবনা – যদিও, তাতে অপরের উপকার হচ্ছে। কিন্তু, একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সেই ব্যবহারের মধ্যেই এমন প্রত্যাশা (সচেতন বা অবচেতন) থেকে যায়, যে, এমন আচরণের বিনিময়ে উপকৃতের কাছে থেকে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে, তাতে উপকারীর স্বার্থই সাধিত হবে এবং বিপরীত পক্ষ থেকে পরিপূরক আচরণ পাওয়া গেলে প্রজাতির টিকে থাকার সুবিধে হতে পারবে। এক কথায়, অন্যের উপকার করতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে নিজের ক্ষতি হলেও, সেই উপকারের মধ্যে দিয়েই আশা করা হচ্ছে যে প্রত্যুপকার পাওয়া যাবে এবং সব হিসেবনিকেশ মিললে, আপাতদৃষ্টিতে যাতে ক্ষতি বলে মনে হচ্ছিল, তেমন আচরণে আখেরে লাভই অনিবার্য। গত শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই তত্ত্বের শুরু এবং ষাট বা সত্তরের দশকের মাথাতেই রীতিমতো গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে উপকারী-প্রত্যুপকারীর সংখ্যা কেমন হলে বিনিময় লাভজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে, সে ব্যাপারটিও ছকে ফেলা সম্ভব হয়।
প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো রেসিপ্রোকাল অলট্রুইজমও একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব – এবং তাকে বিভ্রান্তিকর বলে দাগিয়ে দেওয়ার জন্যে এই আলোচনা নয়। আলোচনা, এই তত্ত্বের বিকৃত অর্থে প্রয়োগ নিয়ে।
তত্ত্বটিকে সহজভাবে দেখা যেতে পারত এইভাবে, যে, এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যেই পরার্থপরতার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল। এবং পরার্থপরতা যে কোনো ব্যতিক্রমী আচরণ নয়, বরং একপ্রকার নিয়মই, এই তত্ত্বের মাধ্যমে সেটাকেই মান্যতা দেওয়া হল। পাশাপাশি, যেহেতু এত হাজার বছরের শেষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গুণাবলীর অন্যতম এই পরার্থপরতা, অতএব এই পরার্থপরতা একটি বিশেষভাবে কার্যকরী ধর্ম এবং সেই ধর্মের লালনপালনে আমাদের যত্নবান হওয়া জরুরী।
কিন্তু, আশ্চর্য ব্যাপার, বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রভাব দাঁড়ালো তার বিপরীত। এমন ধারণা চাউর হতে থাকল, যে, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের মতো স্বার্থপরতা ও উপযুক্ত মুহূর্তে পরার্থপরতা (যা কিনা এই তত্ত্বের বিকৃত প্রয়োগ অনুসারে একধরনের ধান্দাবাজি) আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তির মধ্যেই পড়ে – অতএব, সে নিয়ে আলাদা করে ভাবার দরকার নেই এবং বাড়াবাড়ি ধরণের স্বার্থপরতা নিন্দনীয় ও পরার্থপরতা প্রশংসনীয়, এমন ভাবারও কারণ নেই। এখানে উদাহরণ হিসেবে পরার্থপরতা গুণটির কথা বলছি। কিন্তু, এই একই উদাহরণ সমাজবদ্ধ মানুষের যাবতীয় নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেসব গুণগুলোকে এই কদিন আগেও মহৎ ও শিক্ষণীয় গুণ বলে ভাবা হত, অথচ যেগুলো ইদানীং আমাদের জেনেটিক গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জৈবিক প্রবৃত্তি হিসেবে ও-আর-এমন-কী-ব্যাপার-এ পরিণত হয়েছে।
আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে, এতে অসুবিধের কী আছে!! ভাবতে পারেন, আমাদের দোষগুণের পিছনে জিনের অবদান প্রমাণিত হয়েছে, সে তো ভালো ব্যাপার। বিজ্ঞান যত এগোবে, ততোই আমরা আরো বেশী বেশী করে নিজেদের আচার-ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেতে থাকব, এবং নিজেদের চিনতে শিখব, তাই না?
না। একটু দ্বিমত পোষণ করছি। মলমূত্র ত্যাগ জৈবিক প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই – তার অর্থ এই নয় যে, নেমন্তন্ন বাড়িতে সকলের মাঝে সেই প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের দোষগুণের পিছনে জিনগত ব্যাখ্যা থাকা বা না থাকার সাথে আমরা কোন বৈশিষ্ট্যকে গুণ আর কোন বৈশিষ্ট্যকে দোষ বলে চিহ্নিত করব, তার কোনো সরাসরি যোগাযোগ নেই – মানুষ হিসেবে কোন কোন গুণকে শিক্ষণীয় ও পালনীয় হিসেবে বিবেচনা করব আর কোন কোন দোষকে লাগাতার চর্চা ও শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়াসী হব, তারও অনিবার্য সম্পর্ক নেই। সে কাজ এথিক্স, তথা নীতিশাস্ত্রের।
পরিবেশ দূষণ নিয়ে আজকাল অনেক কথা হয় চারপাশে। বায়ুদূষণ, জলদূষণ বা শব্দদূষণের বিপদ নিয়ে সকলেই ওয়াকিবহাল – সচেতনতাও বেড়েছে অনেকখানি, যদিও কার্যকরী পদক্ষেপের পরিমাণ নামমাত্র। কিন্তু, কার্যকরী পদক্ষেপের আগের সলতে পাকানোর যে সচেতনতা বৃদ্ধির পর্বটি, সে কাজে এগোনো গিয়েছে অনেকখানিই।
অথচ, একটু ভেবে দেখলে অনুধাবন করতে পারা কঠিন নয়, যে, নৈতিক পরিবেশও আমাদের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ – মানুষ হিসেবে মানুষের মতো করে বেঁচে থাকার জন্যে পরিবেশের আর পাঁচটা কাঠামোর চাইতে এর গুরুত্ব কিছু কম নয় – এবং, দূষিত বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ যেমন বিপজ্জনক, বিকৃত ও অবহেলিত এথিক্সের পরিবেশে মানবতার টিকে থাকা তার চাইতে কিছু কম সঙ্কটের নয়।
মুশকিল এই, যে, এই নৈতিক পরিবেশের গুরুত্বের কথা আমরা খুব সহজেই ভুলে যেতে পারি। যেহেতু, আর পাঁচটা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো এই নৈতিক পরিবেশের অস্তিত্ব সহজ প্রমাণযোগ্য নয়, সুতরাং তাকে অগ্রাহ্য করা সহজ। নৈতিক পরিবেশে কী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বা কী করে তাকে আরো ক্লেদমুক্ত করা যেতে পারে, সে আলোচনা শুরু করার আগে জরুরী সেই এথিক্সের পরিবেশের অস্তিত্ব ও গুরুত্বর বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়া।
নাৎসি জার্মানিতে চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীরা কেমনভাবে সহনাগরিকদের নির্যাতন করেছিলেন, হত্যালীলায় অংশ নিয়েছিলেন – ঠিক কেমন করে দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও অত্যাচারী হিসেবে নবকলেবর ধারণ করতে একটুও সঙ্কোচ হয়নি – ঠিক কোন পথে চিকিৎসক রোগীর সাথে তাঁর আবহমান কাল ধরে চলে আসা উপশম ও শুশ্রূষার চুক্তি বা দায় ভুলে নির্যাতনকারী হয়ে উঠলেন – এসব ভেবে শিউরে ওঠার মুহূর্তে বা কী-করে-পারলেন-এমন-পাশবিক-হয়ে-উঠতে এই প্রশ্ন জাগলে, মাথায় রাখুন, কলুষিত ও দূষিত নৈতিক পরিবেশে এসবের কোনোটিই খুব একটা আলাদা করে আশ্চর্যের নয়। নীতিবোধের কাঠামোটাই যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, বা নীতিবোধের প্যারাডাইমটাই যদি সরিয়ে আনা যায় – পুরোনো নীতিবোধের পরিবর্তে ভিন্ন নীতিবোধ, যেখানে স্বার্থপরতা বা আত্মকেন্দ্রিকতা মার্জনীয়, এমনকি স্বাভাবিক ও কাম্যও – তাহলে আচরণের নৈতিক বা অনৈতিক বিচারের মানদণ্ডটিই তো ভিন্ন হয়ে যায়, তাই না? কথাটা মেডিকেল এথিক্স তো বটেই, বৃহত্তর এথিক্সের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।
নাৎসি জার্মানি একটি চরম উদাহরণ – চূড়ান্ত অধঃপতনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু, একমাত্র উদাহরণ নয়। এবং সমাজব্যবস্থায় এই এথিক্সের পরিবেশের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন না হলে, তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব – শুধু সম্ভবই নয়, হয়ত অনিবার্যও।
না, নাৎসি জার্মানির মতো দলে দলে মানুষকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠিয়ে নিকেশ করে ফেলা হবে আবারও, এমনটা এখুনি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু, সমাজের এক অংশের মানুষকে অপর বা মনুষ্যেতর হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে তাদের কষ্টে নিস্পৃহ থাকা – এমনকি, প্রত্যক্ষ না হলে, পরোক্ষে তাদের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনকে সমর্থন করা – খুবই সম্ভব। অত্যাচারীর মুখ বদলানোর সাথে সাথে অত্যাচারের ধরণও বদলায় – নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত হলে কিছুই অন্যায্য বোধ হয় না। আর, যেহেতু একটি বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রদর্শন সর্বময় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং যেহেতু সে ব্যবস্থা আমূল বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা এখুনি নেই – ব্যক্তিগত নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত হলে রাষ্ট্রীয় বয়ানের আড়ালে বহুজনের অবরুদ্ধ ক্রন্দন সহজে দৃশ্যমান হয় না – দৃশ্যমান হলেও, আপত্তিকর বলে বোধ হয় না। কথাটা চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সবার জন্যেই প্রযোজ্য।
(চলবে)




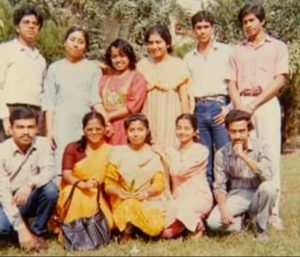

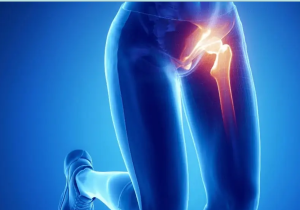







অসাধারন।