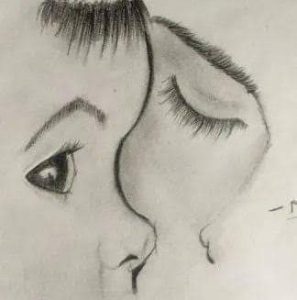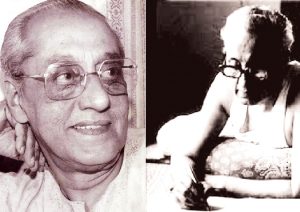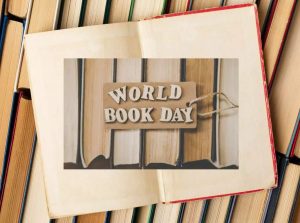-স্যার, এখনও সময় আছে। বাসের টিকিট ক্যান্সেল করে প্লেনের টিকিট কেটে দিই? কষ্ট কম হবে। চট্টগ্রামের টিকিট অ্যভেইলেবল। ট্র্যাভেল এজেন্ট কে ফোন দিব? এই যে দেখুন স্যার।
কথাগুলি বলে তার মোবাইলটা এগিয়ে দিল জামশেদ। সে সার্চ করে বার করেছে টিকিটের খতিয়ান। জামশেদ নামের এই সপ্রতিভ যুবকটি ইউনিসেফ বাংলাদেশের তরফে ঢাকায় আমার দেখাশুনো করছে। তার মতে অযথা এই বাস ভ্রমণের কষ্ট চাইলেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমার থেকে বেশ কিছুটা ছোটো এই যুবকের কাছে আমি মস্ত একজন কেউ। সে জানে আমি ডলারে মাইনে পাই। এই উপমহাদেশে ডলারের চেয়ে উঁচু আরাধ্য স্বপ্ন মধ্যবিত্তের আর কিছু নেই।
ঢাকা থেকে রাঙামাটি যাচ্ছি। ভায়া বান্দরবান। আমি ইউনিসেফের লোক। নেহাত নীচু থাকের না। একটু উঁচু পদেরই। অনায়াসে এরোপ্লেনে চট্টগ্রাম গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরতে পারতাম। কিন্তু হাতে সময় আছে। এবারের এই কাজটা আমি নিজেই যেচে নিয়েছি।
ইউনিসেফের যে অংশটা অনাথ আর পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে আমি সেই টিমে কাজ করি।
এক হিসেবে এই কাজটা আমার খুবই মনের মত। আমি ওই শিশুদের চিনি। আজ থেকে নয়। অনেক ছোটোবেলা থেকেই। আমি নিজেই যেখানে বড় হয়েছি সেটা ছিল আগরতলার একটা ইউনিসেফ এইডেড অনাথাশ্রম।
আমি অমিত লারমা। দেশগত ভাবে আমি ভারতীয়।
যদিও বাংলায় কথা বলি. আমার বেড়ে ওঠা, পড়াশুনো বাংলা মাধ্যমে। আমি কিন্তু জনজাতিগত পরিচয়ে একজন চাকমা। ভারতে জন্মেছি বলে ভারতীয় চাকমা। বাংলাদেশে জন্মালে আমি হতাম বাংলাদেশি চাকমা। আমার মুখের অবয়ব কিছুটা মঙ্গোলীয়। আমার স্বজাতীয় চাকমারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা মিজোরাম অরুণাচলে আর বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়িতে।
কী ভাবে আমার মা আমাকে সমেত সেই মিশনারি ডেস্টিটিউট হোমে পৌঁছেছিল আমার জানা নেই। মায়ের মুখ আমার মনেও পড়ে না ভালো। অনেক ধরাধরি করে আমাকে বাঁচাবার তাগিদে আমার মা বিনতা লারমা আমাকে জমা করবার ব্যবস্থা করেছিল সেখানে।
অনাথাশ্রমের লোকেদের কাছে শুনেছি তার কিছুদিন বাদেই সে মারা যায় আগরতলার এক হাসপাতালে। না, আমার বাবার কোনও খোঁজ মা হোমের ওদের বলে যায়নি।
তারপর সেখানেই বড় হলাম। ক্রিশ্চান মিশনারিরা চালাতেন। যিশুবাবার গানটান গাইতে হত যদিও, লাগোয়া ইশকুলটায় লেখাপড়া হত ভালোই। আমাদের ক্রিশ্চান বানানোর তাগিদ টিচারদের তেমন ছিল না।
বরং হেড স্যার, আমরা বলতাম বড় পাদ্রিবাবা, ধর্মের ক্লাসে বাইবেল পড়াতেন বটে, কিন্তু খুব জোর দিতেন ভালো আর সৎ মানুষ হবার ব্যাপারে।
নিজে বোধহয় পড়াশুনোয় সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিলেন। তাই জোর দিতেন বিজ্ঞান শেখার ব্যাপারে। বলতেনও, -বিজ্ঞান মানেই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত। এর মত সততা আর কোখাও নেই। যদি জীবনের সব কটা ধাপে সৎ থাকতে পারিস তবে তুই সব চেয়ে বড় ধার্মিক।
একটু উঁচু ক্লাসে উঠে বুঝেছি বিজ্ঞানের সব কটা ধাপে সৎ থাকতে বলে ফাদার আসলেই কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।
আর আমিও বলতে গেলে লেখাপড়ায় মন্দ ছিলাম না। শেষ পরীক্ষায় ভালোই রেজাল্ট হয়েছিল। অনাথাশ্রমের যা নিয়ম আঠারো বছর বয়েস পেরোলেই সেখানের পালা শেষ। আমাকে কিন্তু ওঁরা ছাড়লেন না। ছোটোখাটো কাজ দিয়ে ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর পাশাপাশি পড়াশুনোও করতে থাকলাম।
ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা নিয়ে পড়তেই পারতাম। আমাদের সায়েন্স টিচারদের খুব ইচ্ছে ছিল, রেজাল্ট যখন ভালো হয়েছে, আমি যেন ডাক্তারি নিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার ডাক্তার হবার ইচ্ছে ছিল না। বরং খুব ইচ্ছে করত মানুষকে জানতে। আগরতলায় আমার গ্র্যাজুয়েশনের বিষয় ছিল নৃতত্ববিদ্যা।
ফাদার মেনে নিয়েছিলেন। -হ্যাঁ, ওটাও বিজ্ঞান বই কি। কী জানো, সব বিষয়ই বিজ্ঞান। ইতিহাস, ভূগোল, এমনকি লিটারেচরের গ্রামার অংশটাও। প্রসিড মাই বয়।
শুধু মেনে নেওয়াই নয়, পরের পড়াশুনোটুকু যাতে ঠিক ভাবে করতে পারি দেশে বিদেশে চিঠি চালাচালি করে খরচ চালাবার স্টাইপেন্ড অবধি জোগাড় করে দিয়েছিলেন সেই আলো সমান মানুষটি।
অ্যানথ্রোপলজিতে গ্র্যাজুয়েশন করতে গেলাম লক্ষ্ণৌএর ন্যাশনাল পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে। মাস্টারসও করলাম সেখানেই। ট্রাইবাল এথনিসিটির ওপর আগ্রহ ছিল। তাই সেখানকার প্রফেসর বাগচির উপদেশে পরের পিএইচডির কাজ করলাম রাঁচি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হেমব্রমের কাছে। এই উপমহাদেশের নানা আদিবাসীদের এথনো-বায়োলজি নিয়ে পিএইচডির কাজ। এই দীর্ঘ পড়ার সময়ে কতজনের কথাই যে জেনেছিলাম।
ইউরোপের নানান দেশের কত যে সাহেবরা এই দেশের পাহাড় জঙ্গল নদী পেরিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কত না আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্ত বিষয়ে কত অজানা কথা যে জানিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু কি ইংরেজ? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, জার্মান বেলজিয়াম, সব জায়গা থেকে এসেছিলেন তাঁরা। কীসের টানে কে জানে!
তারপরে তো এদেশি মানুষেরাও প্রচুর কাজ করেছেন। শরৎ চন্দ্র রায় থেকে শুরু করে ডঃ দিনেশ্বর প্রসাদ, ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা, ডঃ কে সুরেশ সিং মায় পি দাশ শর্মা অবধি তো বটেই তারপরেও কতজন মাইলস্টোন কাজ করে গেছেন।
আমি পিএইচডির শেষে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গেলাম। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের অ্যানথ্রপলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে পোস্ট ডক করলাম।
চাইলে ওদেশেই কিম্বা বিদেশে অন্য কোথাও থেকে যেতে পারতাম। সেই অর্থে পিছুটান তো ছিল না তেমনকোনও। সবাই ভাবত, এমনকি আমিও ভাবতাম, শেষ অবধি লেখাপড়ার লাইনেই থেকে যাব। কিন্তু ভাগ্যদেবী ভেবে রেখেছিল অন্য রকম। সেই আমার অদ্ভুত ছোটোবেলার টানে টানেই।
ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন ইউনিসেফের কর্তারা। বোর্ডে অন্যদের সঙ্গে ক্যাথরিন রাসেলও ছিলেন। তখনও এত উঁচু পোস্টে যাননি উনি। সিভি খুব খুঁটিয়ে পড়েছিলেন মনে হল। অন্তরঙ্গ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন ছোটোবেলা থেকে বড় হওয়ার ইতিহাসের সবটুকু। তারপরে আচমকাই জিজ্ঞেস করলেন, -অন্যরা যা করে, সেই রকম উঁচু মাইনেতে দেশ ছেড়ে বিদেশের কোনও ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না?
আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, এই কাজের জন্য ইউনিসেফই একটা উপযুক্ত প্ল্যাটফরম। পৃথিবীময় ইউনিসেফ শিশুদের নিয়ে কাজ করে। এদেশেও। ইউনিসেফের কাজ এই দেশে বিশেষ করে যারা সহায়হীন সেই শিশুদের সাহায্য করা। তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা।
কবছরই বা আর বাকি আছে জীবনের। যদি কিছু করতে হয় আমার সেই মা হারা ছেলেবেলাটার জন্য, তা এখানেই।
সেই কথাই ক্যাথরিনকে বলেছিলাম, ইন্টারভিউএ।
একেবারে সমাপ্তির আগে জিজ্ঞেস করলেন ইন্টারভিউ বোর্ডের একজন মেম্বার, -কোথায় পোস্টিং পেতে চাও। এই নিয়ে কাজের স্কোপ তো সব মহাদেশে। অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ নাকি তোমার সাবকন্টিনেন্টেই?
হেমব্রম স্যারের কথাগুলো যেন কানে বাজছিল। সেই যে মাতৃঋণ শোধ করতে হবে বলেছিলেন স্যার, সেই কথা। দেশে ফিরে এলাম। ইউনিসেফের কাজ নিয়ে।
উঁচু পদেই। প্রথমে কাজ শুরু করলাম ঝাড়খণ্ডে। তারপরে নিজের আগ্রহেই কাজের ক্ষেত্র বদলালো। বেছে নিলাম নিজের পছন্দের কাজ। কী সেই কাজ? খুলে বলি।
আমার পরের দিকের পড়াশুনো আর গবেষণার ক্ষেত্রও ছিল এই আদিবাসী উপজাতি আর জনজাতি যাই বলা হোক এরাই। পরে সেই ক্ষেত্র আরও সূচীমুখ হয়েছে। একরকম জোর করে স্থানচ্যুত করানো হয়েছিল এদের একটা অংশকে। তারাই ছিল পিএইচডি-তে আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র।
সহায়হীন অধিকারহীন শিশুদের একটা বড় অংশই আছে ঠাঁইনাড়া আদিবাসী উপজাতি আর জনজাতিদের মধ্যে।
আংকল টমস কেবিনে যে গল্প রয়েছে, এই দেশের গল্পও তার থেকে আলাদা কিছু না। এই স্থানচ্যুত প্রকারান্তরে দাস বানানো মানুষদের সন্তানেরা সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই বংশানুক্রমে না খেতে পাওয়া অশিক্ষা অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারে বেড়ে ওঠা এক শ্রেণী।
*
আমার সেই পুরো কাহিনিটা বলি।
পিএইচডি করার সেই সময়ে আমার থিসিস গাইডের নাম আগেই বলেছি। প্রফেসর হেমব্রম।
সেদিন ডিপার্টমেন্টে প্রথম গেছি। ডিপার্টমেন্টের কাজ শুরু করিনি তখনও। স্যরের সঙ্গে দেখা করেছি।
তাঁর সঙ্গে আগেই ইমেইলে আমার আগ্রহের বিষয়ে কথা হয়েছে। স্যার এই ব্যাপারে অথরিটি।আমার পিএইচডির বিষয়ের অভিমুখ নিয়ে আগামীকাল কথা হবে। এইটুকু শুধু কথা হল আজ।
কথা সেরে বেরিয়ে এসে ইউনিভার্সিটির বাইরে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি। দেখি স্যার বেরোচ্ছেন। মুখোমুখি দেখা। স্যারের কতকগুলো বাড়াবাড়ির ব্যাপার কলকাতায় থাকতেই শুনেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে সাইকেলে যাওয়া আসা করেন। আমাকে দেখে তড়িঘড়ি নামলেন। আমি একগাল হেসে স্মার্ট হবার চেষ্টায় বললাম,-স্যার, চা বলি একটা?
সেই চা খেতে খেতেই আমার অভিমুখ নির্ধারিত হয়ে গেল।
স্যার বললেন,-চা? বলতেই পারো। এ তো আমাদের জাতীয় পানীয় প্রায়। তবে একটু খেয়াল করলে এই চায়ে কিন্তু খুব সহজেই রক্ত আর ঘামের গন্ধ পাবে। কাল এই নিয়ে কথা হবে তোমার সঙ্গে।
বললেন বটে কাল কথা হবে, কথা বলা শুরু করে দেখি কথা শেষই হতে চায় না। সেই কথা মানে থিসিসের বিষয় নিয়ে স্যারের সঙ্গে আলোচনা আর শেষ হতেই চায় না।
পর দিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন,-শোনো হে, একজনকে আসতে বলেছি। বাঙালি। নাম পরিমল মুখার্জি। সে আসা অবধি ওয়েট করো।
তিনি আবার কে, কে জানে! হবেন হয় তো ইউনিভার্সিটিরই কোনও টিচার।
স্যারকে জিজ্ঞেস করতে বললেন,-না না, টিচার নয় সে। সিভিল সার্ভিসের লোক। কিন্তু তোমাকে যে ব্যাপারে জড়াব সে ব্যাপারে তার অনেক জ্ঞান। সেই আসলে গাইড করবে তোমাকে। তার খুব আগ্রহ আর জানাশোনা এই সব ব্যাপারে। এর পরে অনেক জায়গায় বাস্তবিকই যেতে হবে তোমাকে প্রোজেক্ট ওয়ার্কে। সে তোমাকে সুলুক সন্ধান দেবে সে সবের।
কিছু পরেই এলেন সেই ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পরিচয় হতে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবেন। ভদ্রলোক ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। সরকারি অফিসের গতানুগতিক কর্মী নন। ধরাবাঁধা কাজের বাইরেও প্রচুর আগ্রহ এই বিষয়ে।
কথাবার্তা শুরু হল। স্যারের সঙ্গে তো হচ্ছিলই। এবার পরিমল বাবুর সঙ্গেও।
আসলে স্যার চাইছিলেন আমার কাজটা হোক গতানুগতিকতার বাইরে।-বুঝলে অমিত, আদিবাসীদের নিয়ে লেখাপত্র গবেষণা অনেক আছে। কিন্তু এই এদের কথা তেমন নেই। আদিবাসী হয়েও যারা প্রায়শই নেগলেক্টেড তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে তোমাকে।
চমকে উঠেছিলাম, আদিবাসী হয়েও আদিবাসী নয়, তারা আবার কারা?
স্যার বললেন -আছে, আছে। তাদের আদিবাসী পরিচয় যাতে মুছে যায় তার জন্য প্রচুর মাথা খাটিয়ে তাদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভারতে। শুধু ভারতেই বা বলছি কেন, সাবকন্টিনেন্টের নর্থ ইস্ট জুড়ে সর্বত্র। ঘরের পাশে বাংলাদেশেও।
– তারা কারা স্যার? মিজো নাগা খাসি জয়ন্তিয়া মিরি, দিমাসা, কুকি, ওয়াংচু, মিশমি, বোরো… এক নিঃশ্বাসে আমার জ্ঞান উজাড় করে দিলাম।
-না হে, সেই ভূমিপুত্রদের কথা বলছি না। সেই হিসেবে ধরলে তুমিও তো ওই নর্থ ইস্টের থেকেই উঠে আসা, চাকমা। আমি পায়ের নীচে মাটি থাকা মানুষদের কথা বলছি না। বলতে চাইছি, যাদের পায়ের নীচের মাটি কেড়ে নিয়ে, বলতে গেলে এক্সপ্লয়টেশনের কৌটোয় ঝাঁকিয়ে আইডেন্টিটি কেড়ে নিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা বানিয়ে দেওয়া হল।
এক পর্যায়ে স্যার বললেন,-ভেবো না যেন, পরিমল এই ডিপার্টমেন্টের কাজ করে বলে এত কিছু জানে। ও আসলেই, এই চাকরি পাবার আগে থেকেই এই ব্যাপারে নেশাগ্রস্ত।
এত প্রশংসা শুনে পরিমল নামের ভদ্রলোক বেশ লজ্জা পেয়ে গেলেন।-বড্ড বাড়িয়ে বলেন আপনি!
স্যার বললেন,- লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার এই ছাত্রটিকে তোমার জিম্মায় দিচ্ছি পরিমল। ওকে মোটামুটি যে ব্যাপারটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে, সেটা ট্রাইবালদের ব্যাপার হলেও একটু অনালোচিত। মাইগ্রেটরি ঠিক না, ডিসপ্লেসড ট্রাইবাল লাইফ। বিরাট পার্সপেকটিভে ওরা ছড়িয়ে আছে এই সাবকন্টিনেন্টের ইতিহাসে… ব্রিটিশ… ভারত… পাকিস্তান… বাংলাদেশ সব পিরিয়ডে।
আমার দিকে ফিরে বললেন -এই পরিমল ঝাড়খন্ড সিভিল সার্ভিসের এই চাকরিতে আসার আগে জলপাইগুড়িতে ছিল। চা বাগানে ছেলেবেলা কাটিয়েছে।
*
আলাপ হবার এক সপ্তাহের মধ্যে কোন মন্ত্রে কে জানে, আমি পরিমলদার ভাইয়ের মত হয়ে গেলাম। স্যার বলে দিয়েছেন,
-রোজ ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টে আসার দরকার নেই। তুমি পরিমলের সঙ্গে ওর অফিসে গিয়ে ওদের কাগজপত্র লাইব্রেরি ঘেঁটে ফিল্ডটা জেনেবুঝে নাও। মাস দুয়েক তো লাগবেই। তারপরে ফিল্ডের কাজ শুরু করবে।
সরকারি অফিসে ফাইলপত্র থাকে জানতাম। কিন্তু লাইব্রেরিও থাকতে পারে প্রথম জানলাম। বলতে গেলে পরিমলদার নিজের উদ্যোগেই তৈরি। আর সেখানে খালি তত্ত্বের কচকচি ভরা স্ট্যাটিসটিকসের ছোটোবড়ো অঙ্ক গোঁজা নীরস বইই নয়, এই ব্যাপারে ইংরেজি হিন্দি বাংলা আর অন্য ভারতীয় ভাষায় যা সাহিত্য রয়েছে তারও প্রচুর সম্ভার। আমি বাংলা মিডিয়াম বলে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহী বলাই বাহুল্য।
★
পরিমলদা’ আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, -আমার বাবা ছিলেন ডুয়ার্সের চা বাগানের বাবু। চা বাগানের ব্যাপার মোটামুটি সব জায়গায়ই এক রকম। সে ডুয়ার্স বলো কী আসাম বরাক বলো। সেখানে মোটামুটি তিন শ্রেণীর লোক, বুঝলে তো। সব চে উঁচু পজিশনে মালিকপক্ষ, টিপ্ল্যান্টাররা। এককালে ছিল ইউরোপিয়ান সাহেব আর দিশি মালিকেরা। স্বাধীনতার পরে অবশ্যি পুরোটাই দেশি সাহেব। মাঝের লেভেলে থাকত এই বাবুরা। ডুয়ার্সে তারা আমার বাবার মত। অধিকাংশই বাঙালি। আর একদম নীচের তলায় থাকত কুলিলাইনের লোকগুলো। তুমি যাদের নিয়ে কাজ করবে।
★
আমার মানসিক অসুখ আছে। মাঝে মধ্যে সেই অসুখ মাথাচাড়া দেয়। মায়ের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে খুব।
একসময় আমি নেট ঘেঁটে আত্মহত্যার উপায়গুলি দেখতাম অতীতে। সম্ভবত এই অসুখের মূল লুকিয়ে রয়েছে আমার অগোছালো মা-হীন ছেলেবেলার মধ্যে।
মা, আমার মা। একলা একটা চাকমা মেয়ে। কে জানে, হয় তো সিঙ্গল মাদারই ছিল। স্বামী তো নেইই। পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। ভরসা শুধু আগরতলায় লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ। আর কেউ নেই। আমাকে সঙ্গে নিয়েই মায়ের কাজের বাড়িতে যেত মা।
-কী রে বিনতা, ভদ্দরলোকের বাড়িতে কাজ করে দিনকে দিন ফরসা হয়ে যাচ্ছিস তো! খুব কিরিম পাউডার মাখচিস না কী?
আমার হলদেটে হতে থাকা মাকে ঠাট্টা করে শুধোত বস্তির অন্য মেয়েরা। আসলেই তখন মা ভেতরে ভেতরে মরতে শুরু করেছিল।
কপালগুণে যে বাড়িতে কাজ করত মা, সে বাড়ির গৃহকর্তা বিনোদ মজুমদার ছিলেন স্থানীয় চার্চের কর্মী। মায়ের যখন রক্তে ক্যান্সার ধরা পড়ল, ওই বাড়ির সবাই খুব করেছিলেন মায়ের জন্য।
মা যখন সরকারি হাসপাতালে মরল, তার আগে ওই মজুমদার বাবুই আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর চার্চের ফাদারের কাছে। ফাদারের চিঠি নিয়ে হোমে।
আমার জীবনে সেই এক মোড়। মায়ের ওপর অভিমান যেতে চায় না। মা, তুই কেন রে আমাকে এই বিশাল পৃথিবীতে এনেছিলি? আনলি যদি, থাকলি না কেন? সেই পাঁচ বছরের ছেলেটা কোথাও উত্তর পেত না।
অন্য বাচ্চাদের কেউ আসে দেখতে। আমার জন্য কেউ আসত না।
শুধু বড় ফাদার। প্রায় দেবতাসম এক মানুষ, আমাকে বড় ভালোবাসতেন।
সে কি প্রথমে একদিন কাঁদছিলাম এমন অবস্থায় ধরে ফেলেছিলেন বলে?
ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার চলে যাওয়া মাকে আকুল আর্জি জানাচ্ছিলাম, -মা, আমারে তোর কাছে নিয়া চল। বড় খিদা লাগে!
সাদা জোব্বা পরা ফাদার, সেই হেডস্যার, যাকে সমীহ করত বড়রাও, আমাকে কোলে তুলে নিলেন, শেখালেন, -কোনও ভয় নেই। ভয় কীসের? আমরা সবাই আছি তো!
বড় হতে লাগলাম। অঙ্ক করতে ভারি ভালো লাগত। বিজ্ঞানও। আর ভালো লাগত ইতিহাস ভূগোল। খুব জানতে ইচ্ছে করত আমি কে, কোথা থেকে এলাম। কিন্তু পড়ার বইয়ে সেই খবর থাকে না। ক্লাস এইট নাইনে উঠে স্কুলের লাইব্রেরিতে উথালপাথাল খুঁজতাম আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলো। একটাই শুধু সুতো। সেই যে মা নাম লিখিয়েছিল সেই পরিচয়। চাকমা।
আমাদের লাইব্রেরিয়ান যিনি ছিলেন সেই যুধিষ্ঠির গোমস একদিন জিজ্ঞেস করলেন, -কী এত পড়িস এই সব আউট বইয়ে?
আমার কাছে শুনে বললেন,-শোন, সেই রকম বই আমাদের লাইব্রেরিতে তেমন নেই। তুই বড় ফাদারকে বলে, এখন তো বড় হয়েছিস, লাইব্রেরির কমপিউটারটায় হাত দেবার পারমিশন নে। ইন্টারনেটে অনেককিছু জানতে পারবি। নেটের সব কথাই হয় তো ঠিক না। আমাকে দেখিয়ে নিবি।
সেই আমার কমপিউটার ঘাঁটা শুরু হল। আর এই করতে গিয়েই বিপদে পড়লাম।
আমার ছোটোবেলার অর্জন সেই ডিপ্রেশন। তারই এক এপিসোডে হেড স্যার ডেকে পাঠালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কথা বললেন। ফাদার টের পেয়েছিলেন, কমপিউটারের হিস্ট্রি থেকে।
আমি আত্মহত্যা কী ভাবে করতে হয় খুঁজে দেখেছি।
সেই অনেক দিন আগে বলা কথাই আবারও বললেন,-ভয় কী? আমরা সবাই আছি তো!
এখন তো বড় হয়েছি। তাই আরও কিছু কথা বললেন।-আত্মহত্যার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বেঁচে থাকা। আমরা সবাইই একদিন না একদিন মরব। বেঁচে থাকলেই তুই আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবি মৃত্যুর দিকে। সেটা করাই সোজা না? জানবি ধর্ম একটাই। তা হচ্ছে বেঁচে থাকা।
আরও বড় হয়েছি। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে গেছি। আমার জীবনের সেই আলো-মানুষের বলা কথা ভুলিনি।
তবু আমার মুখ ভুলে যাওয়া মায়ের ছবি আমাকে ডাকত। মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হত। এই যে ইউনিসেফ বাংলাদেশের ডাকে এখানের চা বাগানের প্রোগ্রামে এসেছি, তার পেছনেও সেই ইচ্ছে। ইচ্ছেটাকে উসকে দিয়েছে জুলি।
জুলি কে?
ওঃ, বলিনি বুঝি? আসলে জীবনটা অগোছালো বলে আমার বলাটাও অগোছালো।
লোকে ভুল করে ভাবে উঁচু মাপের চাকরি করে মানেই,অমিত লারমা ওয়েল অর্গানাইজড… ওয়েল এস্টাব্লিশড।
*
পরিমলদা’র সঙ্গে প্রথম আলাপের মাস দুয়েক বাদে পরিমলদা এক শনিবার বললেন, -কাল তো রবিবার। কী করবে কাল সারাটা দিন?
-কী আর করব? সারা সপ্তাহের জমা জামা কাপড় কাচব। তত গুছোনো নই। তবু এলোমেলো হয়ে থাকা ঘর গুছোব। আর বকেয়া লেখাপড়ার কাজ সারব।
-ব্যাস, এই সবই? কাল তবে তোমার নেমন্তন্ন আমার বাসায়। রীনা, তোমার বউদি এত গল্প শুনেছে তোমার। কাল তোমাকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে! তা ছাড়াও অন্য কারণ আছে একটা।
পরিমলদা মানুষটা বেশ। মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান এই জাতীয় মানুষেরা যেমন হয়ে থাকেন। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই। আসলে অশান্তি না। রীনাবৌদি এক ধরণের প্রশ্রয়ই হয় তো বা দেন। বাবা নেই। বৃদ্ধা মা আর এক বোন। সন্তানটি বছর দশেক বয়স। নিটোল লোভহীন এক মধ্যবিত্ত পরিবার। যার কর্তাটির ধ্যানজ্ঞান আদিবাসী উন্নয়ন।
আসলেই ঘটনা যত সরল ভাবে এগোবে ভেবেছিলাম, তা এগোল না।
পরিমলদা’র আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগে এক বিরাট তছরুপ ধরা পড়ল। এই পোড়া দেশে কে না জানে, যেখানেই গুড়ের হাঁড়ি সেখানেই পিঁপড়ে। আদিবাসী উন্নয়নের বিরাট এক অঙ্কের টাকা গোলমালের ব্যাপার। সরকারি আধিকারিক পরিমলদা’কে তদন্তের ব্যাপারে ব্যস্ত হতে হল।
গোলমালটা হয়েছে একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে। কাজেই পরিমলদা’ আমাকে আর সেই রকম সময় দিয়ে উঠতে পারছিলেন না। ওঁর অফিসে যাতায়াত করেও সুবিধে হচ্ছিল না তেমন। একদিন ওঁর ব্যস্ততার মধ্যেই দেখা হল।
-ও পরিমল দা, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো! স্যারকে বললেই বলছেন, পরিমল সব জানে।
-অমিত, তোমাকে বড্ড দেরি করিয়ে দিচ্ছি। আসলে ডিপার্টমেন্টে অ্যাত্তো ঝামেলা শুরু হয়েছে। শোনো, কাল তো রবিবার। তুমি আমার বাড়িতে চলে এসো।
বাসা মানে কোয়ার্টারের ঠিকানা লিখে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।
সরকারি অফিসারদের ফ্ল্যাট। আবাসনের দুতলায় কোয়ার্টারের বেল বাজাতে, বৌদি দরজা খুললেন। মধ্যবিত্ত সরকারি চাকুরের ফ্ল্যাট যে রকম হয়। আড়ম্বর নেই কিন্তু গুছোনো। পরিচয় দিলাম। বৌদি ড্রয়িং রুমে বসিয়ে জানালেন দাদা বাজারে গেছেন। ফিরবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।
পরিমলদা’ ফিরে আমাকে দেখেই ভেতর দিকে ফিরে উঁচু গলায় বৌদিকে বললেন, -অমিত কিন্তু আজকে দুপুরে খাবে এখানে।
ড্রয়িং রুমে বসে আছি। গান শুনতে পেয়ে উৎকর্ণ হলাম। মেয়েলি গলায় আশেপাশে কোথাও কেউ গাইছে।
— সহসা ডালপালা তোর উতলা যে… ও চাঁপা ও করবী।
কে গাইছে? দাদার দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতে দাদার কাছে জানা গেল, তাঁর বোন এসেছে।
– তোমাকে তো বলেছিলাম বোন শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনো করে। কলাভবনে। ইন্সটিটিউট অফ ফাইন আর্টসে। তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব। সেই জন্যেই ডেকেছি আজ তোমাকে। ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স আছে ওর এই ডিসপ্লেসড ট্রাইবালদের ব্যাপারে।
একটু ঘাবড়ে গেলাম। তখনও তো সে ভাবে আলাপ হয়নি। ভাবলাম, কাটিয়ে দেবার মতলব নাকি রে বাবা।
গান গাইছিল ওই মেয়েই। রবীন্দ্রনাথের গান তার খুব প্রিয়।
এর পরের এক বছর আক্ষরিক অর্থেই কাটল এই স্থানচ্যূত আদিবাসীদের পুরো ব্যাপারটা জানতে।
পরিমলদার আসলে ছোটোবেলা কেটেছে ডুয়ার্সের এক চা বাগানে। খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন আর পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় যা জেনেছেন, আমাকে তন্ন তন্ন করে জানিয়েছেন সেই ইতিহাস। কিন্তু আসল সাহায্যটা করল জুলি, ওর ওই ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারটা দিয়ে। সেই ব্যাপারটা জেনেছিলাম পরে।
জুলি কলাভবনে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টসে পড়ে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে হিস্ট্রি অফ আর্ট এ অনার্স। নাম শুনে বিষয় বুঝলাম না। নিশ্চয়ই খুব কঠিন কিছু হবে। এক সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে।
পরিমল দা জুলির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। -অমিত, আমি তো ব্যস্ত থাকব কিছুদিন। তোমাকে আমার বোন জুলিই সাহায্য করুক আপাতত। তোমার সেক্রেটারিও বলতে পারো। হেমব্রম স্যারকে বোলো, কনটিনজেন্সির ওপরে চাপ না দিয়ে কেমন ফ্রিতে সেক্রেটারিও পেয়ে গেছো।
একসপ্তাহের মধ্যে চলে যাবে যে মেয়ে, সে কীভাবে সাহায্য করবে কে জানে।
বলতেই পরিমল দা বললেন, -করবে করবে, আমার চাইতেও বেশি নলেজ ওর।
*
এক সপ্তাহে আরও কয়েকবার দেখা হল জুলির সঙ্গে। কথা হল। কাজের কথাই।
চমৎকার ঝকঝকে স্মার্ট মেয়ে। গান সেই প্রথমদিন শুনেছিলাম। পরে জেনেছি ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতও ভারি যত্ন নিয়ে শিখেছে সে। রবীন্দ্রনাথই নাকি তার ঈশ্বর। কিন্তু এই ব্যাপারেই কথা বলতে গিয়ে একদিন ঝাঁঝিয়ে উঠল জুলি। -দেখবেন, আপনিও যেন অন্যদের মত আমাকে দেখেই আবার কাঁপা গলায় গেয়ে উঠবেন না, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি। দু চোখে পছন্দ করি না আমার ঈশ্বরের এই একটা মাত্র গান।
জুলির গায়ের রঙ বেশ চাপা, ওই যাকে বলে কৃষ্ণবর্ণই। সেই জন্যেই কি?
আরও একবার খুব বকল আমাকে চলে যাবার আগের দিন।
একটু তরল ভাবেই বলেছিলাম, -জুলি, আপনি কিন্তু বকলমে আমার থিসিস গাইড। প্রফেসর হেমব্রম আর পরিমল মুখার্জি এই দুজনের হাত ফেরতা উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার হাতে পড়েছি। শুধু ওই রবিঠাকুরের কবিতার দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে ওই সব না বলে আমাকে সলিড কিছু দু তিন মাসের মধ্যে রেডি করে দিন। যা জানেন সব।
জুলি বলেছিল, -সে দেব এখন। বুঝিয়ে দেব পুরোটাই ওই সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে টাইপের ব্যাপার না।
একসপ্তাহ পর থেকে যোগাযোগটা রইল ইমেইলে।
*
সেই চিঠিগুলি…
From amit.larma@hotmail.com
To juli1993@rediffmail.com
জুলি দেবী,
আপনার মেইলের অপেক্ষায় আছি।
অমিত।
From juli1993@rediffmail.com
To amit.larma@hotmail.com
শ্রদ্ধেয় অমিত দা’,
বহু বছর আগে চীন ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও চায়ের বাণিজ্যিক চল ছিল না। ১৬১০ থেকে ওলন্দাজ বণিকরা চীন থেকে চা বাণিজ্য শুরু করে। ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের রূপ পাল্টালে ইউরোপ নিজেই চা চাষের সিদ্ধান্ত নেয়।
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চায়ের বাণিজ্যিক আবাদের প্রস্তুতি নেয়। এভাবেই সুরমা আর বরাক উপত্যকায় ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের বাণিজ্য কারবার শুরু করে।
সেই ঔপনিবেশিক বণিকেরা সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহের জন্য সমতল ভারতের দিকে নজর দেয়।
চা শ্রমিকদের সাদরি ভাষায় গাওয়া গানে সেই ইতিহাস কাঁদে।
রাচিকের বাঙ্গাল কুলি
দে দোলাই টুকরি
ঝুমড়ি ঝুমড়ি পাতা তুলেলা
চারাবাড়ি
হায়রে দেইয়া
কাহা গেলাক হামরিকের
ঘরবাড়ি।
অর্থাৎ,
রাঁচি থেকে এলো কুলি
দেওয়া হল পাতি টুকরি
সারাদিন চা বাগানে ঘুরে ঘুরে পাতি তুলি
হে ভগবান,
কোথায় গেল আমাদের
ঘরবাড়ি
বিস্তারিত পরে জানাচ্ছি।
ইতি,
জুলি
পুনশ্চঃ- আমি কিন্তু দেবী নই নিতান্তই মানবী।
★
From amit.larma@hotmail.com
To juli1993@rediffmail.com
জুলি,
আপনার কাছে পাওয়া তথ্য কিছু বইপত্রে যাচাই করার সুযোগ হল। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে চুয়াড়, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওরাওঁ বিদ্রোহ সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরাই যখন চা বাগানে শ্রমিক তখন কিন্তু সেই বিদ্রোহের আঁচ এঁদের মধ্যে পড়েনি।
এই ব্যাপারে কোনও তথ্য পেলে জানাবেন।
অমিত।
…………
শ্রদ্ধেয় অমিত দা,
কথাটা আপনি ঠিকই লিখেছেন। তাদের নিজস্ব জাতির যে আন্দোলন আর বিদ্রোহ তাতে চা শ্রমিকেরা সামিল হননি। কিন্তু অন্য ধরণের বিদ্রোহ তাঁরা করেছিলেন বই কী।
মাঝে কলকাতা গিয়েছিলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আদিবাসী বিদ্রোহের ওপর লেখা বই পত্র থেকে কিছু নোট এনেছি। সেগুলি অ্যাটাচমেন্টে পাঠাচ্ছি। ……।
চারগোলা কুলি এক্সোডাস বলে সেই অধ্যায় এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীতেও আছে। ১৯২১ সালের ২০ মে চা শ্রমিকদের ওপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদে ‘মুল্লুকে চল’ (দেশে চল) আন্দোলনের শুরু হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সিলেট থেকে পায়ে হেঁটে চাঁদপুরের মেঘনা স্টিমার ঘাটে পৌঁছান এ অঞ্চলের ৩০ হাজারের বেশি চা শ্রমিক। কিন্তু, ব্রিটিশ সেনাদের গুলিতে শ্রমিকদের জাহাজে চড়ে দেশে ফেরার স্বপ্ন শেষ যায়। মেঘনার জলে ভাসতে থাকে শত শত চা-শ্রমিকের মরদেহ। আর যারা গুলির মুখ থেকে স্টিমার ঘাট থেকে পালালেন, আন্দোলনে শামিল হওয়ার অপরাধে তাদের ওপরেও নেমে আসে নির্মম নির্যাতন।
চা বাগানের শ্রমিকদের জোগাড় করা হত আড়কাঠি লাগিয়ে। আড়কাঠিরা এদের আনত বাংলা, ইউনাইটেড প্রভিন্স, সেন্ট্রাল প্রভিন্স মাদ্রাজের নানান কষ্টসহিষ্ণু উপজাতিদের মধ্যে মিথ্যে আর লোভ ছড়িয়ে। নানান উপজাতির সেই মানুষেরা এমনিতেই খুব আর্থিক দুর্দশায় থাকত। সেই সুযোগটাই নিত এই দালালেরা।
নিজেদের পায়ের তলায় মাটি হারানো মানুষেরা চা বাগানে পৌঁছে আবিষ্কার করত স্বর্গের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে আসলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নরকে। খাবার নেই, স্বাস্থ্য নেই।
সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধইরে আন
সাহেব বলে লিবো পিঠের চাম রে নিঠুর শ্যাম
ফাঁকি দিয়া আনালি আসাম
আমরা বই পত্রে আমেরিকার দাসপ্রথা পড়েছি। আঙ্কেল টমস কেবিন আমাদের অবাক করে। বর্বরতার সেই উচ্চতা প্রায় স্পর্শ করা এই ইতিহাসকে অনায়াসেই আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস সরবরাহের দেশীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে।
ইতি
জুলি
*
অমিত দা’,
আপনি ভারতে চা চাষের ইতিহাসের মধ্যেই পেয়ে যাবেন এই বাস্তুচ্যুত উপজাতিদের কথা।
চা উৎপাদনে ভারতের জায়গা চিনের পরেই। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় চিনে। তারপরেই ভারতে। বলা ভালো ভারতীয় উপমহাদেশে। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ১.২ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ সালে ৪০০০ কোটি টাকারও বেশি চা রফতানি করে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে ছিল।
ভারতে চা উৎপাদনে অসম সবচেয়ে এগিয়ে (৩ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর চা বাগান), তার পরেই পশ্চিমবঙ্গ (১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর), তামিলনাড়ু (৭০ হাজার হেক্টর) এবং কেরল (৩৫ হাজার হেক্টর)। এই পরিসংখ্যানটা এই আখ্যানে জরুরি,চা শ্রমিকের বিশাল সংখ্যাটা আন্দাজ করার জন্য।
বিশ্বের মোট চায়ের বাজারের ৮৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটা মাত্র বহুজাতিক।
তাদের মার্কেটিং দক্ষতা এবং প্রভাব সহজেই অনুমেয়। এই হচ্ছে চায়ের বাজার — যেখানে ভিড় করে রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা এবং তাদের মাথায় বসে রয়েছে কর্পোরেটরা। এই পিরামিডের সবচেয়ে দুর্বল এবং ভঙ্গুর বিন্দুতে যে চা-শ্রমিকরাই থাকবেন, তা বোঝা ভারি সহজ। এখানে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা থাকলে কোম্পানিদের চলবে না।
সেই জন্যেই এই শ্রমিকদের স্থানীয় ভিত্তি অর্থাৎ পায়ের তলায় মাটি থাকলে চলবে না। বিশ্ববাজারে চায়ের দাম শিখর স্পর্শ করছে, কিন্তু চা-শ্রমিকরা আজ থেকে ৩০ বছর আগে যা মজুরি পেতেন, এখনও প্রায় তা-ই পাচ্ছেন, এবং অনেকক্ষেত্রে তা কমেও গিয়েছে।
পরিসংখ্যান বলছে, চা-শিল্প শ্রমিক সংখ্যার দিক থেকে ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। সারা দেশের ১৬৮৬টি টি-এস্টেট এবং ১৫৭৫০৪টি ছোট বাগিচার মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩৫ লক্ষেরও বেশি, যার বেশিরভাগই মহিলা।
এই খানেই লুকিয়ে রয়েছে সেই স্ট্যটিস্টিক্যাল বিস্ময় যা সাধারণভাবে আদিবাসীদের নিয়ে কথা বলার সময় ভাবাই হয় না।
ভারতের দুই প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকরা মূলত আদিবাসী। আদিবাসী… কিন্তু স্থানীয় আদিবাসী না। ঔপনিবেশিক বাগান মালিকেরা আজ থেকে ১৫০ বছরেরও আগে এদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে জোর করে তুলে এনে এই বাগানগুলিতে কাজে লাগিয়েছিল। তখন অবশ্য নাম আলাদা ছিল জায়গাগুলির। সেন্ট্রাল প্রভিন্স, ইউনাইটেড প্রভিন্স, মাদ্রাজ।
চা বাগানের কুলি লাইনের আদিবাসীদের কথা বলার আগে বলতে হবে আসাম বরাক বা ডুয়ার্সে যেখানেই চা বাগান সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কথা। তারাও কিন্তু প্রকৃত অর্থে আদিবাসীই ছিল। কিন্তু স্থানীয় সেই উপজাতির মানুষেরা এই কাজে সে ভাবে উৎসাহী হয়নি।
চা বাগানে কাজের শর্ত আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু তার চাইতেও বড় কারণ ছিল, ডুয়ার্সেই যেমন, টি প্ল্যান্টারেরাও কৌশলগত কারণেই স্থানীয় রাভা, মেচ রাজবংশীদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে চায়নি, কেন না স্থানীয় জনজীবন থেকে চা বাগানের এই বিপুল পরিমান শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখা বাস্তবিকই ঔপনিবেশিকদের কাছে দরকারি ছিল।
বিপুল পরিমানে অরণ্য উচ্ছেদ করে যখন চা বাগানগুলি আসামে আর ডুয়ার্সে বানানো হচ্ছিল সেই সময়ে সমস্যা ছিল অনেকই। এক তো সেই নিবিড় অরণ্য কেটে সাফ করা। তার ওপরে পরবর্তী কাজের জন্য শ্রমিক জোগাড় করা। সেই সময়ে আবার ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের কারণে প্রায় এক বধ্যভূমি। আর সেই সঙ্গে ছিল হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বিপদ।
এখন এমনকি বাংলাদেশেরও চা বাগানে আমরা যাদের চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে দেখছি এখন, তাদের প্রায় পুরো অংশই এসেছে ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে।
ব্রিটিশরা মিথ্যা মজুরি আর সুবিধার গল্প বানিয়ে পাহাড়-অরণ্য থেকে নানা আদিবাসী জাতির নারী-পুরুষদের গ্রামসুদ্ধ ধরে এনে চা বাগানের দাস-মজুর বানিয়েছে। এখনও কান পাতলে শোনা যায় সেই সব প্রচার।
‘গাছ ছিলালে রুপিয়া মিলে’, ‘গাছ নাড়ালে পয়সা পড়ে’, ‘চা গাছ ঝাঁকালে সোনা পাওয়া যায়’, এ রকমভাবেই ব্রিটিশ বণিকরা আর তাদের দালালেরা গরিব আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে বুঝিয়েছিল। ।
সেই ভুল বোঝানো, আর আড়কাঠি লাগিয়ে লোভ দেখিয়ে শেকড় ওপড়ানো মানুষেরা নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে লোকগান বেঁধেছে।
চল মিনি আসাম যাবো
দেশে বড় দুখ রে
আসাম দেশে রে মিনি চা বাগান ভরিয়া
চল মিনি আসাম যাব
কুড়ল মারা যেমন তেমন,
পাতা তুলা কাম গো
-কুড়ল মারা যেমন তেমন
পাতা তুলা কাম গো
হায় যদুরাম
ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম।
ছোঁয়ার কান্দে ডিহির ডিহি
কাকরিমে পানি নাই
বাপ দাদা রে ফাঁকা
মুরলী বাজাইছি
চল মিনি আসাম যাবো
সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বইলে ধইরে আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম
হে যদুরাম
ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম
চল মিনি
আসাম যাবো
দেশে বড় দুঃখ রে…
এই যদুরামরাই ছিল স্বজাতির মধ্যে থেকে গজিয়ে ওঠা সেই আড়কাঠি, যাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ বণিকরা চা বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে এক নির্মম ‘দাস-বাণিজ্যকে’ বৈধ করে।
তরাইয়ের ম্যালেরিয়াপ্রবণ জলবায়ুতে কঠিন শ্রমের কাজ করার পক্ষে এই আদিবাসীরা যথেষ্ট শক্ত-পোক্ত ছিলেন৷ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ধরে এই আদিবাসীরাই চা-বাগানে প্রধান শ্রমশক্তি হয়ে ওঠেন৷
ছোটোনাগপুরের মত জায়গা থেকে অর্থাৎ মধ্যদেশ থেকে এসেছিলেন বলে, এঁদের ‘মদেশিয়া’ বলা হয়৷ এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এলেন, ফলে জেলার জনসংখ্যায় একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটল৷ ১৮৭২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ২৪৪.২ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে৷ ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, গোন্দ- এঁরাই প্রথমে ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে ডুয়ার্স এসেছিলেন কিন্ত ক্রমশ শ্রমিকের চাহিদা যে ভাবে বাড়ছিল, তাতে অন্যান্য জনজাতির মানুষও কাজে এসে যোগ দিচ্ছিলেন৷ ১৮৯১ সালের জনগণনার রিপোর্টে ওঁরাও, মেচ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, গারো- কেবল এই পাঁচটি জনজাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে৷ অথচ ১৯৬১ সালের জনগণনা রিপোর্টে কুড়িটিরও বেশি জনজাতির নাম নথিভুক্ত হয়েছে৷ ক্রমে দার্জিলিং থেকেও ডুয়ার্সে কিছু নেপালি শ্রমিকরা এসে যোগ দেন৷
এই সব তথ্য থেকে যে কথাটা বেরিয়ে আসে, সেটি হল, বাকি দেশের থেকে ঐতিহাসিক ভাবেই চা-বাগানের সাংস্কতিক পরিমণ্ডল, জীবনযাপনের ধরন, অর্থনৈতিক বিন্যাস সবই আলাদা হয়ে যায়৷ ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা এই সব শ্রমিকদের কোনও বাসস্থান ছিল না৷ ফলে, চা-বাগানগুলি ঘিরে শ্রমিক বসতি তৈরি হয়ে ওঠে৷
সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল, মাহালি, ওঁরাও, খাড়িয়া, কন্দ, মুসহর, রবিদাস, ভূমিজ, উড়িয়া, শীল, নায়েক, রাজপুত, অসমিয়া, ভর, লোহার, ডুকলা, পাইনকা, গঞ্জু, পাল, তাঁতি, বড়াইক, সিং, বাগদী, মাহাতো, তুরী, নিষাদ, দোসাদ, রাজোয়াড়, পাহাড়িয়া, মালো, মালী এ রকম নানা ঐতিহাসিক জাতিগুলোর অনেকেই নিজ জন্মমাটি ও আত্মপরিচয় থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে একটা সময় অনিবার্যভাবে বহুজাতিক কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত বাগানের চা শ্রমিক হয়ে যায়। জাতি, গোত্র, বংশ, নাম, পরিচয় সব মুছে চা বাগানে এদের এক নতুন নাম হয় ‘কুলি’। এদের কৌম পরিচয়, জাতি পরিচয়, সংস্কৃতি পরিচয় মুছে যায়।
প্রায় আমেরিকার দাসেদের মতনই জীবন ছিল তাদের সেই শুরুর দিনগুলোতে। দিন গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই হত দরিদ্র মানুষদের অবস্থা পাল্টায়নি। বরং আজ ভেবে দেখলে খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে তাদের হাল। যখন চা বাগানের অবস্থা ভালো ছিল, তখনও ওই মানুষেরা খারাপ অবস্থায়ই ছিল। এখন তো চা বাগানগুলো নিজেরাই ধুঁকছে।
ইতি
জুলি
★
অমিত দা’,
হয় তো জানো। কিম্বা জানো না। চা চাষের কিছু কথা তোমাকে শোনাই।
মূলত তিনটি বিষয়ের উপর চা-চাষের পরিমাণ ও উত্কর্ষ নির্ভর করে৷ সেচ, পাতা তোলা এবং আবার নতুন চারা লাগানো৷ এই কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না করলে, চা উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই শুধু না, চায়ের গুণগত মানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ বাগান রাখার জন্য যে ভাবে এটা করতে হয়, প্রায় প্রত্যেকটি বন্ধ হওয়া চা-বাগানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেটা সে ভাবে হয়নি৷ না হওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে৷ যেমন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রুনিং-এর কাজটা করে ফেলতে হয়৷ অর্থাৎ পুরনো পাতা ফেলে, ডাল ছেঁটে গাছকে নতুন রূপ দিতে হয়। কিন্ত্ত বাগান বন্ধ থাকার কারণে কাজটা যদি ফেব্রুয়ারির মধ্যে না হয়, তা হলে পরের বছর যথেষ্ট পরিমাণ চা পাওয়া অসম্ভব৷ বাগানে নতুন গাছ লাগানোর কাজেও সমান গাফিলতি। তাই এত চা বাগান রুগ্ন।
ইতি
জুলি
*
অমিতদা’,
মাঝে অনেকদিন মেইল করিনি। এবারে পর পর দুটো মেইল করলাম।
কেন?
দাদারা জানে না। আমি এখনকার কী অবস্থা সরেজমিন দেখে আসব বলে শান্তিনিকেতন থেকেই জলপাইগুড়ি গেছিলাম। আমার ছোটোবেলার জায়গা। ওখানকার টিবি হাসপাতালের ডাঃ সব্যসাচী সেনগুপ্তর মিসেস আমার ছোটোবেলার চেনা। ওঁদের কাছেই উঠেছিলাম।
তোমাকে চা বাগানের এই উপজাতি শ্রমিক যাদের এককথায় কুলি বলা হত, তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছু বলি?
যে দেশে চা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়, সেখানে খুব অল্প মানুষই এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে, সেই চা যেখানে চাষ হয়, সেই বাগানের ভেতর একটা নীরব মহামারী শ’য়ে শ’য়ে চা শ্রমিকের জীবন নিয়ে নিচ্ছে। আজ থেকে না। সেই শুরু থেকেই।
২০০০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে উত্তরবঙ্গের ১৭টা বন্ধ চা-বাগানে ১৪০০ জন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। এই বাগানগুলিতে দেখা গিয়েছে মৃত্যুর মূল কারণ ভয়াবহ অপুষ্টি। অন্য বাগানগুলিতেও এ ধরনের মৃত্যু কম নয়, কিন্তু সেগুলো প্রায়ই খবরে আসেনি।
এই অনাহারে মৃত্যুগুলির একটা বড় অংশই ঘটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। এই অনাহারের থাবা বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানগুলির শ্রমিক পরিবারগুলির ওপর সবচেয়ে বেশি। তাঁদের উপার্জনের একমাত্র পথ বন্ধ, ফলত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি, এবং ভয়াবহ মৃত্যুহার।
গত দশকে চা-বাগানে মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-তে এটা কার্যত মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সে বছর রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে ৫০ জন, বান্ধাপানিতে ২২ জন এবং রায়পুরে ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। সেই সময়েই ১৪ বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা ঢেকলাপাড়া চা-বাগানে ৩৯ জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসে। বন্ধ হয়ে থাকা ডানকান চা-বাগানেও মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১০০। এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি সবই বন্ধ চা-বাগানের। কোনও কাজ নেই, ফলে উপার্জনও নেই। বেঁচে থাকাটাই সেখানে এক নিত্যদিনের সংগ্রাম।
২০১৪ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি শ্রমিকদের বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) দেখা গিয়েছিল ১৮.৫-এর নিচে। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আদর্শ বিএমআই হওয়ার কথা ২৩ থেকে ২৪-এর মধ্যে। বিএমআই কম থাকার অর্থ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির আশঙ্কা অনেক বেড়ে যাওয়া। অথচ বিপুলসংখ্যক চা-শ্রমিকদের বিএমআই দেখা গিয়েছিল ১৪-র আশেপাশে। যেসব পরিবারে সদস্যদের বিএমআই ১৭ থেকে ১৪-র নীচে ঘোরাফেরা করছে, দেখা গিয়েছে তাঁদের মৃত্যুহার অন্যদের দ্বিগুণ। পুষ্টির সামগ্রিক ঘাটতির এই ছবিটাই প্রমাণ করে গোটা চা-শ্রমিক সম্প্রদায় কী মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সর্বোচ্চ আয়ুষ্কাল অনেকদিন ধরেই কমছে। ১০৭টি বাগানের মধ্যে কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই!
শিশুদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৪২টি বাগানে কোনও স্কুল নেই, ফলে বাচ্চাদের মিড-ডে মিল পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বর্তমানে বন্ধ বাগানগুলির শ্রমিকদের উপার্জনের একমাত্র বিকল্প পথ নদীতে পাথর ভাঙা। যে সামান্য টাকা এর থেকে পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের প্রয়োজন তো মেটেই না, দুর্দশা আরও বাড়তে থাকে।
তুমি তো ডাক্তার বিনায়ক সেনের নাম শুনেছ।
তাঁর মতে, এই অঞ্চলে ক্রমাগত অনাহারে মৃত্যুর কারণের সঙ্গে খাদ্য এবং পুষ্টির উৎসের অভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । এই দিকটিতে গুরুতর আপোষ করা হয়। এখানে পুষ্টিকর এবং বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য পাওয়া যায় না। শৌচব্যবস্থাও খুবই অস্বাস্থ্যকর। এঁদের অনেকেই ভর্তুকিযুক্ত রেশন পায় না। পানীয় জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নেই। এই সীমিত খাদ্য এবং নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিধির পরিণতি যা হওয়ার তাই হচ্ছে – ভয়াবহ স্বাস্থ্যহানি।
শিশুদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৪২টি বাগানে কোনও স্কুল নেই, ফলে বাচ্চাদের মিড-ডে মিল পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।
চা বাগানের শ্রমশক্তির একটা বড়ো অংশ মেয়েরা৷ এত বেশি মেয়ে আর কোনও শিল্পের সঙ্গে জড়িত নয়৷ সাধারণ ভাবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কাজ করেন৷ এবং সমান মজুরি পান৷ মেয়েদের অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব দিয়ে প্রথম থেকেই চা বাগানে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ‘ক্রেশ’ চালু করা হয়েছিল৷ সেই ব্যবস্থা আজও খাতায় কলমে আছে৷ কিন্ত যখনই বাগানে কোনও সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রথমেই ক্রেশ বন্ধ হয়ে যায়৷ শিশুর স্বাস্থ্য, লেখাপড়া কোনওটাই ঠিক নেই৷ প্রসূতির প্রয়োজন তো দূর অস্ত৷
তবে কথা বলে মনে হয়, সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বাসস্থানের৷ আগেই উল্লেখ করেছি যে চা বাগানের শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষ৷ তাদের বাধ্য হয়ে চা বাগানে কাজ করতে হয়, কেন না তাদের পায়ের নিচে নিজস্ব মাটি নেই। ওই কুলি লাইনের খুপরিই ভরসা।
এক ডুয়ার্সেই গত দশ বছরে প্রায় ৬০টি বাগান বন্ধ হয়ে গেছে৷ অনাহারে মারা গেছেন প্রায় ১৬০০ শ্রমিক৷ এটা নথিভুক্ত হিসেব৷ এর বাইরেও বহু মৃত্যু আছে, যার খবর পাওয়া যায় না ৷ ২০০৫ সালে উৎপাদন ভিত্তিক বেতন চালু হয়৷ এর ফলে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতা তোলা বাধ্যতামূলক৷ নিজেরা কাজ শেষ করতে না পেরে, অনেক শ্রমিকই তাঁদের শিশুসন্তানদেরও কাজে লাগাচ্ছেন কোটা পূরণ করতে৷ কাজেই তাদের পড়াশুনো শিকেয় উঠছে। স্কুলে না যাওয়ার জন্য মিড ডে মিলও পাচ্ছে না শিশুরা।
ডাঃ সব্যসাচী বললেন, আগের তুলনায় মশারি ব্যবহার বেড়েছে বলে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর এখন কম। কিন্তু অন্যান্য অসুখ আর অস্বাস্থ্য চলছেই। ঘরে ঘরে টিবি রোগী। একই ঘরে অনেকে থাকে বলে সমস্যা। আর সেই জন্যেই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস খুব বেশি।
পরের মেইলে খুব দরকারি কিছু কথা বলব নিজেকে নিয়ে।
ইতি,
তোমার জুলি
পুনশ্চঃ- লক্ষ করেছ কি, এই এতদিনে তোমাকে তুমি বললাম। শেষে লিখলাম “তোমার জুলি”।
আসলে যার জন্য নিজের পড়ার ক্ষতি করে হাল হকিকত জানতে নর্থ বেঙ্গলে নিজের খরচায় গেলাম, আমার সেই অমিতকে এখন থেকে তুমি করেই বলব… বেশ করব!
*
জুলি,
এই যে আমাকে তুমি করে বললে, বেশ লাগল। অবাক হয়েছি ভেবে, যে এতদিন বলনি কেন?
তোমার শরীর আর মন ভালো আছে তো? কী সব নিজের কথা লিখবে বলেছ। একলা মানুষ আমি। এই সব শুনলে ভয় পেয়ে যাই। তাড়াতাড়ি মেইল কোরো। উদ্বেগে থাকলাম।
ইতি,
তোমার
অমিত দা’
*
অমিত দা’,
তোমার মনে আছে কি, রবিঠাকুরের গান এত ভালোবাসি কিন্তু কৃষ্ণকলি গানটা কেমন যেন সহ্যই করতে পারি না?
আচ্ছা, তোমার কোনওদিন সন্দেহ হয়নি, আমাকে দেখে… আমার গায়ের রঙ দেখে? দাদা বৌদি আর মা সেই কথা কাউকে বলবে না আমি জানি। কিন্তু আমি যে ওঁদের রক্তের কেউ নই, আমাকে দেখে বোঝোনি?
শোনো তবে তোমাকে বলি। আমার নাম জুলি। কিন্তু পদবী মুখার্জি না। ওঁদের কাছে আমি বড় হয়েছি। মানুষ হয়েছি। পদবীটা ওঁরা আমাকে স্কুলে ভর্তি করানোর সময় দিয়েছেন। নইলে অসুবিধে হত বোধহয়।
আমার জন্মদাত্রী মা ছিল কাদু সোরেন আর বাবা রামলাল সোরেন। দুজনেই চা বাগানে কাজ করত। মা বাগানের কাজ সেরে দাদাদের বাড়িতে কাজ করতে আসত। ওই যাকে তোমরা বলো ঘরের কামকাজ।
আমার তখন বয়স মোটে চার। আমি মায়ের সঙ্গে ওই বাড়িতে আসতাম।
এক রাত্তিরে মা বাবা, দুজনে একসঙ্গে মারা গেল পেটের অসুখে। ডাক্তার ছিল না। পরে শুনে বলেছিল আন্ত্রিক।
আমাদের কুলি লাইনে এই রকম হরবখত মরত। অনাথ বাচ্চারা, নিজের লোক কেউ না থাকলে, চেয়েচিন্তে ভিখ মেঙে একরকমের বড় হত। চা বাগানের কুলিকামিন হত। নইলে একটু বড় হলেই বাইরে পাচার হয়ে যেত। মেয়েদের দাম ছিল বেশি। কেন, বুঝতেই পারছ।
আমার কিন্তু ভাগ্যে লেখা ছিল অন্যরকম। দাদা তখন উঁচু ক্লাসে পড়ে।
একদিন মা বাবা আর ছেলের মিটিং বসল, আমাকে নিয়ে। বাবার খুব মেয়ের সখ। মায়েরও।
দাদাকে শুধোলো ওরা, -এই মেয়েটাকে পালব আমরা। তোর কোনও আপত্তি নেই তো বাবু?
দাদা এ সবের বোঝেই বা কী। একপায়ে খাড়া।
ওই সব দিকে সরকারি নিয়ম কানুন বেশ আলগা।বাবা কুলি বস্তির মাতব্বরদের সঙ্গে কথা বলে আমাকে দত্তক নিল।
সেই থেকে আমি এই ফ্যামিলির মেয়ে। আমি জুলি মুখার্জি। পরিমলদার মা বাবাই আমার নতুন মা আর বাবা।
জানো, মা বাবা আর দাদার সঙ্গে প্রথম যেবার কলকাতায় এলাম তখন আমি দশ বছরের। ক্লাস ফোরে পড়ি। কলকাতার ওদের আত্মীয়রা থাকে। তারা তো জানে আমি কে কী কোত্থেকে এসেছি।
রমলাপিসি আর বড়জেঠি নিজেদের গা টেপাটেপি করল। বড়জেঠি পিসিকে বলল, ফিসফিসিয়ে না, বেশ জোরেই,
-দেখলি রমলা, চা বাগানে কাজ করার সুবিধে? কী রকম দিব্যি একটা কাজের লোক জোগাড় করে ফেলেছে। আর আমার বাড়ির মানুষটা। অত বছর সুন্দরবনের বিডিও থাকল। একটা এই রকমের ডাঁটো কাজের মেয়ে আনতে পারল না!
বাবা, মানে পরিমলদা’র বাবা একটু ফ্যাকাসে হেসে বললেন,
-কাজের মেয়ে কাকে বলছ বড় বৌদি? ও তো আমার আর মিলির মেয়ে। এই পরিমল যেমন ছেলে তেমনি। এক ছেলে এক মেয়ে আমাদের।
ওঁরা এই রকম ভাবলেও অন্যরা ভাবত না। তাই তো দাদা বাংলায় না থেকে ঝাড়খণ্ডে চলে এল।
আমার আসল মা বাবার কথা জেনে একটু ঘেন্না করছে কি তোমার? সেই কোনকালে মিথ্যে লোভে পড়ে আমার মদেশিয়া পূর্বপুরুষেরা একটু বাঁচার আশায় পৌঁছেছিল ডুয়ার্সের চা বাগানে।
একবার ভাবো অমিতদা’, নিজেদের যেটুকু ছিল, তা হারিয়ে গেছে অতীতের গর্ভে৷
সে সব কথা মনেও পড়ে না৷ খানিকটা মুখে মুখে ফেরা গল্পের মধ্যে আছে, খানিকটা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে আর বাকিটা চা বাগানের মাটিতে মিশে গেছে৷
‘এটাই ঘর বল, দেশ বল, জন্মভূমি বল- সবই চা বাগান৷’ ঘোলাটে কোটরগত চোখ আর তোবড়ানো শীর্ণ চেহারার মানুষরা জানে এ কথা। অথচ এই জমিতে, এমনকী শ্রমিক বসতির মাটিতে লাগানো সাদা নাম-না-জানা ফুলগাছটির উপরও শীর্ণ মানুষটির কোনও অধিকার নেই৷
‘কুথাক যাব?’ এই প্রশ্নের সামনে কোনও উত্তর নেই৷ আর তাই মাথার ওপর ভাঙাচোরা এই ছাউনিটুকুর জন্য অবসর নিলে বা মৃত্যু হলে, বাড়ির কনিষ্ঠতমটিকেও কাজে ভর্তি করতে হয়৷
না হলে বসতিতে কোনও ঠাঁই নেই৷ এমন হাত-পা বাঁধা শোষণের রূপ ভারতবর্ষের আর কোনও সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্র আছে কি না, জানি না৷
ব্রিটিশ আমলে কালো মেয়েদের যৌন দাসী বানাত ব্রিটিশ প্ল্যান্টারেরা। ঠিক নীচের ধাপের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও ব্যতিক্রম ছিল না। খেলা ফুরোলে দেশে ফেরার আগে ডিসপোজেবল এই মেয়েদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেত সাহেব আর বাবুরা। এখনও খুঁজলে কিছু স্বর্ণকেশ নীলনয়ন হতভাগা জারজ খুঁজে পাবে তরাই, বরাক আর পাহাড়ের খাঁজে। সেই অনাথদের মধ্যে মেয়েগুলো লোকাল ব্রথেলে জায়গা পায়।
আমার কপাল খুব অন্যরকম যে এই ঘুর্ণির ভেতরে পড়তে হয়নি আমাকে।
হ্যাঁ, অমিত দা’, এই আমার নিজের সম্বন্ধে বলার ছিল এই জরুরি কথাগুলি। এর মধ্যেই জীবনে কী ভাবে যেন এসে গেলে তুমি। হয় তো আগেই বলে নেবার কথা ছিল এগুলি। জানি না, এর পরেও তুমি আমাকে…সহ্য করবে কী না!
যদি অসহ্য মনে হয়, পারলে আমাকে মাপ করে দিয়ো।
ইতি
*
জুলি,
তুমি তো সাতখান করে নিজের ঝুলি উপুড় করলে। আমার কী হবে? আমিও তো তোমাকে আমার কথা বলিনি। বলিনি আমিও যে অরফ্যানেজে মানুষ হওয়া এক মানব শিশু। ভেসে যাবার কথা ছিল যারও। আমার পুরো গল্প না মেইলে নয়, তোমাকে মুখোমুখি বসে বলব।
ইতি,
অমিত
*
এই মেইলটা পাঠিয়ে এমনকি পরিমলদা’কেও না জানিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে জুলির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওকে মুখোমুখি বসে বলেছিলাম, আমার ছেলেবেলার সব কথা। মাকে খোঁজার আর মায়ের ওপর অভিমানের সব গল্প।
আমি যে চাকমা বলে এক অবহেলিত জনজাতির মানুষ জুলি জানত। কিন্তু্ সেই জাতির মানুষেরা আজও অধিকার বঞ্চিত সীমান্তের এপারে আর ওপারেও সেই তথ্য জুলি পুরোটা জানত না।
*
সেই শান্তিনিকেতনে সেবারেই জুলি আর আমি, আমরা পরস্পরকে নিজেদের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলাম।
জুলি বলল, -ইস্, পুরোটা কেমন যেন ঘোটুল থেকে সঙ্গী বেছে নেবার মত হল না? সেই যেমন প্রথা ছোটোনাগপুরের আদিম জনজাতিদের মধ্যে চালু ছিল… তাই না অমিত দা’?
আমি পিএইচডি শেষে দুবছরের পোস্টডক প্রোগ্রামে আমেরিকা গেলাম আগেই বলেছি।
সেই তখনই, দেশ ছাড়ার আগেই পরিমলদা’কে আমি আর জুলি দুজনেই জানিয়ে দিয়েছি, আমরা একসঙ্গে জীবন কাটাব ঠিক করেছি।
আমরা জানতে পেরেছি আমাদের দুজনেরই ধর্ম এক। না বৌদ্ধ, হিন্দু,, খ্রীস্টান ধর্ম এই সব না। আমাদের দুজনেরই ধর্ম বেঁচে থাকা।
★
বাংলাদেশে ইউনিসেফের কাজে এসেছি, তার আড়ালেও জুলির সুপ্ত আর একটা বাসনা আছে। বলা যায় তার নির্দেশেই এসেছি এই রুটে।
আমি বিদেশে থাকার সময় আমাকে ঘূণাক্ষরেও জানতে দেয়নি মেয়ে। সে একা একা আগরতলায় আমার ছেলেবেলার সেই হোম ঘুরে এসেছে। সেখানে অফিস থেকে আমার মা বিনতা চাকমার ইতিহাস খুঁড়েছে। পায়নি তেমন কিছু যদিও। থাকলে তো আমিই পেতাম। আমিও তো অনেক খুঁজেছি।
জুলিকে জিজ্ঞেস করলাম, -আমি যে খুঁজেছি মাকে তার নয় কারণ আছে। তুমিও কেন খুঁজেছ? কেন? কেন?
আমার আকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে জুলি যা বলেছে শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। -তোমার মাও তো ছিলেন আমারই মত ডিসপ্লেসড এক উপজাতি কন্যা। আমি তাঁর আশীর্বাদ খুঁজতে গেছিলাম। যদি খুঁজে পেতাম এক টুকরো স্মৃতিকণা!
কিন্তু আমি যেটা করিনি জুলি সেটা করেছে। আসলে তো ছোটোবেলা থেকেই জুলিকে তাড়া করেছে তার পূর্বপুরুষদের স্থানচ্যুতির নির্মম ইতিহাস। আমার মাকে খুঁজতে গিয়ে চাকমাদের মধ্যে সে খোঁজ পেয়েছে এক হারিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির। তার নায়িকা সেই আগ্নেয়গিরির নাম কল্পনা চাকমা।
আমার মা বিনতা লারমা দারিদ্র আর অসুখের কাছে হেরে গেছে।
আর সেই মেয়ে… কল্পনা কে হারিয়ে দিয়েছে বলা ভালো উধাও করে দিয়েছে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা।
১৯৯৬ সালের ১২ই জুন চট্টগ্রামের রাঙামাটির বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়।
তার বিরতিহীন লড়াই ছিল বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে। দারিদ্র চাপিয়ে দিয়ে জনজাতির সংস্কৃতিগত অধিকার মুছে দেওয়ার যে কৌশল নেয় তথাকথিত সভ্য সমাজ তার বিরুদ্ধে। আধিপত্যবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা করার জন্য জন্মেছিল সেই মেয়ে। কল্পনার কথাগুলি যেন উপমহাদেশের আদিবাসী বিশেষ করে নারীদের চলমান লড়াইয়ের ইশতেহারে পরিণত হয়েছে।
কল্পনাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
জুলির নির্দেশ, রাঙ্গামাটি থেকে, কল্পনার বাড়ি থেকে এক টুকরো মাটি নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে গিয়ে দিতে হবে তার হাতে। জুলি নিজেই যে কল্পনার এক উত্তরাধিকারিণী, যে নিজের আত্মপরিচয়ের খোঁজে হেঁটে চলেছে জন্মাবধি।
*
তথ্যসূত্রঃ-
(১) চা জনগোষ্ঠির সংস্কৃতিঃ পরিমল সিংহ বাড়াইক
(২) মাণিক সান্যালঃ চা শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলনঃ পশ্চিমবঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা
(৩) সমীর চক্রবর্তীঃ উত্তরবঙ্গের আদিবাসী শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃত্ মনীষা অক্টোবর ১৯৯২
(৪) অপূর্ব দাশগুপ্তঃ ডুয়ার্সে চা বাগান,ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
(৫) সুধীর কুমার বিষ্ণুঃ আদিবাসী চা শ্রমিকদের ভাষা।
(৬) Coolie Exodus from Assam’s Chargola Valley, 1921: An Analytical Study
:Kalyan K. Sircar: Economic and Political WeeklyVol. 22, No. 5 (Jan. 31, 1987)
, pp. 184-193 (10 pages)
Published By: Economic and Political Weekly
(৭) বিবেকানন্দ মহান্তঃ চাঁদপুর এক্সোডাস(বই এবং টেলিফোনে বাক্যালাপ)
(৮) India’s Northeast in UK Parliament: Colonial account of 1921 uprising of tea garden workers in Chargola and Longai valleys in Assam,HC Deb ( House of Commons Debates) 27 June 1921 vol 143
(৯) Coolies of Capitalism: Assam Tea and the Making of Coolie Labour Nitin Varma · 2018
(১০) ভারতের আদিবাসী, সমাজ পরিবেশ ও সংগ্রামঃ শুচিব্রত সেনঃ বুকপোস্ট পাবলিকেশন
(১১) জীবন উজ্জীবনঃ সলিল চৌধুরীঃ প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
(১২) জোবাইদা নাসরীনঃ কল্পনা চাকমা বলে কেউ ছিল না!, প্রথম আলো,আপডেট: ১৩ জুন ২০১৯
(১৩) সজীব চাকমাঃ কল্পনা চাকমা অপহরণ: রাষ্ট্রের বিচারহীনতা ও বৈষম্যের ২৪ বছরঃ Hill Voice -জুন 12, 2020
(১৪) এবং আরও বহু তথ্য যা অন্যান্য বই ও ইন্টারনেট থেকে পাওয়া…