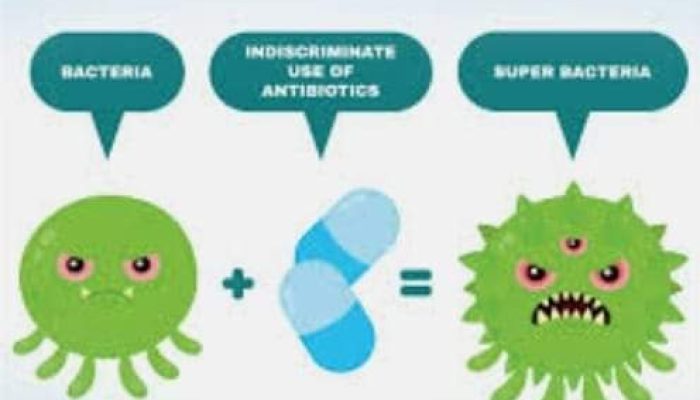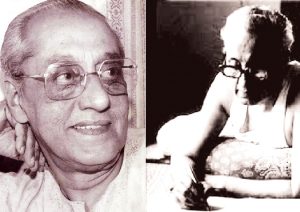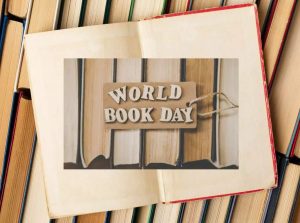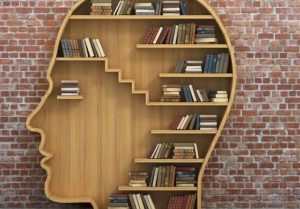অনেকদিন বাদে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কী-প্যাড ধরছি। যদিও এসব ব্যাপার নিতান্তই নীরস তত্ত্বের কচকচি। কারোরই তাতে বিশেষ যায়-আসে না। এটাও জানি, এসব ব্যাপারে বেশি বলে ফেললে সফল চিকিৎসক হয়ে ওঠা যায় না। তবু আকাট বেকুবের মতো মাঝে মাঝে চিৎকার করে ফেলি। আবার গলা বসে গেলে চুপ করে যাই। তাতে জগৎ ও জীবনের কুটোটাও বদলায় না, সেটাও নিশ্চিতভাবেই জানি।
আমার জ্ঞানগম্যি বা অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প। শিশুদের চিকিৎসা নিয়ে অল্প কিছু কাজ করার চেষ্টা করি। রোজ অন্তত ঘন্টাখানেক পড়াশোনা করবো না, এরকম বড় ডাক্তার এখনো হয়ে উঠতে পারিনি। প্রতিদিন শিখি। আর প্রতিদিনই আরও বেশি করে বুঝতে পারি, শিখেছি যৎসামান্য। না শেখার ভাগটাই সমুদ্রের মতো। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে সারা জীবন পড়াশোনা করে গেলেও শেখা শেষ হবে না। কিন্তু, লাভ কী তাতে? হাজার একটা গাইডলাইন, লক্ষটা ইন্ডিকেশন-কন্ট্রাইন্ডিকেশন-সাইড এফেক্ট পড়ে ফেললাম। শিখে প্রতিদিনের প্র্যাক্টিসে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। মাথায় রাখতে চাইলাম, কীভাবে ধাপে ধাপে ওপরের দিককার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়। তারপর? চোখের সামনে দেখলাম- যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার আগে অসংখ্য থিওরির পাতা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হই; সেই অ্যান্টিবায়োটিক দিব্যি রোগী নিজে নিজেই ব্যবহার করা শুরু করে দিচ্ছেন। কার পরামর্শে? যাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিদ্যালয়ের গন্ডি ছাড়ায় নি। মেরোপেনেম, ভ্যাঙ্কোমাইসিন, লিনেজোলিড ইত্যাদি যথেষ্ট বড় ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিব্যি প্রেস্ক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর ডোজ? থাক সে কথা। কোথায়, কাকে, কে আটকাবে? মাছের ঝিলে, গবাদিপশুর খাদ্যে কোটি, কোটি অ্যান্টিবায়োটিক! কী লাভ পড়াশোনা করে? এত মেডিক্যাল কলেজ, বইপত্র, রাত জাগা… ইত্যাদি প্রভৃতি মিলিয়ে ঠিক কী হয়?
পাশ করা ডাক্তার মানে আগে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপাতাটি ভাবতাম। সে ভুল আমার বহুদিনই ভেঙেছে। ফাইনাল ইয়ারে স্ত্রী ও প্রসূতীবিদ্যার পরীক্ষায় ‘গাইনিকোলজি’র আলাদা একটা বই হয় এটাও না জানা লোক তিনমাস বাদে পাশ করে বেরিয়ে গেছে, এটা চোখে দেখা। বুকের খাঁচার ভেতর দুটো হৃৎপিণ্ড আর একটা ফুসফুস; এরকম বলার পরেও প্রথমবারে না হোক, পরেরবার পাশ করে গেছে। উঁহু, খুব পড়াশোনা করে ভোল বদলে গেছিল ভাববেন না। সে গুঢ় কারণ আপনিও জানেন, আমিও জানি। এবং, এটা রাজ্যের এক নম্বর কলেজের গল্প। যেখানে সবচেয়ে ভালো র্যাঙ্ক করা ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। হিসেব মিলিয়ে আজকের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কলেজগুলোর কথা ভেবে নিন। পেছন দরজার ছাড়পত্র থাকলে ছ-সাত লক্ষ র্যাঙ্ক করেও ডাক্তারি পড়া যাচ্ছে। আর সবাই খাতায়-কলমে পাশও করছে। কাজেই যা হওয়ার তাই হচ্ছে।
ক’দিন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন গাইডলাইন আসে। ক’দিন হইচই হয়। অবশ্য, গুটিকয়েক লোকই হইচই করে। প্রতিদিন একটার পর একটা অ্যান্টিবায়োটিক ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলে। রিসার্চ কোম্পানিগুলো অ্যান্টিবায়োটিক বানানোর পেছনে সময় বা অর্থব্যয় করতে চায় না আজকাল। কী হবে নতুন আবিষ্কার করে? সেই তো গবেষকের বহু সাধনার ধন গিয়ে পড়বে কিছু অযোগ্য মানুষের হাতে। ক’মাসেই অ্যান্টিবায়োটিক স্রেফ ‘মরে যাবে’। লিখে রাখুন, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকেও ভয়ানক জিনিস হতে যাচ্ছে। সবই নিশ্চিত ভবিতব্য জানি। তবু… অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে অজস্র বাচ্চাকে মারা যেতে বা ধুঁকতে দেখেছি বলে আমি চিৎকার করি। সফল চিকিৎসক হওয়ার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা করতে চাই বলে চিৎকার করি। এখনো চোখের সামনে থেকে আয়নাটা সরে যায়নি বলে চিৎকার করি। ওদিকে কিছু মানুষের গুটিকয়েক ভয়ার্ত চোখের সামনে নদীর মতো বয়ে যায় গ্যালন গ্যালন অ্যান্টিবায়োটিক।
একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের খিচুড়ির মতো মিশ্রণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। সরকারের তরফে জানানোও হয়েছে বারবার। কী লাভ হয়েছে? পাতলা পায়খানা হলেই মুড়ি-মুড়কির মতো ওফ্লক্সাসিন-অরনিডাজোল, সিপ্রোফ্লক্সাসিন-মেট্রোনিডাজোলের খিচুড়ি বিতরণ শুরু হয়ে যায়। ব্র্যান্ডের নামগুলো সবার মুখে মুখে ফেরে। সেফিক্সিম-অ্যাজিথ্রোমাইসিন সহ আরও কত রকমের খিচুড়ি বাজারে চলে তার ইয়ত্তা নেই। কোনও উন্নত দেশে এসব চলে না। তাতে অসুবিধে নেই। ভারতীয় উপমহাদেশ সারা পৃথিবীর সস্তায় ময়লা ফেলার জায়গা।
কোন পথে শাপমুক্তি কেউ জানে না। পেনিসিলিন আবিষ্কারকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কাল বলে ধরা হয়। আবিষ্কারের বছরখানেক বাদেই বিজ্ঞানী ফ্লেমিং বলেছিলেন, আমাদের অবিমৃষ্যকারিতায় অ্যান্টিবায়োটিক তার কর্মক্ষমতা হারাবে। অ্যান্টিবায়োটিক-পূর্ব যুগের অসহায়তা ফিরে আসবে। সেই যুগ, আমরা যার গল্পই শুনেছি শুধু। যখন সামান্য কাটা ঘা বিষিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ মারা যেত। প্রসূতি-মৃত্যু প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল।
যে ধ্বংসের খেলা শুরু হয়েছে তাকে রোধ করা প্রায় অসম্ভব। এখনো অব্দি হাসপাতালের বাইরে কোলিস্টিন, টিজেসাইক্লিন, টিকোপ্ল্যানিন দেখতে পাইনি। সেটাও ক’দিন বাদে দেখা যাবে নিশ্চিতভাবেই। গুটিকয়েক বাজার-অসফল ‘ছোট ডাক্তার’ নিজেদের ক্ষুদ্র গন্ডিতে ফার্স্ট-লাইন, সেকেন্ড-লাইন অ্যান্টিবায়োটিকের তত্ত্ব কপচাবে। তাদের কেউ পাত্তা দেয় না। কোন ক্ষুদে মাছ স্রোতের বিপক্ষে ছোটে, জানতে সবার ভারী বয়ে গেছে। আসলে সেই ক্ষুদে মানুষগুলো কোনও এক পাঁচ বছরের অয়ন, তিন বছরের সাবিনা কিংবা দশ মাসের ইব্রাহিমকে কিছুতেই ভুলতে পারে না; যারা চোখের সামনে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণে স্রেফ ঝরে গেছে। ভুলতে পারে না বলেই চিৎকার করে। করেই যায়…
ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের থেকেও ভয়াবহ কালো মেঘে আঁধার নামে। দিগন্তজোড়া, আলোর দিশাহীন আঁধার।